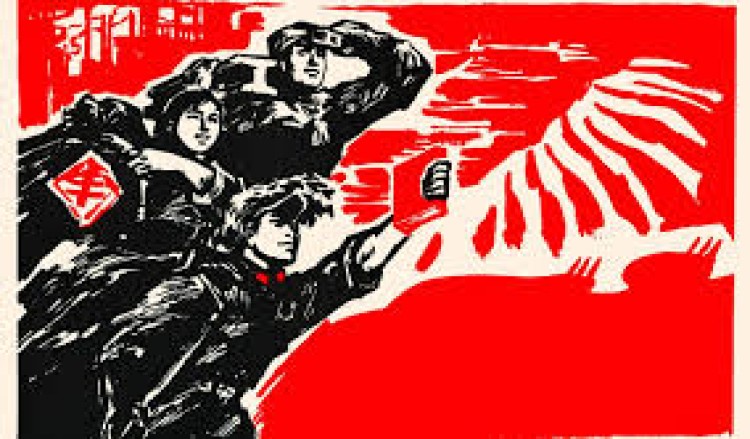একটি বিদ্যায়তন থেকে অবসর নেওয়ার বেশ কিছুদিন পরে একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠান চলাকালিন অর্থনীতির দুয়েকজন তরুণ শিক্ষকের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তাঁরা কম্যুনিজম সম্পর্কে বীতস্পৃহ, কেবল এজন্য নয় যে সোভিয়েত রাশিয়া ভেঙ্গে গেছে, সেখানে গোষ্ঠিপতির রাজত্ব চলছে বা চিনে যেটা চলছে তাকে তাঁরা সমাজতন্ত্র বলে মনে করেন না, তাঁদের তাত্বিক যুক্তি, উৎপাদনের ধরণেই বিপুল পরিবর্তন এসেছে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এসে গেছে এখন আর মার্ক্সের সময়ের শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের ভিত্তিতে সমাজকে দেখলে চলবে না। তাছাড়া, সেই ভালগার ছেঁদো যুক্তিতো আছেই যেখানে মানুষের বিভিন্নতা ও উচ্চ-নিচ কর্মদক্ষতা ও যোগ্যতার জন্য বন্টনের সাম্য সম্ভব নয়, এবং উচিত নয় কারণ তার ফলে জগতের উৎপাদনশীলতা কমবে। যাঁরা কথা বলছিলেন তাঁরা দক্ষিণপন্থী নয়, বরং বামপন্থীই বলা যায়, কিন্তু রাজ্য ও দেশের মধ্যে বামপন্থার অতিক্ষীণ ও ক্রমহ্রাসমান অবস্থা দেখতে দেখতে বামপন্থা তথা সমাজতন্ত্রের প্রতিই তাঁদের সংশয় তৈরি হয়েছে। মার্কসবাদের সত্যতা সম্পর্কেও তাঁরা সংশয়দীর্ণ। এই সংশয় তথা অবিশ্বাসের ছাপ প্রকট হয়ে উঠেছে। পৃথিবী ব্যাপী অতি-দক্ষিণপন্থার, বকলমে ফ্যাসিবাদীদের, দাপাদাপি ক্রমাগত বাড়া সত্বেও এদেশে একাডেমিক স্তরে কম্যুনিজম, মার্কসবাদ, লেনিনবাদের চর্চা খুব একটা চোখে পড়ছে না। বামদিক ঘেষা কিছু যশস্বী দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ, ইতিহাসবিদ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এখনো বর্তমান আছেন কিন্তু কতদিন সেই ধারা বজায় থাকবে তা নিয়ে সংশয়ের অবকাশ তৈরি হয়েছে।
যে কথা আমার তরুণ বন্ধুরা বলছিলেন সেটা যে কেবল তাঁদের কথা এমনটা নয়। যশস্বী মার্কসবাদী চিন্তক ডেভিড হার্ভে (যিনি এ কম্প্যানিয়ন টু মার্ক্স’স ক্যাপিটাল লিখেছেন) ২০১৯ সালের একটি ইন্টারিউতে কতকটা এমন কথাই বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন,
“আমি মনে করি পুঁজিবাদের অভ্যন্তরে যে রূপান্তর ঘটছে সে বিষয়ে বামপন্থীরা যথাযথ সাড়া দেননি এবং কিছু পুরোনো ভুলের পুনরাবৃত্তি করার বিপদের মুখে রয়েছেন।
১৯৮০-৯০এ পশ্চিমে বড় মাত্রায় বিশিল্পায়ন হয়েছিল, অধিকাংশই প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের জন্য, এবং প্রথাগত শ্রমিক-শ্রেণির জনতাকে রক্ষা করার জন্য বামপন্থীরা তার বিরোধিতা করেছিল। বামপন্থীরা সেই লড়াইটা হেরে গিয়েছিল, সেই প্রক্রিয়ায় বিশ্বাসযোগ্যতার যথেষ্ট ক্ষয় হয়েছিল। এখন আমরা দেখছি কৃত্রিম প্রযুক্তি পরিষেবা ক্ষেত্রে সেটাই করতে চলেছে যা অটোমেশন ম্যানুফাাকচারিংএর ক্ষেত্রে ঘটিয়েছিল। প্রযুক্তিগত কারণে যা উবে যেতে চলেছে তেমন কিছুকে রক্ষা করার প্রচেষ্টার বিপদের মুখে রয়েছে বামপন্থীরা।
আমার মনে হয় আমাদের গঠনমূলক বামপন্থী হয়ে ওঠা দরকার, পুঁজির থেকে অনেক বেশি এগিয়ে থেকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, অটোমেশন সমেত সম্পূর্ণ নতুন কাজ ও নিয়োগ কাঠামোর সামগ্রিক ধারণাকে আঁকড়ে ধরা প্রয়োজন। কিন্তু তার মানে হল এক বিকল্প রাজনীতি। অনেক দেশেই ধ্রুপদি শ্রমিক শ্রেণির অস্তিত্ব আর নেই, তার সঙ্গেই সনাতনী বাম রাজনীতির ভিত্তি উবে গিয়েছে। অবশ্যই, তা সম্পূর্ণ চলে যায়নি, তবে তা গুরুতরভাবে খর্বিত হয়েছে।
সুতরাং, আমাদের দরকার নুতন রূপের বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গী যা নিবদ্ধ থাকবে যাকে আমি বলছি পুঁজিবাদ-বিরোধী রাজনীতি: কেবল কাজের জায়গায় নিবদ্ধ থাকবে না, বরং প্রাত্যহিক জীবনযাপনের, আবাসনের, সামাজিক সুরক্ষা বন্দোবস্তের অবস্থা, পরিবেশ সম্পর্কে ভাবনার, সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও সাংস্কৃতিক রূপান্তরের বিষয়ের প্রতিও নিবদ্ধ হবে।
হার্ভের কথার মানে হল যে, মার্ক্সের সময়কাল থেকে অনেক দেশে পুঁজিবাদ এতটাই পরিবর্তিত হয়েছে যে মার্ক্স যে শ্রমিক শ্রেণীর কথা বলেছিলেন তা আর নেই। আগেই বলেছি, এরকম মনোভাব অনেক বামপন্থীই পোষণ করছেন। একটু ভেবে দেখা যাক।
কিছু বিষয় রয়েছে যা পরিবর্তনশীল নয়- যেমন, পুঁজিপতিদের চাহিদা, শ্রমিক শ্রেণিকে শোষণ করে গড় মুনাফার হার অর্জন করা। কিছু বিষয় পরিবর্তনীয়। ধরুন কেউ মনে করেন যে শ্রমিক হতে হলে কারখানায় কাজ করতে হবে। তারপর যদি দেশে কারখানার শ্রমিকের সংখ্যা কমে যায়, তাহলে হার্ভের মতো এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে যে শ্রমিক শ্রেণি উবে যাচ্ছে, সঙ্কুচিত হচ্ছে অথবা মৌলিকভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। এই ক্ষেত্রে, আসলে যা পরিবর্তন করা দরকার তা হল শ্রমিক শ্রেণির সম্পর্কে ভুল দৃষ্টিভঙ্গি। যদি শ্রমিক শ্রেণির মৌলিক প্রকৃতি সম্পর্কে কারো দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়, তাহলে এর অর্থ এই নয় যে শ্রমিক শ্রেণি নিজেই মৌলিকভাবে পরিবর্তিত হয়েছে,
ধ্রুপদী বা অ-ধ্রুপদী শ্রমিক শ্রেণি বলে কিছু হয় না। শ্রমিক শ্রেণি গঠিত হয পুরুষ এবং মহিলা (এবং অনেক শিশু) দ্বারা যাদের (ক) উৎপাদনের উপকরণের উপর নিয়ন্ত্রণ নেই, (খ) তাই জীবিকা নির্বাহের জন্য তাদের শ্রমশক্তি বিক্রির উপর নির্ভর করতে হয়, (গ) কর্মক্ষেত্রে উৎপাদনের উপকরণ নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিদের কাছে তাদের উৎপাদিত পণ্যের একটি বড় অংশ সমর্পণ করতে হয় এবং (ঘ) উৎপাদন ও বিনিময় এবং প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উপর তাদের কার্যকরভাবে খুব কম নিয়ন্ত্রণ থাকে। মার্ক্সের সময়েও এটি সত্য ছিল। ১৯৭০-এর দশকে এটি সত্য ছিল । এবং, এটি এখনও সত্য।
মার্ক্সের সময় এবং তার আগে, মানুষের খাদ্য, পানীয়, আশ্রয়, পোশাক, হাসপাতাল, গ্রন্থাগার, রাস্তাঘাট, থিয়েটার ইত্যাদির প্রয়োজন ছিল এবং এখনও তা রয়েছে। এই জিনিসগুলি তখনও আকাশ থেকে পড়েনি, শ্রেণিকক্ষে বা আলোচনা কক্ষে বা সংসদে তৈরি হয়নি। এখনও তা হয় না। এই দ্রব্য ও পরিষেবাগুলি, যেরূপেই তা হোক না কেন, তখনকার মতো এখনও প্রকৃতি এবং শ্রমের (শারীরিক এবং মানসিক) মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সহ সকল উৎপাদনের জন্য কেবল উৎপাদনের উপকরণই যথেষ্ট নয় (যার মধ্যে প্রকৃতি থেকে আহরণ করা বস্তুগত সম্পদও আছে), এছাড়াও প্রয়োজন সামাজিক আন্তক্রিয়া মার্ক্স যাকে উৎপাদনের সামাজিক সম্পর্ক বা শ্রেণি সম্পর্ক বলেছিলেন। মার্ক্সের সময় এবং তার আগে এটি সত্য ছিল। এটি এখনও সত্য। শ্রমিক শ্রেণির মানুষ - পুরুষ ও নারী, কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ, সমকামী ও সরল, হিন্দু, খ্রিস্টান ও মুসলিম, নিম্ন বর্ণ ও উচ্চ বর্ণ ইত্যাদি - খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয় এবং রাস্তা ইত্যাদি উৎপাদন করে, কিন্তু তাদের চাহিদা অপূর্ণ থাকে এবং তারা অনিশ্চয়তার জীবনযাপন করে। তখনও এটি ছিল এখনকার মতো। মানুষ লাঙল, হাতুড়ি বা কলম দিয়ে কাজ করে কিনা, অথবা তারা তা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহার করে কিনা, তা ভিন্ন বিষয়। তারা ব্যাংকে কাজ করে কিনা, খনির ভেতরে কাজ করে কিনা, অথবা খামারে কাজ করে কিনা তাও ভিন্ন বিষয়।
যদি শ্রমিক শ্রেণিকে কেবল শিল্প শ্রমিক হিসেবে দেখা হয় (অর্থাৎ যারা গাড়ি বা বিস্কুট ইত্যাদি উৎপাদন করে), তাহলে সেটি হবে একটি সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি, যার রাজনৈতিক অভিঘাত এমন যে তা শ্রমিক শ্রেণির রাজনৈতিক প্রাধান্য লঘু করে। তাছাড়া, শ্রমিক শ্রেণি উবে যাচ্ছে এই ধারণাটি একটি বিভ্রান্তিকর এবং জাতীয়তাবাদী ধারণাকে প্রকাশ করে। মাত্র কয়েকটি দেশের অভিজ্ঞতালব্ধ প্রমাণের ভিত্তিতে, যেখানে বিশ্ব জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু (অর্থাৎ প্রধানত সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব) বাস করে, শ্রমিক শ্রেণি সম্পর্কে এই দৃষ্টিভঙ্গি গভীরভাবে ইউরো-আমেরিকান-কেন্দ্রিক। চিন (যার অর্থনৈতিক আকার এখন পিপিপির পরিভাষায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়েও বেশি), ভারত এবং গ্লোবাল সাউথের অন্যান্য অংশে লক্ষ লক্ষ শিল্প শ্রমিক কি গুরুত্বপূর্ণ নয়?
বিশ্বের কোন কোন দেশে কমিউনিস্ট আন্দোলন সাশ্রয়ী আবাসন বা এই জাতীয় সমস্যাগুলিকে উপেক্ষা করে? উদাহরণস্বরূপ, ভারতে বামপন্থী আন্দোলন সামাজিক নিপীড়ন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের মধ্যে অযৌক্তিকতার প্রবর্তন, মুসলমানদের অধীনতা, জমি দখল, বিদ্যুতের বেসরকারীকরণ, ভর্তুকিযুক্ত খাদ্য ইত্যাদির বিরুদ্ধে লড়াই করে আসছে।
কর্মক্ষেত্রের সমস্যার উপর গুরুত্ব হ্রাস করে শহরের দৈনন্দিন জীবনের এবং সাশ্রয়ী আবাসনের সমস্যার উপর আরোপ করার কথা বলা হয়েছে। মার্ক্স যে পুঁজিবাদের কথা বলেছিলেন তা কি এতটাই মৌলিকভাবে পরিবর্তিত হয়েছে যে শোষণের হার বৃদ্ধির সমস্ত পুঁজিবাদী পদ্ধতি সমেত কর্মক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণি যে সমস্যার মুখোমুখি হয়, তা কি আর গুরুত্বপূর্ণ নয়?
এই নব্য “মার্কসবাদি’ প্রকল্পের বিপরীতে প্রকৃত মার্কসবাদি দৃষ্টিভঙ্গি খুব সোজা সাপটা। সেই মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি আগেও বলেছে এখনো বলে যে,
ক. শ্রেণি সম্পর্ক এবং পুঁজিবাদকে উৎখাত করতে হবে কারণ তাদের সংস্কার করা যাবে না;
খ.এর জন্য প্রয়োজন হল বিভিন্ন সামাজিক পটভূমির শ্রমিক এবং ক্ষুদ্র উৎপাদনকারীদের, তাদের দলগুলির সহায়তা এবং নেতৃত্বে, গণতান্ত্রিকভাবে সংগঠিত স্ব-মুক্তি সংগ্রাম,
গ. একটি নতুন সমাজের জন্য সংগ্রামকে অবশ্যই
১. সাধারণ গণতান্ত্রিক অধিকার (বাকস্বাধীনতা এবং সমাবেশের অধিকার সহ) এবং সামাজিকভাবে নিপীড়িত গোষ্ঠীগুলির (যেমন নারী, বর্ণবাদী, সংখ্যালঘু এবং আদিবাসীদের) নির্দিষ্ট গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য সংগ্রাম,
২.শোষণকারী সম্পত্তির-মালিক শ্রেণি এবং তাদের রাষ্ট্র থেকে অর্থনৈতিক-পরিবেশগত-সাংস্কৃতিক সুবিধা (যেমন জীবিকা নির্বাহের মজুরি; দূষণের মাত্রা হ্রাস; সাংস্কৃতিক বিনোদনের উপায়ের ব্যবস্থা; শহরের পাবলিক স্পেসে সাশ্রয়ী মূল্যের প্রবেশাধিকার) আদায়ের সংগ্রাম, এবং
৩.শ্রেণি সম্পর্ক এবং পুঁজিবাদ বিলোপের লড়াইয়ের অংশ হয়ে উঠতে হবে।
কম্যুনিস্টরা এমনটা মনে করে না যে আধিপত্য বিস্তারকারীদের দেওয়া শ্রেণি সংক্রান্ত যুক্তির ব্যাপারটা শাশ্বত, অর্থাৎ প্রাচীনকাল থেকে কোনো না কোনো প্রাধান্য বিস্তারকারী শ্রেণির কাছে যে শ্রমিকেরা মাথা নিচু করে রয়েছে তা চিরন্তন, অবশ্যম্ভাবী ও অপরিবর্তনীয়, যে রকমটা প্রাধান্য বিস্তারকারীরা আরোপ করতে চায়। কম্যুনিজমের উপপাদ্য হল যে, উৎপাদনের অন্য রকম সংগঠন ও সম্পর্ক সম্ভব যা সম্পদের বৈষম্য এমনকি শ্রমের বিভাজনকেও অপসারিত করবে। ব্যক্তি কর্তৃক বিপুল সম্পদের দখল ও উত্তরাধিকারের মাধ্যমে তার মালিকানা অর্পণের বন্দোবস্তের বিনাশ হবে। নাগরিক সমাজের থেকে আলাদা দমনমূলক রাষ্ট্র থাকা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হবে : প্রকৃত উৎপাদকদের পুনর্গঠনের দীর্ঘ প্রক্রিয়া রাষ্ট্রের অবসান ঘটাবে।
বিশ্বজোড়া কম্যুনিস্ট রাজনীতির সঙ্কোচন ঘটলেও কেবলমাত্র কম্যুনিস্ট আন্তর্জাতিকতাই পারে মানুষের অনিশ্চয়তার যাপনকে নিশ্চিত ঝুঁকিহীন যাপনের রাস্তায় নিয়ে যেতে, পারে বিশ্বজোড়া সামরিক অত্যাচার ও যুদ্ধের তাণ্ডবকে আটকাতে। প্রযুক্তির চরম উন্নতি ঘটলে কম্যুনিজম অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায় না বা মার্কসবাদের অন্তর্বস্তু শ্রেণি সংগ্রাম অন্তর্হিত হয় না। শ্রেণি হিসেবে অধিক মজুরির শ্রমিকও শ্রমিক শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত, কম মজুরির শ্রমিকও তাই। শ্রমিকদের মধ্যে মজুরির পার্থক্য, বিভিন্ন শিল্পে মজুরির পার্থক্য, দেশে দেশে মজুরির তারতম্য এসব মার্ক্সের সময়েও ছিল, এখনো আছে। প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনও ছিল। তাতে মালিক শ্রেণির প্রাধান্য বিস্তারকারী ভূমিকা বা শোষণ করার ও মুনাফা করার উদ্দেশ্যের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। কম্যুনিস্ট রাজনীতির অন্তর্বস্তুর কোনো পরিবর্তনের কথা তাই উঠতেই পারে না। জোরের সঙ্গেই সে কথা বলার দরকার কম্যুনিস্টদের।
১৭৭ বছর আগে কম্যুনিস্ট ইস্তাহার প্রকাশের সময় কম্যুনিজমের যে ভূত দেখছিল ইউরোপের বুর্জোয়ারা, আর কিঞ্চিদধিক তিন দশক আগে, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর, কম্যুনিজমকে ভূত হয়ে যেতে দেখেছিল যারা, তারা আজ আবার কম্যুনিজমের ভূত দেখতে শুরু করেছে। চার দশকের বেশি সময় ধরে নব্য উদারবাদি অর্থনীতি বাঁধাহীন ভাবে চালানোর পরেও, একমেরু বিশ্বে পুঁজির একছত্র আধিপত্যের পরেও, চিলি থেকে ব্রাজিল, ভেনেজুয়েলা থেকে লিবিয়া, ইরাক থেকে আফগানিস্তান সর্বত্র অপছন্দের রেজিম চেঞ্জের সফল বা ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালাতে হয়েছে। তারপরেও মার্কিন দেশের কংগ্রেসে “গুরুত্বপূর্ণ কম্যুনিজম শিক্ষণ আইন (ক্রুসিয়াল কম্যুনিজম টিচিং এ্যাক্ট)” প্রণয়নের জন্য পেশ করা হয়েছে, এবং গত ৬ ডিসেম্বর তা হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভে অনুমোদিত হয়েছে ৩২৭-৬২ ভোটের ব্যবধানে। রিপাবলিকানরা বিলটি পেশ করলেও বহু ডেমোক্রাট যে তা সমর্থন করেছে বোঝাই যাচ্ছে কারণ হাউসে রিপাবলিকানদের সংখ্যা ২২০। আইনটি কম্যুনিজম শেখাবে না, কম্যুনিজমের বিপদ শেখাবে। আইনটির উদ্দ্যেশ্য হিসেবে বলা হয়েছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ক) শেখানো হবে যে, কম্যুনিজম ১০ কোটি মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে, খ) বোঝানো হবে কম্যুনিজমের বিপদ ও গ) বোঝানো হবে যে ১৫০ কোটি মানুষ এখনো কম্যুনিজমের আওতায় থেকে ভুগছে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি বেশ কিছুদিন ধরেই কম্যুনিজমের ভূত দেখছেন। নির্বাচনের টিকেট পাওয়ার লড়াইএর সময়ই তিনি বলেছিলেন কম্যুনিস্ট ও মার্ক্সিস্টদের অভিবাসন তিনি রদ করবেন। এর পরে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার পরে বলেছেন সেনাবাহিনীতে কম্যুনিস্ট ও মার্ক্সিস্টদের ঠাঁই হবে না। যে দেশে কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য সংখ্যা ১৫ হাজার (জনসংখ্যা ৩১ কোটি), এবং তার মধ্যে সক্রিয় অত্যন্ত কম, সেখানে কী এমন ঘটল যে কম্যনিস্টদের বিরুদ্ধে সাজো সাজো রব উঠেছে। কারণ, ভয় ধরেছে। জেনারেশন জেড-এর ২৮ শতাংশ কম্যুনিজমকে ভালো মতাদর্শ বলেছে। তাদের ১৮ শতাংশ মনে করে যে কম্যুনিজম ক্যাপিটালিজমের থেকে উত্তম মতাদর্শ এবং আমেরিকায় তা বিবেচনা করা দরকার।
বিশ্বজুড়ে যে অতি দক্ষিণপন্থার দাপট বেড়েছে তার মূলে রয়েছে ক্রমবর্ধমান অসাম্য, অনিশ্চিত যাপন, দারিদ্র ও কর্মহীনতা। এগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই-এর আসল শক্তি বামপন্থীরা। কিন্তু এই ভয়ানক ত্রুটিগুলির উপর ভিত্তি করেই কোথাও ট্রাম্প, কোথাও অর্বান (হাঙ্গেরি), কোথাও মোদি, কোথাও এরদোগান (তুরস্ক), কোথাও মিলেই (আর্জেন্টিনা), কোথাও মেলোনি ((ইতালি)র উত্থান ও ক্ষমতা দখল। জনমোহিনী এবং বিভাজনের কথা বলে মানুষের মনে ঘৃণা ও হিংসার সঞ্চার করেই এই অতি দক্ষিণপন্থার বাড়বাড়ন্ত। শ্রেণি বিন্যাসের পরিবর্তন, মালিক শ্রেণির দ্বারা শ্রমিক শ্রেণির শোষণ, অসাম্যের হ্রাস, শ্রমিকের জীবন যাপনের অনিশ্চয়তা বিনাশ এগুলির কোনো কিছুই অতি দক্ষিণপন্থীদের উদ্দেশ্য নয়। ধর্ম, বর্ণ, জাতি (রেস), লিঙ্গ, অভিবাসী ইত্যাদির ভিত্তিতে বিভেদ সৃষ্টি করে শাসন করাই তাদের উদ্দেশ্য। এর একদম বিপরীতে বামপন্থীরা সমাজের ওইসব পাপের বিরুদ্ধে লড়তে পারে সমাজের সমস্ত নিপীড়িত বর্গকে একত্র করে, যারা সকলেই একত্রে শ্রমিক শ্রেণি।
ভাবনা সূত্র: হার্ভের সাক্ষাতকারের প্রেক্ষিতে কানাডার ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু জে দাস “দি গুড এণ্ড ব্যাড ইন ডেভিড হার্ভে’জ পপুলার মার্ক্সিজম” শীর্ষ নামের একটি সমালোচনামূলক নিবন্ধ লেখেন সেজ জার্নালস-এর ৪৯ নং ভল্যুমের ৭-৮ নং ইস্যুতে। সেই নিবন্ধের উপর বহুলাংশে ভিত্তি করা হয়েছে।