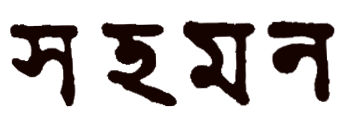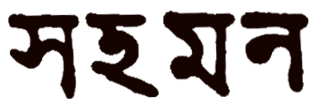আমাদের দেশ ভারতে “আধুনিক পরিবেশ ভাবনা”-র উদ্ভব ঘটেছে ১৯৭০ সালের আশপাশে। এই সময় থেকে পরিবেশ-প্রতিবেশকে কেন্দ্র করে নানান কথা আর সেই কথা থেকে নানান প্রশ্ন উঠতে শুরু হয়। মনে রাখতে বাধা নেই যে গত শতকের এই বহু-চর্চিত “সত্তর দশক”-এই আবার আমরা দেখা পেয়েছি নতুন ধরনের রাজনৈতিক চিন্তার। আন্তর্জাতিক স্তরে যে রাজনৈতিক প্রশ্নগুলি সেই সময়ের মানুষদের স্থিতাবস্থা পরিবর্তনের প্রয়াসে সামিল হতে উদ্বেল করে তুলেছিলো, আমাদের দেশের পরিবর্তনকামী শক্তিগুলিও এক রকমভাবে প্রায় কাছাকাছি ধরণের চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হচ্ছিলেন, তখন তাই সঙ্গত কারণেই শ্লোগান উঠত, “গঙ্গা-মেকং দিচ্ছে ডাক”, বা “… ওরে আমার তরঙ্গিণী ভাগীরথী গাং/ ডাকে তোরে ভল্গা-মেকং, ডাকেরে হোয়াং…”।
সারা বিশ্বের কাছে অবিভক্ত ভারতের পরিচয় ছিল একটি উপমহাদেশ হিসেবে। ভৌগোলিক বিস্তারের দিক থেকে দেখলে এই বর্ণনা অনেকটাই বাস্তবের কাছাকাছি। ভারতীয় উপমহাদেশের ভৌগোলিক বিস্তার বিপুল। অবিভক্ত ভারতের কথা ধরলে তা দাঁড়ায় আজকের পেশোয়ার বা কুষাণ বংশের বর্ধিষ্ণু রাজধানী পুরুষপুর থেকে প্রাগজ্যোতিষ, যা আজকের আসাম। সড়কপথে দূরত্ব হবে কম-বেশি প্রায় ২৫০০ কিমি। অন্য দিকে, আফগান সীমান্ত থেকে কন্যাকুমারী, দূরত্ব হবে কম-বেশি ৪৩০০ কিমি। আমরা যদি এই দূরত্বগুলির সঙ্গে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের শহরের মধ্যকার দূরত্বগুলির তুলনা করি, তাহলে আমরা উপমহাদেশের বিশালত্ব সম্পর্কে খানিকটা আঁচ করতে পারি। যেমন লন্ডন থেকে বার্লিন, দূরত্ব সড়কপথে কম-বেশি ১১০০ কিমি! মস্কো থেকে ভ্লাডিভস্তক, রেলপথে ৭৫০০ কিমি! মনে রাখতে হবে অবিভক্ত রাশিয়া পৃথিবীর ক্ষেত্রফলের দিক থেকে বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো দেশ, সেই দেশটিও অবিভক্ত ভারতের মাত্র চারগুণ বেশি স্থলভাগ অধিকার করে আছে। আমাদের দেশে রয়েছে ১৫টি জলবায়ু অঞ্চল। ভারতের মূল ভূখণ্ডের বেলাভূমির দৈর্ঘ ৬১০০ কিমি আর যদি আমরা আন্দামান-নিকোবর ও লাক্ষ্মাদ্বীপের অংশটুকু হিসেবে আনি, তাহলে এই দৈর্ঘ্য বেড়ে দাঁড়াবে প্রায় ৭৫০০ কিমি। এদেশে একই সঙ্গে রয়েছে মরুভূমি, রয়েছে বরফাচ্ছাদিত অঞ্চল, প্রচুর বৃষ্টিপাতের অঞ্চল থেকে প্রায় শুখা অঞ্চল, মালভূমি, উচ্চ পর্বতমালা। এদেশেই দেখা মিলবে পূর্ববাহিনী থেকে পশ্চিমবাহিনী নদীর। আসানসোলে যখন খুব গরম, লাহুল-স্পিতি-তে তখন বরফের আচ্ছাদন! তাই এখানকার মানুষদের চেতনায় পরিবেশ-ভাবনায় বৈচিত্র্য থাকাই স্বাভাবিক।
আমাদের চেনা মহলে পরিবেশ নিয়ে টুকটাক কথাবার্তা শোনা যেতে থাকে সেই যাকে বলে “প্রোভার্বিয়াল” সত্তর সালের আশপাশে। অন্যান্য নানান সামাজিক-সাংস্কৃতিক আর তার গা ঘেঁষে যে সব রাজনৈতিক কথা উঠে আসে, সেগুলোর উৎস বেশি ভাগ ক্ষেত্রেই সেই সত্তরেই। আজকের স্কুল পাঠক্রমে পরিবেশ নিয়ে পড়াশুনো শুরু হয়ে যায় প্রাথমিক স্তর ছাড়িয়েই। পাঠ্য বইতে থাকে গাড়োয়াল হিমালয়ের “চিপ্কো আন্দোলন” বা গাছ বাঁচানোর আন্দোলনের কাহিনী। ক্ষুদেদের জন্য লেখা বলেই হয়ত, পরিবেশ সচেতনতার প্রাথমিক পাঠ দেওয়াকে বেশি ওজন দিতে গিয়ে এ দেশের মানুষদের পরিবেশ সচেতনতার শুরু হিসেবে সেই চিপকো-ই প্রাধান্য পেয়ে গেছে। কিন্তু ভারতে পরিবেশ সচেতনতার এবং সেই সচেতনতাকে জড়িয়ে নিয়ে চার পাশের প্রকৃতিকে বাঁচানোর প্রয়াস শুরু হয়েছে চিপকো আন্দোলন শুরুর বেশ অনেককাল আগে থেকেই।
একটি অঞ্চলের পরিবেশ-ভাবনায় ভূগোলের যেমন ভূমিকা আছে, সেই ভাবনাকে একটি সংহত রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে ইতিহাস বড় কম ভূমিকা পালন করে না। এদেশে নানান রাজবংশ রাজত্ব করেছে, তাদের হাত ধরে ইতিহাস, সংস্কৃতি নির্মাণের পাশাপাশি তৈরি হয়েছে পরিবেশের ওপর প্রভাববিস্তারকারী নানান কাজের ইতিহাসও। প্রত্যেক রাজবংশ তাদের রাজত্বের আগে থেকে চলে আসা পরম্পরা মেনে যেমন জমি, জল, চারণভূমি, ক্ষেত, খামার ও ফসল ফলানো বিষয়ে আগের পদ্ধতি বজায় রাখার পাশাপাশি তাদের নিজেদের পছন্দ মতো করে নতুন কিছু কিছু পদ্ধতি চালু করেছে। স্থানীয় স্তরে সীমাবদ্ধ এই সব কাজের রূপায়ণ এক সংহত রূপ নেয় এই অঞ্চলে রাজত্ব করতে আসা বিভিন্ন মত, ধর্ম এবং ধারণার অধিকারী মানুষদের আগমনে; তাদের কেউ কেউ এদেশেরই এক স্থান থেকে অন্য স্থানে এসে বসতি করে, আবার কেউ বাইরে থেকে এসে এদেশে থেকে যায় প্রজন্মের পর প্রজন্ম। কালক্রমে এদেশে চলে আসা পরিবেশ ভাবনা, এবং যে অন্য ভাবনার অধিকারীরা এদেশকে আপন করে নেয়-- কালক্রমে এই দুই অনুশীলনের মিশ্রণের ওপর ভিত্তি করে প্রকৃতি-প্রতিবেশ নিজের মতো করে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছে, ভূ-প্রকৃতিতে এসেছে কিছু অনন্য পরিবর্তন।
এদেশে রাজত্বের ইতিহাসে একদল বাইরে থেকে এসে এদেশে রয়ে গেছে, আবার একদল পর্যায়ক্রমে এদেশে এসে কিছুকাল বসবাস করে আবার হয় তাদের আদিবাসভূমে ফিরে গেছে বা অন্য অঞ্চলে চলে গেছে। এশিয়ার ইরান অঞ্চল থেকে আগমন ঘটে মুঘল-দের। মুঘলরা এদেশে থেকে যায় এবং এদেশে তাদের সাম্রাজ্য স্থায়ী রূপ নেয় বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে।
মুঘলরা তাদের কৃষ্টি এবং পরিবেশ-ভাবনা দ্বারা পরিচালিত হয়ে এদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ এবং ভৌগোলিক বৈচিত্র্যকে তাদের নিজেদের দৃষ্টিকোণ থেকে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার চেষ্টা করে। এর ফলে ভারতীয় উপমহাদেশে পরিবেশ-প্রতিবেশের বিকাশের যে ধারার অনুশীলন ও অনুসরণ শুরু হয়, সেই প্রক্রিয়াকে এক কথায় বলা যায় যে তা হলো অনেক পরম্পরাগত স্থানীয় ধারণার পাশাপাশি মুঘলদের সঙ্গে করে নিয়ে আসা ধারণার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। অনেক ক্ষেত্রে মুঘল প্রশাসকরা স্থানীয়ভাবে চলে আসা পরম্পরাগত প্রকৃতি-প্রতিবেশ ব্যবস্থাপনার ধারণাগুলো সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়; এই সব ক্ষেত্রে প্রায়শই স্থানীয় ক্ষেত্রে যথাযথ প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা শাসকদের, বা বলা ভালো স্থানীয় প্রশাসকদের, চিন্তা-চেতনা অনুসারী প্রক্রিয়ার রূপায়ণ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। স্থানীয় চরিত্র গুণসম্পন্ন প্রকৃতি ব্যবস্থাপনা অপেক্ষাকৃত বড়ো মাপের ব্যবস্থাপনা দ্বারা রূপায়িত, কখনও প্রতিস্থাপিত হয়। এইসব বড়ো মাপের ব্যবস্থাপনার বিষয়গুলি যখন এক বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে রূপায়িত হতে থাকে, সেগুলি তখন দীর্ঘকালীন প্রেক্ষিতে অনেক সমস্যার জন্ম দিতে থাকে। কিন্ত এখন এই সব প্রকৃতি ব্যবস্থাপনা পেয়ে গেছে রাজানুকূল্য, ফলে পরিবেশ ব্যবস্থাপনা গড়পড়তা এই পথ বেয়েই এগিয়ে চলে আর এই ব্যবস্থাপনার বিরূপ প্রভাব এসে পড়ে দেশের মানুষদের ওপর। অনেক প্রভাবই তখন হয়ে উঠেছে অপ্রত্যাহারযোগ্য-- শাঁকারির করাতের মতো, করাতের গতি আগুপিছু যা-ই হোক-না কেন, দুদিকেই তা কাটবে!
এরপর এই উপমহাদেশে জলপথে আগমন ঘটে ইউরোপের কয়েকটি মুখ্য শক্তির। ঐ সব দেশের রাজা বা ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধি হিসেবে যারা এদেশে আসে তাদের জলদস্যু হিসেবে “খ্যাতি” ছিলো, ইতিহাসে তাদের নাম খোদাই হয়ে আসে “কঙ্কুইস্টেডার”, বা “আক্রমণকারী”। এরা উন্নত সভ্যতাগুলি, যেমন ইনকা, মায়া সহ আফ্রিকার নানান জানা-অজানা-অচেনা সভ্যতার শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলি ধ্বংস এবং লুঠপাট করে। সময়ের সঙ্গে এদের নাম ক্রমে ক্রমে মোলায়েম হয়ে এলেও এদের কাজের ধরণ মূলত একই থেকে যায়।
দস্যুতার আলোকবর্তিকাবাহী এই সব সভ্যতার স্বাদ-বঞ্চিত মানুষের দঙ্গল যখন প্রাচ্য দেশে পদার্পণ করে, সংস্পর্শে আসে এক সম্পূর্ণ নতুন সংস্কৃতি জগতের, তারা দেখে সেখানে প্রকৃতি এবং প্রাণী, বিশেষ করে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির আন্ত:সম্পর্ক নিয়ে সমাজে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা ধারনা ইউরোপের চিন্তার চেয়ে অন্যরকম। পৃথিবীর নানা দেশে রাজত্ব ও দখলদারি বজায় রাখার যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের ফলে ইউরোপের এই সব পরদেশ দখলদাররা ভারতীয় উপমহাদেশকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। আর তার ফলে জন্ম নেয় নানান স্থানে নানা ধরনের নিয়ন্ত্রণ, শক্তির ও ক্ষমতার এই ভারসাম্যের পরিবর্তন পরিবেশ চিন্তায় ছাপ ফেলে।
১৮৪০ সালের আশপাশে দেখা যায় যে ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ মুখ্য শাসকের ভূমিকা দখল করে নিয়েছে। অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তিগুলির ( ফ্রান্স, ডাচ) ব্রিটিশ-শাসিত ভারতের ছোটো স্থানে নিজেদের স্থানীয় শাসনের বাইরে আর তাদের কোনও শক্তিশালী উপস্থিতি নেই। অনেক ইউরোপীয় দেশ এমনকি ভারতে তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থের বিষয়েও উৎসাহ হারায়।
ভারতীয় উপমহাদেশের মাটিতে ইউরোপের শক্তিগুলির আগমন পূর্বের মোঘলদের ভারতীয় উপমহাদেশে আগমনের চেয়ে গুণগতভাবে ভিন্ন ছিল। মুঘল সম্রাটবৃন্দ এবং তাঁদের সঙ্গে আসা সেপাই-শান্ত্রী-আমির-ওমরাহ, পাশাপাশি পাচক-দাস-দাসী, এক কথায় পুরো যুদ্ধ শিবিরে থাকা সবাই, বা বেশিরভাগই এদেশে স্থায়ী বসতি স্থাপন করে রয়ে গেলো। এই পুরো সম্প্রদায়টিই তাদের আদি বাসভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এদেশে পাকাপাকিভাবে থাকতে গিয়ে তারা এই উপমহাদেশ থেকে যে সম্পদ আহরণ করে, পাশাপাশি নিজেরা এই দেশে যে সম্পদ সৃষ্টি করে, সেগুলি তারা এই উপমহাদেশেই নিযুক্ত করে—এই সব সম্পদ এই উপমহাদেশের বাইরে, তাদের আদি বাসভূমিতে পাচার করার কোনও অভিপ্রায় তাদের ছিল না। তাই তাদের এদেশের পরিবেশ ধ্বংসের পরিবর্তে সেটিকে রক্ষা করার কিছুটা হলেও তাগিদ ছিল। এই কারণে মুঘলরা এদেশের উপযোগী পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনার রূপরেখা নির্মাণে দেশজ পদ্ধতির পাশাপাশি তাদের নিজেদের সংস্কৃতির সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যেসব পদ্ধতি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল, সেগুলো নিয়েও নিরীক্ষা চালায়।
ইউরোপীয় জাতিগুলি যখন আমাদের দেশে পা রেখেছিল, তখন তাদের এক এবং একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল এদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করে তাদের দেশে আদি বাসভূমিতে চালান করা, কেননা তাদের এদেশে স্থায়ীভাবে মিশে যেতে আসে নি। তাদের বলা যেতে পারে স্রেফ পরিযায়ী। পরিযানের বিভিন্ন পর্বে তারা বাধ্য হয়েছিল এদেশে সাময়িক ঘাঁটি গাড়তে; সেই স্বল্প দৈর্ঘ্যের বাসকালে তারা বাধ্য হয়েছিল এমন সব ব্যবস্থা নিতে, যার ফলে এদেশের প্রাকৃতিক সহ অন্যান্য সম্পদ আহরণ করে নিজেদের আদি বাসভূমে মসৃণভাবে চালান করা অব্যাহত রাখা যায়। তাদের কাছে ভারতের পরিবেশ-প্রতিবেশ, ভৌগোলিক বৈচিত্র্য এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যসূচক প্রক্রিয়াগুলি ছিল আবশ্যিক উৎপাত—খরা-বন্যা-মহামারী ইত্যাদি তাদের সম্পদ আহরণের বিস্তার এবং হার-কে অনভিপ্রেতভাবে যেন কমিয়ে দিচ্ছে।
১৮৬০ সালের পর এই উপমহাদেশে ব্রিটেনের একচেটিয়া প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তারা এই উপমহাদেশে ভারতীয় প্রকৃতির এই “বেয়াড়াপনা” নিয়ন্ত্রিত করার জন্য তাদের নিজেদের দেশের অপেক্ষাকৃত কম বৈচিত্র্যযুক্ত ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চলের জন্য প্রকৃতি-পরিবেশ-প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার আদর্শটি রূপায়ণের জন্য বিরাট আকারের উদ্যোগ নেয়। ইউরোপের শক্তিগুলির, বিশেষত ব্রিটেনের এই মানসিকতার প্রতিফলন আমরা দেখি তাদের প্রকৃতি-পরিবেশ-প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিগুলির নামকরণ থেকে। ভারতীয় উপমহাদেশের জলসম্পদ “ব্যবস্থাপনার” অভিপ্রায়ে তারা “নদী-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা” গড়ে তোলে। এই প্রক্রিয়ার তারা নাম দেয় “রিভার-ট্রেনিং” বা “নদী-শাসন”—অর্থাৎ তারা চেয়েছিল নদীর স্বাভাবিক গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করে, তাকে শাসকের ধারনামতে যে পথটি যথাযথ, নদীকে সেই “সভ্য” পথে, “সভ্য” চলনে “প্রশিক্ষিত” করতে বা নদীকে “অসভ্য নেটিভ”-দের মতো “ট্রেনিং” দিতে। একই রকমভাবে “বনাঞ্চল ব্যবস্থাপনা”, “প্রাণীসম্পদ ব্যবস্থাপনা”, “উদ্ভিদসম্পদ ব্যবস্থাপনা”, “কৃষিক্ষেত্র ব্যবস্থাপনা” ইত্যাদি সব কটি বিভাগকেই “প্রশিক্ষিত” করার মানসিকতা থেকে “উন্নত ব্যবস্থাপনা”-র বন্দোবস্ত তারা পাকা করে ফেলে।
তাদের এই মানসিকতার মূলে ছিল তাদের শ্বেতাঙ্গ জাতিদম্ভের বিষ। আর তাই তারা “স্বাভাবিক” ভাবেই ধরে নিয়েছিল যে, এদেশে আগে থেকেই পরম্পরাগত যেসব ব্যবস্থাপনার বন্দোবস্ত এবং ধারনা আছে, সেগুলি সবই নিকৃষ্ট, সেই ধারনাগুলিকেও “সুষ্ঠুভাবে প্রশিক্ষিত” করা দরকার।
“রাজা” হিসেবে ইংরেজ এদেশে থেকেছে অপেক্ষাকৃত অল্পদিন, কিন্তু এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই ইংরেজের হাতে পড়ে এদেশের প্রয়োজনীয় এবং সময় দ্বারা পরীক্ষিত পরিবেশ-প্রতিবেশ সংক্রান্ত পরম্পরাগত জ্ঞান অবলুপ্তির পথে পা বাড়ায়। আর তার সঙ্গে লুপ্ত হতে থাকে সেই সব সম্প্রদায়গুলি, যাঁরা এই সব পরম্পরাগত জ্ঞান অনুশীলন করতেন এবং সেই জ্ঞানের প্রয়োজনীয় পরিবর্ধন করতেন।
এই উপমহাদেশ জাতি-বর্ণ ব্যবস্থায় বিভক্ত থাকার অনেক বিষম্য ফলের মধ্যে অন্যতম এক উত্তরাধিকার আমরা আজও এই পরিবেশ-প্রতিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে বহন করে চলেছি। জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে হাতে-কলমে অনুশীলনের পরম্পরা বহন করে চলেছেন এই উপমহাদেশের নিম্নবর্গের মানুষেরা, আর “বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চা”, যে চর্চায় হাতে কাদা লাগে না, জামায় ঘাম লাগে না, কায়িক পরিশ্রম তেমন হয় না, এমন সব কাজে নিয়োজিত হয়েছেন অপেক্ষাকৃত উচ্চ বর্ণের মানুষরা। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে এই আরোপিত সামাজিক বিভাজন আমাদের দৃষ্টিকে খর্বিত করেছে, জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে গুরুতর সীমাবদ্ধতার জন্ম দিয়েছে, যা পরিবেশ ভাবনা ও তার সুরক্ষার ক্ষেত্রে যথাযথ উপায় অবলম্বনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে।
এদেশের জ্ঞানচর্চা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে আর্থিকভাবে সবল উচ্চ বর্ণের কতিপয় মানুষের মধ্যে; অন্যদিকে অনুশীলন, পর্যবেক্ষণ এবং তার থেকে উদ্ভূত ফলিত জ্ঞান রয়ে গেছে নিম্নবর্ণের সামাজিক সম্প্রদায়গুলির মধ্যে। যে তত্ত্বচর্চা তাঁদের ফলিত জ্ঞানের বনিয়াদকে আরও সবল করতে পারতো, সেই জ্ঞান এখন রয়ে গেলো উচ্চ বর্ণের মানুষের কাছে, যে গোষ্ঠীর সঙ্গে এই বর্ণের মানুষদের বিচ্ছেদ ঘটা প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। এটাও তো সত্যি যে ফলিত জ্ঞান তাত্ত্বিক জ্ঞানকে আরও শাণিত, আরও সংহত করতে পারতো, এই বিচ্ছেদের ফলে সেই মেলবন্ধনও আর হয়ে উঠলো না। পরিবেশের ওপর জ্ঞানচর্চার এই বিকৃত পদ্ধতি বিরূপ প্রভাব নিয়ে দীর্ঘকালীন প্রেক্ষিতে আজ আমাদের সদর দরজায় কড়া নাড়তে শুরু করেছে।
ইংরেজরা এদেশে লুণ্ঠন করতে এসে সাথী হিসেবে বেছে নিয়েছিল এই উচ্চ বর্ণ ও আর্থিকভাবে সবল এই “নেটিভ” সম্প্রদায়ের মানুষদেরই। রাজ্য চালানোর জন্য তাদের দরকার পড়ে একটি “দক্ষ” প্রশাসনের, “দক্ষ” এই অর্থে যে সেই প্রশাসন এই লুণ্ঠন প্রক্রিয়াকে মসৃণভাবে চলতে সাহায্য করবে। এদেশের উচ্চ বর্ণের মানুষদের ব্যবহারে ও মননে নিম্নবর্গ ও “নিম্নবর্ণের” মানুষদের প্রতি যে অবহেলা, তাচ্ছিল্য এবং অবজ্ঞা যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত ছিল, সেই ধারনাগুলি ব্রিটিশ রাজত্বের প্রথম দিন থেকেই তাদের প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে বসে।
এইসব নানা কারণ, কোনও একটা নয়, তাদের সম্মিলিত ফল বা সমাহার, প্রকৃতি-পরিবেশ-প্রতিবেশ “ব্যবস্থাপনা”-র ক্ষেত্রে সব দিক থেকে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। মানুষের পাশাপাশি প্রকৃতিও এই উৎকট শাসন ও “ব্যবস্থাপনা”-র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এদেশের পরম্পরাগত পরিবেশ-ভাবনা, যার মধ্যে অনেক ইতিবাচক দিক ছিল, সে সমস্ত কিছুই ইংরেজ প্রশাসন পুরোপুরি বর্জন করে। ইতিবাচক দিকগুলি নষ্ট হয় এবং নেতিবাচক দিকগুলিকে আরও নেতির দিকে ঠেলে দেওয়ার প্রবণতা বাড়ে।
এই টানাপড়েন আমাদের আজকে হাজির করেছে ভয়াবহ সব পরিবেশ বিপর্যয়ের সামনে। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, সমাজ-সংসার-রাজনীতি অর্থনীতির এক অনন্য রসায়নের ফলে যে বাস্তুতন্ত্রে আমাদের বসবাস, তার পরিবেশের ইতিহাস নিয়ে চর্চা তাই আজ এক জরুরি কার্যক্রম হয়ে উঠেছে।
দ্বিতীয় পর্ব পড়ুন নীচের সূত্রে।
পরিবেশের সাত কাহন পর্ব-দুই ভারতে পর্তুগিজ আগমনের ইতিবৃত্ত