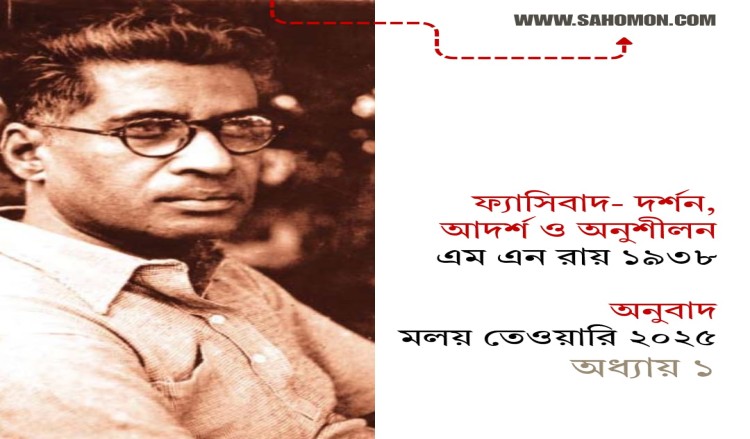অধ্যায় ১
ফ্যাসিবাদের দর্শন
ফ্যাসিবাদ অপেক্ষাকৃত নতুন একটি সামাজিক-রাজনৈতিক পরিঘটনা। ১৯১৯ সালে ইতালিতে প্রথম দেখা গেছিল। তারপর তা ইউরোপের নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এদের মধ্যে বেশ কয়েকটি দেশে ফ্যাসিবাদ সম্পূর্ণ বিজয় অর্জন করে। আকস্মিক উদ্ভব আর চোখ ধাঁধানো অগ্রগতির ফলে স্বভাবতই তা বর্তমান বিশ্বে বিশেষ আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। ফ্যাসিবাদ যে নৃশংসতা ঘটিয়েছে তা সমগ্র প্রগতিশীল ও মুক্তিকামী বিশ্বকে কাঁপিয়ে দিয়েছে। এর পক্ষে আর বিপক্ষে বহু কিছু লেখা হয়েছে। এর সমর্থক আর স্তাবকেরা না চাইলেও ফ্যাসিবাদ বিশ্বজুড়ে ধিক্কৃত হয়েছে; রাজনৈতিক ভাবে পশ্চাদগামী আর সামাজিক ভাবে প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদ হিসেবে নিন্দিত হয়েছে। মুমূর্ষু পুঁজিবাদকে রক্ষা করার হিংস্র মরিয়া প্রচেষ্টা হিসেবে এর চরিত্রায়ন করা হয়েছে। এর উত্থানের সূত্র চিহ্নিত হয়েছে মহাযুদ্ধের ধ্বংসাত্মক পরিণতিতে সৃষ্ট বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির অভ্যন্তরে। জার্মানির সাফল্য বর্ণনায় ফ্যাসিবাদের মনোহারি ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।
কিন্তু এই সব কিছু দিয়েও আমাদের সময়ের এই বীভৎসতার গভীরে যথার্থ মাত্রায় আলোকপাত করা যাচ্ছে না। ইতিহাসের দিক থেকে দেখলে ফ্যাসিবাদ বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিকাশ নয়। এরকম এক সমাজ-রাজনৈতিক আন্দোলনের ঝড় হঠাৎ করে সৃষ্টি হতে পারে না। ইতিহাসের এক দীর্ঘ সময়পর্ব ধরে বিকশিত দার্শনিক চিন্তাধারারই যৌক্তিক পরিণতি হল ফ্যাসিবাদী মতাদর্শ। ফ্যাসিবাদ যদি এক সমাজ-রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া হয়, তাহলে তার মতাদর্শগত ভিত্তিও অবশ্যই এক দার্শনিক প্রতিক্রিয়াতেই প্রতিষ্ঠিত। বলা হয়ে থাকে যে ফ্যাসিবাদের কোনও মতাদর্শ নাই। এটা একটা ভুল ধারণা। এই ভুল ধারনার ফলে ফ্যাসিবাদকে সঠিকভাবে অনুধাবন করার ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হয়। অবশ্যই ফ্যাসিবাদের নির্দিষ্ট দর্শন আছে। সামাজিক-রাজনৈতিক পরিঘটনা রূপে অবতীর্ণ হওয়ার আগের পর্বে এই দর্শন লম্বা সময় ধরে বিকশিত হয়েছে। যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক দর্শন অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের বৈপ্লবিক মতাদর্শগত ভিত্তি রচনা করেছিল, ফ্যাসিবাদী দর্শন হল তার বিরুদ্ধ চিন্তাধারা।
ফ্যাসিবাদের দর্শন হল হেগেল-পরবর্তী ভাববাদের স্বাভাবিক ফলশ্রুতি—অতি আধুনিক প্রত্যক্ষবাদ, নয়া বাস্তববাদ ও অনুভবমূলক জ্ঞানতত্ত্বের ছদ্ম বৈজ্ঞানিক ঘরানার দর্শন। এই দর্শন ভাববাদকে নাকচ করার ভাণ করে আসলে এক নতুন ধরণের অধিবিদ্যক অতীন্দ্রিয়বাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চায়। ছদ্মবেশী ও অসৎ ভাববাদের এইসব ঘরানাগুলি শেষ পর্যন্ত প্রয়োজনবাদ ও নয়া হেগেলিয় ভাবধারায় গিয়ে চরম বিন্দুতে পৌঁছায়। প্রথম ক্ষেত্রে “স্থুল বস্তুবাদের শিস্নোদর-দর্শন”-এর সাথে “ধর্মীয় অভিজ্ঞতা”র সমন্বয় সাধন করে, আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে হেগেলিয় দ্বন্দ্বতত্ত্বের বৈপ্লবিক হাতিয়ারকে বিকৃত করা হয় জঙ্গি প্রতিক্রিয়াশীল উদ্দেশ্য সাধনে।
নীতিনৈতিকতা, সুবিচার ও স্বাধীনতার সমস্ত ইহজাগতিক মানদণ্ড ধূলিসাৎ করে ফ্যাসিবাদ ঐশ্বরিক অনুমোদনপ্রাপ্তি দাবি করে। ইতালিয় ফ্যাসিবাদের সরকারি দার্শনিক জিওভান্নি জেন্টাইল সর্বপ্রথম এই দাবি হাজির করেছিলেন। তিনি লেখেন, “মানুষ স্বভাবতই ধর্মবিশ্বাসী। চিন্তা করা মানেই তো ঈশ্বরের ধ্যান করা। যে যত গভীরে চিন্তা করবে সে ততই ঈশ্বরের সান্নিধ্য অনুভব করবে। ঈশ্বরই সবকিছু, তুলনায় মানুষ কিছুই না” (“ফ্যাসিজম অ্যাণ্ড কালচার”)। রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া ও সামাজিক বর্বরতাকে সমর্থন দিতে গিয়ে ফ্যাসিবাদের এই দার্শনিক আধুনিক ইউরোপিয় সংস্কৃতির অন্যতম বুনিয়াদি নীতি মানবতাবাদকে পাছা দেখায়।
ইহজাগতিক স্বাধীনতার সংগ্রাম গড়ে তোলার আগেই দৈব অভিভাবকত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করতে হয়েছে মানুষকে। কঠোর সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে মানুষ যে রাজনৈতিক মুক্তি ও নাগরিক অধিকার অর্জন করেছিল তা থেকে তাকে বঞ্চিত করতে রেনেসাঁর সময়ে পাওয়া আত্মিক মুক্তির উত্তরাধিকারকে তার কাছ থেকে ঠকিয়ে ছিনিয়ে নেওয়া দরকার হয়ে পড়ে। ফ্যাসিবাদের দর্শন মানুষের যে অতিধার্মিক আত্মসমর্পনের প্রচারণা চালায় তা স্থুল বা বিকৃত বস্তুবাদের বহিপ্রকাশ। দার্শনিক বস্তুবাদের বৈপ্লবিক মতবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মধ্যে দিয়ে এই বিকৃত ধরণের বস্তুবাদের উত্থান ঘটে। ফ্যাসিবাদী বিশ্বাস জাহির করে নশ্বর মানুষটি সর্বব্যাপী দৈব সত্ত্বায় আত্মবিলোপ করে শুধুমাত্র স্রষ্টার হাতিয়ার রূপে পুনরুত্থিত হতে—তার ইচ্ছা ও কর্ম তখন এই পৃথিবীর সকল নিয়ম-নীতির ঊর্ধ্বে। চরাচরে ব্যাপ্ত ঐশ্বরিক উদ্দেশ্য সাধনে যে বীভৎসতা ও হিংস্রতা চালাতে হয় তাকে যুক্তিসিদ্ধ করতে নিজেদের চিন্তন ও কর্মপদ্ধতিকে এই ভণ্ডেরা “ঈশ্বরের অভিপ্রায়” বলে অভিহিত করে। সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা ও প্রণোদনা। মুমূর্ষু ক্ষয়িষ্ণু এই পুঁজিবাদকে রক্ষার দায়িত্ব যেন ঈশ্বর নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন। এবং এই বিকৃত বস্তুবাদের জীর্ণ ব্যবস্থাটির সকল অন্ধভক্ত যেন একেকজন উদ্দীপ্ত ঐশ্বরিক এজেন্টে উন্নীত হয়েছেন। নিজের আসল চেহারা আড়াল করার এই ধূর্ত কৌশলের মাধ্যমে সে নিজের জন্য অবাধ স্বাধীনতা বরাদ্দ করে, আর অন্যদের ক্ষেত্রে তা অস্বীকার করে। ফ্যাসিস্টরা হল দ্যা সুপারম্যান।
আত্মবিলোপের এই অতি-ধার্মীক মতবাদ সত্ত্বেও ফ্যাসিবাদের জগাখিচুড়িবাদী দার্শনিক জিওভান্নি জেন্টাইল অবশ্য “মানুষের শাশ্বত ও অনন্ত সারসত্তা” আবিষ্কার করা থেকে বিরত থাকেন না। যে ব্যবস্থা জীর্ণ মুমূর্ষু নিঃশেষ হয়ে এসেছে তাকে রক্ষা করার ঐতিহাসিকভাবে অসম্ভব কার্যটি সম্ভব করার দায়িত্ব যারা নিয়েছেন তাঁদের তো “অন্তহীন, নিঃশর্ত ও মুক্ত” হতেই হয়। জেন্টাইল তাঁর আত্মবিলোপের মতবাদ এবং ফ্যাসিবাদীদের সর্বময় ক্ষমতার আরাধনার মধ্যে যে মোটা দাগের বিরোধাভাস বর্তমান তারও “দার্শনিক” ব্যাখ্যা হাজির করতে কোনও অসুবিধা দেখেন না। একজন নব্য-হেগেলিয় হিসেবে তিনি জানেন কীভাবে দ্বন্দ্বতত্ত্বকে বিকৃত করে নিজের উদ্দেশ্য সাধনের খাপে পুরে নেওয়া যায়। উপযোগিতার “আধ্যাত্মবাদী” দর্শন হিসেবে প্রয়োজনবাদও তাঁকে এ’কাজে সাহায্য করে। “চিন্তা মানেই আসলে ঈশ্বরধ্যান” –প্রথমে এই শিক্ষায় শিক্ষিত করার পর তিনি দেখাতে থাকলেন সেই সব কিছু, যেগুলিকে তিনি দ্বন্দ্বতত্ত্বের চমৎকারিত্বের এক বুদ্ধিদীপ্ত প্রদর্শন বলে মনে করেন।
“ঈশ্বর এবং চিন্তন দুটোই জীবনের দুই বিপরীত মেরুর প্রতিনিধিত্ব করে; দুটোই জরুরি, দুটোই অপরিহার্য। কিন্তু তবু তারা পরস্পর বিরুদ্ধ, একে অন্যকে বিরোধ করে” (ফ্যাসিজম অ্যান্ড কালচার)। আবার, ঈশ্বর ও মানুষের ঐক্যকে বলা হয়, “আত্মোপলব্ধির আভ্যন্তরীণ গতির অনন্তযাত্রায় এক নমনীয় ঐক্য—এক সজীব এবং তাই সতত অস্থির ঐক্য, সর্বদা আপনাতে আপনি অতৃপ্ত”(পূর্বোক্ত)। হেগেলিয় দ্বন্দ্বতত্ত্বের এক বিকৃত অনুকরণ এই নয়া-বিদ্যাম্ভরিতা হিন্দু অতীন্দ্রিয়বাদের সাথে আশ্চর্যরকম মিলে যায়। পরীক্ষা নিরিক্ষায় প্রদর্শিত বৈজ্ঞানিক সত্য এবং যুক্তির পথ বেয়ে প্রতিষ্ঠিত দার্শনিক ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করতে জ্ঞানান্ধতায় আশ্রয় নেওয়ার মানসিক বিভ্রান্তি ছাড়া অতীন্দ্রিয়বাদ আর কী? জেন্টাইল ব্যাখ্যাত ফ্যাসিবাদী দর্শন অতীন্দ্রিয়বাদের একটি ক্লাসিক নমুনা।
চিন্তন হল ঈশ্বরধ্যান, তথাপি তার বিষয়বস্তুর সাথে তার সম্পর্ক বৈরিতার, দ্বন্দ্বের! বিষয়বস্তু যখন একই থাকছে তখন ধ্যানের অক্রিয় অবস্থা কীভাবে বিরোধিতার সক্রিয় কর্ম হিসেবে উপস্থিত হতে পারে তা যুক্তিবুদ্ধির অতীত। কিন্তু আধ্যাত্মিক ধারণা তো যুক্তিবুদ্ধির চৌহদ্দির বাইরের জিনিস। ধ্যানকে চিন্তনের সাথে এক করে দেওয়াটা তাহলে এক জ্ঞানতাত্ত্বিক উদ্ভাবন। কোনও বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা করলে আমরা সেই বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করি। ধ্যান তো এরকম কোন ফল দেয় না। ধ্যান হল জানা বিষয়েই ঘুরপাক খাওয়া। যদি কেউ ধর্মীয় পূর্বপ্রতিজ্ঞা দিয়ে শুরু করে তাহলে সে ঈশ্বরে আরোপিত গুণাবলি ধ্যান করতে পারে। কিন্তু তাঁর এই পূর্বপ্রতিজ্ঞাই তাঁর ধ্যানের বিষয়কে চিন্তন নামক মানসিক ক্রিয়ার নাগালের বাইরে রাখবে। সুতরাং চিন্তনকে ধ্যানের সাথে এক করে দেওয়াটা হয় ভাবনার এক খাঁটি বিভ্রান্তি অথবা এটা জ্ঞানতত্ত্বের মূল নীতির এক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিকৃতি।
এইসব অতীন্দ্রিয়বাদকে দার্শনিকভাবে যতই বিভ্রান্ত ও বিহ্বল মনে করা হোক না কেন তার বাস্তব ব্যবহারিক ভূমিকা কিন্তু খুব পরিস্কার। তারা একদম বিশুদ্ধ বস্তুবাদী, সবচেয়ে কদর্য অর্থে। রাষ্ট্রের হেগেলিয় তত্ত্ব থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে জেন্টাইল আসলে ফ্যাসিবাদী একনায়কতন্ত্রের অধিবিদ্যক অনুমোদন আবিষ্কার করেন। “ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র ধর্মসহ সমস্ত রকম আধ্যাত্মিক মূল্যবোধকে আঁকড়ে ধরে ও অন্তর্ভুক্ত করে… রাষ্ট্র যদি অন্য কোনও সার্বভৌম ক্ষমতাকে মান্যতা দেয় তাহলে তা রাষ্ট্রের পক্ষে আত্মহত্যার সামিল। যা আধ্যাত্মিক তা মুক্ত, তবে তা রাষ্ট্রের ক্ষমতার বৃহৎ সীমার মধ্যে মুক্ত, যে ক্ষমতা নিজেই আধ্যাত্মিক” (ফ্যাসিজম অ্যান্ড কালচার)। ফ্যাসিবাদের অনুশীলন, যা অন্য অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে, দেখায় কোন কদর্য বস্তুবাদী উদ্দেশ্যে ফ্যাসিবাদী একনায়কতন্ত্রের ঈশ্বরপ্রদত্ত ক্ষমতা রচনা করা হয়।
বুর্জোয়ারা তাদের ক্ষয়প্রাপ্ত ক্ষমতাকে রক্ষা করতে ফ্যাসিবাদী একনায়কতন্ত্রের রক্তমাখা হাতিয়ার দিয়ে “রাজার ঈশ্বর প্রদত্ত অধিকার”-এর দাবিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। রাজারা অতীতের বিষয় হয়ে গিয়ে থাকতে পারে, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত অধিবিদ্যক হেগেলিয় মতবাদ দ্বারা বিমূর্তভাবে সৃষ্ট ঐশ্বরিক অনুমোদনের বিশেষাধিকার রাষ্ট্রের জন্য সংরক্ষিত থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত বৈধভাবে না হলেও অন্তত যুক্তি দিয়ে এই অধিকার সেই শ্রেণী দাবি করতে পারে যে শ্রেণী রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করে। মধ্যযুগের অনুজ্ঞা—“রাজা কোনও ভুল করতে পারে না”—এখন ফ্যাসিবাদের দার্শনিকদের দ্বারা প্রসারিত করা হয়েছে নতুন অনুজ্ঞায়—“রাষ্ট্র কোনও ভুল করতে পারে না”।
ঘটনাক্রমে, একথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ফ্যাসিবাদের দার্শনিক শেকড় ‘গীতা’-র ঐশ্বরিক দর্শনে খুঁজে পাওয়া যাবে, যেখানে বলা হয়েছে, এই দুনিয়ার সমস্ত ক্ষমতা (বিভূতি) হল ঈশ্বরের ক্ষমতা। এইভাবে দেখলে ফ্যাসিজম কোনও নতুন দার্শনিক প্রপঞ্চ নয়; আর ফ্যাসিবাদের কোনও দার্শনিক ভিত্তি নেই এমনটাও ঠিক না। ফ্যাসিবাদী দর্শন জীবনের আধ্যাত্মিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির স্বাভাবিক ফলশ্রুতি। গীতা যে মতবাদে পৌঁছয় তার সাথে ফ্যাসিবাদী নয়া-হেগেলিয় অধিবিদ্যক রাষ্ট্রবাদের যৌক্তিক সংযোগ সহজেই অনুধাবন করা যায়। বাস্তবত ফ্যাসিবাদী একনায়কতন্ত্রের দর্শন অতীন্দ্রিয়বাদ ও আধ্যাত্মিকতাবাদের আধুনিক ঘরানা থেকে সরাসরি উদ্ভূত যার উদ্দেশ্য বৈজ্ঞানিক জীবনদর্শনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া জাগানো। এর ভারতীয় শেকড়কে চিহ্নিত করা যায় শোপেনাওয়ারের মধ্যে, যার শিষ্য নীৎসে হলেন ফ্যাসিবাদী দর্শনের জনক।
ফ্যাসিবাদের উৎপত্তির তত্ত্বসন্ধানের আগে আসুন আধ্যাত্মিকতাবাদী উন্মাদনার এই ভয়ঙ্কর বহিপ্রকাশকে আরও একটু কাছ থেকে দেখে নেওয়া যাক। “ফ্যাসিবাদী আন্দোলন এক গভীর আধ্যাত্মিক তাড়নায় সক্রিয় হয়। ফ্যাসিবাদের তত্ত্ব হল তার অ্যাকশান। এটা মতাদর্শগতভাবে আবদ্ধ কোনও ব্যবস্থা নয়। এটা চিন্তনের এক নতুন রূপ, যাপনের এক নতুন পদ্ধতি। ফ্যাসিবাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হল তার ধর্মীয় আবেগ” (জিওভান্নি জেন্টাইল, “ফ্যাসিজম অ্যান্ড কালচার”)। ফ্যাসিজমের তাড়না খুব স্পষ্টভাবে তার অ্যাকশান বা কার্যকলাপে প্রকাশ পায়। ফ্যাসিবাদী দার্শনিকের ভাষ্য মতে এই অ্যাকশানগুলোই হল এক কথায় ফ্যাসিবাদী নীতি।
দিগভ্রষ্ট মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠিকে ফ্যাসিবাদী আন্দোলন এক মতান্ধ বাহিনীতে ঐক্যবদ্ধ করে। উত্তপ্ত ভাষণবাজির মধ্যে দিয়ে তাঁদের নিজেদের দাসত্ব বন্ধনকেই আরও আঁটোসাঁটো করার এক আপাতবিরোধী ধর্মযুদ্ধে নিয়োজিত করে। পুঁজিবাদে যারা শোষিত দাস, তাঁদের বিদ্রোহকে হিংস্র নির্মমতায় দমন করা ফ্যাসিবাদী আন্দোলনের কাজ। আর সেই অগৌরবের কাজ সম্পন্ন করার জন্য ফ্যাসিবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করে প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়ারা। তারা ফ্যাসিবাদের একনায়ত্ব কায়েম করতে সাহায্য করে। ফ্যাসিবাদের “গভীরে নিহিত” আধ্যাত্মিক তাড়না বছরের পর বছর ধরে অগণিত হিংস্র কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে পরিস্ফুট হয়। এগুলি সবই সম্পন্ন হয় পুঁজিবাদকে রক্ষা করার পবিত্র কর্তব্যে, যে পুঁজিবাদ হল বিকৃত বস্তুবাদের অনুশীলন। এইসব ফ্যাসিবাদী কার্যকলাপ কীভাবে “গভীরে নিহিত আধ্যাত্মিক তাড়না”-র সাথে সাযুজ্যপূর্ণ হয়? ফ্যাসিবাদের দার্শনিক তারও উত্তর দিয়েছেন: ফ্যাসিবাদের কোনও নীতি নাই; মতাদর্শের কোনও রকম যুক্তিকাঠামোর বাঁধনে তা ভারাক্রান্ত নয়; আধ্যাত্মিকতাবাদ কোনও নিমিত্তের ধার ধারে না; এখানে যুক্তির কোনও জায়গা নাই। ফ্যাসিজমের আধ্যাত্মিকতাবাদী চরিত্র তার যথেচ্ছাচারে ভাষা পায়। আধ্যাত্মিকতাবাদের এই উন্মত্ত প্রকাশের একমাত্র বিধি হল উপযোগিতা—পুঁজিবাদী আধিপত্যের উপযোগিতা। তা কখনও যুক্তিপূর্ণ নীতিমালার যথাযথ দার্শনিক তত্ত্বের ভারা বেঁধে নিজেকে ভারাক্রান্ত করতে চায় না। পুঁজিবাদী সভ্যতার কদর্য বিকৃত বস্তুবাদ থেকে সমাজকে মুক্ত করতে চাওয়া সমস্ত রকম শক্তির বিরুদ্ধে ফ্যাসিবাদ ধর্মযুদ্ধ চালায়, এবং সেই যুদ্ধে যে কোনও হাতিয়ার তুলে নেওয়ার জন্য নিজেদের দু’হাত মুক্ত রাখতে চায় তারা। বোধের অতীত এক স্বর্গীয় ইচ্ছার, ধর্মীয় অভিজ্ঞতার, আধ্যাত্মিক তাড়নার ও ধর্মীয় ভাবাবেগের এই মতবাদ ইহজাগতিক ক্ষমতার অবাধ স্বেচ্ছাচারিতাকে বৈধতা দিতে খুব কাজে আসে— অতিপ্রাকৃত এক উদ্দেশ্য সাধনের কথা বলে দিলেই হল, যা কোনও আইন জানে না, যার কাছে মানুষের বানানো কোনও আইনই খাটে না।
জেন্টাইলের মতে ফ্যাসিবাদ হল, “সমস্ত ধরণের বিমূর্ত, যুক্তিবাদী, অ-ধর্মীয়, এমনকি অস্বাভাবিক উদারতাবাদ ও যথেষ্ট মাত্রার বস্তুবাদী ফ্রি-ম্যাসন সৌভ্রাতৃত্ব ইত্যাদির সমস্ত ধরণ ও ব্যবস্থার” ঘোষিত জাতশত্রু। এখানে আমরা দেখি যে ছদ্মবেশ ছিন্ন করে আধ্যাত্মিকতাবাদ তার আসল চেহারায় প্রকাশিত হয়ে দাঁড়ায়। ফ্যাসিবাদ রিলিজিয়াস; তাই সে যুক্তিবাদকে বিপদ হিসেবে আর উদারতাবাদকে অনাসৃষ্টি বলে ঘোষণা করে। ফ্যাসিবাদ দার্শনিক বস্তুবাদের বিরুদ্ধে, কারণ দার্শনিক বস্তুবাদ হল স্থুল বিকৃত বস্তুবাদ অনুশীলনের বিরুদ্ধ মতবাদ। ফ্যাসিবাদ ধর্মের রক্ষাকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হয়, কারণ ধর্মবিশ্বাস অজ্ঞানতার পালকপোষক। অজ্ঞান জনতার ওপর শোষণ চালানো সহজ।