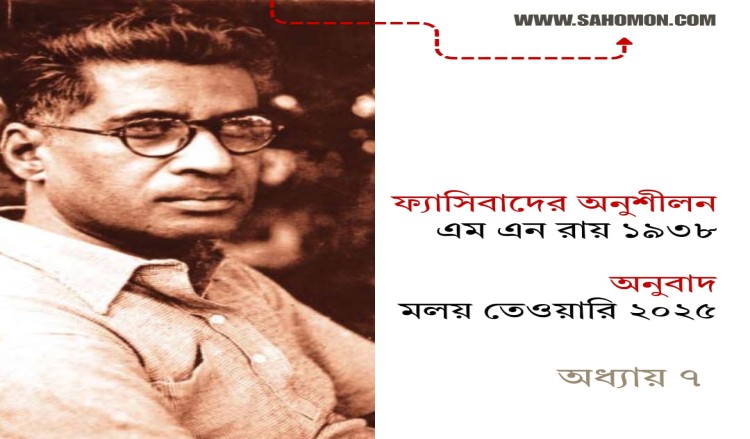অধ্যায় ৭
ফ্যাসিবাদের অনুশীলন
১৯৩৪ সালের আগস্ট মাসে বিশ্বজুড়ে ফ্যাসিবাদের সাংস্কৃতিক হুমকির বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক কংগ্রেস আহ্বানের জন্য বিপুল সংখ্যক বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডের নেতাদের স্বাক্ষরযুক্ত একটি ইশতেহার প্রকাশিত হয়। ঐতিহাসিক সেই দলিল থেকে নিম্নোক্ত অংশ উদ্ধৃত হলো:
“আমরা জানি, ফ্যাসিবাদী দেশগুলোতে বহু সম্মানিত পণ্ডিতকে তাদের কর্মক্ষেত্র থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে অথবা তাঁরা স্বেচ্ছায় স্বদেশ ত্যাগ করেছেন, কারণ তাঁরা তাঁদের শিক্ষাদীক্ষা কর্তৃত্বপরায়ণ রাষ্ট্রের হিংস্র দাবির কাছে বলি দিতে অস্বীকার করেছিলেন। বিশেষত জার্মানিতে সংঘটিত ঘটনাবলি বিজ্ঞানের স্বাধীনতা রক্ষার বিষয়ে আমাদের গভীর উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। সে দেশে, বিজ্ঞানের যথার্থ শাখাগুলোকে প্রকাশ্যে খর্ব করে যুদ্ধশিল্পের সেবায় নিয়োজিত করা হয়েছে। কেবলমাত্র সেইসব গবেষণাকে উৎসাহিত করা হচ্ছে যা বিশ্বে অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সহায়ক। তাই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের কাজে লাগে না পদার্থবিজ্ঞানের এমন সমস্ত শাখাকে বাধা দেওয়া হয়েছে এবং সীমিত করা হয়েছে। মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে প্রসারিত করেছে এমন গবেষণাগুলোকে ‘অনর্থক বুদ্ধিবাদিতা’ বলে প্রকাশ্যে অবহেলা করা হচ্ছে। বংশগতি ও জাতি সংক্রান্ত প্রমাণিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। তার স্থানে হাজির করা হয়েছে নতুন মতবাদ, যা সত্যানুসন্ধানের মাধ্যমে যাচাই করা হয়নি, বরং তা প্রণয়ন করা হয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষের অস্তিত্ব ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করতে। সামাজিক স্বাস্থ্যবিধির সমস্ত ন্যায্যতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে ন্যাশনাল সোশ্যালিস্টদের এই বিশ্বাসের ওপর দাঁড়িয়ে যে, জৈবিকভাবে দুর্বলদের সাহায্য করা শক্তিশালীদের ক্ষতি করার নামান্তর। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ‘প্রাকৃতিক নিরাময়’-এর চেয়ার প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য করা হয়েছে। এভাবে কুসংস্কার ও প্রতারণার দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে। ঐতিহাসিক সত্যকে উপেক্ষা করে প্রাগৈতিহাসিক ও প্রাচীন যুগকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে যা সংশ্লিষ্ট জাতির শ্রেষ্ঠত্ব ও অন্যান্য সকলের নিকৃষ্টতার তত্ত্ব প্রমাণ করে। প্রায়শই, সত্যের অস্বস্তিকর দিকগুলোকে ঢাকতে ইচ্ছাকৃত রহস্যবাদকে কাজে লাগানো হচ্ছে। মুক্ত গবেষণার দমন ও সত্যের অপলাপ সবচেয়ে স্পষ্টভাবে দেখা যায় নতুন আইনশাস্ত্রে, যা মধ্যযুগীয় আইনী ধারণার উপর ভিত্তি করে নির্মম ও স্বেচ্ছাচারী কর্মকাণ্ডকে তাত্ত্বিক ভিত্তি দান করে। বিজ্ঞানের মতই শিক্ষাদান ও অধ্যয়নকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হচ্ছে। মুক্ত গবেষণার প্রতি এই অবজ্ঞা ও অপব্যবহারের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সমগ্র কাঠামো ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, এবং এর ধ্বংসাবশেষ থেকে এক নতুন ধারার ছদ্মবিজ্ঞান গড়ে উঠবে, যা মানবজাতির অগ্রগতির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে।”
হিটলারের ক্ষমতা দখলের মাত্র দুই মাসের মধ্যে, দুই শতাধিক বিশিষ্ট পণ্ডিতকে তাঁদের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বহিষ্কার করা হয়। এই বর্বরতা সংঘটিত হয়েছিল এই অজুহাতে যে ওই ব্যক্তিরা ইহুদি। তাঁদের অনেকেই ইহুদি ছিলেন, কিন্তু তাঁদের প্রকৃত অপরাধ ছিল মুক্তচিন্তার অধিকারী হওয়া—কেউ সমাজতন্ত্রী, অধিকাংশ উদারপন্থী, এবং বাকিরা কেবল “ন্যায়পরায়ণতা ও সততার অধিকারী, যা নাৎসিদের দৃষ্টিতে সবচেয়ে বড় অপরাধ।” (দ্য ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান, মে ১৯৮৮)। ফ্যাসিবাদের বর্বরতার শিকার এই মহান ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন বিশ্ব-ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বরা, যেমন আলবার্ট আইনস্টাইন, বার্লিনের বিখ্যাত স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ প্রফেসর জন্ডেক, শীর্ষস্থানীয় রসায়নবিদ রিচার্ড উইলস্টাটার ও ফ্রিৎস হেবার, হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা মনোবিজ্ঞানী অটো মেয়ারহফ, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদ মরিজ বন এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় সমান খ্যাতিসম্পন্ন আরও অনেকে। আইনস্টাইনকে “জাগ্রত জার্মানির শত্রু নং-১” ঘোষণা করা হয়েছিল। এই ঘটনাই ফ্যাসিবাদকে মানবতার আদালতে সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্মাদ শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। এই সাক্ষ্য আরও অভিভূতকর হয়ে ওঠে যখন জানা যায় যে সমকালীন জার্মানির বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিল্পজগতের সমস্ত নক্ষত্রদের নাৎসি থার্ড রাইখ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।
নাৎসিরা জার্মানির শিক্ষাকেন্দ্রগুলো থেকে তাদের খ্যাতিমান পণ্ডিতদের বিতাড়িত করেই ক্ষান্ত হননি। তারা তাদের এই বর্বরতা সমগ্র বিশ্বের উপর চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। আইনস্টাইন জার্মানি ত্যাগ করার পর তাঁকে কলেজ দ্য ফ্রঁস অধ্যাপক পদ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানায়। এরপর নাৎসি সংবাদমাধ্যমগুলো চিৎকার করে দাবি জানাতে থাকে যে ভবিষ্যতে বহিষ্কৃত শিক্ষাবিদদের জার্মানি ছেড়ে চলে যেতে দেওয়া উচিত হবে না, “জার্মানির শত্রুরা তাদের সম্মানিত করে জার্মানিকে অপমান করতে না পারে” তা দেখতে হবে।
আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার পোড়ানো ইতিহাসের অন্যতম জঘন্য ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। কিন্তু ফ্যাসিবাদীরা শেষ পর্যন্ত আলেকজান্দ্রিয়ার অগ্নিসংযোগকেও ছাপিয়ে গেছে। তারা বিশ হাজারেরও বেশি বই পুড়িয়ে ফেলেছে। মানবজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মহান লেখকদের রচনা সব। আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার প্রাচীন সভ্যতার পতনের পরের বর্বর যুগে পোড়ানো হয়েছিল। কিন্তু নাৎসিদের দ্বারা বিজ্ঞান ও সাহিত্যের বিপুল সংগ্রহকে ইচ্ছাকৃতভাবে ধ্বংস করা হল বিংশ শতাব্দীতে, আধুনিক সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে। এ কোনো উন্মত্ত জনতার আবেগতাড়িত কাজ ছিল না। এটা ছিল এক সুপরিকল্পিত উদ্যোগ—বৈজ্ঞানিক গবেষণা, সাংস্কৃতিক অগ্রগতি ও শিল্পসম্মত সৃষ্টিকর্মের সঞ্চিত ফসলকে ধ্বংস করার। কারণ এইসব সৃষ্টি ফ্যাসিবাদের বর্বর সংস্কৃতির সাথে খাপ খায়নি। এমন সমস্ত “অবাঞ্ছিত” রচনার একটি দীর্ঘ তালিকা তৈরি করা হয়েছিল। সেগুলো জোর খাটিয়ে সংগ্রহ করে দেশের বিভিন্ন স্থানে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল।
বিজ্ঞান ও সাহিত্য সমূহের এই সংগঠিত ধ্বংসযজ্ঞ সারা বিশ্বকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। “সভ্যতা যে সমস্ত মানদণ্ড তৈরি করেছে, সেই সমস্ত কিছুকে সমূলে উৎপাটিত করা হচ্ছে।” (দ্য নেশন, নিউ ইয়র্ক, ৫ জুলাই ১৯৩৩)। এই অবিশ্বাস্য নাশকতা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে আমেরিকায় বসবাসরত এক বিখ্যাত জার্মান লেখক লিখেছিলেন: “উদাহরণস্বরূপ, টমাস মানের রচনা পোড়ানো—এ কাজ অন্য যে কোনো অপরাধের চেয়েও গভীরভাবে নাৎসিদের ধিক্কৃত করেছে। কারণ, এটা হল মানব সভ্যতায় ওই জাতিরই অর্জিত সর্বোচ্চ আদর্শকে নিজেদেরই প্রত্যাখ্যান করার এবং প্রকাশ্যেই এক অধঃপতিত বর্বরতায় ফিরে যাওয়ার ইঙ্গিতবাহী। লক্ষণীয় যে, মননের জীবন, সমস্ত বৌদ্ধিক মূল্যবোধ, গবেষণা ও নিঃস্বার্থ চিন্তা, মানবাত্মার দীর্ঘ অর্জিত অধিকার, রেনেসাঁর সময় থেকে বয়ে আসা মানুষের জীবন ও মরণের সমস্ত নীতি, সত্য ও স্বাধীনতা—সবকিছুর বিরুদ্ধে এমন এক আক্রমণ চালানো হচ্ছে, যা আগে কখনও দেখা যায়নি।” (লুডউইগ লুইসন, দ্য নেশন, নিউ ইয়র্ক, ২১ জুন ১৯৩৩)।
নাৎসিরা “বুদ্ধিবাদ”-এর প্রতি তাদের অবজ্ঞা নিয়ে গর্ববোধ করে। বস্তুত, অজ্ঞতার মহিমাকীর্তন তাদের সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। “আজকের তরুণ নাৎসিরা জ্ঞানহীনতাকে এবং জার্মান সংস্কৃতির বহু প্রজন্মের অর্জিত শিক্ষাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করাকে গুণ হিসেবে গণ্য করে” (হ্যামিল্টন ফিশ আর্মস্ট্রং, ফরেন অ্যাফেয়ার্স, জুলাই ১৯৩৩)। এটি কোনো নাৎসি-বিরোধী প্রপাগান্ডা নয়। নাৎসি শিক্ষামন্ত্রী রুস্ট নিজেই ঘোষণা করেছিলেন, “ন্যাশনাল সোশ্যালিজম (নাৎসিবাদ) বিজ্ঞান-বিরোধী নয়, তবে তা তত্ত্বের শত্রু।” তত্ত্ববিহীন বিজ্ঞানের কথা শুনে আপনাদের হাসি পেতে পারে, আপনারা ভাবতে পারেন, আদৌ তা কি সম্ভব? তবে মন্ত্রী মহোদয় বিশ্বকে ধ্বন্দে রাখেননি। ফ্যাসিবাদীদের সাংস্কৃতিক বিশ্বাসে তারা একেবারে নির্মমভাবে স্পষ্টবাদী। তিনি তত্ত্ববিহীন বিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন এভাবে: “দর্শন ও বিজ্ঞানকে ঝটিকা বাহিনীর চেতনা অনুসারে পুনর্বিন্যস্ত করতে হবে।” এই “চেতনা”-র বর্ণনা নাৎসিদের নিজস্ব ভাষায় সবচেয়ে ভালোভাবে পাওয়া যাবে:
“ঝটিকা বাহিনী দাঁড়িয়ে আছে,
জাতির যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত;
ইহুদিরা রক্তাক্ত হলে তবেই
আমাদের মুক্তি আসবে বাস্তব।”
(জাতীয় সঙ্গীত)
“কেন ১৯৩৩ সালের ৩০ জানুয়ারি জার্মানি তার শব্দভাণ্ডার থেকে ‘শান্তিবাদ’ (প্যাসিফিজম) শব্দটি বাদ দিয়েছে তা দুনিয়াকে বোঝানোর চেষ্টা তাদের অবশ্যই করতে হবে” (ফন পাপেন, হিটলারের প্রথম সরকারের উপ-চ্যান্সেলর)। সেই দিনই হিটলার জার্মানির চ্যান্সেলর হন।
“যুদ্ধে প্রাণ দেওয়া জার্মানদের অপূর্ণ অভীষ্ট পূরণ করাটা জীবিত জার্মানদের পবিত্র দায়িত্ব। রক্তে লেখা অঙ্গীকার রক্ত দিয়েই শোধ করতে হবে” (গোয়েরিং)। স্টর্ম ট্রুপারদের চেতনার সবচেয়ে বড় প্রতীক গোয়েরিং নারীদের ভূমিকা নির্ধারণ করেছিলেন: “নারীর স্থান গৃহে; তাদের কর্তব্য হল ক্লান্ত যোদ্ধাকে পুনরুজ্জীবিত করা।” আর স্টর্ম ট্রুপারদের চেতনায় উদ্বুদ্ধ নাৎসি তরুণীরা তার জবাব দিয়েছিল: “যুদ্ধে সন্তান পাঠানোর চেয়ে মহত্তর ও ঊর্ধ্বতর কোনো অধিকার নারীর নেই।”(‘রেড স্বস্তিকা’ নারী সংঘের ঘোষণা)। সবশেষে, নাৎসি প্রচারমন্ত্রী গোয়েবলসের “জ্ঞানবাণী”: “নারীর কাজ হলো সুন্দরী হওয়া ও সন্তান জন্ম দেওয়া। স্ত্রী পাখি পুরুষের জন্য সাজে আর তার জন্য ডিমে তা দেয়। বিনিময়ে, পুরুষ পাখি খাবার আনে অথবা পাহারা দেয় ও শত্রু তাড়ানোর দায়িত্ব নেয়।” “জাগ্রত জার্মানি”-র এই নতুন চেতনায় মানুষ ও মানবেতর প্রাণীর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। প্রাণীদের পরিচালিত করে যে প্রবৃত্তি, তা-ই মানুষের জন্য প্রযোজ্য। এটাই নাৎসি দর্শন ও বিজ্ঞানের “পুনর্বিন্যাস”।
ফ্যাসিবাদীদের উগ্র জাতিগত বিদ্বেষ মধ্যযুগীয় বর্বরতারই আরেক নিদর্শন। তবে এটা একটা সুবিধাজনক ছদ্মাবরণও বটে। কাল্পনিক এক “আন্তর্জাতিক ইহুদি অর্থব্যবস্থা”-র বিরুদ্ধে তাদের বিষোদ্গার বাস্তবে আসল লগ্নিকারী ও শিল্পপুঁজির শক্তির কাছে তাদের আত্মসমর্পণকে ঢাকার এক ধোঁয়াশা মাত্র। অর্থনীতিতে নয়, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেই ইহুদিরা প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। অর্থনীতিতে তারা সাধারণ ব্যবসায়ীদের থেকে বেশি কিছু ছিল না। অধিকাংশই ছিল ক্ষুদ্র দোকানদার। জার্মানির অর্থনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণকারী বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী ও ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানগুলো, যারা রাজনৈতিক নিয়তিও নির্ধারণ করে, সবই খ্রিস্টানদের মালিকানায় ও নিয়ন্ত্রণে ছিল। ইহুদি বুদ্ধিজীবী (যাদের অনেকে বিজ্ঞান ও শিল্পজগতে শীর্ষে ছিলেন), সমাজতন্ত্রী ও ব্যবসায়ীদের (প্রধানত ক্ষুদ্র দোকানদার) কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট জাতিগত বিদ্বেষের বলি করা হয়েছে, যাতে পুঁজিবাদের নির্মম শিকার সরলমনা ক্ষুদ্র বুর্জোয়াদের ব্যবহার করে ফ্যাসিবাদীরা তাদের লোলুপ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারে।
হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক সিডনি ফে নাৎসিদের উন্মত্ত ইহুদি-বিরোধিতার কারণ ব্যাখ্যা করেন: “উনবিংশ শতকে সামাজিক কুসংস্কার ও রীতিনীতি ইহুদিদিগকে সেনাবাহিনী ও সরকারি উচ্চপদ থেকে প্রায় বাদই দিয়ে দিয়েছিল। এজন্যই ইহুদিরা আইন, চিকিৎসা, সাহিত্য ও অনুরূপ পেশায় বেশি মনোযোগ দিয়েছিলেন এবং এসব ক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তার করেন। আর তা ন্যাশনাল সোশ্যালিস্টদের(নাৎসিদের) ঈর্ষা ও হিংসার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ওরা নিজেরা এইসব জায়গা দখল করতে চায়” (সিডনি ফে, ইতিহাসের অধ্যাপক, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি, “নাৎসি ট্রিটমেন্ট অব দ্যা জ্যুজ”, “কারেন্ট হিস্ট্রি”, নিউ ইয়র্ক, জুন ১৯৩৩)।
নাৎসিরা আরেকটি কাল্পনিক যুক্তি দিয়ে তাদের ইহুদি-বিরোধিতাকে ন্যায্যতা প্রদান করতে চায়: সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদকে তারা “আন্তর্জাতিক ইহুদি ষড়যন্ত্র”-এর ফসল বলে প্রচার করে। মার্ক্সবাদকে তারা “ইহুদি লোভের প্রকাশ” আখ্যা দেয়, যা জার্মান জাতির স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর এবং “টিউটনিক জাতির সংস্কৃতির সাথে সাংঘর্ষিক”। এই যুক্তিতে, ইহুদি-বিদ্বেষকে বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলন দমনের ধর্মযুদ্ধের অংশ বানানো হয়।
কিন্তু বাস্তবতা হলো, জার্মান শ্রমিক শ্রেণির প্রায় সম্পূর্ণটাই “টিউটনিক” জাতিভুক্ত ছিল। জার্মানির অন্যান্য শ্রেণির চেয়েও অধিক। শ্রমিক আন্দোলনের বুদ্ধিজীবী নেতাদের মধ্যে ইহুদিরা থাকলেও সাধারণ কর্মীদের পুরোটাই ছিল খাঁটি খ্রিস্টান।
আজও নাৎসি জার্মানিতে পঞ্চাশ হাজারের বেশি নারী-পুরুষ কারাগারে বা ডিটেনশন ক্যাম্পে আটক রয়েছে। এই ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসের শিকারদের মধ্যে মাত্র এক শতাংশ নিষিদ্ধ ইহুদি জাতির সদস্য। কিন্তু নব্বই শতাংশই শ্রমিক শ্রেণিভুক্ত মানুষ। এই উন্মত্ত বর্ণবিদ্বেষের পেছনে কোনো “বৈজ্ঞানিক” বা রাজনৈতিক কারণ নেই। সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক। প্রত্যেক ইহুদিকে অধ্যাপক, পেশাদার বা ব্যবসায়ীর পদ থেকে উৎখাত করা হয়েছে, যাতে একজন পদলোভি নাৎসি, যে নিজ যোগ্যতায় সফল হতে পারেনি সে, ওই জায়গা দখল করতে পারে। ইহুদি-বিদ্বেষের ফল কিছু “আর্য” ব্যবসায়ীর জন্য লাভজনক হলেও, জার্মানির শিক্ষা ও সংস্কৃতির জন্য তা মারাত্মক অবনতি ডেকে এনেছে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পণ্ডিতদের সরিয়ে খালি করা আসনগুলি এখন মধ্যমেধার দখলে। এই ঘৃণার সংস্কৃতি জার্মানির বৌদ্ধিক জীবনকে ধ্বংস করে দিয়েছে। এই কাজকে “বৈজ্ঞানিক” ভিত্তি দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে নৃতত্ত্ববিদ্যাকে বিকৃত করে। রক্তের বিশুদ্ধতা ও উচ্চগুণের মতবাদ ঝটিকা বাহিনীর উদ্দীপনায় “বিজ্ঞান”-এর মর্যাদায় উন্নীত হয়। এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন একজন হতাশ বিজ্ঞাপন আঁকিয়ে যিনি জার্মানিকে নরক বানিয়ে ছাড়েন।
“মুখে শয়তানি হাসি নিয়ে কালো চুলের ইহুদি যুবক ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওৎ পেতে থাকে অসতর্ক জার্মান মেয়ের জন্য, তাকে নিজের রক্তবীর্যে কলুষিত করবে বলে, এবং তাকে তার নিজের জাতি থেকে ছিনিয়ে নেবে বলে। যে জাতিকে সে পদানত করতে চায় সেই জাতির জাতিগত ভিত্তিকে সে যে কোন উপায়ে ধ্বংস করতে চায়। যেমন সে ব্যক্তিস্তরে নারীকে বোকা বানিয়ে কলুষিত করে, তেমনি ভিনদেশিদের আটকাতে যে জাতের গণ্ডি তোলা আছে তাকেও সে ভেঙ্গে দিতে কুন্ঠিত হয় না। ইহুদিরাই নিগ্রোদের রাইন নদীর তীরে এনেছিল এবং আনছে। সেই একই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে। যে শ্বেতাঙ্গ জাতিকে তারা ঘৃণা করে সেই স্বেতাঙ্গ জাতিকে ধ্বংস করার জন্য। বেজন্মার চাষ করার মাধ্যমে। যে সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব স্বেতাঙ্গরা অর্জন করেছে তা বিনষ্ট করে শ্বেতাঙ্গদের প্রভু হয়ে ওঠার জন্য! ব্যক্তিকে ধারাবাহিকভাবে কোরাপ্টেড করে ওরা জাতি’র স্তরকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে নামিয়ে আনতে চায়!” (হিটলার, আত্মজীবনী)
এই উন্মত্ত জাতিবিদ্বেষের রচয়িতা নিজেই একজন কালো চুলের সংকর। যে অপরাধের জন্য সে ইহুদি যুবকদের অভিযুক্ত করে, তা সে নিজেই করেছে। সেই অঞ্চলে জন্ম নিয়েছে যেখানে রক্তের বিশুদ্ধতা ইতিহাসের উষালগ্ন থেকে কখনোই ছিল না। সে আজ জার্মানিকে কলুষিত করতে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু এই “রক্ত ও বর্ণ” উপাসনার আসল অর্থ হলো সাম্রাজ্যবাদ। নাৎসিদের বিশ্বাস—স্বর্ণকেশী, নীলচোখ নর্ডিক সুপারম্যান শ্বেতাঙ্গ জাতি অন্যান্য সকল জাতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তাই বিশ্ব শাসন করা তাদের নিয়তি।
“ন্যাশনাল সোশ্যালিজম (নাৎসিবাদ) গোবিনো ও হিউস্টন স্টুয়ার্ট চেম্বারলেনের মতবাদ থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। সর্ব-জার্মানিবাদে রঞ্জিত হয়েছে। তৃতীয় রাইখের মৌলিক নীতি হলো ‘আর্য শ্রেষ্ঠত্ব’-র মতবাদ” (উইকহাম স্টিড, হিটলার: কোথা থেকে এবং কোথায়?)। অবশ্য, বাস্তবে নাৎসি সাম্রাজ্যবাদীদের আর্য প্রপিতামহরা সবাই সেন্ট্রাল এশিয়া থেকেই এসেছিল এমন নয়। তারা উত্তরের মেরু অঞ্চল থেকেও এসেছিল।
হিটলারের ক্ষমতায় আসার বহু আগে থেকেই নাৎসি আন্দোলনের একটি জনপ্রিয় স্লোগান ছিল—“জার্মানির নিজস্ব উপনিবেশ দরকার!” সম্প্রতি এই দাবি আরও জোরালো হয়েছে, যুদ্ধের হুমকি দিয়ে এই দাবি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু জার্মানির ঔপনিবেশিক প্রসার ঘটানোর চিৎকার সর্বদাই নাৎসি প্রপাগাণ্ডার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে থেকেছে। বস্তুত তাদের কর্মসূচীর ছদ্ম সমাজতান্ত্রিক উপাদানগুলিকে সবসময় পাশে সরিয়ে রাখা হয়েছিল এই কথা বলে যে উপনিবেশ সম্প্রসারণ কার্যকর না করা পর্যন্ত জার্মানির সামাজিক সমস্যাগুলি সমাধান করা সম্ভব হবে না। গোয়েরিং বলেছেন: “যখন জার্মানির মত ছোট্ট এক ভূখণ্ডে ৬৫ মিলিয়ন মানুষ বাস করে, তখন সামাজিক সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা অবাস্তব, কারণ সমাধানের জন্য জরুরি অপরিহার্য শর্তগুলিই বিরাজ করছে না। সমাধানের একমাত্র উপায় হলো বাহ্যিক শক্তি অর্জন, যা জাতির জন্য প্রাণরস ও পরিসর তৈরি করবে।” (গোয়েরিং, বার্লিনে শ্রমিক সমাবেশে ভাষণ, ৯ এপ্রিল ১৯৩৩)
জার্মান জনগণকে অর্থনৈতিকভাবে ধ্বংস করে জার্মানিকে পুনরায় বিপুলভাবে সামরিকীকরণ করে ‘বাহ্যিক শক্তি অর্জন’-এর পর, এখন নাৎসিরা যুদ্ধের পথে হাঁটছে “শ্বেতাঙ্গ পুরুষের দায়” বহনের জন্য। হিটলার সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন: “জার্মানিকে শক্তিশালী হতেই হবে, যাতে সে তার উপনিবেশ ফিরে পাওয়ার দাবি সফলভাবে তুলে ধরতে পারে”। এবং গোয়েরিং আরও স্পষ্টভাবে বলেছেন: “আমাদের উপনিবেশের দাবি জোরালো করতে হবে, যতক্ষণ না বিশ্ব তা মেনে নেয়। সত্য হলো, জার্মানির এখন একটি নতুন ও শক্তিশালী সেনাবাহিনী আছে, এবং সে তার হীনমন্যতা কাটিয়ে উঠেছে!” সুপারম্যানদের রাজত্ব চলছে জার্মানিতে। তারা তাদের জাতের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে স্থিরনিশ্চিত। এবং তারা এই ধরাতলে তাদের জায়গা ফিরে পেতে দৃঢ়সংকল্প। এটাই হল জাত ও রক্তের অতীন্দ্রিয় উপাসনার ব্যবহারিক অভিব্যক্তি।
ফ্যাসিবাদ জন্মলগ্ন থেকেই এক আন্তর্জাতিক পরিঘটনা। এবং জন্মলগ্ন থেকেই ফ্যাসিবাদ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সাম্রাজ্যবাদী। ১৯১৯ সালে মুসোলিনি লিখেছিলেন: “সাম্রাজ্যবাদ হলো জীবনের চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয় নিয়ম।” এখন উনি সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণের পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে চলেছেন। আবিসিনিয়া আক্রমণের অব্যবহিত পূর্বে তিনি তার এই পরিকল্পনা ঘোষণা করেছিলেন: “ইতালির ভবিষ্যৎ পশ্চিম বা উত্তরে নেই। ইতালির ভবিষ্যৎ আছে পূর্ব ও দক্ষিণে—এশিয়া ও আফ্রিকায়। এশিয়ার বিপুল সম্পদকে কাজে লাগাতে হবে, আফ্রিকাকে সভ্যতার আওতায় আনতে হবে। আমরা চাই—যে জাতিগুলি ইতিমধ্যে আফ্রিকায় প্রবেশ করেছে, তারা যেন ইতালির সম্প্রসারণে বাধা না দেয়।”
ফ্যাসিবাদীরা তাদের সম্প্রসারণের গতিপ্রকৃতি গোপন করে না। তাদের স্লোগান: “নতুন জায়গা ও কাজের জন্য যুদ্ধ!” যুদ্ধের মাধ্যমে উপনিবেশ দখল আবশ্যক, কারণ যুদ্ধ বেকারত্ব সমস্যারও সমাধান করবে বেকার জনতাকে “তোপের খোরাক” হিসেবে ব্যবহার করে। পুঁজিবাদ তার পতনের পর্যায়ে শ্রমিক শ্রেণিকে নিয়োগ দিতে পারে না। সম্পূর্ণ বেকার হয়ে পড়া মানুষকে রিলিফও দিতে পারে না মুনাফার পতনের ফলে। সেই কারণে, অবক্ষয়ী পুঁজিবাদে সৃষ্ট বেকারত্ব সমস্যার সমাধান একমাত্র হতে পারে আভ্যন্তরীন দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত এক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই মূমূর্ষু পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবসান। কিন্তু ফ্যাসিবাদের ঐতিহাসিক দায় হল সর্বসাধারণের কল্যাণের পরিপন্থি হয়ে ওঠা এই পচাগলা পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটাকে অন্য পথে টিকিয়ে রাখা। তাই ফ্যাসিবাদ বেকারত্বের “সমাধান” খোঁজে যুদ্ধে। সঠিকভাবেই বলা হয়ে থাকে যে ফ্যাসিবাদ মানেই যুদ্ধ। নীচের বিখ্যাত সব উক্তিগুলি থেকে তা স্পষ্টতর হবে। “ফ্যাসিবাদ যুদ্ধ থেকে জন্মেছে, এবং যুদ্ধেই তার মুক্তি। আমাদের দেশ কেবল একটি মহাযুদ্ধের মাধ্যমেই এগিয়ে যেতে পারে।” (মারিও কার্লি)।
“থ্রি চিয়ার্স ফর ওয়ার! আমি এই শ্লোগান তুলতে পারি নিশ্চয়। থ্রি চিয়ার্স ফর ইটালি’স ওয়ার! সবার ওপরে, সব থেকে মহৎ এই শ্লোগান। সাধারণ ভাবে সব যুদ্ধের জন্যই থ্রি চিয়ার্স!” (পপলো ডি’ইতালিয়া)। এটা ফ্যাসিস্ট আন্দোলনের একদম শুরুর পর্বে মুসোলিনির লেখা একটি প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত। দু’বছর বাদে, তখনও তিনি ক্ষমতায় আসেননি, ঐ একই পত্রিকায়, তার পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্রে, তিনি লিখছেন, “শান্তি এক অবাস্তব ধারণা, অথবা বলা যায় শান্তি হল নিছক যুদ্ধ বিরতি”। ১৯২৬ সালে চেম্বার অব ডেপুটিজ-এর এক সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি ঘোষণা দেন, “ইতালিয় নেশন এক চিরস্থায়ি যুদ্ধাবস্থায় থাকবে”। পরের বছর তিনি ফ্যাসিবাদের আদর্শ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এই চিত্রবৎ বর্ণনা দিচ্ছেন: “আমাদের চোখের নিমেষে পাঁচ মিলিয়ন সৈন্য মোবিলাইজ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে এবং তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিতে সক্ষম হতে হবে; আমাদের নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীকে শক্তিশালী করতে হবে—এগুলোর ওপর আমি আরো বেশি বেশি আস্থাশীল হয়ে উঠছি—এদের সংখ্যা আর তেজ এমন হতে হবে যাতে এদের ইঞ্জিনের গর্জন এই উপদ্বীপের অন্য যেকোনো শব্দকে থামিয়ে দেয়, আর তাদের ডানার ছায়ায় আমাদের দেশের আকাশ ঢেকে যায়!” এই লক্ষ্য পূরণে ইতালির জনগণকে অর্থনৈতিকভাবে ধ্বংস করা হয়েছে। তাদের দুঃখকষ্ট ও প্রতিবাদের আওয়াজ নিষ্ঠুরভাবে দমন করা হয়েছে যাতে ইতালির মাটিতে কেবল যুদ্ধ দামামাই শোনা যায়।
আবিসিনিয়া যুদ্ধের আগেই ইতালি সরকার ১৫০ বিলিয়ন লিরার অবিশ্বাস্য পরিমাণ ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ে। তারপর তা আরও অন্তত ৫০ শতাংশ বেড়েছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চালানোর মতো অর্থ না থাকায় আমদানি ক্রমাগত ব্যাপকভাবে সীমিত করা হয়েছে। আর সেই সীমিত আমদানির সিংহভাগ বরাদ্দ করা হয়েছে যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য। ফলস্বরূপ, খাদ্য ও নিত্য ব্যবহার্য পণ্যের দাম আকাশছোঁয়া, আর মজুরি ও বেতন ক্রমাগত কমছে। লিরার মূল্য হ্রাস ও ক্রয়ক্ষমতা ধ্বংস হওয়ায় একটি ক্ষুদ্র ধনিক শ্রেণি ছাড়া বাকি সবাই দারিদ্র্যের গভীরে তলিয়ে যাচ্ছে।
জার্মানিতে নাৎসিরা ইতালির ফ্যাসিবাদীদের চেয়েও এগিয়ে গেছে। “দুর্বল ও পিছিয়ে পড়া” জাতিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়ার পাশাপাশি তারা দেশের ভেতরেই শত্রু নির্মূলকরণের নামে অবর্ণনীয় অত্যাচার চালিয়েছে। শুধু শ্রমিক শ্রেণিই নয়, সব ধরণের প্রগতিশীল অংশ—উদারপন্থী, শান্তিবাদী, মানবতাবাদী, প্রকৃত খ্রিস্টানদেরও “শত্রু” হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে তাদের নিকেশ করে ন্যাশনাল সোশ্যালিজমকে জয়যুক্ত করার লক্ষ্যে। হাজার হাজার মানুষকে কারাগারে ও ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখা হয়েছে, যেখানে মধ্যযুগীয় নির্যাতনের মাধ্যমে তাদেরকে নাৎসি শাসনের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য করা হয়। অভ্যন্তরীন শত্রুদের নিকেশ করার সপক্ষে যুক্তিও খাড়া করে নাৎসিরা। ১৯৩৫ সালে বার্লিনে অনুষ্ঠিত ‘আন্তর্জাতিক শাস্তিবিদ্যা কংগ্রেস’-এ গোয়েবলসের নেতৃত্বে জার্মান প্রতিনিধিদল “কারাগারে কঠোর শাস্তি”-র পক্ষে যুক্তি দেয় এবং অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিদের প্রস্তাবিত “মানবিক আচরণ ও শিক্ষা”-র বিরোধিতা করে। গোয়েবলস নির্লজ্জভাবে দাবি করেন, “বন্দীদের উপর অত্যাচার প্রয়োজনীয় ও উপকারী।” নাৎসিদের এই বর্বর বক্তব্যে বিদেশাগত প্রতিনিধিরা এতটাই স্তম্ভিত হয়ে যান যে একজন ফরাসি আইনবিদ বলেছিলেন: “ন্যায়বিচারের ভাষা থেকে প্রতিশোধের ধারণাকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলতে হবে। নাহলে আমরা আবার বর্বরতায় ফিরে যাব।” বহু বিদেশি প্রতিনিধি এই কংগ্রেস ত্যাগ করেন এই বলে যে তাদের দেশের দণ্ডবিদ্যার সাথে জার্মানির ফারাক এতটাই গভীর যে নাৎসি বিচারমন্ত্রী সহ অন্যান্য প্রতিনিধিদের উত্থাপিত নীতিগুলি নিয়ে আলোচনা চালানো অর্থহীন।
“আমি জার্মানির একটি শ্রমিক শিবিরে ছিলাম। আমি জার্মানির জেলেও ছিলাম। ভয়াবহ ব্যাপারস্যাপার দেখেছি আমি। ওই নরক থেকে দূরে থাকুন। জার্মানি এখন নরক, কারণ মানুষ আশাহারা হয়ে পড়ে। আমি একজন খ্রিস্টান। আমি নাৎসিদের সাথে কথা বলতে পারি না। কিন্তু কমিউনিস্টদের সাথে বলতে পারি। কারণ, আর যাই হোক না কেন তারা যুক্তিবাদী এবং মানবতার মঙ্গল নিয়ে ভাবে।” –যে গণভোটের ফলাফলকে নাৎসিদের প্রতি জনপ্রিয় সমর্থন হিসেবে তুলে ধরা হয় সেই গণভোটের প্রাক্কালে সার উপত্যকার একটি শ্রমিক সমাবেশে এক ক্যাথলিক পাদ্রি এই কথাগুলি বলেছিলেন। তিনি তো বলশেভিকদের বন্ধু ছিলেন না। ফ্যাসিবাদের নির্মম অভিজ্ঞতা তাকে এই স্বীকারোক্তিতে বাধ্য করেছিল যে, যে কমিউনিস্টদের ধ্বংস করাই ফ্যাসিবাদের ঘোষিত লক্ষ্য, সেই কমিউনিস্টরাই প্রকৃতপক্ষে মানবতার রক্ষক। এই একটি সাক্ষ্যই ফ্যাসিবাদকে এক অভিশাপ হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য যথেষ্ট।
আগের পর্বের সূত্র