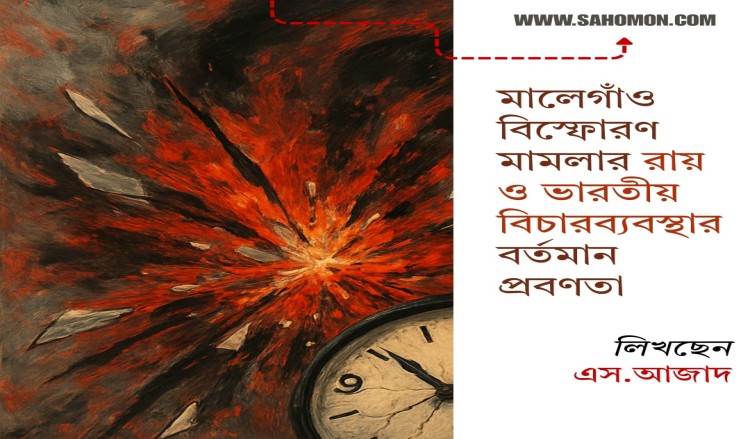সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভারতীয় বিচারব্যবস্থায় এক উদ্বেগজনক প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে—গুরুতর সন্ত্রাসবাদ, সাম্প্রদায়িক সহিংসতা এবং দুর্নীতির মতো স্পর্শকাতর মামলায় অভিযুক্ত, বিশেষত হিন্দু চরমপন্থার সঙ্গে যুক্ত রাজনৈতিক নেতা বা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা "প্রমাণের অভাবে" মুক্তি পেয়ে যাচ্ছেন। এই প্রবণতা বিচারব্যবস্থার নিরপেক্ষতা, তদন্তকারী সংস্থার ভূমিকা এবং আইনের শাসনের প্রতি জনগণের আস্থা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তৈরি করেছে। ২০১৪ সালে কেন্দ্রে রাজনৈতিক পালাবদলের পর সন্ত্রাসবাদ সংক্রান্ত আলোচনায় একটি স্পষ্ট পরিবর্তন দেখা যায়। যেসব ঘটনাকে আগে "হিন্দু সন্ত্রাস" বা "গেরুয়া সন্ত্রাস" বলে উল্লেখ করা হতো, তা ধীরে ধীরে অস্বীকার করা শুরু হয়। অনেক বিশ্লেষক মনে করেন, এই ধরনের মামলাগুলো দুর্বল হয়ে যাওয়া বা অভিযুক্তদের খালাস পাওয়ার পেছনে বিচারব্যবস্থার ওপর পরোক্ষ রাজনৈতিক চাপ বা প্রভাব থাকতে পারে। রাষ্ট্রের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য যখন বিচার প্রক্রিয়ার উপর প্রভাব ফেলে, তখন ন্যায়বিচারের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক।মালেগাঁও বিস্ফোরণ, বাবরি মসজিদ ধ্বংস, গুজরাট দাঙ্গা, সোহরাবুদ্দিন শেখ ভুয়া এনকাউন্টার, বেস্ট বেকারী এবং কর্ণাটকের জমি দুর্নীতির মতো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মামলার রায় বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ভারতের বহুমুখী গণতন্ত্রের পরিবর্তে একমুখী স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতা।
২০০৮ সালের মালেগাঁও বিস্ফোরণ মামলা এই প্রবণতার এক গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত। এই ঘটনায় সাধ্বী প্রজ্ঞা ঠাকুর এবং কর্নেল প্রসাদ পুরোহিতের মতো ব্যক্তিরা অভিযুক্ত হন। দীর্ঘ বিচার প্রক্রিয়ার পর, প্রাথমিক তদন্তকারী সংস্থা মহারাষ্ট্র এটিএস-এর দেওয়া অনেক প্রমাণ পরবর্তীকালে জাতীয় তদন্ত সংস্থা (NIA) দ্বারা দুর্বল হয়ে যায়। ফলস্বরূপ, অভিযুক্তদের অনেকে জামিনে মুক্তি পান এবং অনেকে খালাসও পেয়ে যান। এটি বিচার প্রক্রিয়ার অস্বাভাবিক দীর্ঘসূত্রিতা এবং তদন্তকারী সংস্থার রাজনৈতিক প্রভাবের ইঙ্গিত দেয়। একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে সোহরাবুদ্দিন শেখ ভুয়া এনকাউন্টার মামলায়, যেখানে তৎকালীন গুজরাটের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-ও অভিযুক্ত ছিলেন। এই মামলায় অভিযুক্ত ২২ জন পুলিশ কর্মকর্তাকে ২০১৮ সালে প্রমাণের অভাবে খালাস দেওয়া হয়, যা বিচারব্যবস্থার নিরপেক্ষতা নিয়ে আরো গভীর প্রশ্ন তোলে।
যখন কোনো রাজনৈতিক নেতার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ ওঠে, তখন বিচার প্রক্রিয়া প্রায়শই রাজনৈতিক প্রভাবের শিকার হয়। ১৯৯২ সালের বাবরি মসজিদ ধ্বংস মামলা এর একটি স্পষ্ট উদাহরণ। এই মামলায় বিজেপি-র শীর্ষস্থানীয় নেতা যেমন লাল কৃষ্ণ আদভানি এবং মুরলী মনোহর জোশী অভিযুক্ত ছিলেন। দীর্ঘ ২৮ বছর পর, ২০২০ সালে, আদালত রায় দেয় যে মসজিদ ধ্বংসের ঘটনা পূর্বপরিকল্পিত ছিল না এবং সব অভিযুক্তকে খালাস করে দেয়। একইভাবে, ২০০২ সালের গুজরাট দাঙ্গা মামলায় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে সুপ্রিম কোর্ট ক্লিনচিট দেয়। এই রায়গুলো বিজেপির কাছে বড় রাজনৈতিক বিজয় হিসেবে বিবেচিত হলেও, বিরোধী দল এবং মানবাধিকার সংস্থাগুলোর মতে এটি ন্যায়বিচারের ব্যর্থতা।
এই সমস্ত মামলাগুলোর বিশ্লেষণ থেকে এটি স্পষ্ট যে, ভারতের বিচারব্যবস্থা আজ এক কঠিন সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। বিচার প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রিতা, রাজনৈতিক প্রভাব, তদন্তকারী সংস্থার পক্ষপাতিত্ব এবং আইনি বৈষম্য—এই সবকিছু মিলে আইনের শাসনের মূল ভিত্তিকেই দুর্বল করে দিচ্ছে। যখন ন্যায়বিচার ক্ষমতা এবং রাজনীতির হাতে বন্দি হয়ে পড়ে, তখন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ হুমকির মুখে পড়ে। একটি সুস্থ গণতন্ত্রের জন্য বিচারব্যবস্থার সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা, দ্রুত বিচার এবং সকল নাগরিকের প্রতি সমান দৃষ্টিভঙ্গি অপরিহার্য। এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা না করলে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব।
ভারতীয় বিচারব্যবস্থা, রাজনৈতিক প্রভাব, এবং পুঁজিবাদের সংকট :
ভারতের বিচারব্যবস্থায় সাম্প্রতিক যে প্রবণতাগুলো লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যেখানে প্রভাবশালী ব্যক্তিরা গুরুতর অভিযোগ থেকে মুক্তি পাচ্ছেন, তা শুধুমাত্র রাজনৈতিক পক্ষপাত বা সাম্প্রদায়িক বিভাজনের ফল নয়। এর একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে পুঁজিবাদের কাঠামোগত সংকটের সঙ্গে। বিংশ শতকে দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধের জনক পুঁজিবাদ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক ও মানবিক বিপর্যয় মোকাবিলার পথেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্ম দিয়েছে, যেটা ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের থেকেও আরও ভয়াবহ, ব্যাপক ও সর্বাত্মক। আজও গোটা পৃথিবী জুড়ে চলছে যুদ্ধের মহড়া, ধর্ম ও জাতি দাঙ্গা, বর্ণ বিদ্বেষে উস্কানি, অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক হাঙ্গামায় মদত দিয়ে শক্তিধর রাষ্ট্র গুলো একদিকে যেমন তাদের প্রভাবাধীন অঞ্চল তৈরি করতে চাইছে, অন্যদিকে উন্নয়নের রঙিন ফানুস আর চটকদার বক্তব্যের আড়ালে ভুলিয়ে রাখতে চাইছে সাধারণ মানুষকে। আরও ভাল করে বললে, সংকট মোচনের কোনো স্থায়ী সমাধান নেই জেনেও সে সাময়িক স্বস্তির পাঠ নিতে চাইছে চূড়ান্ত অধঃপতিত ব্যক্তিবাদ আর তা থেকে সঞ্চাত ঘৃণা (ব্যবস্থার প্রতি নয়), পরিপার্সিকের প্রতি উন্নাসিকতা (যা মানুষের নৈতিক চেতনাকে পঙ্গু করে দেয়) আর অর্থনীতির সমরিকীকরণের মধ্যে। পুঁজিবাদের এই সংকট তার রাজনৈতিক এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রভাবিত করছে, যা বিচারব্যবস্থার মতো স্তম্ভকেও দুর্বল করে তুলছে।
পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যখন প্রেম প্রীতি স্নেহ ভালোবাসা পিতৃত্ব মাতৃত্ব সবকিছুই বিক্রয়যোগ্য পণ্য, তখন ন্যায়বিচারই বা নয় কেন? এখানে যে যত অর্থপূর্ণ, তার কাছে ন্যায়বিচার তত সহজলভ্য। ভারতে মামলা পরিচালনার জন্য কেবলমাত্র আইনজীবীর পারিশ্রমিকই নয়, বারংবার তারিখ পরিবর্তন, সাক্ষীর অনুপস্থিতি, তদন্তের অসম্পূর্ণতা—সব মিলিয়ে বিচার একটি দীর্ঘ, ব্যয়বহুল প্রক্রিয়া হয়ে দাঁড়ায়। ফলে সমাজের নিম্নবর্গ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য এটি প্রায় অপ্রাপ্তিযোগ্য। অন্যদিকে, প্রভাবশালী শ্রেণি ও ধনী অভিযুক্তরা দক্ষ আইনজীবী, মিডিয়া ব্যবস্থাপনা, এমনকি কখনও তদন্তকারী সংস্থার ওপর প্রভাব খাটিয়ে নিজেদের রক্ষা করতে সক্ষম হন। বিচার প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রিতা এবং ব্যয়বহুলতা গরীব ও প্রান্তিক মানুষের জন্য ন্যায়বিচারকে দুর্লভ করে তোলে। অপরদিকে, প্রভাবশালী এবং ধনী ব্যক্তিরা তাদের আর্থিক ক্ষমতা ব্যবহার করে বিচার প্রক্রিয়াকে নিজেদের অনুকূলে নিয়ে আসতে পারে। এটি মামলার রায় কেনা বা তদন্তে প্রভাব খাটানোর মাধ্যমে হতে পারে। উক্ত মামলা গুলো ও তার রায় এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ, প্রতিটি ক্ষেত্রেই অভিযুক্তরা আইনের ফাঁকফোকর ব্যবহার করে পার পেয়ে যান। এর কারণ হলো, পুঁজিবাদ নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রের ধ্বস্ত কাঠামোতেই এমন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে যেখানে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা একে অপরের পরিপূরক। এই ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা বিচার প্রক্রিয়াকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারেন।
রাষ্ট্র বিচার ও নৈতিকতা : একটা তাত্ত্বিক পটভূমি
আরিস্টটল বলেন, ন্যায়বিচারই হলো রাষ্ট্রের বন্ধন। রাষ্ট্র টিকে থাকে ন্যায়বিচারের মাধ্যমে, এবং বিচার ব্যবস্থার কাজ হলো সেই ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা। তিনি বিচার ব্যবস্থাকে শুধু আইন প্রয়োগের একটি কাঠামো হিসেবে দেখেননি, বরং ন্যায়, নৈতিকতা ও রাষ্ট্রের মঙ্গলসাধনের একটি মৌলিক উপাদান হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তিনি বলছেন, বিচারকগণ হবেন যুক্তিবাদী, পক্ষপাতহীন এবং নৈতিকভাবে সংবেদনশীল। তিনি আরও বলেন, “Law is reason free from passion.” অর্থাৎ, আইন হতে হবে যুক্তিনির্ভর, আবেগমুক্ত, এবং বিচারক সেই যুক্তিকে প্রয়োগ করবেন ন্যায়ের আলোকে। (Aristotle, Politics, Book III, Chapter 16.)
প্লেটোর মতে, বিচারব্যবস্থা হতে হবে জ্ঞানভিত্তিক ও নৈতিকভাবে সুশৃঙ্খল। বিচারকগণ দার্শনিক প্রকৃতির, যারা যুক্তি ও ন্যায়বোধ দ্বারা পরিচালিত। যেখানে ন্যায়বিচার শুধু বাহ্যিক শৃঙ্খলা নয়, বরং অন্তর্নিহিত নৈতিক ভারসাম্য। তিনি বাহুবলের ভিত্তিতে ন্যায়বিচারকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন, ‘জোর যার, ন্যায় তার’—এই চিন্তা অরাজকতা ডেকে আনে। প্লেটো বিশ্বাস করেন, আইন যদি নৈতিকতার ভিত্তি না থাকে, তবে তা মানুষের প্রকৃত কল্যাণ সাধনে ব্যর্থ হয়। (The Republic, Plato) মহাত্মা গান্ধী বিশ্বাস করতেন, আইন হতে হবে ন্যায়ের প্রতিচ্ছবি। যদি আইন অন্যায়কে বৈধতা দেয়, তবে তা মান্য করা উচিত নয়। অগাস্টিন বলেছেন, “যে আইন ন্যায়সঙ্গত নয়, সেটি আদৌ আইন নয়।” (Augustine, De Libero Arbitrio, Book I, Chapter 5.)
কার্ল মার্কস বিচারব্যবস্থাকে কখনও নিরপেক্ষ বা “সর্বজনীন ন্যায়” হিসেবে দেখেননি। বরং তিনি দেখেছেন—এটি মূলত শ্রেণি বিভক্ত সমাজে শাসক শ্রেণির স্বার্থরক্ষার একটি উপকরণ। “Law is the will of the ruling class, made into a law for all.” (The Communist Manifesto 1848. Section I, Marx-Engels Collected Works ) —আইন কোনো নিরপেক্ষ বা চিরন্তন ন্যায়ের প্রতিফলন নয়। বরং সমাজে যে শ্রেণি ক্ষমতাবান, তারা তাদের স্বার্থকে “আইন” আকারে প্রতিষ্ঠা করে। তাই পুঁজিবাদী সমাজে আইন মূলত বুর্জোয়া শ্রেণির (ধনী মালিক শ্রেণির) স্বার্থরক্ষার মাধ্যম। “Your jurisprudence is but the will of your class made into a law for all...”“তোমাদের আইনব্যবস্থা আসলে তোমাদের শ্রেণির ইচ্ছাকে সর্বজনীন আইন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।” (The Communist Manifesto 1848. Section I, Marx-Engels Collected Works ). A Contribution to the Critique of Political Economy (1859)–এ মার্কস বলেন, “The legal system is determined by the economic base.” (“আইন ও বিচারব্যবস্থা মূলত অর্থনৈতিক ভিত্তির দ্বারা নির্ধারিত।”) Critique of the Gotha Programme (1875)–এ মার্কস বলেন,“Right can never be higher than the economic structure of society.” (“অধিকার কখনো সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর চেয়ে উঁচুতে যেতে পারে না।”) The German Ideology–তে মার্কস ও এঙ্গেলস বলেন, “The executive of the modern state is but a committee for managing the common affairs of the whole bourgeoisie.” (“আধুনিক রাষ্ট্রের নির্বাহী অংশ আসলে সমগ্র বুর্জোয়া শ্রেণির যৌথ স্বার্থের তদারকি কমিটি।”) ভারতের বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তক শিবদাস ঘোষের মতে, আইন, বিচার ও ন্যায় এক ঐতিহাসিক, শ্রেণীগত এবং আপেক্ষিক ধারণা। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, আইন ও বিচার সর্বদা কোনো একটি শাসক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করে, তাই তা কখনোই নিরঙ্কুশভাবে নিরপেক্ষ হতে পারে না। তিনি মনে করতেন, বুর্জোয়া সমাজে আইনের উদ্দেশ্য হলো পুঁজিবাদের শোষণমূলক কাঠামোকে টিকিয়ে রাখা। শিবদাস ঘোষ প্রশ্ন তোলেন, যা আইনসম্মত, তা কি সবসময়ই ন্যায়সঙ্গত? তিনি দেখান যে, শাসকরা অনেক সময় এমন আইন প্রণয়ন করে যা তাদের স্বার্থ রক্ষা করে এবং জনগণের অধিকার হরণ করে।
ভারতীয় বিচার ব্যবস্থার স্বরূপ : পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের মুখোশ
ভারতীয় বিচার ব্যবস্থার দিকে তকালে দেখি; প্রাক্তন বিচারপতি মদন লোকুর Unlawful Activities (Prevention) Act বা UAPA-এর মতো কঠোর আইনের অপব্যবহার নিয়ে বারবার প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে, এই আইনের অধীনে ভিন্ন মত পোষণকারী অ্যাক্টিভিস্ট, সাংবাদিক বা সাধারণ নাগরিকদের দীর্ঘদিন ধরে বিনা বিচারে কারাগারে আটকে রাখা হচ্ছে, যা বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতার জন্য ক্ষতিকর। বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে তিনি বিচার ব্যবস্থার নিরপেক্ষতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, যখন রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল মামলাগুলিতে তদন্তকারী সংস্থাগুলির ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে এবং কিছু ক্ষেত্রে অভিযুক্তরা সহজেই জামিন পায়, তখন বিচার ব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থা কমে যেতে পারে। তার বিভিন্ন সময়ের বক্তব্য থেকে এই ধরনের একটি পর্যবেক্ষণ উঠে আসে যে, হিন্দুত্ববাদী অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা দুর্বল করা হচ্ছে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে। তিনি বারবার বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতা, তদন্তকারী সংস্থাগুলির পক্ষপাতিত্ব এবং ভিন্ন মতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলার বিষয়ে সরব হয়েছেন।
পুঁজিবাদের সংকটে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো যে গুলো ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে ক্রিয়াশীল থাকে তারা, ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং কর্পোরেট পুঁজির নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। ভারতের কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা যেমন CBI, ED, NIA প্রভৃতি সংস্থাগুলি আইনত স্বাধীন হলেও বাস্তবে এগুলি রাজনৈতিক ক্ষমতাসীন দলের প্রভাবাধীন হয়ে উঠেছে। এই সংস্থাগুলি প্রায়শই বিরোধীদলের নেতাদের বিরুদ্ধে তৎপর, অথচ শাসকদলের নেতাদের বিরুদ্ধে দুর্বল তদন্ত চালায় বা মামলা দুর্বল করে দেয়।
মালেগাঁও বিস্ফোরণ মামলার মতো অন্যান্য ঘটনাতেও NIA-এর ভূমিকা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠেছে। প্রথমে যে তদন্তকারী সংস্থা (যেমন, এটিএস) শক্ত প্রমাণ হাজির করে, পরে NIA সেই মামলা হাতে নিয়ে অনেক সময়ই সেই প্রমাণগুলোকে দুর্বল করে দেয়। এর ফলে জনমনে এই ধারণা তৈরি হচ্ছে যে, তদন্তকারী সংস্থাগুলো রাজনৈতিক অভিপ্রায়ে প্রভাবিত হয়ে কাজ করছে। তদন্তকারী সংস্থার নিরপেক্ষতা যখন প্রশ্নের মুখে পড়ে, তখন জনগণের বিচারব্যবস্থার ওপর আস্থা কমে যায়। ২০১৩ সালে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি আর.এম. লোধা CBI-কে “একটি খাঁচার তোতাপাখি” (a caged parrot) হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন, এবং তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও গভীর পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছিল ‘NIA বর্তমানে একটি রাজনৈতিক হাতিয়ার হয়ে উঠেছে’।
পুঁজিবাদ চায় রাজনীতিকে কর্পোরেট দ্বারা নিয়ন্ত্রিত রাখতে, বিচারব্যবস্থাকে ক্ষমতাধর শ্রেণির নিরাপত্তা বেষ্টনীতে পরিণত করতে, গণতন্ত্রের মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে। কিন্তু এসব করতে গিয়ে সে নিজেই তার ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধ্বংস করে ফেলে—যেমন গণমাধ্যম, আদালত, শিক্ষাব্যবস্থা। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর জনগণের বিশ্বাস ক্ষয়ে যায় এবং সমাজ এক নতুন post-truth authoritarianism-এর দিকে এগোয়।
পুঁজিবাদের বাণিজ্যিক যুক্তি অনুযায়ী, যে কোনো প্রতিষ্ঠান তখনই কার্যকর, যখন তা পুঁজির স্বার্থ রক্ষা করে এবং লাভজনক হয়। এই যুক্তি বিচারব্যবস্থার ওপর চাপিয়ে দিলে ন্যায়বিচার আর নীতিনির্ভর থাকে না, হয়ে ওঠে শ্রেণি-নির্ভর। উচ্চবিত্ত শ্রেণি দামী আইনজীবী, প্রভাবশালী লবিং, মিডিয়া প্রভাব এবং রাজনৈতিক যোগাযোগ ব্যবহার করে বিচারকে নিজের অনুকূলে নিয়ে আসে। অপরদিকে, নিম্নবর্গ ও প্রান্তিক জনগণ বিচারপ্রক্রিয়ায় প্রবেশের ক্ষমতা হারায়। রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী, অপর্যাপ্ত সাক্ষ্যসংগ্রহ, দেরিতে চার্জশিট—সব মিলিয়ে ন্যায়বিচার তাদের নাগালের বাইরে থেকে যায়। এই বিচারের পণ্যায়ন Marx-এর “commodity fetishism” তত্ত্বেরই এক আধুনিক রূপ: যেখানে পণ্য হিসেবে ন্যায়বিচার বিকোচ্ছে, অথচ তা মানুষ বুঝতেও পারছে না।
পুঁজিবাদের সংকট কেবল অর্থনৈতিক মন্দা বা বাজারের ওঠানামার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটি একটি কাঠামোগত বৈপরীত্য, যা মুনাফার নিরন্তর তাগিদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এই তাগিদ যখন মানবিকতা, সামাজিক ন্যায় এবং রাষ্ট্রের ন্যায়বিচারমূলক প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, তখন সেই ব্যবস্থা এক গভীর সংকটের সম্মুখীন হয়। বিগত কয়েক দশকে বিশ্বজুড়ে উদারীকরণ এবং কর্পোরেট পুঁজির উত্থান বিচারব্যবস্থাকেও তার প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে পারেনি। বিখ্যাত ভূগোলবিদ ও সমাজতাত্ত্বিক ডেভিড হার্ভে যেমন বলেছেন, পুঁজিবাদ যখন সংকটে পড়ে, তখন রাষ্ট্র কর্পোরেট স্বার্থের সেবক হিসেবে কাজ করে। এর ফলে, জনগণের জন্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যম হিসেবে বিচারব্যবস্থার ভূমিকা ক্রমশ ক্ষুণ্ণ হয়। এটি আর একটি নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান থাকে না, বরং ক্ষমতা ও অর্থের খেলার একটি অংশে পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়ায়, আইন ও বিচার পদ্ধতি এমনভাবে পরিবর্তিত হয় যে, তা অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করে এবং দুর্বল শ্রেণির জন্য ন্যায়বিচারকে আরও কঠিন করে তোলে
রাজনৈতিক দলগুলি কর্পোরেট পুঁজির সহায়তায় নির্বাচনে অংশ নেয়; নির্বাচনের পর সেই কর্পোরেট স্বার্থ রক্ষা করাই তাদের প্রথম কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। ফলে, রাষ্ট্রের তদন্ত সংস্থাগুলি স্বাধীনতা হারায় এবং বিচারব্যবস্থা রাজনৈতিক অর্থনীতির একটি হাতিয়ারে পরিণত হয়। এর ফলে, যখন কোনো রাজনৈতিক নেতা বা কর্পোরেট ব্যক্তির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে, তখন তদন্তকারী সংস্থাগুলো দুর্বল প্রমাণ হাজির করে অথবা মামলার গতি কমিয়ে দেয়, যা শেষ পর্যন্ত অভিযুক্তদের খালাস পেতে সাহায্য করে।
সংকটগ্রস্থ পুঁজিবাদ বনাম সাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষতা :
পুঁজিবাদের সংকটে যখন মন্দা, বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি সমাজে অসন্তোষ তৈরি করে, তখন রাষ্ট্র সেই ক্ষোভকে অন্য খাতে প্রবাহিত করতে চায়। এখানে কার্যকর হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায় সাম্প্রদায়িক বিভাজন। জনগণের দৃষ্টি অর্থনৈতিক সংকট থেকে সরিয়ে দিতে এবং ভোটব্যাঙ্ক সুসংহত করতে মুসলিম সম্প্রদায়কে “অভ্যন্তরীণ শত্রু” হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। এই রণনীতির অংশ হিসেবে হিন্দু চরমপন্থার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও, তাদের খালাস দেওয়া হয় বা মামলা দুর্বল করে দেওয়া হয়। আবার মুসলিম অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ কারাবাস ও ন্যায্য বিচারবিচ্ছিন্নতা দেখা যায়। অন্যদিকে বাবরি মসজিদ ধ্বংস মামলায় (1992) অভিযুক্ত এল.কে. আদবানি, মুরলি মনোহর যোশীসহ ৩২ জনের সবাইকে ২০২০ সালে খালাস দেওয়া হয়। বেস্ট বেকারি মামলায় সাক্ষীদের ভয় দেখানো, প্রমাণ দুর্বল করা ইত্যাদি মাধ্যমে প্রথমে অভিযুক্তরা ছাড়া পান। পরে পুনর্বিচারে কেবল অল্প কয়েকজন দোষী সাব্যস্ত হয়। হাশিমপুরা হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত PAC সদস্যরা ৩২ বছর পর খালাস পায়। হায়দরাবাদ মক্কা মসজিদ বিস্ফোরণ এবং সমঝোতা এক্সপ্রেস মামলায় মুসলিমদের পরিবর্তে হিন্দু সংগঠনের সদস্যরা অভিযুক্ত হন, কিন্তু পরে প্রমাণের অভাবে ছাড়া পেয়ে যায়।
পুঁজিবাদ যখন কর্মসংস্থান দিতে ব্যর্থ হয়, তখন ভুক্ষা পেটের অসন্তোষ দমন করতে আইডিওলজিক্যাল রণনীতি অবলম্বন করে। এর মধ্যে অন্যতম কার্যকর পন্থা হল সাম্প্রদায়িকতা ও জাতিগত বিভাজন। ভারতীয় প্রেক্ষাপটে মুসলিম জনগোষ্ঠীকে “জাতীয় নিরাপত্তার শত্রু” হিসেবে চিহ্নিত করে জাতীয়তাবাদকে উস্কে দেওয়া হয়। এই বিভাজন শাসকশ্রেণির ভোটব্যাঙ্ক সুরক্ষা করে এবং অর্থনৈতিক ন্যায্যতার দাবিকে ঢাকা দেয়। একইসঙ্গে, বিচারব্যবস্থা এই বিভাজনকে অনুমোদন করে, যখন হিন্দু চরমপন্থীদের খালাস দেওয়া হয় এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে মামলার সংখ্যা বাড়ে। এই কৌশলকে দীপেশ চ্যাটার্জি বলেন “Islamophobia as a state policy of late capitalism”। তিনি তাঁর "Islamophobia as a State Policy" নামের একটি নিবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে ইসলামোফোবিয়াকে পুঁজিবাদের স্বার্থে একটি রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ('The International Journal of Zizek Studies'-এর ভলিউম ৪, সংখ্যা ২)
ভারতে বিচারব্যবস্থায় ধর্মভিত্তিক পক্ষপাত ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠছে। হিন্দু চরমপন্থীদের সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা বারবার “ভুল বোঝাবুঝি” হিসেবে রূপায়িত হয়, অথচ মুসলিম অভিযুক্তদের ক্ষেত্রে সামান্য সন্দেহই দীর্ঘ বন্দিত্বের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। PUCL (People's Union for Civil Liberties) এবং Jamia Teachers' Solidarity Association-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ২০ বছরে মিথ্যা সন্ত্রাসবাদী মামলায় অভিযুক্ত শতাধিক মুসলিম যুবক ১০-১৪ বছর জেল খেটেছেন, পরে আদালতে খালাস পেয়েছেন।
মালেগাঁও বিস্ফোরণ, বাবরি মসজিদ ধ্বংস, গুজরাট দাঙ্গা এবং অন্যান্য মামলায় যে বিচার বিভাগের দুর্বলতা ও রাজনৈতিক প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তা শুধুমাত্র বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং একটি পুঁজির বৃহত্তর কাঠামোগত সংকটের প্রতিফলন। এখানে পুঁজিবাদ, রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং বিচারব্যবস্থার অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়। গণতান্ত্রিক কাঠামোর ভিত দুর্বল করে এক ধরনের “corporate authoritarianism” প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, যেখানে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো জনগণের বদলে ক্ষমতাসীনদের সেবা করছে।
পুঁজিবাদের সংকট বিচারব্যবস্থায় এক ধরনের দ্বৈত মান তৈরি করেছে। একদিকে, ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো (NCRB)-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতে বিচারাধীন বন্দিদের একটি বিশাল অংশ (৭৬%) দরিদ্র ও দলিত সম্প্রদায়ভুক্ত, যারা বিচার ছাড়াই বছরের পর বছর জেলে কাটান। অন্যদিকে, রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী অভিযুক্তরা খুব সহজেই জামিন বা খালাস পেয়ে যান। এই বৈষম্য আইনের শাসনের ধারণাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে এবং জনগণের মনে এই ধারণা তৈরি করে যে, আইন সবার জন্য সমান নয়, বরং এটি ক্ষমতা এবং অর্থের কাছে নতি স্বীকার করে। এই দ্বৈত মান সামাজিক ন্যায় ও সমতার ধারণাকে দুর্বল করে দেয় এবং সমাজে বিভাজন আরও বাড়িয়ে তোলে। শিবদাস ঘোষের মতে, বছরের পর বছর ধরে হাজার হাজার বিচারপ্রার্থী মানুষ বিচার না পেয়ে জেলে বন্দী থাকে, যা বিচার ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা এবং শ্রেণীগত পক্ষপাতিত্বের একটি বড় উদাহরণ।
পুঁজিবাদী নিরপেক্ষতা : কর্পোরেট ও ন্যায়বিচার
পুঁজিবাদী সংকটের আরও এক মুখ্য বৈশিষ্ট্য হল রাষ্ট্র ও কর্পোরেট পুঁজির একীভবন। Antonio Gramsci একে বলেন “passive revolution”, যেখানে শাসকশ্রেণি পুরনো কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে ক্ষমতা রক্ষা করতে রাষ্ট্রকে ব্যবহার করে।
এই বাস্তবতায় রাজনীতিকরা কর্পোরেট অনুদানে ক্ষমতায় আসে। ক্ষমতায় এসে তারা কর্পোরেট স্বার্থ রক্ষা করে আইন, নীতি ও তদন্তকে প্রভাবিত করে। রাষ্ট্রীয় তদন্ত সংস্থা ও বিচারব্যবস্থা কর্পোরেট-রাজনৈতিক প্রভুদের নির্দেশে কাজ করে। একে Gramscian পরিভাষায় বলা যায়—hegemony through coercion and consent। উদাহরণস্বরূপ, ২০১৪ সালের পর থেকে SEBI, RBI-এর মতো স্বাধীন আর্থিক সংস্থা সরকারের নীতির মুখপাত্রে পরিণত হয়েছে। Adani গ্রুপের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলেও তদন্ত বারবার স্তব্ধ হয়ে যায়।
এগুলো পুঁজিবাদের সংকটেরই প্রতিফলন। পুঁজিবাদের কাঠামোতে অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও রাজনৈতিক ক্ষমতা একীভূত হয়ে প্রতিষ্ঠানগুলোকে দুর্বল করে দেয়, ন্যায়বিচারকে সীমিত করে এবং সামাজিক বিভাজনকে উৎসাহিত করে। যখন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের কাছে নতি স্বীকার করে, তখন গণতন্ত্রের মূল স্তম্ভগুলো ভেঙে পড়ে। এর ফলে, আইনের শাসন কেবল একটি কথার কথা হয়ে দাঁড়ায় এবং সমাজে ন্যায়বিচারের পরিবর্তে ক্ষমতারই জয় হয়। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে শুধুমাত্র বিচারব্যবস্থার সংস্কার যথেষ্ট নয়, বরং পুঁজিবাদের কাঠামোগত সংকটকে মোকাবেলা করার জন্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটি সামগ্রিক পরিবর্তন প্রয়োজন।
মালেগাঁও বিস্ফোরণ মামলার সহ অন্যান মামলায় অভিযুক্তদের মুক্তি শুধু একটি আইনি সিদ্ধান্ত নয়, এটি ভারতীয় বিচারব্যবস্থার বর্তমান রাজনৈতিকীকরণ, সাম্প্রদায়িক পক্ষপাত এবং তদন্ত ব্যবস্থার দুর্বলতার প্রতিচ্ছবি। এটি কেবল ন্যায়বিচারের প্রশ্ন নয়, বরং একটি গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে আইনের শাসন কতটা দুর্বল হয়ে পড়ছে, তার একটি স্পষ্ট ইঙ্গিত। একটি সুস্থ গণতন্ত্রের জন্য বিচারব্যবস্থার নিরপেক্ষতা, দ্রুততা এবং সকল নাগরিকের প্রতি সমান দৃষ্টিভঙ্গি অপরিহার্য। যখন এই স্তম্ভগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন সমাজে বিভেদ ও অবিশ্বাস বাড়ে, যা সামগ্রিক রাষ্ট্রের সুস্থতার জন্য ক্ষতিকর।
বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র ভারতের বিচারব্যবস্থা, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা—সবই পুঁজিবাদের সংকটের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে নিজেদের অস্তিত্ব হারাচ্ছে। এই বাস্তবতা আমাদের সামনে এক সুস্পষ্ট সত্য তুলে ধরে, বিচারব্যবস্থার সংস্কার কেবল প্রক্রিয়াগত পরিবর্তনে সীমাবদ্ধ রাখা যাবে না। বরং ন্যায়বিচারের মৌলিক চরিত্র ফিরিয়ে আনতে পুঁজিবাদ-উত্তর রাজনৈতিক বাস্তবতা গড়ে তুলতে হবে। এই মুহূর্তে প্রয়োজন সাম্যবাদী বা গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রভিত্তিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো, যেখানে বিচার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য—এসব মৌলিক প্রতিষ্ঠান জনগণের নিয়ন্ত্রণে থাকবে, পুঁজির নয়।
তথ্য ঋণ :
-
BBC Hindi, “Babri Masjid demolition case: All accused acquitted”, 30 Sept 2020
-
Tehelka, “Justice delayed, justice denied in Best Bakery case”, 2014
The Caravan, “Justice Loya's mysterious death and the Sohrabuddin case”, Nov 2017 -
The Wire, “How NIA weakened the Malegaon case after taking it over”, April 2019
-
India Today, 2016: “Yeddyurappa gets clean chit in land denotification case”
Human Rights Watch, “The ‘Anti-Nationals’: The misuse of terror laws against minorities in India”, 2020. -
PTI. “All Accused Acquitted in Sohrabuddin Encounter Case.” The Hindu, 21 Dec. 2018.
-
Indian Express, “NIA drops MCOCA charges against Sadhvi Pragya, six others”, May 14, 2016.
-
Caravan Magazine, “How the NIA was pushed to go soft in the Malegaon case”, March 2019
-
The Hindu, “Malegaon blast accused Sadhvi Pragya gets clean chit from NIA”, 13 May 2016.
-
Scroll.in, “Malegaon blast: Pragya Thakur’s motorcycle was used to plant bomb, says NIA officer”, 18 April 2019.
-
Paranjoy Guha Thakurta, “The Real Face of Corporate Cronyism in India”, Economic & Political Weekly, 2022
-
Thomas Piketty, “Capital and Ideology”, Chapter 13: "Inequality and Institutions in India"
-
Scroll Staff. “Malegaon Blast Case: All Accused Acquitted.” Scroll.in, 25 Apr.2023.
-
Ghosh, Subir. “Justice Delayed and Denied: The Story of Gujarat Riots.” Economic and Political Weekly, vol. 45, no. 15, 2010, pp. 23–27.
-
Ghosh, Sibdas. Selected Works.
-
Marx-Engels Collected Works, The Communist Manifesto 1848. Section I.
-
A Contribution to the Critique of Political Economy (1859)
-
Augustine, De Libero Arbitrio, Book I, Chapter 5.
-
Marx-Engels Collected Works, Critique of the Gotha Programme (1875)
-
Marx-Engels Collected Works, The German Ideology
-
Aristotle, Politics, Book III, Chapter 16.
-
Plato, The Republic.