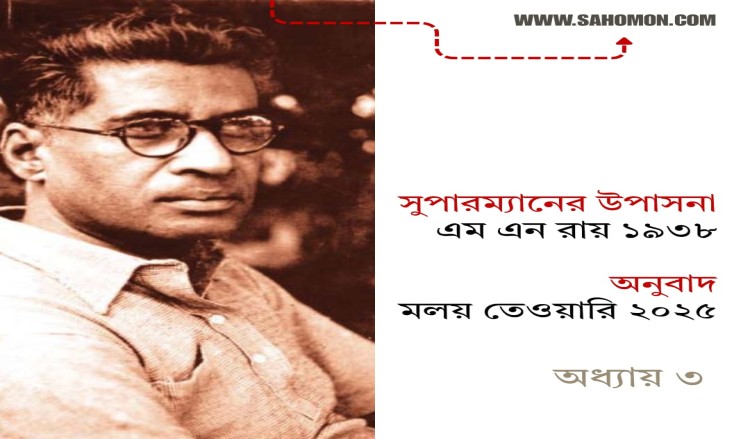আগের দুটি পর্বের সূত্র।
প্রথম পর্ব -
ফ্যাসিবাদ - দর্শন, আদর্শ ও অনুশীলন
দ্বিতীয় পর্ব -
ফ্যাসিবাদী দর্শনের ভিত্তি
ফ্যাসিবাদী দর্শনের সবচেয়ে স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য হলো সুপারম্যানের উপাসনা। এই উপাসনার জনক নীৎশে ছিলেন শোপেনাওয়ারের শিষ্য; আর শোপেনাওয়ার “উপনিষদের দর্শনে সান্ত্বনা লাভ” করেছিলেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, জড়বাদী ভোগসর্বস্বতার নিকৃষ্টতম প্রকাশ এবং ভারতীয় রক্ষণশীল জাতীয়তাবাদের আধ্যাত্মিক মতাদর্শের মধ্যে এক গভীর আত্মীয়তা বিদ্যমান। ফ্যাসিবাদ হলো পুনরুজ্জীবনবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত জাতীয়তাবাদ। ফ্যাসিবাদের চর্চা আমাদের দেখায় পুনরুজ্জীবনবাদ কোথায় গিয়ে পৌঁছাতে পারে। অন্যদিকে, এর মতাদর্শিক পটভূমি প্রকাশ করে যে পুনরুজ্জীবনবাদ হলো সামাজিক প্রতিক্রিয়ার আত্মা; এ হল প্রগতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের এক মতাদর্শিক হাতিয়ার, যে প্রগতির পূর্বশর্ত বিপ্লব।
ফ্যাসিবাদের গ্র্যাণ্ডফাদার শোপেনাওয়ার ছিলেন নৈরাশ্যবাদের অবতার। উপনিষদের “দিব্য দর্শন”-এর অনুরাগী হিসেবে তিনি হেগেলের দর্শনের বিপ্লবী সত্তার বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম চালিয়েছিলেন। তবে হেগেলের দর্শনের বিরুদ্ধে দার্শনিকভাবে লড়াই করা তাঁর মানসিক সামর্থ্যের বাইরে ছিল। তাই প্রতিক্রিয়াশীলের অসহায় ক্রোধ গালিগালাজ রূপে বেরিয়ে এসেছিল। ১৮৪৮ সালের বিপ্লবে পরাজিত জার্মান বুর্জোয়াদের মতাদর্শ ছিল শোপেনাওয়ারের দর্শন। পরাজয় নৈরাশ্য সৃষ্টি করেছিল। জীবনের কঠোর বাস্তবতা থেকে পলায়নের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে এই নৈরাশ্য প্রকাশ পেয়েছিল।
শোপেনাওয়ারের মতে, প্রকৃতির অনড় অপরিবর্তনীয় নিয়ম মানুষকে নিকৃষ্টতম জগতে বাস করতে বাধ্য করে। যেহেতু জীবনের অসহনীয় অবস্থা পরিবর্তন করা যায় না, তাই সেই অবস্থার জগৎ থেকে পালিয়ে বাঁচার ইচ্ছা অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। স্বাভাবিকভাবেই শোপেনাওয়ারের পীড়িত আত্মা, যা ছিল পরাজিত জার্মান বুর্জোয়াদের হতাশার মূর্ত প্রকাশ, উপনিষদের দর্শনে সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছিল—এমন এক দর্শন যা যুগ যুগ ধরে ভারতীয় জনগণকে জীবনের বাস্তবতাকে বদলে দেওয়ার লক্ষ্যে সাহস ভরে মোকাবেলা করা থেকে বিরত রেখেছিল। শোপেনাওয়ারের দর্শনের সারমর্ম হলো স্বাধীন মানবেচ্ছাকে হেয় করা। তাঁর দর্শনে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাকে “সম্পূর্ণরূপে দুষ্ট ও নীচ” বলে ঘোষণা করা হয়। প্রগতির বস্তুগত শক্তিগুলো যেহেতু মানব সংকল্পে প্রকাশ লাভ করে তাই মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে হেয় করার ফলে শোপেনাওয়ারের দর্শনের তাৎপর্য দাঁড়ায় সকল প্রগতির প্রতি নেতিবাচক মনোভাব পোষণ। এই মতবাদ নিয়ে শোপেনাওয়ার হিন্দু দর্শনের সাথে একই ভূমিতে এসে দাঁড়ান। হিন্দু দর্শনও আত্ম উপলব্ধিকে সত্যিকারের জ্ঞানের উৎস এবং আকাঙ্খাকে তার প্রতিবন্ধক বলে ঘোষণা করে। শোপেনাওয়ারের দর্শন এতই স্ববিরোধিতায় পূর্ণ ছিল যে দর্শনের এক সুচিন্তক ইতিহাসবিদ নিম্নোক্ত মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছিলেন: “যদি জগৎ এমন এক বস্তু হয় যা না থাকাই ভালো ছিল, তবে এই জগতেরই অংশ হিসেবে দার্শনিকদের চিন্তাগুলোও না ভাবাই ভালো ছিল।” (ফ্রানৎস মেহরিং, “দর্শনের ইতিহাস প্রসঙ্গে”)। কিন্তু এই দার্শনিক তাঁর সময়ের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ি এবং যে অবস্থার মধ্যে তিনি বাস করতেন সেই অনুসারে ভাবনাচিন্তা করেছিলেন। তিনি ছিলেন প্রতিক্রিয়ার দার্শনিক। অন্যভাবে ভাবা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। শোপেনাওয়ারের দর্শন এতটাই সর্বাত্মক প্রতিক্রিয়াশীল ছিল যে ফ্যাসিস্টদের ঘৃণ্য ইহুদী-বিদ্বেষ এবং নারীদের প্রতি মধ্যযুগীয় দৃষ্টিভঙ্গিকেও তাঁর কৃতিত্ব হিসেবে খুঁজে পাওয়া যায়।
নীৎশে তাঁর গুরুকে আরও পরিমার্জিত করলেন। এবং মূলগতভাবে ঘোষণা করলেন যে, “দুষ্ট ও নীচ” ইচ্ছার জন্য মানুষের লজ্জা পাওয়ার মোটেই দরকার নেই। যেহেতু তা দুষ্ট ও নীচ তাই প্রকাশ্যেই তা হোক এবং তা গর্বের সাথে হোক। শোপেনাওয়ার জীবনকে অপরাধ বলেছিলেন। নীৎশে একে সংজ্ঞায়িত করলেন “দখলদারিত্ব, কঠোরতা, নিষ্ঠুরতা, অপরিচিত ও দুর্বলকে পদদলিত করা, নিপীড়ণ ও শোষণ করার ইচ্ছা”-র প্রকাশ হিসেবে। এখানেই ফ্যাসিবাদের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো নিহিত। কিন্তু নীৎশে কীভাবে তাঁর গুরুর নৈরাশ্যবাদ থেকে এমন এক জঙ্গী মতাদর্শ গঠন করতে পারলেন? প্রতিক্রিয়ার দর্শনের এই পুনর্গঠন ঘটেছিল জাতির সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনে জার্মান বুর্জোয়াদের অবস্থানের পরিবর্তনের ফলে।
শোপেনাওয়ার তাঁর নৈরাশ্যবাদ প্রচার করার পর থেকে জার্মানিতে এমন ঘটনা ঘটেছিল যা বুর্জোয়াদের সাহসী করে তুলেছিল। তারা তাদের অনুভূতিকে ভিন্ন ভাষায় প্রকাশ করতে শিখেছিল। নৈরাশ্যবাদের স্থান নিয়েছিল নির্মম অবজ্ঞাবাদ। জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণি রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে ব্যর্থ হয়েছিল। ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের পরাজয় ঘটেছিল, কারণ বুর্জোয়ারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। কিন্তু বিপ্লব ছিল এক ঐতিহাসিক অপরিহার্যতা। তা ঘটারই ছিল। বুর্জোয়া শ্রেণি বিপ্লব আনতে ব্যর্থ হওয়ায় উপর থেকে বুর্জোয়া শাসন চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল—বিসমার্কের অনুগ্রহে, যিনি ভীত ও হতমনোবল বুর্জোয়াদের ধাক্কা দিয়ে তুলে এনেছিলেন প্রুশিয়ান জাঙ্কারদের সাথে ক্ষমতা ভাগ করে নেওয়ার অবস্থানে, অবশ্য অধস্তন হিসেবে। বুর্জোয়াদের সামাজিক অবস্থানের এই পরিবর্তন তাদের দর্শনে ছাপ ফেলেছিল।
পুঁজিবাদী উন্নয়নের পথ আর অবরুদ্ধ ছিল না। নৈরাশ্যবাদের কারণ দূরীভূত হয়েছিল। কিন্তু বিজয়লব্ধ আত্মবিশ্বাসের ফসল রূপে কোন স্বাস্থ্যকর আশাবাদ দ্বারা সেই নৈরাশ্যবাদ প্রতিস্থাপিত হয়নি। জার্মান বুর্জোয়াদের জীবন তখনও বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত সামরিক গোষ্ঠী ও ভূস্বামী অভিজাতদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। তখনও তা ছিল “দুষ্ট ও নীচ”। তাই তারা এই খারাপ চুক্তির মধ্যে থেকেই সর্বোচ্চ লাভ তুলে আনার সিদ্ধান্ত নিল। এভাবেই তাদের নির্মম অবজ্ঞাবাদ নীৎশের দর্শনে প্রকাশ পেল।
জীবন একটি ক্ষণস্থায়ী ঘটনা; অতএব, এর থেকে সর্বোচ্চ ফায়দা লুটে নেওয়া যাক। এমনকি জীবনের এই নির্মম দৃষ্টিভঙ্গি, যেখানে সবাই নিজের নিজের জন্য, যেখানে দুর্বৃত্তকেই সবকিছুর দখল নিতে দেওয়া হয়—তাকেও আধ্যাত্মিক মোড়ক দেওয়া যায়, যদি আমরা হিন্দু মানদণ্ড গ্রহণ করি: “জীবন আমাকে প্রভাবিত করছে না, আমিই জীবনের প্রভু”। আধুনিক ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের আধ্যাত্মিক গুরু বিবেকানন্দ নীৎশের প্রতিধ্বনি করেন। তিনি গর্বিতভাবে ঘোষণা করেন: “আমি মদ পান করি, মদ যেন আমাকে পান না করে”। তিনি ইউরোপীয় প্রতিক্রিয়ার এই নির্মম দার্শনিকের কাছ থেকেই শিখেছেন এমনটা নাও হতে পারে। কারণ তাঁর পবিত্র গুরুই তাঁকে এই শিক্ষা দিয়েছিলেন। অদ্ভুত ভাষায় রামকৃষ্ণ উপদেশ দিয়েছিলেন: “শূকরের মাংস খাইয়াও মন ঈশ্বরচিন্তা করিতে পারে, হবিষ্য খাইয়াও কামিনী-কাঞ্চনের দাস হইতে পারে”। অর্থাৎ, আধ্যাত্মিক সংস্কার বা ভান করেও একজন জড়বাদী ভোগসর্বস্ব জীবনযাপনের অধিকারী হতে পারেন। বিংশ শতাব্দীর এই অবতারের শিক্ষা নীৎশের নির্মম বাস্তববাদ থেকে আলাদা নয়। বস্তুত, রামকৃষ্ণের সমগ্র শিক্ষা, যা বিবেকানন্দ যুক্তিযুক্ত করেছিলেন, এই ধারায় প্রবাহিত হয়েছে—যা হিন্দুধর্মের চেতনাকে সম্পূর্ণভাবে প্রতিফলিত করে। কলিযুগে খাঁটি আধ্যাত্মিকতার উচ্চ আদর্শ বাস্তবায়নযোগ্য নয়। এখন মানুষ সংসারী জীবন যাপন করবে; এবং তা ন্যায্য যতক্ষণ তারা বৈরাগ্য ভরে, শ্রদ্ধার সাথে, উপাসনার মনোভাব নিয়ে তা করে। বাস্তবে আধ্যাত্মিক আদর্শ পরিত্যক্ত হয়। এ কখনই বাস্তব ছিল না। শেষ পর্যন্ত, এই প্রাচীন মায়া পরিত্যাগ করা হয়—বিপ্লবী সাহসিকতায় নয়, বরং ভণ্ড ধার্মিকতায়। জড়বাদী ভোগসর্বস্বতা ঈশ্বরের আশীর্বাদ পায়। কিন্তু বস্তুবাদী দর্শন তখনও নিষিদ্ধই থেকে যায়। সামাজিক উপযোগিতা হারানোর পরেও টিকে থাকা ধর্মীয় জীবনদৃষ্টি এই অসততা ও কপটতা থেকে মুক্ত হতে পারে না।
নীৎশের পুঁজিবাদী দর্শন ভারতীয় পথ অনুসরণ করে। যতক্ষণ আপনি এই আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি ধরে রাখেন যে জীবন একটি অপরাধ, মানুষের ইচ্ছা দুষ্ট ও নীচ—ততক্ষণ আপনি এই অপরাধে যত খুশি লিপ্ত হতে পারেন, আপনার আধ্যাত্মিক সত্তাকে অশুচি না করে; যতক্ষণ আপনি আপনার ইচ্ছার মালিক থাকবেন ততক্ষণ দুষ্টতা ও নীচতা আপনার প্রকৃত সত্তার পবিত্রতাকে নষ্ট করবে না। তখন আপনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন—জীবনের অধিকারলিপ্সাকে, দুর্বলকে পদদলিত ও আঘাত করার ইচ্ছাকে, লাগামহীন মুক্ত করে দিন; আপনি নিশ্চিন্তে, নৈতিকভাবে এটা করতে পারেন, কারণ জগৎ স্বভাবতই নিকৃষ্টতম, একে তার থেকে আর বেশি খারাপ করা যায় না। নীৎশে শোপেনাওয়ারের উপনিষদ-ভিত্তিক দর্শন থেকে এই সিদ্ধান্তগুলো যুক্তিযুক্তভাবে টেনে এনেছিলেন। জীবন-সংকল্পের নেতিকরণ থেকে জন্ম নিয়েছিল ক্ষমতার ইচ্ছা। জীবনের দুঃখ-কষ্টের প্রতি সহানুভূতি রূপান্তরিত হয়েছিল অবমাননায়। এভাবেই সুপারম্যান উপাসনার বিকাশ ঘটে—যাকে স্থাপিত করা হয় আধুনিক উদীয়মান শিল্পের অধিপতিদের মধ্যে।
এই সুপারম্যানেরা হলেন “মুক্ত আত্মা”, “ভালো ইউরোপীয়”—বিশ্বের টিউটনিক ত্রাণকর্তা, “আধ্যাত্মিক আর্য সংস্কৃতি”-র গর্বিত রক্ষক, যারা সভ্যতা বিস্তার মিশনের “শ্বেতাঙ্গের বোঝা” ব্রিটিশদের সাথে ভাগ করে নেওয়ার জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। নীৎশের দর্শনের তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক প্রকাশ ছিল জার্মান সাম্রাজ্যবাদের “সূর্যের নিচে জায়গা” (উপনিবেশিক সম্প্রসারণ) দাবি। ফ্যাসিবাদ হল ক্ষমতা ও লুণ্ঠনের এই একই দর্শনের নগ্নতম প্রকাশ। নীৎশীয় সুপারম্যান উপাসনা—ফ্যাসিবাদী দর্শনের এই মৌলিক মতবাদকে— সঠিকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, “এমন এক দর্শন যা বস্তুত বড় পুঁজির মহিমা কীর্তন করে এবং জনসাধারণকে আকৃষ্ট করে” (মেহরিং, “দর্শনের ইতিহাস প্রসঙ্গে”)।
এভাবেই উপনিষদের উচ্চাদর্শ থেকে জার্মান সাম্রাজ্যবাদ ও পরবর্তীতে ফ্যাসিবাদের জন্য মতাদর্শ নির্মিত হয়েছিল। এটা না ছিল বিকৃত, না ছিল অপব্যবহৃত। পার্থিব স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতার ন্যায্যতা সর্বদা যুক্তিযুক্তভাবে এসেছে এক অধিবিদ্যিক “প্রথম সত্য”-র ধারণা থেকে যা কোনো আইন মানে না। এই ধারণাভিত্তিক ভারতীয় দর্শনও জড়বাদী ভোগসর্বস্বতার মতাদর্শে পরিণত হয় যখন শ্রেণিসম্পর্ক এমনভাবে পুনর্বিন্যস্ত হয় যাতে বুর্জোয়াদের জবরদস্তি চালানোর প্রয়োজনীয় অস্ত্র জোগান দেওয়া যায়। তাদের ক্ষমতার সূর্যালোকে জায়গা দিন, আর আপনি দেখবেন আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি তার অপ্রচলিত রূপ ও পরিভাষা ঝেড়ে ফেলে নতুন সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে। বস্তুত, আমাদের এই পবিত্র আধ্যাত্মিক দর্শন উচ্চশ্রেণীর স্বার্থসিদ্ধি ছাড়া আর কিছুই করেনি। সময়ে সময়ে শাসক শ্রেণীর সামাজিক গঠন অনুযায়ী তার রূপ ও পরিভাষা পরিবর্তন করতে হয়েছে মাত্র। এমনকি আজও, “সত্য ও অহিংসা”-র ঐশ্বরিক মতবাদ সামাজিক অসন্তোষ ও রাজনৈতিক বিদ্রোহের শক্তিকে স্তব্ধ করার কাজে নিয়োজিত। সাম্রাজ্যবাদের দয়ায় পাওয়া সামান্য ক্ষমতার স্বাদ আমাদের আধ্যাত্মিক-মনা জাতীয়তাবাদীদের ফ্যাসিবাদী অনুশীলনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। যে দেশের দর্শন ফ্যাসিবাদের আদর্শিক অগ্রদূতদের অনুপ্রাণিত করেছিল সে দেশে এটা হওয়া কোন আশ্চর্য বিষয় নয়।
নীৎশের “মুক্ত আত্মারা” ঈশ্বরের “বিভূতি” লাভ করেছেন। তাই তারা স্বভাবতই “শাসক ও অধীনস্তকারী” হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট; তাদের স্বাভাবিক “অধিকার আছে মানুষ নামক জন্তুদলকে শাসন ও পদানত করার”, যে জন্তুদল “অক্ষমতা ও অবিচারের শিকার হওয়ার প্রারব্ধেই অভিশপ্ত”। মানবিক সম্পর্ক বিষয়ে এই বীভৎস দৃষ্টিভঙ্গি—যা শোপেনাওয়ারের মতবাদ ‘মানুষের সহজাত দুষ্টতা ও নীচতা’ থেকে যুক্তিসঙ্গতভাবে উদ্ভূত—নীৎশেকে একজন উগ্র সমাজতন্ত্রবিরোধিতে পরিণত করেছিল। তিনি ইতিহাসে আবির্ভূত হয়েছিলেন ফ্যাসিবাদের মার্ক্সবাদ-বিরোধী ধর্মযুদ্ধের প্রত্যক্ষ আদর্শিক অগ্রদূত হিসেবে।
ভারতার্য আধ্যাত্মিক জীবনদর্শনের একটি মৌলিক নীতি হলো—জীবনের সমস্ত দুঃখ-কষ্টকে হাসিমুখে ও নিঃস্বার্থে সহ্য করতে হবে। নীৎশে এই নীতির দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। তাই তিনি ঘোষণা করতে পেরেছিলেন যে, শ্রমিকদের অবস্থার প্রকৃত উন্নতি ঘটবে তাদেরকে শেখানো যায় দুঃখকে আনন্দের সাথে সহ্য করতে। সহজেই বোঝা যায়, নীৎশের সমাজতন্ত্র-বিরোধী প্রচারণা ছিল গান্ধীবাদেরই এক অগ্রিম ছায়া। সুতরাং, যদি গান্ধীবাদকে ধর্মীয়-নৈতিক মতবাদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়—যা প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির সারমর্ম—তাহলে বিশ্ব ইতিমধ্যেই এর আধুনিক রাজনৈতিক প্রকাশ প্রত্যক্ষ করেছে। দার্শনিক ঐতিহ্য হিসেবে গান্ধীবাদ হিটলারবাদের দিকে পরিচালিত করেছে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের এই সত্যটি মনে রাখা উচিত। ইতিহাসের যুক্তি জার্মানির মতোই ভারতের জন্যও সমানভাবে প্রযোজ্য।
ফ্যাসিবাদের আধ্যাত্মিক পিতা বিশ্বাস করতেন, ধনীদের জন্য যা অসহনীয়, দরিদ্ররা তা সহ্য করতে পারে; তাই তার মত ছিল যে শ্রমিকদের সহজেই দুঃখ সহ্য করার গুণ শেখানো যেতে পারে। গান্ধীবাদ অনুসারে, পুঁজিপতি ও শ্রমিক উভয়েই ঈশ্বরের সন্তান; এবং দরিদ্রদের তাদের ধনী ভাইদের প্রতি ঈর্ষা করা উচিত নয়। ত্যাগ ও দুঃখভোগকে গান্ধীবাদ মহৎ গুণ হিসেবে মহিমান্বিত করে। যদি এই অন্ধবিশ্বাসকে মেনে নেওয়া হয়, তাহলে এই গুণাবলী চর্চা করার জন্য যেকোনো ব্যবস্থা নেওয়াই নৈতিক ও যৌক্তিকভাবে বৈধ বলে বিবেচিত হবে। যদি কোন আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য সবকিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকা না যায় তাহলে সেই দর্শন থাকারই বা কী মানে হয়? সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত গান্ধীবাদীরা দেখাচ্ছেন যে প্রয়োজনে তাঁরা ভারতীয়দের মধ্যে এই গুণাবলী চাপিয়ে দিতে যেকোনো ব্যবস্থা নিতে প্রস্তুত—যা তাদের বক্রদর্শী দর্শন অনুযায়ী জনগণকে “ভালো মানুষ” বানাবে।
নীৎশের দর্শন, যা নগ্ন শ্রেণীশোষণকে ন্যায্যতা দেয়, হিন্দু কর্মবাদ ও ভগবদ্গীতার বাণীর সাথে আশ্চর্যরূপে মিলে যায়: “চতুর্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ” (গীতা ৪.১৩)। বর্ণপ্রথা বিভিন্ন গোষ্ঠীকে বিভিন্ন সামাজিক স্তরে স্থাপন করে। যদি এই ব্যবস্থা দৈবভাবে নির্ধারিত হয়, তবে নিম্নস্তরের লোকদেরকে চিরকাল তাদের অবস্থান মেনে নিতেই হবে। এভাবে দৈব ইচ্ছার কর্তৃত্বে সামাজিক অসমতা চিরস্থায়ী হয়। দাস চিরকাল দাসই থাকবে! শাসক শ্রেণী তার ক্ষমতা ও বিশেষাধিকার ঈশ্বরের দান হিসেবে ভোগ করবে, যা কেবল পাপীরাই কেড়ে নেওয়ার সাহস করতে পারে। গীতায় ভগবান আরও ঘোষণা করেছেন যে পৃথিবীর সমস্ত ক্ষমতা তারই শক্তির প্রকাশ। দৈব কর্তৃত্বে কেবল ব্রাহ্মণের পৌরহিত্যের বিশেষাধিকারই প্রতিষ্ঠিত নয়; অতীতে রাজা-মহারাজারাও ঈশ্বরের অবতার হিসেবে শাসন করতেন; এমনকি আজও পরজীবী জমিদার যাদের শোষণ করে সেই কৃষকদেরই “প্রাকৃতিক নেতা” বলে নিজেকে দাবি করে; এবং দেশীয় রাজারা—যারা ব্রিটিশ প্রদেশগুলোতে রিপ্রেজেন্টেটিভ গভর্নমেন্টের দাবি করে—তারাই প্রাচীনপন্থী জাতীয়তাবাদীদের সমর্থনে স্বৈরাচারী ক্ষমতা অনুশীলন করে।
“মানুষ জন্তুর দলকে”-কে অসহায় ও পদানত অবস্থায় নিক্ষেপ করার পর, তাদের জন্য নীৎশের আর কোনো সহানুভূতি অবশিষ্ট থাকে না। তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন: “প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তনে পৃথিবীতে সুখ কখনই বৃদ্ধি পাবে না; তা অর্জিত হবে বিষন্ন, দুর্বল, ধর্নাপন্ন, অভিযোগপরায়ণ মানসিকতার বিলুপ্তির মাধ্যমে”। এখানেও ফ্যাসিবাদী দর্শনের ভেতরে ভারতের আধ্যাত্মিক কণ্ঠের প্রতিধ্বনি শোনা যায়: পার্থিব বস্তু মানুষকে প্রকৃত সুখী করতে পারে না; সুখ হলো মনের একটি অবস্থা, যা বাইরের জগৎ থেকে স্বাধীন। এটি সম্পূর্ণরূপে মানসিকতার বিষয়। একজন মানুষ নিজেকে সুখী বলে কল্পনা করলেই সে সুখী হতে পারে।
আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি ভারতীয় জনতাকে শিখিয়েছে যে, তারা যে সামাজিক অসাম্য ও বৈষম্যের শিকার হন সে বিষয়ে কেউ দৃষ্টি আকর্ষণ করলে যেন তারা হাতের পাঁচ আঙুলের আকারের পার্থক্যকে তুলে ধরে। তাদের শেখানো হয়েছে যে তাদের অবস্থা ও অধীষ্ঠান তাদের যোগ্যতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাদের কেবল কঠিন কঠোর প্রারব্ধ মেনে নিতেই শেখানো হয়নি, বরং প্রতিষ্ঠিত সামাজিক ব্যবস্থাকে দৈব বিধানের প্রকাশ হিসেবে দেখতেও শেখানো হয়েছে। নীৎশেও যুক্তি দিয়েছিলেন, “যেহেতু অনেক কঠিন ও রুক্ষ কাজ সম্পাদন করতে হবে, তাই কিছু মানুষকে এমন অবস্থায় রাখতে হবে যাতে তারা ওই ধরনের কাজের জন্যই উপযুক্ত হয়”। ভারতের বিশেষ জিনিয়াসদের সৃষ্ট বর্ণপ্রথা এই নীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। ফ্যাসিবাদের দার্শনিক জাতবর্ণের আর্য চেতনা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে প্রস্তাব করেন যে, “এশিয়া ও আফ্রিকার বর্বরদের আমদানি করা যেতে পারে, যাতে অসভ্য বিশ্ব ক্রমাগত সভ্য বিশ্বের সেবায় নিয়োজিত থাকে”। কেনই বা নয়? আর্য ব্রাহ্মণরা কি তাদের মিত্র যোদ্ধাদের সহায়তায় ভারতের আদিবাসী জনগণকে শূদ্রের চিরস্থায়ী দাসত্বে নিক্ষেপ করেনি? আপনার মুদ্রাতেই আপনার প্রাপ্য যখন কেউ শোধ করে তখন কি তার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো আপনার শোভা পায়? ‘সেবার পূজা’ ভারতের আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির একটি বৈশিষ্ট্য। এটি গান্ধীবাদের একটি ডগমা, এবং গান্ধীবাদ হলো প্রাচীনপন্থী জাতীয়তাবাদের মতাদর্শ। যেহেতু সেবাকে অধিবিদ্যক গুণে ভূষিত করা হয়, তাই দাসত্ব সম্মানের মর্যাদায় স্থাপিত হয়—এবং এর এক্তিয়ারের উপর যৌক্তিকভাবে কোনো সীমা আরোপ করা যায় না। ঈশ্বরের কৃপা লাভ করতে চাইলে আপনাকে সেবা করতে হবে, যে কৃপা আপনার থেকে অধিক সৌভাগ্যবান শ্বেতাঙ্গ সন্তানদের মাধ্যমে কার্যকর হয়।
নীৎশে নৈতিক ভালো-মন্দের ধারণার ঊর্ধ্বে “মুক্ত আত্মাদের” স্থান দিয়েছেন। কারণ খ্রিস্টধর্মের আদি যুগ থেকেই এইসব নীতিনৈতিকতা “মানুষ জন্তুদল”-এর অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে “মুক্ত আত্মাদের” বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে। নীৎসের অতিমানবের নৈতিকতা সংক্রান্ত রচনা ফ্যাসিবাদের বাইবেল-এ পরিণত হয়েছে। এখানে কিছু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উদ্ধৃতি দেওয়া হলো:
“ধর্ম হল শক্তিশালী, মুক্ত, শাসন করার জন্য নির্ধারিত ও সেই লক্ষ্যে তৈরি ব্যক্তিদের হাতের একটি অস্ত্র, যাদের বুদ্ধিমত্তা ও কলাকৌশল মিলে একটি শাসকজাতি তৈরি করে। তাদের কাছে, ধর্ম হল প্রতিরোধ কাটিয়ে উঠে শাসন করার অন্যতম হাতিয়ার। ধর্ম পদানতদের শাসকদের সাথে বেঁধে রাখে, তাদের মধ্যে সেই গোপন, অন্তর্নিহিত বিবেককে দমিয়ে দেয় যে বিবেক শাসকদের প্রতি অবাধ্য হতে প্ররোচিত করে”।
“যখন ধর্ম সার্বভৌম ক্ষমতা দখল করতে চায়—দার্শনিকদের হাতে প্রজনন ও লালন-পালনের অন্য সমস্ত মাধ্যমের মত একটি মাধ্যম হওয়ার বদলে ধর্ম নিজেই যখন চূড়ান্ত লক্ষ্য হয়ে ওঠে—তখনই এর ভয়াবহ পরিণতি হয়... একটি ভালো ও সুস্থ অভিজাততন্ত্রের মূল গুণ হলো তা নিশঙ্ক চিত্তে সেই মানুষগুলির বলিদান গ্রহণ করতে পারে যাদেরকে সে নিপীড়িত করে মানুষের স্তর থেকে নামিয়ে দাসত্বে, শ্রমের যন্ত্রে পরিণত করবে”।
“আত্মকেন্দ্রিকতা উচ্চতর আত্মার স্ব-ভাব। আত্মকেন্দ্রিকতা বলতে আমি এই দৃঢ় বিশ্বাসকে বোঝাই যে, অন্যরা স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মতো মানুষদের অধীনস্ত হবে, আমাদের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করবে। এই ধরনের আত্মকেন্দ্রিকতা উচ্চতর আত্মাদের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। এতে কোনো কঠোরতা, জবরদস্তি বা স্বেচ্ছাচারিতার অনুভূতি নেই। বরং এটি হল জগতের মৌলিক নিয়ম। এর একটা নাম দিতে হলে একে আমি ‘ধর্মপরায়ণতা’ বলব”।
(“বিয়োন্ড গুড অ্যান্ড এভিল”)
নীৎশে ফ্যাসিবাদের সমস্ত মৌলিক নীতি ঘোষণা করলেও, এই রক্তাক্ত আন্দোলনের আদর্শিকরা ছিলেন বার্গসন বা তার শিষ্য জর্জ সোরেলের অনুসারী। এই আধ্যাত্মিক পরম্পরা বোঝার জন্য মনে রাখতে হবে যে বার্গসন বস্তুর বাস্তবতাকে তার অধিবিদ্যিক মতবাদের অধীনস্থ একটি সহায়ক বিভাগ হিসেবে মেলানোর চেষ্টা করেছিলেন। তিনি বস্তুবাদী দর্শন প্রত্যাখ্যান করলেও জড়বাদী ভোগসর্বস্বতাকে আধ্যাত্মিক সুরক্ষা দিয়েছিলেন। বার্গসনের এই দুগলা দর্শন ফ্যাসিবাদের আদর্শিক ভিত্তি তৈরি করে।
অতীতে এই দ্বিচারী দর্শনের রাজনৈতিক প্রকাশ ছিল সামন্ততান্ত্রিক রাজতন্ত্রের স্বৈরাচারে; আজ, এটি সংসদীয় গণতন্ত্রের বিলোপ ও ফ্যাসিবাদী একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় প্রকাশ পাচ্ছে। দুগলা দর্শন ধর্মীয় মৌলবাদের পুনরুত্থান ঘটায়—এক মনুষ্যসদৃশ ঈশ্বরের আদিম ধারণা, এবং তার দ্বারা বিশ্ব সৃষ্টি হওয়ার মতবাদ। এই আদিম ধর্মীয় ধারণা, আবার, পার্থিব স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতার আদর্শিক প্রতিফলন, যা আজ ফ্যাসিবাদী একনায়কতন্ত্রের রূপ নিতে বাধ্য—যা আদতে বুর্জোয়া শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র। একসময় বিপ্লবী শ্রেণি হিসেবে পুঁজিপতিরা রাজাদের ঐশ্বরিক অধিকারবাদের বিরোধিতা করেছিল; আর আজ, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি হিসেবে তারা সেই একই কল্পিত অধিকারের আশ্রয় নিচ্ছে, যেগুলোর বিরুদ্ধে তারা এককালে সংগ্রাম করেছিল সেই রাজনৈতিক স্বৈরশাসন, নাগরিক জবরদস্তি, অর্থনৈতিক ধ্বংসযজ্ঞ ও সামাজিক বর্বরতার সমস্ত রকম ব্যবস্থার মাধ্যমেই এখন তারা ক্ষমতায় টিকে থাকতে বদ্ধপরিকর।
স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা ও সীমাহীন লালসার দার্শনিক-নৈতিক বৈধতা সুপারম্যান উপাসনার ভিত্তি তৈরি করে—এ এমন এক পূজা যা অবধারিতভাবে নিষ্ঠুরতা, হিংসা, জবরদস্তি, দমন-পীড়ন—সংক্ষেপে ফ্যাসিবাদের সমস্ত বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে। একজন মুসোলিনি বা হিটলার হলেন এই সুপারম্যান উপাসনার মূর্ত প্রতীক। একজন সুপারম্যান হিসেবে তিনি আধ্যাত্মিক ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব করেন এবং পার্থিব বিষয়ে মানুষের স্বাধীনতা, অধিকার, ন্যায়বিচার বা নৈতিকতার কোন ধারণায় তিনি বাঁধা নন। তাই বিশ্বের এই “ত্রাতা” বা “পুনর্স্রষ্টা” মহোদয়েরা লাজলজ্জাহীনভাবে ঘোষণা করেন যে স্বাধীনতা মোটেই নাগরিকত্বের অপরিহার্য উপাদান নয়; ব্যক্তি নাগরিক পরম ক্ষমতার মধ্যেই, অর্থাৎ রাষ্ট্রের ইচ্ছাচারের মধ্যে, প্রকৃত স্বাধীনতা উপভোগ করে। এবং সুপারম্যান হল অষ্টপদী ক্ষমতার ব্যক্তিরূপ। ধনিকশ্রেণির সেবায় নিয়োজিত আধুনিক ডিক্টেটর অতীতের সামন্ত প্রভুদের নকল করে ঘোষণা করে “লে তা সে মোয়া” –আমিই রাষ্ট্র, এবং তিনি প্রায় একইরকম দৈব অধিকার প্রাপ্তির দাবি করেন। প্রুশিয়ার প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণের সময় গোয়েরিং নিজেকে “প্রুশিয়ার রাজাদের প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী” হিসেবে ঘোষণা করেছিল যে রাজারা ছিলেন “সর্বোচ্চ বিশপ”। সেই সামন্ততান্ত্রিক রাজারা শাসন করতেন “ঈশ্বরদত্ত অধিকার” নিয়ে; আর তাঁদের সরাসরি উত্তরসূরি হিসেবে ফ্যাসিস্ট একনায়কও সেই অধিকার দাবি করে।
হিটলারের মতে, রাষ্ট্রই সব, নাগরিকের কোনো অধিকার নেই—তাকে রাষ্ট্রের স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতার বাধ্যতামূলক বাহক হতে হবে, রাষ্ট্র যে কোনো সময় তার জীবন কেড়ে নেওয়ার অধিকারী। পরম ক্ষমতার এই মধ্যযুগীয় আধ্যাত্মবাদী রাজনৈতিক দর্শনের যৌক্তিক পরিণতি হল ফ্যাসিবাদী যুদ্ধোন্মাদনা। পরম একক শাসকের অহঙ্কার ও মর্জি যখন খুশি জনগণকে ডাক দিতে পারে মোলোখের বেদীতলে আত্মবলি দিতে। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে এটা করতে হবে, অথবা করতে হবে দেশপ্রেমিক কর্তব্য হিসেবে, তার পেছনে দেশ বা জাতির কোনও স্বার্থ প্রকৃতই থাক বা না থাক। ফ্যাসিবাদী রাজনৈতিক দর্শনের এই বাস্তব তাৎপর্য ভন পাপেন নৃশংস আন্তরিকতায় ব্যক্ত করেন, ভন পাপেন হলেন তিনি যিনি জার্মান বুর্জোয়াদের রাজি করিয়েছিলেন হিটলারকে ক্ষমতায় বসাতে। তিনি বলেন, “নারীদের কাজ হলো সৈন্য জন্ম দেওয়া। জীবনের চেয়ে গৌরবময় মৃত্যু, যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেওয়ার থেকে গৌরবময় জীবনাদর্শ আর কিছুই হতে পারে না”। এই রক্তলোলুপ উপাসনাচার মাতৃত্বকে হেয় করে, তাই বস্তুবাদী দর্শনের অনুসারীরা এর বিরোধিতা করে। কিন্তু ভারতীয় গোঁড়া জাতীয়তাবাদীদের কাছে এটি মোটেই অপরিচিত নয়—এ হল ক্ষাত্র ধর্মেরই প্রতিধ্বনি মাত্র।
“ন্যাশনাল সোশ্যালিজম” বা হিটলার হলো মধ্যযুগীয় প্রুশিয়ানিজমের ভয়ঙ্কর প্রেতাত্মা—যাকে ভারত আজও ক্ষত্রিয় ধর্মের গৌরব হিসেবে প্রচার করে। জনসাধারণ যখন সামন্তপ্রভুর দাসত্বে বাঁধা ছিল তখন তাদের এই “ধর্ম” শেখানো হয়েছিল। সামন্তপ্রভুর শ্যাটেল, তা সে ভারতীয় হোক বা প্রুশিয়, লাঙল ছেড়ে তরবারি ধরে বেরিয়ে পড়তে হত কৃষিকাজ ফেলে। এইভাবে জীবিকা বদলে নেওয়া যেহেতু তাদের নিজেদের ইচ্ছায় হত না, বরং তা হত প্রভুর স্বার্থে (সেসব দিনে লুন্ঠনযুদ্ধ শান্তিপূর্ণ কৃষিকাজের চেয়ে লাভজনক ছিল), তাই ক্ষাত্র বীরত্বের আদর্শ জনমানসে প্রোথিত করা হয়েছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেওয়ার আদর্শকে মহাকাব্যে মহিমান্বিত করা হয়েছিল, কিংবদন্তি গল্পগাথার মাধ্যমে প্রচার করা হয়েছিল। বাস্তবত মহাকাব্য লেখাই হয়েছিল জনগণের মধ্যে বীরত্বের অদম্য আবেগ উৎপন্ন করতে; এবং প্রুশিয় জাতীয়তাবাদের মতই ক্ষাত্র্য বীরত্বের বাস্তব মূল্য ছিল সামন্ত প্রভুর প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতে। কখনো কখনো প্রভুও সেই বীরত্বের পালটা ঝাপটে ঝাড় খেলে সেটাও ছিল খেলারই অঙ্গ। জুয়া ও এডভেঞ্চারের ক্ষেত্রে লাভ যেমন আছে তেমনই ঝুঁকিও তো আছে।
“আমাদের সমাধিলিপিতে লেখা হোক: আমরা নির্মম ছিলাম, আমরা নির্দয় ছিলাম—কিন্তু আমরা ভালো জার্মান ছিলাম” (হিটলার)। সুপারম্যান উপাসনাচারে হিটলারবাদের আরেক হিরো নির্মম অবজ্ঞায় চিৎকার করে ওঠেন, “নিজের আইন নিজেই ভাঙার সাহস রাষ্ট্রের থাকতে হবে” (গোয়েবলস)। পৃথিবীতে এই ধরনের স্বেচ্ছাচারী, সীমাহীন ক্ষমতার নৈতিক বৈধতা কেবল একটি অপদর্শন থেকে আসতে পারে—এক অতিপ্রাকৃত আধ্যাত্মিক শক্তির ধারণা, এক ঐশ্বরিক ইচ্ছা যা প্রকৃতির নিয়মে আবদ্ধ নয় কিন্তু মানুষের ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করে। এটিই ফ্যাসিবাদের দর্শন, যার সারমর্ম হলো সুপারম্যানের পূজা। এটি এমন একটি দর্শন যা বেদান্ত ও দ্বৈতবাদী হিন্দু দর্শনের সাথে আশ্চর্যরকম মিলে যায়—যেখানে বিশ্বকে ঈশ্বরের লীলা হিসেবে দেখা হয়। এই সাদৃশ্যের কারণে, জার্মান ফ্যাসিবাদের মতাদর্শিকরা —স্পেংলার, স্প্যান, কাইজারলিং প্রমুখ— প্রাচ্যের আধ্যাত্মিক বার্তাকে পাশ্চাত্যের ত্রাতা হিসেবে প্রশংসা করেছেন।
ফ্যাসিবাদের দর্শন মূলত ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার থেকে অভিন্ন। যদি ফ্যাসিবাদ কখনও পুঁজিবাদী সভ্যতাকে রক্ষা করতে পারে, তবে ভারতের আত্মা তার প্রতিফলিত গৌরব দাবি করতে পারে। কিন্তু তা বস্তুবাদ থেকে বিশ্বকে মুক্ত করা হবে না। বরং তা হবে স্থুল বস্তুবাদী ভোগসর্বস্বতাকে মানুষের উপর তার আধিপত্য বজায় রাখতে সাহায্য করা। আমরা কি এমন একটি দর্শন নিয়ে বড়াই করতে পারি যা আমাদের এহেন গৌরব এনে দিতে পারে? বরং, এতকাল ধরে একটি মিথ্যা আদর্শ লালন করে আসার এই গৌরব কি আমাদেরকে লজ্জিত করবে না? এগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। যারা নিছক পূর্বসংস্কারে আচ্ছন্ন নন, বা যারা সচেতনভাবে প্রতিক্রিয়াশীল অর্থাৎ সম্ভাব্য ফ্যাসিস্ট নন, সেইসব ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের এগুলি গভীরভাবে ভাবা উচিত।