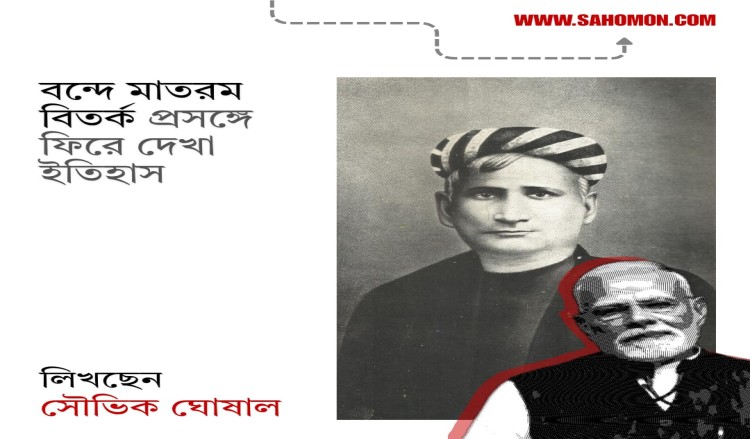১৮৮২ সালে প্রকাশিত হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাস আর সেখানেই ছিল বন্দেমাতরম গানটি। তবে আনন্দমঠের অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রকাশিত হলেও এই গানটি লেখা হয়েছিল আরো বছর পাঁচেক আগে, সম্ভবত ১৮৭৫ বা ১৮৭৬ সালে। সেই নিরিখে এই গানটির বয়েস এখন দেড়শ বছর। ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাস যাঁদের কেন্দ্রে রেখে লেখা, সেই সন্তান দলের কন্ঠে গানটি উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়েছিল। উপন্যাস প্রকাশের পরেই গানটি এবং বন্দেমাতরম ধ্বনিটি প্রবল জনপ্রিয় হয়। ১৮৯৩ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর তিন বছরের মধ্যেই এই গান উঠে আসে রাজনৈতিক সম্মেলনের মঞ্চে। ১৮৯৬ সালে জাতীয় কংগ্রেসের এক সম্মেলনে এই গানটি পরিবেশন করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শ্রী অরবিন্দ ঘোষ ছিলেন তখনকার অন্যতম প্রধান রাজনীতিবিদ। তিনি এই গানটিকে ‘বঙ্গদেশের জাতীয় সঙ্গীত’ নামে অভিহিত করেন। জাতীয় কংগ্রেস ও সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন – দুই ধারার রাজনীতির লোকেরাই এই গানটিকে তাঁদের নিজস্ব সঙ্গীত হিসেবে ব্যবহার করতে থাকেন। কিন্তু স্বাধীনতার পর এই গানটির বদলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জনগণমনকে জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা দেওয়া হয়। বন্দেমাতরমকে বলা হয় জাতীয় স্তোত্র। তবে আনন্দমঠ উপন্যাসে থাকা গানের মূল পাঠটিকে জাতীয় স্তোত্র না করে তার প্রথম অংশটিকে কেবল জাতীয় স্তোত্র হিসেবে বেছে নেওয়া হয়। জাতীয় স্তোত্র হিসেবে গৃহীত অংশটি হল –
বন্দে মাতরম্
সুজলাং সুফলাং
মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং
মাতরম্।
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীম্,
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।
আর এর বাইরে গানের যে অংশটি মূল উপন্যাসে ছিল, কিন্তু জাতীয় স্তোত্রে এল না, সেই অংশটি হল –
সপ্তকোটি কণ্ঠ কলকল নিনাদ করালে,
দ্বিসপ্তকোটী ভুজৈ র্ধৃত খর-করবালে,
অবলা কেন মা এত বলে৷৷
বহুবলধারিণীং
নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং
মাতরম্৷৷
তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে৷৷
বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে॥
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমল-দলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী
নমামি ত্বাং
নমামি কমলাম্
অমলাং অতুলাম্
সুজলাং সুফলাম্
মাতরম্॥
বন্দে মাতরম্
শ্যামলাং সরলাম্
সুস্মিতাং ভূষিতাম্
ধরণীং ভরণীম্
মাতরম্॥
সম্প্রতি এই বর্জনের জন্য সেকালের কংগ্রেস নেতৃত্বকে সমালোচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বলেছেন ১৯৩৭ সালেই জাতীয় কংগ্রেস তাঁদের পক্ষ থেকে এই গানের বড় অংশকে বাদ দিয়ে দিয়েছিল। মোদি সেইসঙ্গে এও বলেছেন যে এই বর্জনের সূত্র ধরেই বিভাজনের বীজ মাথাচাড়া দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিল এবং পরবর্তীকালে দেশভাগের দিকে ইতিহাসকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। বন্দেমাতরম গানের দেড়শো বছর প্রসঙ্গে নরেন্দ্র মোদির বক্তৃতায় এই সমালোচনা উঠে আসার পরেই নতুন করে দেখা দিয়েছে বিতর্ক। এই বিতর্কের তাৎপর্যটি বুঝতে হলে আমাদের সেই সময়ের ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকাতে হবে।
১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর অনেকগুলো প্রদেশে কংগ্রেসের সরকার তৈরি হয়। বিধানসভার অধিবেশনগুলোতে যখন বন্দে মাতরম গানটি গাওয়া হত, তখন অনেক মুসলিম সদস্য তাতে তাঁদের অস্বস্তি ও আপত্তি জানিয়েছিলেন। গানটিতে যেভাবে পৌত্তলিকতা এসেছে তা তাঁদের ধর্মানুভূতিতে আঘাত করছে, এরকম একটা কথাই তাঁরা তুলেছিলেন। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বিষয়টি নিয়ে তখন আলাপ আলোচনা শুরু হল৷ পুরো ‘বন্দে মাতরম’ গানটিকে বাতিল করা কংগ্রেসের পক্ষে সম্ভব ছিল না, কারণ এই গানটি স্বাধীনতা আন্দোলনের বীজমন্ত্র হয়ে উঠেছিল। আবার ধর্মনিরপেক্ষ ভাবমূর্তি বজায় রাখতে হলে মুসলিম সম্প্রদায়ের আপত্তিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করাও তাঁদের পক্ষে কঠিন হচ্ছিল। মধ্যপন্থা হিসেবে তখন গানটির প্রথম অংশটি রেখে বাকী অংশটি, যেখানে দেবদেবীর প্রসঙ্গ ছিল, তা বাদ দিয়ে সরকারী অনুষ্ঠান ও বিধানসভার অধিবেশনে বন্দে মাতরম গাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই সিদ্ধান্ত ওয়ার্কিং কমিটিতে পাশ করানোর আগে তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি জহরললাল নেহরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে এসে এই বিষয়ে তাঁর মতামত চান। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য একই সময়ে সুভাষচন্দ্র বসু, তখন যিনি ওয়ার্কিং কমিটির একমাত্র বাঙালি সদস্য, একই বিষয়ে মতামত চেয়ে রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লেখেন। সুভাষচন্দ্রের চিঠির ভাষা থেকে মনে হয় তিনি বন্দে মাতরম এর ওপর কাঁচি চালিয়ে তার অঙ্গচ্ছেদের বিপক্ষেই ছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মনে করলেন বন্দে মাতরম এর প্রথম অংশটি গাইলেই যথেষ্ট৷ লিখিতভাবেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর মত প্রকাশ করেন। এই গানে দেশকে দেবী হিসেবে কল্পনা যে মুসলিমদের অনুভূতিতে আঘাত আনতে পারে, এটা রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টভাবে লেখেন। রবীন্দ্রনাথের কথার সূত্র ধরে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বন্দেমাতরম এর প্রথম অংশকে সরকারী অনুষ্ঠানে গাওয়ার জন্য বেছে নিল। ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবের বয়ান সম্ভবত সভাপতি নেহরু নিজেই লিখেছিলেন।
শেষপর্যন্ত কোনও প্রচেষ্টা বা আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়েই অবশ্য দেশভাগ আটকানো যায় নি। হিন্দু মুসলিম দাঙ্গার রক্ত ও শবের ওপর দাঁড়িয়ে বিভাজনের দিকেই গেল ভারত ভূখণ্ড। তৈরি হল পাকিস্তান। পাকিস্তান কার্যত ইসলামিক দেশে পরিণত হলেও ভারতকে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ধর্মনিরপেক্ষ রাখতেই সচেষ্ট হলেন। স্বাধীনতা ও দেশভাগের পরও তাই বন্দেমাতরমকে জাতীয় সঙ্গীত করা হয় নি, বরং গানটি ক্রমশ পার্শ্বিক ভূমিকায় সরে গেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জনগণমনই হয়ে উঠেছে ভারতের জাতীয় সঙ্গীত। দেশভাগের উত্তপ্ত প্রেক্ষাপটে এই নিয়ে অবশ্যই অনেক বিতর্ক হয়েছে। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে নিউইয়র্কে আয়োজিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের এক অধিবেশনের সাধারণ সভায় ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে বাদ্যযন্ত্রে জনগণমন গানটি বাজানো হয়েছিল। কেন জনগণমন বাজানো হল এবং বন্দে মাতরম্ বাদ গেল তাই নিয়ে বিতর্ক উঠলে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু বলেন যে সেখানকার যন্ত্রে অন্য কোনও গান না থাকায় এই ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। এরপর স্বাধীন ভারতের সংবিধান সভা গণ পরিষদ জাতীয় সংগীত নির্ধারণের জন্য একটি কমিটি তৈরি করে। গণ পরিষদ কর্তৃক গঠিত ‘জাতীয় সংগীত নির্ধারক কমিটি’ বলেছিলেন জনগণমন এবং বন্দে মাতরম উভয়কেই জাতীয় সংগীত হিসেবে স্বীকার করা হবে। বাদ্যযন্ত্রে বাজবে জনগণমন এবং কন্ঠে গাওয়া হবে বন্দে মাতরম।
১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর গণপরিষদ বা কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি ভারতের সংবিধান রচনা সম্পূর্ণ করে তা জাতিকে উপহার দেন। এর পরে গণপরিষদের শেষ অধিবেশন বসে ১৯৫০ সালের ২৪ জানুয়ারি। সেখানে সেইদিন যখন সই সাবুদের পালা চলছে তখন দেখা যায় গণ পরিষদে জাতীয় সংগীত বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নি। জাতীয় সংগীত নির্ধারক কমিটির সুপারিশের বিষয়টি অনেকদিন ধরেই আলোচনার অপেক্ষায় ছিল, কিন্তু আলোচনা করা হয়ে ওঠে নি। সেদিন আর আলোচনার সময় ছিল না। তখন সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ ‘জাতীয় সংগীত’ সম্পর্কে একটা বিবৃতি দেন। সেই বিবৃতিতে তিনি বলেন জনগণমন হবে ভারতের রাষ্ট্রীয় সঙ্গীত, আর বন্দেমাতরমও সমভাবে সম্মানিত হবে এবং জনগণমনের সমমর্যাদা পাবে। ক্রমশ দেখা গেল জনগণমন ই কার্যত জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে সর্বত্র বাজতে লাগল, সব জায়গায় গাওয়া হতে থাকল। বন্দে মাতরম ধীরে ধীরে গৌণ হয়ে গেল।
পরিশিষ্ট – ১
বন্দে মাতরম বিতর্কে রবীন্দ্রনাথকে লেখা সুভাষচন্দ্রের চিঠির বয়ান -
পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু -
আপনার বর্তমান শারীরিক অবস্থায় আপনাকে বিরক্ত করা অত্যন্ত অন্যায়, কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনীয় কারণে আপনার উপদেশের জন্য লিখিতে বাধ্য হইতেছি। এর সঙ্গে পণ্ডিত জহরলালজীর একখানি চিঠি পাঠাইতেছি। তাহা হইতে দেখিবেন যে কংগ্রেস মহলে “বন্দে মাতরম্” গানের বিষয়ে আলোচনা চলিতেছে। ২৬ তারিখে Congress Working Committee–র যে সভা কলকাতায় বসিবে, সেখানে এ বিষয়ে আলোচনা হইবে। হয়ত উক্ত কমিটি এই গান বর্জনের প্রস্তাব গ্রহণ করিবে। এ বিষয়ে আপনার মতামত আমি জানি না এবং জানিবার জন্য এই পত্র লিখিতেছি। বাঙ্গলা দেশে এবং বাঙ্গলার বাহিরে হিন্দু সমাজে, খুব চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে এবং বহু বন্ধুর অনুরোধে আপনার উপদেশ পাইবার জন্য এই পত্র লিখিতেছি।
৯ অক্টোবরের “Comrade” পত্রিকায় বিশ্বভারতীর শ্রীযুক্ত কে. আর. কৃপালনীর এক প্রবন্ধ পাঠ করিলাম। তাহাতে শ্রীযুক্ত কৃপালনী বিশ্বভারতী পত্রিকার সম্পাদক বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি “বন্দে মাতরম” গানের বিরুদ্ধেই লিখিয়াছেন। তাহার মত বিশ্বভারতীর মত কি না তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।
আপনার যদি এই মত হয় যে “বন্দে মাতরম” গানের বর্তমান মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা উচিত তাহা হইলে আপনি যদি পণ্ডিত জহরলাল ও মহাত্মা গান্ধীকে এ বিষয়ে লেখেন তাহা হইলে খুব ভালো হয়। মহাত্মাজীর কাছে আপনার কথার কতটা মূল্য আছে তাহা আপনি নিশ্চয়ই জানেন। জহরলালজী বোধ হয় কলকাতায় আসিবার পথে আপনার সহিত দেখা করিবেন - অতএব আপনি ইচ্ছা করিলে এ বিষয়ে তাহাকে নিজেই বলিতে পারেন। মহাত্মাজীকে কিন্তু লেখাই ভাল। উনি বোধ হয় ২৬শে তারিখে কলকাতায় পৌছিবেন এবং ১নং Woodburn Park-এ থাকিবেন।
সতত আপনাকে স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য আমরা প্রার্থনা করি। আমার বিজয়ার আন্তরিক প্রণাম আপনি গ্রহণ করিবেন। ইতি -
বিনীত
শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু
পরিশিষ্ট – ২
বন্দে মাতরম বিতর্কে রবীন্দ্রনাথের লিখিত বয়ান -
An unfortunate controversy is raging round the question of suitability of ‘Bande Mataram’ as national song. In offering my own opinion about it I am reminded that the privilege of originally setting its first stanza to the tune was mine when the author was still alive and I was the first person to sing it before a gathering of the Calcutta Congress. To me the spirit of tenderness and devotion expressed in its first portion, the emphasis it gave to beautiful and beneficient aspects of our motherland made special appeal so much so that I found no difficulty in dissociating it from the rest of the poem and from those portions of the book of which it is a part, with all sentiments of which, brought up as I was in the monotheistic ideals of my father, I could have no sympathy.
It first caught on as an appropriate national anthem at the poignant period of our strenuous struggle for asserting the people’s will against the decree of separation hurled upon our province by the ruling power. The subsequent developments during which ‘Bande Mataram’ became a national slogan cannot, in view of the stupendous sacrifices of some of the best of our youths, be lightly ignored at a moment when it has once again become necessary to give expression to our triumphant confidence in the victory of our cause.
I freely concede that the whole of Bankim’s ‘Bande Mataram’ poem read together with its context is liable to be interpreted in ways that might wound Moslem susceptibilities, but a national song though derived from it which has spontaneously come to consist only of the first two stanzas of the original poem, need not remind us every time of the whole of it, much less of the story with which it was accidentally associated. It has acquired a separate individuality and an inspiring significance of its own in which I see nothing to offend any sect or community.
পরিশিষ্ট – ৩
কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির গৃহীত প্রস্তাব, যেটি সম্ভবত তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি জহরলাল নিজেই লিখেছিলেন, তার বয়ানটি ছিল -
...The song and words ‘Bande Mataram’ were considered seditious by the British Government and were sought to be suppressed by violence and intimidation. At a famous session of the Bengal Provincial Conference held in Barisal in April 1906, under the Presidentship of Shri A. Rasul, a brutal lathi charge was made by the police on the delegates and volunteers and the ‘Bande Mataram’ badges worn by them were violently torn off. Some delegates were beaten so severely as they cried ‘Bande Mataram’ that they fell down senseless. Since then, during the past thirty years, innumerable instances of sacrifice and suffering all over the country have been associated with ‘Bande Mataram’ and men and women have not hesitated to face death even with that cry on their lips. The song and the words thus became symbols of national resistance to British imperialism in Bengal especially, and generally, in other parts of India. The words ‘Bande Mataram’ became a slogan of power which inspired our people, and a greeting which ever remind us of our struggle for national freedom.
...
The Working Committee feel that past associations, with their long record of suffering for the cause, as well as popular usage, have made the first two stanzas of this song a living and inseparable part of our national movement and as such they must command our affection and respect. There is nothing in these stanzas to which any one can take exception. The other stanzas of the song are little known and hardly ever sung. They contain certain allusions and a religious ideology which may not be in keeping with the ideology of other religious groups in India. The Committee recognise the validity of the objection raised by Muslim friends to certain parts of the song. While the Committee have taken note of such objection in so far as it has intrinsic value the Committee wish to point out that the modern evolution of the use of the song a part of National life is of infinitely greater importance than its setting in a historical novel before the national movement had taken shape. Taking all things into consideration therefore the Committee recommend that wherever the Bande Mataram is sung at national gatherings only the first two stanzas should be sung, with perfect freedom to the organisers to sing any other song of an unobjectionable character, in addition to, or in the place of, the Bande Mataram song.