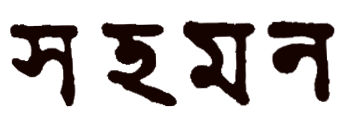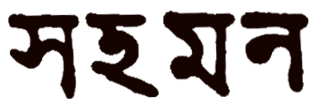নটিলাসের সমুদ্রযাত্রার কথা আমি প্রথম শুনি গোপালের কাছ থেকে। জাহাজের সেই ডুব দেওয়া। সমুদ্রের ঢেউ। জলোচ্ছ্বাস। জলতলের গভীর সেই নির্জনতা। গুড়গুড় ধ্বনি। ওর বলার কায়দায় পেরিস্কোপে চোখ রাখা গোপন এক একাকিত্ব কিন্তু ফুটে উঠত চমৎকার।
খেলা শেষ হলেই বাঁ-দিকের গোলপোস্টের কাছে জড়ো হতাম আমরা। গোলপোস্ট মানে সুপুরি গাছের টুকরো, নারকেল দড়ির গিঁট। আমগাছের ডাল আর পাতায় তখন একটানা কিচিরমিচির— ঘরে ফিরে আসতে থাকা পাখিরা। পূর্ণিমা থাকলে সন্ধের পরপরই ডালপাতার ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ত আকাশের ছেঁড়া ছেঁড়া সেই হালকা হলুদ। ধুলো মাখা রবারের বলটা তখন হয়তো সেন্টার করার জায়গাতেই। আসলে খেলা শেষ করার কিছুক্ষণ পর পর্যন্ত চলত গোল খাওয়া বা মিস করা নিয়ে দোষারোপের পালা। মন্টুর সঙ্গে রতনের মারপিট তো ছিল একেবারে রোজকার ব্যাপার।
গোপাল এসে হাজির হত একেবারে শেষ দিকে। মানে খেলার উত্তেজনা যখন তুঙ্গে। মানে রেজাল্ট হয়তো ছয়-পাঁচ কি তিন-দুই। বয়সের দিক দিয়ে ও হয়তো তখন আমাদের দ্বিগুণ নিতাইদাদের বয়সীই। ঢ্যাঙা টাইপের, হাঁটত একটু খুঁড়িয়ে। পরনের জামা আর প্যান্টটাকে কোনও দিন পাল্টাতে দেখেছি বলেও মনে পড়ে না। এখানে ওখানে সুতো বের হওয়া, কোঁচকানো। মাঠে এসেই বাঁ দিকের গোলপোস্টের পাশে বসে পড়ত। বিড়ি ধরাত একটা। এমনকী খেলা শেষ হওয়ার পরেও ভাবান্তর দেখা যেত না কোনও। বড়জোর মন্টু আর রতনের ঝগড়াটা মাত্রাছাড়া হলে ঠান্ডা গলায় জানতে চাইত, কী হয়েছে রে?
আমাদের তখন ফাইভ-সিক্স। হাফপ্যান্ট। বাজার থেকে কিনে আনা প্যান্টে সেফটিপিন আটকে দড়ি ভরতে হত। দড়ি-গোঁজা সেফটিপিন প্যান্টের সেই সুড়ঙ্গে ঢুকিয়ে সুড়ঙ্গের কাপড়ের সেই ভাঁজ করা আর ভাঁজ খোলার কথা মনে পড়ে। সেফটিপিন একসময় কোমরের পুরোটা ঘুরে একেবারে শুরুর জায়গার মুখোমুখি এসে হাজির হত।
বয়সে দ্বিগুণ হওয়া সত্ত্বেও গোপালকে নাম ধরেই ডাকতাম আমরা। পাড়ার ছোত-বড় সবার কাছেই ও ছিল ‘গোপাইল্যা’।
ছোটমামার বাড়িতে তখন ছোট বলতে স্রেফ আমিই। কোনও এক ফ্যাক্টরিতে কাজ করত ছোটমামা। নীল রঙের শার্ট আর খাকি ফুলপ্যান্ট ছিল একটা। ডিউটি যাওয়ার বাঁধা পোশাক। সকালের ভোঁ পড়ার আগেই ঘুম থেকে উঠে পড়ত হত আমাকে। বই নিয়ে বসতে হত। আর পড়তে হত চিৎকার করে— সবাইকে শুনিয়েই, যেন সবাই ভাল ছেলে বলে ভাবতে পারে আমাকে। যেন পাড়ার আর পাঁচজনকে ছোটমামা বলতে পারে, টুকুন তো আর সবার মতো নয়। অন্তত পাঁচ-সাত বাড়ি দূর থেকে পড়া শোনা যেত তখন। ‘এসেছে শরত হিমের পরশ... ।’
স্টেশন থেকে কলোনির মুখ দিয়ে বি টি রোডের দিকে চলে যাওয়া রাস্তাটিকে বলা হত ওল্ড স্টেশন রোড। দূরের স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়ার শব্দ হত খুব। ঝকঝক ঝকঝক। সঙ্গে ধোঁয়া। আমাদের শেঠকলোনি থেকে আকাশময় ছড়িয়ে পড়া সেই ধোঁয়া স্পষ্টই চোখে পড়ত তখন।
কী কারণে বা কোত্থেকে যে গোপাল আমাদের পাড়ায় এসে হাজির হয়েছিল বা কেনই যে শিবু দত্তরা ওকে থাকতে দিয়েছিল সে সব নিয়ে আগ্রহী হওয়ার বয়স তখন আমাদের নয়। ঢ্যাঙা শরীরটাকে নিয়ে একটু খুঁড়িয়েই হাঁটত ও। পরিস্কার না করা বা বিড়ির ধোঁয়ায় হলুদ হয়ে যাওয়া বেঢপ টাইপের দাঁতগুলি বাইরে বেরিয়ে থাকত সব সময়। এখানে আসার আগে ও নাকি লাইটম্যানের কাজ করত কোন সিনেমায়। টর্চ জ্বেলে সিট দেখাত লোকদের। ওকে তাই টুলু-মন্টুরা খ্যাপাত খুব। বাড়িঘর কিংবা গাছপালার আড়াল থেকে লাইটম্যান বলে ডেকেই দৌড় লাগাত।
আমাদের খেলার জায়গাটা ছিল কলোনির একেবারে মাঝামাঝি। গৌর হালদার নামে একজন কারও ছেড়ে যাওয়া প্লট। সবাই বলত গৌর হালদারের বাড়ি। একপাশে আমগাছ। গাছটাকে সেই ওল্ড স্টেশন রোড থেকেই চোখে পড়ত সবার। শেঠকলোনির সেই বিকেলগুলিতে একেক দিন গৌর হালদারের বাড়ির একপাশে পড়ে থাকা ভাঙা ঘরে ঢুকে পড়তাম আমরা। বাইরে হয়তো বৃষ্টি পড়ছে খুব। ভাঙা টালি। গোপালের দেশলাই জ্বালানো আর বিড়ির ধোঁয়ার সেই ভাসতে থাকার মধ্যেই ঢুকে পড়ত জলকণা। টালির চালের উপর পড়তে থাকা জলের একটানা ঝমঝম ধ্বনির মধ্যে রোমিও ও জুলিয়েটের ভালবাসার কথা বলত গোপাল। একজনের জন্য আর একজনের মন কেমন করা। লুকিয়ে আদর করা। মৃত্যুর কথাও আসত এক সময়। কবরখানার সেই সুড়ঙ্গপথ। বিষ। আর রোমিওর সেই ডাক, জুলিয়েট, জুলিয়েট।
সিক্স থেকে সেভেনে ওঠার পর মা এল একদিন। সঙ্গে বাবা। এসেই জামা-প্যান্ট গোছাতে বলল। বাবার কথায় আমি নাকি বাজে হয়ে যাচ্ছি একদম। বাড়ি নিয়ে যাবে আমাকে। ভাল স্কুলে ভর্তি করবে। দুপুরে স্নান করতে গিয়ে রতন, মন্টু, টুলুকে বললাম, চলে যাচ্ছি। বিকেলে আমি যখন বাবার পেছন পেছন হাঁটছি, মায়ের হাত ধরে আমি যখন সেই গৌর হালদারের প্লট পার হচ্ছি, ওরা তখন খেলছে। রতন, টুলু, মন্টু, প্রদীপ। সেই আমগাছ, ভাঙা ঘর। টালি। রবারের বলটাকে সেই আমার শেষবারের মতো দেখা। জলকাদা মাখা, লাল। সবাই মিলে পয়সা জমিয়ে কেনা। আমি হঠাৎ করেই ডেকে উঠলাম, এই মন্টু,এই রতন। মন্টুর পায়ে বল ছিল না তখন, একা ও-ই তাকাল। তাকিয়ে কী ভাবল কে জানে? শুধু বলল, আসবি না আর? বলেই দৌড় শুরু করল বলের জন্য।
টাউনে এসে বড় স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর যা হওয়ার কথা, অর্থাৎ রাশি রাশি ছাত্রের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া একেবারে। টিফিনের সময় সেই একা থাকার মুহূর্তগুলিতে মাঝেমধ্যেই আগেকার ভাঙা স্কুলঘরের কথা মনে পড়ত আমার। সেই ফাঁকা প্লট, গৌর হালদারের বাড়ি। আমগাছ আর ভাঙা পুকুরপার। আর গোপালের বলা গল্পগুলির কথাও। বড় স্কুলের প্রথম দিককার দিনগুলিতে নটিলাস ডুবোজাহাজের নাবিকের মতোই লাগত নিজেকে। নীল জলের গভীর থেকে পেরিস্কোপের আয়নায় চোখ। গভীর একাকীত্ব থেকে যেন জগতটাকে দেখছি আমি। দূরের আকাশ, দিগন্তে মিলিয়ে যেতে থাকা নোনা জল। জলের উচ্ছ্বাস, সমুদ্র চিল।
দেখতে দেখতে শহরটাকে মানিয়ে নিলাম একদিন। নতুন করে বন্ধু হল অনেক। স্কুলের মাঠে চামড়ার তৈরি ফুটবল। লাইব্রেরি, বিশাল সেই ক্লাসঘরগুলি। তাদের হাইবেঞ্চ আর দেওয়ালগুলি সমেত এক সময় নিজের হয়ে গেল একেবারে। এইটে থাকতে বিজ্ঞানের স্যারকে অদ্ভুত কথা বলে ফেললাম একটা। কথায় কথায় স্যার জিজ্ঞেস করেছিলেন, বড় হয়ে কী হতে চাও তোমরা? কেউ বলল, ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনিয়ার। আমি সমুদ্রযানের কথা বললাম। সাবমেরিন। সমুদ্র? স্যার তো অবাক। তখনও এমনকী সিনেমাতেও সাবমেরিন দেখিনি কোনও দিন। বা সমুদ্রজলের নীল। বিজ্ঞানের বইয়ে পড়া পেরিস্কোপের বিবরণ। পরস্পর সমান্তরাল দুটি আয়না, অক্ষের সঙ্গে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ। আর গোপালের গল্পটি যে টোয়েন্টি থাউজেন্ড লিগস আন্ডার দি সি সিনেমা দেখে বলা, তা তখন অব্দি জানা ছিল না আমার।
ইলেভেনে ওঠার পরপরই ফ্যাক্টরি বন্ধ হল বাবার। দমদমের দিকে কোনও এক কাপড়ের মিলে কাজ করতেন উনি। মিল বন্ধ হওয়ায় খাওয়া-পরার অসুবিধা ছাড়াও আর এক অসুবিধা তৈরি হল আমার। ফ্যাক্টরি থেকে লুকিয়ে কাগজ আনতেন বাবা। সম্ভবত তুলো প্যাকিং-এর। সাদা। সারা বছরের কাগজের জন্য তাই নিশ্চিন্ত থাকতে পারতাম একেবারে। আমাকে টিউশনি নিতে হল।
চালের দাম লাফিয়ে বাড়ছে তখন। চারদিকে রাজনীতি। খুন, গুলি বিনিময়। এর মধ্যেই হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করলাম একদিন। ফার্স্ট ডিভিশন। অনার্স নিলাম ফিজিক্সে। না করেছিল অনেকেই। বলেছিল, ফিজিক্সের মতো সাবজেক্ট অনার্স রাখতে পারবি না কিন্তু। ছোটমামা খবর পেয়ে খুশি হল খুব। ঘুরে আসতে বলল শেঠকলোনি থেকে। লোকটার সেন্টিমেন্ট বুঝতে পারি আমি। নিঃসন্তান। তা ছাড়া আমার ছোটবেলার এতগুলি বছর।
কলেজে ভর্তি হওয়ার পর একদিন একাই গিয়ে হাজির। বাড়ি যাওয়ার পথে ট্রেন থেকে নেমে সেই রিকশা স্ট্যান্ড, চায়ের দোকান। এই ক বছরে দেখি সত্যিই পালটে গেছে অনেক। আমার সেই শেঠকলোনি। ওল্ড স্টেশন রোডের সেই বাঁধানো পথের বদলে এখন পিচ। তা ছাড়া রাস্তার নামটাই এখন অন্য রকম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোড। কলোনির মুখে দাঁড়িয়ে কেমন একটা অসোয়াস্তি। একটা অপরাধবোধ যেন। কেন কে জানে, মনে হচ্ছিল কেউ যেন চিনতে পারবে না আমাকে। যেন জানতে চাইবে, কার বাড়ি? কাকে খুঁজছেন আপনি? আশুকাকুর বাড়ির সেই মুদিখানা তখন উধাও একেবারে। দরমার বেড়া আর টিনের চালের জায়গায় দেশলাই বাক্সের মতো ঘর তিন-চারটি। প্লাস্টার না-করা দেওয়াল। আগেকার সেই টিনের চালের উপর বসে থাকা পায়রার ঝঁকের কথা মনে পড়ল আমার। আর তাদের উড়ে যাওয়া। আর আমাদের সেই হাততালি দেওয়ার কথাও। আর হঠাত করেই মনে হল, পায়রারা কি ওই হাততালির শব্দ শুনতে পেত? ওরা কি সত্যিই হাততালির শব্দে ঢেউ তুলত বাতাসে, সত্যিই কি আরও উঁচুতে উড়তে চাইত?
আশুকাকুর বাড়ির কথা তোলায় ছোটমাসি সেবার বলল, ওরা নাকি ভাগ হয়ে গেছে। তিন ভাই। জায়গা নিয়ে মারপিট হয়েছে খুব। সেই আশুকাকু নাকি ফুটপাথে বসছে। স্টেশন রোডের কোথাও বসে নাকি ব্লাউজ বেচছে। আমাদের খেলার সেই গৌর হালদারের জমির উপর ঘর উঠেছে একখানা। ক্লাবঘর। নাম দিয়েছে শক্তি সংঘ। ক্যারাম ঢুকেছে। এছাড়া ঘরের বাইরে রাস্তার আলোয় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মানুষজন। তাসপার্টি। বেশ জমজমাট লাগছিল তখন। টু স্পেড, থ্রি ডায়মন্ড। এ ছাড়া নকশাল-সিপিএম-কংগ্রেস। হরিশদের বাড়িতে দোকানঘর উঠেছে একখানা। হ্যাজাক। মেন্টেলের সেই আলো ছড়িয়ে পড়েছে অনেকটা দূর পর্যন্তই।
মামার বাড়ি আসার পথে রাস্তাতেই ডেকে বসল কে একজন। টুকুন না? ভাল করে তাকিয়ে বুঝতে পারি, অনন্তদা। আগের চেয়ে রোগা হয়ে গেছে অনেক। সবুজ রঙের লুঙ্গি, খালি গা। হাতে ধরে রাখা বাচ্চা ছেলে একটা। কাঁচা-পাকা চুল। কেমন বুড়ো হয়ে গেল লোকটা। বলল, হাঁটা দেখেই চিনতে পারলাম তোকে। কেমন অবাকের না? আর এই প্রথম নিজের একটা বৈশিষ্টের কথা জানা। হাঁটা। সত্যিই কি অন্য রকম কিছু? অনন্তদা বলল, ভারিক্কি হয়ে গেছিস কেমন, দাড়ি রেখেছিস কেন?
অনন্তদাকে মন্টুর কথা জিজ্ঞেস করলাম। লোকটা অবাক হল খুব। ও নাকি আগের বছরই খুন হয়ে গেছে। পার্টি শুরু করেছিল। এরপর যা হয়, পোস্টার লাগানো, এলাকা দখল। বোমা-পাইপগান-ছুরি। অনন্তদা বলল, রেললাইনের পাশেই তো পড়েছিল বডিটা। ফিসফিস করে সাবধান করল লোকটা, বলল, যতই চেনা হোক পার্টির কথা বলিস না কোনও। তোর মতো ভাল ছেলিউপৌঐআঈজ়ংমনেএ।
কলেজে পড়তে পড়তেই প্রেমে পড়লাম। বিউটি। ওকে পড়াতাম আমি। ও ছিল পাখির মতোই নরম, আর হালকা। তুচ্ছ কোনও আঘাতেই ভেঙে পড়বে যেন। কলেজ জীবনে এমনিতে খুব একটা বন্ধু ছিল না আমার। চারপাশে তখন তুমুল রাজনীতি। মাঝেমধ্যে বন্ধ। কোনও ছাত্রের মৃত্যুতে শোভাযাত্রা। বিউটিকে পড়াতে বসে একেক দিন কথা উঠত এসবের। রাজনীতি, মৃত্যু। মৃত ছেলেদের নাম জানতে চাইত বিউটি। বলতাম। ওদের নিয়ে আরও কিছু জানতে চাইলে বানিয়েই বলতে হত আমাকে। আর তখনই লক্ষ করতাম গল্পের মধ্যেই নিজের জন্য চমৎকার একটা জায়গা তৈরি হচ্ছে কেমন। মৃত্যুর কাছাকাছি। একেবারেই গা ঘেঁষাঘেঁষি করা। মৃত্যুর ছোঁয়া বাঁচিয়ে কেমন পার পেয়ে যাচ্ছি আমি। যেন কেউ দেখতেই পাচ্ছে না আমাকে। সেইসব পাইপ গান, কর্কশ হাত বা স্প্লিন্টার। যেন সবার অগোচরে সত্যিই কোনও পেরিস্কোপে চোখ রাখা আছে আমার। চোখে পড়ছে জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, টাইফুন।
বিউটির চিঠিগুলিতে আমার বানানো গল্পগুলির প্রতি ওর দূর্বলতা ধরা পড়ত। সেই সব মৃত ছেলেদের নাম। মৃত্যুর বিবরণ। তারিখ। মৃত্যুর আগে আমার সঙ্গে ওদের কথোপকথন। বিপ্লবীদের প্রতি মেয়েদের দূর্বলতা থাকে বেশ। বিপ্লব মানে ওদের কাছে মৃত্যুর গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে থাকা। দেওয়ালে পিঠ রেখে অনিবার্য কোনও কিছুর জন্য অপেক্ষা করা।
পড়াতে পড়াতে এটা-সেটার গল্প জুড়তে গিয়ে ওর কাছে আমি একদিন সেই সমুদ্রযানের কথা তুললাম। সাবমেরিন। গোপন সেই একাকিত্ব থেকে পেরিস্কোপে চোখ রাখার কথা বললাম আমি। দূরের দিগন্তরেখা। সমুদ্রচিল। নির্জনতার সেই গুরগুর ধ্বনি।
বিউটির বিয়ের বছর আমি এমএসসি দিচ্ছি। ওর দাদার কোনও বন্ধুর সঙ্গেই বাড়ি ছেড়েছিল ও। এরপর যা হয়, দু’-চার দিন খোঁজাখুঁজি পুলিশ। ওর চিঠিগুলি বা ওর ছবি আমি অবশ্য রেখে দিলাম যত্ন করে। সে সব চিঠির কথা এমনকী বিশাখাও জানে না এখন পর্যন্ত।
সেই টাউনের দিনগুলি ফেলে এসেছি অনেকদিন। বাবা মারা গেলেন মা মারা যাওয়ার অনেক আগেই। মানুষ কীভাবে বড় হয়ে যায় ভাবুন। দিনের পর দিন। এরপর মাস, বছর। ছোটমামা মারা যাওয়ার পর মামি এখন একেবারে একা। মামার শেষ কাজের জন্য আমাকে সেই শেঠকলোনিতে যেতে হল ফের। বিশাখা, আমি, আমাদের ছেলে। ট্রেন থেকে নেমে সেই স্টেশন, রিকশা স্ট্যান্ড। আগের সেই চায়ের দোকানের জায়গায় দেখি রেস্টুরেন্ট হয়েছে একটা। এগ রোল, চাউমিন।
শেঠকলোনিকে দেখে তখন আর আমার না চেনারই কথা। অটো চালু হয়ে গেছে নাকি অনেকদিন। অর্থাৎ পাঁচজন যাত্রীর জন্য অপেক্ষা করে একসময় হাত দিয়ে সেই রড টানা, এরপর ভট্ভট্ ভট্ভট্। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোডের আগেকার নাম এখন আর মনেই নেই কারও। মজা করে অটোয়ালা ছেলেটিকে ওল্ড স্টেশন রোডের কথা বলায় ও একেবারে ভুঁরু কুঁচকে উঠল।
পাড়ার ভেতরে রাস্তার দুপাশে তখন একতলা-দোতলা বাড়ি। জানালার ফাঁক দিয়ে কালার টেলিভিশন। পাকা ড্রেন। আমাদের খেলার সেই একচিলতে জমিটাকে খুঁজেই পেলাম না কোথাও। থাকার মধ্যে শক্তি সংঘ সাইনবোর্ড টাঙানো আগেরবারের দেখে যাওয়া সেই ক্লাবঘরটাই। এমনকী সেই আমগাছটাও নেই আর।
মামার শেষ কাজে পাড়ার ছেলেরা সাহায্য করল খুব। ছোটমামির কথায় ওরা না থাকলে মামাকে মরতে হত বিনা চিকিৎসাতেই। ওরাই নাকি অ্যাম্বুনেন্স এনেছে, রক্ত জোগাড় করেছে। ওদেরই কেউ ফোন করে খবর দিয়েছে আমাকে।
ছেলেটাকে আমার সেই পুরনো পাড়াটা, আমার সেই ডাং-গুলি চোর-চোর খেলার দিনগুলিকে দেখানোর ইচ্ছে হচ্ছিল খুব। সেই সব ভাঙা পুকুর পাড়, কুলগাছ। সেই ফাঁকা প্লট, পাখির ডাক। এক সেই প্রাইমারি স্কুলটাই টিকে আছে কোনও মতে। পাড়ার ছেলেরা বলল, এখানে কে আর আসবে এখন? ওদের বাড়ির বাচ্চারাই নাকি দূরের স্কুলে ভর্তি হচ্ছে।
স্কুলটাকে অবশ্য এখন স্কুল বলে চেনাই মুশকিল। চারদিকই এখন দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। একদিকে গ্রিলের ছোট দরজা একটা। আমাদের সময়কার সেই হু-হু করা বাতাস বা বৃষ্টির সেই ছাঁট এখন নেই আর। পুকুরের সেই সব দৃশ্যাবলী। বাসনমাজা, স্নান। ঘাটের কাছে শ্যাওলা খেতে থাকা পুঁটি মাছের ঝিলিক দেখার আর উপায় নেই কোনও। বা চিলের সেই ঝাঁপ।
ছেলে বিরক্ত হচ্ছিল খুব। বিশাখাও। মামার কাজ মিটে যাওয়ার পরদিনই রওয়ানা হলাম। ছেলেবেলার বন্ধুদের মধ্যে এক টুলুর সঙ্গেই দেখা হল শুধু। নিমন্ত্রণ খেতে এসেছিল, সঙ্গে বউ। যে ছেলেটা আমাকে উৎসাহ নিয়ে পাড়া দেখাতে বেরিয়েছিল ও নাকি টুলুরই। টুলুকে দেখে যে চিনতে পারিনি সেটা অবশ্য ওকে বুঝতে দিলাম না একেবারে। মাথায় টাক, গোঁফের প্রায় পুরোটাই সাদা। রোগা হয়ে গেছে খুব, চালের সেই দোকান নাকি উঠে গেছে অনেকদিন। ছেলে পার্টি করছে, চাকরি নাকি হতে পারে ভবিষ্যতে, পার্টির থ্রু-তেই। টুলুর নিজের বলতে এখন একটা চায়ের দোকানই। বলল, শীত-গ্রীষ্ম সারাটা বছর ভোর-ভোর রওয়ানা হয়ে রাত করে বাড়ি ফেরা।
বাঁ দিকের পার বাঁধানো থাকায় রাস্তা ভাঙার ভয় নেই আর। কে যেন লিজ নিয়েছে এখন। মাছ ছেড়েছে সম্ভবত নাইলন টিগাই। ঝাঁক বেঁধে ভেসে একবার করে মুখ খুলছে আর বন্ধ করছে। ক্লাবঘর ছেড়ে অনেকটাই চলে এসেছি তখন। হঠাৎ শুনি কেউ যেন চিৎকার করে ডেকে উঠল কাকে। লাইটম্যান।
মুহূর্তের মধ্যেই একটা গুরগুর ধ্বনি উঠল কোথাও। যেন সত্যিই পেরিস্কোপে চোখ। দুটো আয়নার সেই সমান্তরাল অবস্থান। ফের যেন ডেকে উঠল কেউ, লাইটম্যান।
একদল বাচ্চা বুড়ো মতো একটা লোককে ঘিরেই ধরেছে প্রায়। খ্যাপাচ্ছে। সামনে থেকে, পেছন থেকে এসে লোকটার জামা ধরে টেনেই দৌড় লাগাচ্ছে।
কী হল?
টুলুর ছেলে অবাক হল খুব।
ও তো গোপাইল্যা, ক্লাবঘরের বারান্দায় থাকে, থাকে মানে ঘুমায় রাতে। মাথায় ছিট।
আমি অবশ্য ওর কাছে জানতে চাইনি কিছু। ফের হাঁটা শুরু করতেই ছেলেটি ওর কথার খেই ধরল। ওদের বাড়ির কথা, ওর বাবা, ওর মা। এছাড়া রাজনীতি। রাজনীতি কীভাবে শেষ করে দিল পাড়াটাকে।
ওর বাবার কাছ থেকে নাকি আমার সম্পর্কে অনেক কিছুই শুনেছে ও। সেই সব কষ্টের দিন। আর আমার উন্নতির কথাও। কাগজে আমার সম্পর্কে কিছু লেখা হলে ওরা নাকি গর্ব বোধ করে খুব। এমনকী বলল, ভাগ্যিস আপনি চলে গিয়েছিলেন।
ফাইভ-সিক্সের দিনগুলিতে আকাশে চোখ রাখলে এখান থেকেই সেই কালো ধোঁয়া চোখে পড়ত। সেই রেলস্টেশন, ঝিক্ঝিক্ ধ্বনি। হুইশ্ল। সেই দিনগুলিতে এখান থেকে পেছন ফিরে তাকালেই আমগাছটাকে চোখে পড়ত। সেই ফাঁকা জমি, ভাঙা ঘর, টালি। বৃষ্টি পড়ার সেই একটানা ঝম্ঝম্।
যেন টুলুর ছেলের তাগাদা দেওয়াতেই পা চালালাম। সামনে ও তখন সাইকেল থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়া একজনকে আমার সম্বন্ধে বলছে কিছু। আমাদের পাড়ার..., সেই বাবাদের আমলের... , বাবার বন্ধু।
ওকে ধরে ফেলে, ওর পাশে হাঁটতে হাঁটতে আমি রাস্তাঘাটের কথা তুললাম। মিউনিসিপ্যালিটি, পাকা ড্রেন। সেই লিজ নেওয়া পুকুরের ভাঙা পাড় বাঁধানোর কথাও তুললাম আমি। আসার পথে পাশের পুকুরে ঝাঁক ধরে ভাসতে থাকা মাছগুলির নাম জিজ্ঞেস করলা। সেই দল বেঁধে মুখ খোলা আর মুখ বন্ধ করা। বড় রাস্তায় পড়ার আগে একবারের জন্যও আমি আর পেছন ফিরে তাকালাম না।