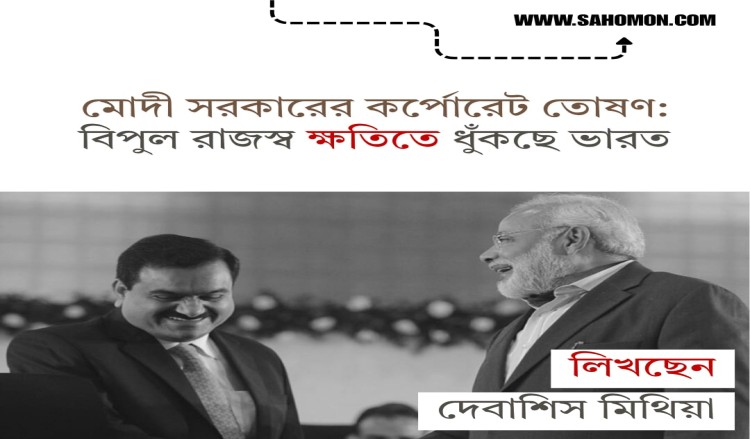ভারতীয় অর্থনীতি এখন এক জটিল সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। একদিকে, মোদী সরকার কর্পোরেট সেক্টরকে অবাধ লুঠের সুযোগ করে দিতে নির্লজ্জভাবে ব্যাপক হারে কর ছাড় দিচ্ছে, অন্যদিকে, সরকারি ব্যাংকগুলো (পিএসবি) কোটি কোটি টাকা অনাদায়ী ঋণ নিয়মিত মকুব করে চলেছে। এই দ্বিমুখী লুঠের ফলে সরকারের কোষাগার কার্যত শূন্য । ফলে দেশের আর্থিক সমস্যাগুলো দিন দিন ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে, যা সামগ্রিক অর্থনীতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।
কর্পোরেট ট্যাক্স ছাড় ও ঋণ মকুব
কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরী রাজ্যসভায় লিখিতভাবে জানিয়েছেন যে, কর্পোরেটদের কর ছাড়ের ফলে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে আনুমানিক ৯৯,০০০ কোটি টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। এটি একটি ধারাবাহিক প্রবণতা। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৮৮,১০৯ কোটি টাকা এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে ৯৬,৮৯২ কোটি টাকা – বিপুল পরিমাণ রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। ২০১৬ সাল থেকে কর্পোরেট করের হার ক্রমাগত কমানো হয়েছে; ২০১৯ সালে তৎকালীন কোম্পানিগুলোর জন্য বেস কর্পোরেট ট্যাক্স ৩০% থেকে ২২% -এ নামিয়ে আনা হয়, যা কর্পোরেটদের জন্য মোদী সরকারের এক নির্লজ্জ উপহার।
এছাড়াও গত ২২শে জুলাই সরকার সংসদে জানিয়েছে, ২০১৫-১৬ থেকে ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরের মধ্যে ভারতের পাবলিক সেক্টর ব্যাংকগুলো মোট ১২.০৮ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ মকুব করেছে। মকুব করা এই বিশাল অঙ্কের ঋণের বেশিরভাগই আদায় করা যায়নি। ২০২০-২০২৪ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে, মকুব করা ঋণের মাত্র ১.৮৫ লক্ষ কোটি টাকা (১৮.৭%) আদায় হয়েছে। অর্থাৎ প্রায় ৮ লক্ষ কোটি টাকার বেশি ঋণ এখনও ফেরত আসেনি। এটা স্পষ্টতই জনগণের টাকার অপব্যবহার।
খেলাপিদের আড়াল
তদুপরি, ২০২৫ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্কগুলো ১,৬২৯ জন কর্পোরেট ঋণগ্রহীতাকে ‘ইচ্ছাকৃত খেলাপি’ (wilful defaulters) হিসাবে চিহ্নিত করেছে, যাদের মোট বকেয়া ঋণের পরিমাণ ১.৬২ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি। ঋণ খেলাপিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে – তেমনটাই সরকার প্রচার করছে । তবে এই প্রচারের বেশির ভাগটাই মিথ্যে।
মন্ত্রী আরও উল্লেখ করেন যে, দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া অভিযুক্তদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, ৯ জন অভিযুক্তকে ‘ফিউজিটিভ ইকোনমিক অফেন্ডার্স অ্যাক্ট, ২০১৮’ (এফইওএ) এর বিধান অনুযায়ী ‘ফিউজিটিভ ইকোনমিক অফেন্ডার’ ঘোষণা করা হয়েছে। এই মামলাগুলোতে, বর্তমানে, পিএমএলএ-এর অধীনে প্রায় ১৫,২৯৮.২৭ কোটি টাকা এবং এফইওএ-এর অধীনে প্রায় ৭৪৯.৮৭ কোটি টাকা মূল্যের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। কিন্তু এই প্রচারমূলক পদক্ষেপ আসলে কর্পোরেট লুটেরাদের রক্ষাকবচ, সাধারণ মানুষের চোখে ধুলো দেওয়ার কৌশল মাত্র।
‘মেক ইন ইন্ডিয়া’র বাস্তবতা
কর্পোরেট কর ছাড় এবং ব্যাংক ঋণ মকুবের পেছনে সরকারের উদ্দেশ্য ছিল অর্থনীতিকে গতিশীল করা, বিনিয়োগ বাড়ানো এবং কর্পোরেট সেক্টরকে চাঙ্গা করা। কিন্তু বাস্তব ছবি সে কথা বলে না, বরং উল্টোটাই প্রমাণ করে। তবে, এই পরিস্থিতির জন্য মোদী সরকারের নীতিগত অবস্থান এবং জনবিরোধী সিদ্ধান্তকে সরাসরি দায়ী করা যায়। দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার উদ্দেশ্যে কর্পোরেটদের জন্য যে দেদার কর ছাড় ও ঋণ মকুবের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তার সুফল সরকারের আশীর্বাদপুষ্ট কর্পোরেট পুঁজিপতি ও লুটেরাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে।
সরকার আশা করেছিল, কর কমলে কোম্পানিগুলোর হাতে বিনিয়োগের জন্য আরও বেশি অর্থ থাকবে, যা তারা নতুন প্রকল্পে ব্যয় করবে এবং ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ উদ্যোগকে শক্তিশালী করবে। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক ফিনান্স অ্যান্ড পলিসি (এন পি আই এফ পি)-এর একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, ২০১৯ সালে কর কমানোর ফলে অভ্যন্তরীণ সংস্থাগুলোর বিনিয়োগে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেয়েছে ( বিশেষ করে বড় সংস্থাগুলোর)। নতুন উৎপাদন সংস্থাগুলোর জন্য ১৫% করের হার ভারতকে উৎপাদন বিনিয়োগের জন্য একটি আকর্ষণীয় গন্তব্যে পরিণত করেছে। তবে এই সাফল্যের পেছনে একটি বড় ‘কিন্তু’ লুকিয়ে আছে, যা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় মোদী সরকারের ভণ্ডামি কতখানি। বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেলেও, কর ছাড়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত অতিরিক্ত অর্থ নতুন প্রকল্পে বিনিয়োগের পরিবর্তে পুরনো ঋণ পরিশোধ, শেয়ার বাইব্যাক অথবা শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে ডিভিডেন্ড বিতরণে ব্যবহার হয়েছে। ফলে, প্রত্যাশিত উৎপাদন বৃদ্ধি বা কর্মসংস্থান সৃষ্টি সেই অর্থে হয়নি, তাই দেশের যুবসমাজ বেকারত্বের জ্বালায় দিশেহারা।
অর্থনীতির শ্লথ গতি মোকাবিলা এবং শিল্প উৎপাদন বাড়ানোর উদ্দেশ্যে এই কর ছাড়কে একটি উদ্দীপক হিসেবে দেখা হয়েছিল। কিন্তু, কর কমানোর ফলে ২০১৯ সালের এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিকে ভারতের জিডিপি বৃদ্ধি ৬ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন ৫%-এ নেমে আসে। যদিও কর কমানোর কারণে কর্পোরেট লাভজনকতা বৃদ্ধি পেয়েছে, অর্থনীতিবিদদের কেউ কেউ মনে করেন এটি ভারতীয় অর্থনীতিকে বিনিয়োগের জন্য আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। তবে, কর কমানোর তাৎক্ষণিক প্রভাব মূল্যায়ন করা কঠিন ছিল, কারণ এর পরপরই কোভিড-১৯ মহামারী শুরু হয়, যা অর্থনীতিতে ব্যাপক ব্যাঘাত ঘটায়। মহামারীর ছায়ায়, কর ছাড়ের প্রকৃত প্রভাব জিডিপি বৃদ্ধিতে কতটা পড়েছে, তা স্পষ্ট নয়। মোদী সরকার নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে মহামারীকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে, যা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়।
বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতায় ভারত
বিশ্বব্যাপী বিনিয়োগ আকর্ষণ করার প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে অনেক দেশই করের হার কমিয়েছে। ভারতও নিজেদেরকে একটি আকর্ষণীয় বিনিয়োগ গন্তব্য হিসেবে তুলে ধরতে এই পদক্ষেপ নেয়। কর কমানোর ফলে ভারতের কর্পোরেট করের হার এশিয়ার অনেক উদীয়মান অর্থনীতির তুলনায় আরও অনুকূল হয়েছে। ভারতের বেস কর্পোরেট ট্যাক্স হার বর্তমানে ২২% (নতুন উৎপাদনকারী সংস্থাগুলির জন্য ১৫%)। এটি বাংলাদেশের ২৭.৫%, পাকিস্তানের ২৯%, এবং মালয়েশিয়ার ২৪% তুলনায় কম। এমনকি, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অর্থনৈতিক শক্তি ইন্দোনেশিয়া (২২%) এর সমান। এই তুলনামূলক কম করের হার বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য ভারতের বাজারকে আরও আকর্ষণীয় করেছে। বিশ্বব্যাংকের ‘ইজ অফ ডুয়িং বিজনেস’ র্যাঙ্কিংয়ে ভারত ২০১৪ সালের ১৪২তম স্থান থেকে ২০১৯ সালে ৬৩তম স্থানে উঠে আসা নাকি তারই ফল !
তবে, কর ছাড় প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (এফডিআই) আকর্ষণের একটি অংশ হলেও, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, দক্ষ শ্রমশক্তি, পর্যাপ্ত পরিকাঠামো এবং বাজারের আকারের মতো অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোও বিনিয়োগকারীদের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। যদি এই মৌলিক বিষয়গুলোতে ঘাটতি থাকে, তাহলে শুধু কর কমিয়ে সুস্থায়ী বিনিয়োগকে আকর্ষণ করা সম্ভব নয় – মোদী সরকার এই চরম সত্যকে উপেক্ষা করতে চাইছে।
ঋণ মকুব: জনগণ বনাম কর্পোরেট
ব্যাংকগুলোর বিপুল অনাদায়ী ঋণ (এনপিএ) তাদের ব্যালেন্স শীটকে দুর্বল করে দিয়েছিল। ঋণ মকুবের মাধ্যমে ব্যাংকগুলো তাদের অ্যাকাউন্ট থেকে এই অনাদায়ী ঋণ সরিয়ে ফেলে, এতে ব্যাংকগুলোর ব্যালেন্স শীট ‘পরিষ্কার’ দেখায়। মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত পাবলিক সেক্টর ব্যাংকগুলোর মোট নন-পারফর্মিং অ্যাসেটস (জিএনপিএ)-এর অনুপাত ২০২৩ সালের ৪.৯৭% থেকে কমে ২.৫৮% এ দাঁড়িয়েছে। তবে এই ‘পরিষ্কার’ হওয়ার ছবিটি একটি বড় প্রশ্নের জন্ম দেয় – জনগণের টাকা কী হচ্ছে? ব্যাংকগুলো তাদের ব্যালেন্স শীট থেকে অনাদায়ী ঋণ সরিয়ে ফেললেও, মকুব করা ঋণের পুনরুদ্ধারের হার অত্যন্ত কম (মাত্র ১৮.৭%)। এর অর্থ হলো, জনগণের বিপুল পরিমাণ অর্থ অনাদায়ী থেকে যাচ্ছে, যা ব্যাংকগুলোর দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক স্বাস্থ্যের জন্য চরম উদ্বেগজনক এবং করদাতাদের ওপর এক বিরাট বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাছাড়া এটি ঋণ পরিশোধে অনীহা তৈরি করছে। একদিকে ঋণ খেলাপিরা ছাড় পাচ্ছেন, অন্যদিকে সৎ করদাতারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন – এটাই মোদী মডেল!
জনকল্যাণ বনাম তোষণ
কর্পোরেট কর ছাড় ও ঋণ মকুবের পেছনে কিছু ইতিবাচক উদ্দেশ্য থাকলেও, এর ফলে সরকারের যে বিশাল রাজস্ব ক্ষতি হচ্ছে, তা সামগ্রিক অর্থনীতির ওপর গুরুতর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে এবং দেশের ভবিষ্যৎকে অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছে।
প্রথমত, প্রতি বছর প্রায় ৯৯,০০০ কোটি টাকা রাজস্ব হারানোর অর্থ হলো শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিকাঠামো এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচির মতো অত্যাবশ্যক জনসেবা খাতে সরকারের ব্যয়ের ক্ষমতা মারাত্মকভাবে কমে যাওয়া। যখন জনগণের করের টাকা জনকল্যাণে ব্যয় না হয়ে কর্পোরেটদের পকেটে চলে যায়, তখন তা অর্থনীতিতে সুদূরপ্রসারী নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। মোদী সরকার আসলে জনগনের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে কর্পোরেটদের সুবিধা পাইয়ে দিচ্ছে।
দ্বিতীয়ত, কর থেকে কম আয় হওয়ায় সরকার বাধ্য হচ্ছে বেশি ঋণ নিতে, যা দেশের রাজস্ব ঘাটতিকে বাড়িয়ে তুলছে। সম্প্রতি সংসদে মাথা পিছু ঋণ সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে অর্থ প্রতিমন্ত্রী জানিয়েছেন যে, গত ৩১ মার্চ পর্যন্ত দেশে মাথা পিছু ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১,৩২,০৫১ টাকা। প্রতি নাগরিকের ওপর ক্রমবর্ধমান এই ঋণের বোঝা ভারতের আর্থিক ভবিষ্যৎকে এক গভীর সংকটের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। এই ঋণের বোঝা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বয়ে নিয়ে যেতে হয়, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের আর্থিক স্বাধীনতাকে খর্ব করে।
তৃতীয়ত, এই কর ছাড়ের সুবিধা প্রধানত বড় কর্পোরেটগুলোই পেয়ে থাকে, যা সমাজের ধনী অংশের হাতে অতিরিক্ত সম্পদ কেন্দ্রীভূত করে। একই সময়ে, সরকারের রাজস্ব ঘাটতি পূরণের জন্য পরোক্ষ কর বা অন্যান্য উপায়ে সাধারণ মানুষের ওপর করের বোঝা চাপাতে থাকে, যা আয় বৈষম্যকে বাড়িয়ে তোলে এবং ট্যাক্স ব্যবস্থাকে পশ্চাদমুখী করে দেয়। এটি আসলে ধনীদের আরও ধনী এবং গরিবদের আরও গরিব করার এক নির্লজ্জ প্রক্রিয়া।
চতুর্থত, পাবলিক সেক্টর ব্যাংকগুলোর যখন বিপুল পরিমাণ কর্পোরেট ঋণ মকুব করে, তখন এক ধরনের নৈতিক ঝুঁকি (মরাল হ্যাজার্ড) তৈরি হয়। এতে বড় ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে দায়বদ্ধতার অভাব দেখা দেয় এবং ব্যাংকের আর্থিক স্বাস্থ্য দুর্বল হয়ে পড়ে। সরকার আসলে ঋণ খেলাপিদের রক্ষা করে জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে।
পঞ্চমত, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও সার্বিক অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে কর্পোরেট ট্যাক্স ছাড়ের যে উদ্দেশ্য, তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। এই ছাড়ের ফলে কিছুক্ষেত্রে বিনিয়োগ ও মুনাফায় উন্নতি দেখা গেলেও, এর সুফল সমাজের প্রতিটি স্তরে বা অর্থনীতির প্রতিটি খাতে সমানভাবে পৌঁছায়নি। একদিকে সরকারের কোষাগার থেকে বিশাল অঙ্কের রাজস্ব হারানো এবং অন্যদিকে প্রত্যাশিত কর্মসংস্থান ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বৃদ্ধি না হওয়ায় এই নীতির কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে – আসলে কার স্বার্থে এই নীতি?
চরম দায়িত্বহীনতা
সংসদে সম্প্রতি প্রকাশিত তথ্যগুলো দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণ করে যে, কর্পোরেট কর ছাড়ের কারণে বিপুল রাজস্ব ক্ষতি এবং বিশাল অঙ্কের ঋণ মকুব – এই দুটি বিষয় ভারতীয় অর্থনীতিকে এক গুরুতর চ্যালেঞ্জের মুখে এনে দাঁড় করিয়েছে, যা ধ্বংসের পূর্বলক্ষণ। এর ফলে, একদিকে সরকারি পরিসেবার মান কমছে, তেমনি অর্থনৈতিক অসমতা বাড়ছে। এই পদক্ষেপগুলো দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক স্থিতিশীলতা, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং জনকল্যাণমূলক উন্নয়নের পথকে রুদ্ধ করে দিচ্ছে। দেশের অর্থনীতির এই সংকটকালে – বিপুল অর্থের অপচয় অযৌক্তিক। তাই জনগণের অর্থ কীভাবে কোথায় ব্যবহৃত হচ্ছে, তার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি।
সমাধানের পথ
দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি কিছু জরুরি পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। এর মধ্যে রয়েছে কর্পোরেটদের জন্য যৌক্তিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ করের হার নির্ধারণ, যা সরকারের রাজস্ব বাড়াবে। একই সাথে, ইচ্ছাকৃত খেলাপিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিয়ে মকুব করা ঋণ পুনরুদ্ধার এবং ব্যাংকগুলোর ঋণ অনুমোদন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। সবশেষে, রাজস্ব আয়ের একটি বড় অংশ জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মতো মৌলিক ক্ষেত্রগুলোতে বিনিয়োগ করা উচিত, যা দীর্ঘমেয়াদে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়ক হবে।