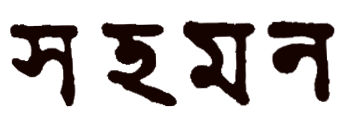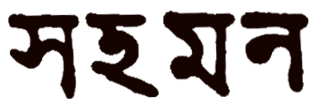ষাট এর দশকের মাঝামাঝি সময় তখন। প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধের স্লোগান ও মিছিলে কল্লোলিত কলকাতা। অগ্নিবর্ষী রাজনৈতিক ভাষণ এবং আন্দোলনের উত্তাপ পৌঁছে যাচ্ছে শহরতলি ছাড়িয়ে দূর মফস্বলেও। চিত্তরঞ্জনের মত একটি শান্ত, নিরুপদ্রব শিল্পনগরীতে বেড়ে ওঠা সদ্য কৈশোর পেরনো এক তরুণ, সেই প্রাণোচ্ছল কলকাতায় এসে পড়াশুনা করার সঙ্গে সঙ্গে দিগন্ত বিস্তৃত চিন্তা ও ভাবনার আকাশে ডানা মেলার স্বপ্ন দেখছিলেন।
১৯৬৫ সাল। হায়ার সেকেন্ডারি পাস করেই চলে এলেন কলকাতায়। ছাত্রাবস্থা থেকেই ডাক্তারি শিক্ষার প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ। ইন্টারভিউ দিলেন ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে। সেটি তখন বেসরকারি কলেজ। নম্বরের মাপকাঠিতে নির্বাচিত হলেও বাধা হলো ক্যাপিটেশন ফি। অত্যন্ত ঋজু মানসিকতার পিতা ছিলেন সশস্ত্র স্বাধীনতা আন্দোলনের আদর্শে অনুপ্রাণিত। তিনি স্পষ্ট বলে দিলেন “ লজ্জা করবেনা পয়সা দিয়ে যোগ্যতা কিনতে?” সেই তরুণ তখন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলেন - ঠিকই তো, ডাক্তারি শিক্ষার কেন্দ্র তো আর হাট- বাজার হতে পারে না। কিছুদিন পরে অবশ্য সরকারি প্রতিষ্ঠান আরজিকর মেডিকেল কলেজে তিনি সসম্মানে ভর্তির যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। তখন চলছে খাদ্য আন্দোলন। মিনার্ভা থিয়েটারে উৎপল দত্তের নাটক কল্লোল। প্রথমে নাউ পরে ফ্রন্টিয়ার পত্রিকার নিয়মিত পাঠক হয়ে উঠলেন সেদিনের তরুণ স্থবির দাশগুপ্ত।
১৯৬৭ সালে চতুর্দিকে দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ছে নকশালবাড়ি রাজনীতি। তারপর এল ঝঞ্ঝা বিক্ষুদ্ধ ১৯৭১ সাল। ততদিনে, সমস্ত ক্লেদ, অন্যায় আর সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা বিদ্রোহীদের দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত হয়েছে আর জি কর মেডিকেল কলেজ। ফাইনাল পরীক্ষার আর বেশি দেরি নেই। কিন্তু পরিস্থিতি দ্রুত বদলাচ্ছে। হিন্দু হোস্টেল থেকে একদিন ফেরার পথে বিনা কারণে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলেন তিনি। কয়েকদিন পরে অবশ্য মুক্তি মিলে ছিল।সেই সময় থেকেই তাঁর বাগমীতা এবং ক্ষুরধার লেখনি, তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যতের অভিমুখ বদলে দিচ্ছিল। ঘেরাও তল্লাশি অভিযান থেকে যখন বাদ পরলো না কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ, তখন একপ্রকার বাধ্য হয়েই পুলিশের চক্রব্যূহ অতিক্রম করে পাড়ি দিলেন অজ্ঞাতবাসে। সেই রোমহর্ষক দুঃসাহসিক অভিযানের ঘটনার উল্লেখ রয়েছে তাঁর রচিত ‘স্বপ্নের সত্তরঃ মায়া রহিয়া গেল’ বইটিতে। বইটি তিনি “স্বপ্নযাত্রীদের” উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছেন।
তবে বইটি কোন স্বপ্নভঙ্গের দলিল নয়। দীর্ঘ ছয় বছর সুন্দরবনের নিকটবর্তী যেসব দুর্গম গ্রাম ও জনপদে অবহেলিত, অসহায় এবং দরিদ্রতম মানুষের মধ্যে তিনি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালিয়েছেন, সেইসব অচেনা মানুষদের প্রতিদিনকার জীবন-সংগ্রাম, জীবন-বোধ, শিক্ষিত এবং ভদ্রবিত্তের অগোচরে থাকা তাদের আত্মত্যাগের উজ্জ্বল এক আলেখ্য তুলে ধরেছেন এই বইটিতে। অসম্ভব স্বপ্নযাত্রায় অপরিণামদর্শী রাজনৈতিক ভাষ্যের বিপরীতে, তিনি সেখানে খুঁজতে চেয়েছেন তাদের জীবন দর্শন ও ভাবনার শিকড় কে। তিনি বলেছেন “সত্তরের সেই ফিকে হয়ে আসা আলোয় মনে হল আন্দোলনের রূপ স্থির করে নেয় মানুষ, কোন ইস্তাহার না”।
১৯৭৬ সাল। অবিশ্বাস্য উজান শেষে মূলধারায় ফিরে আসাটা মোটেই সহজ কাজ ছিল না। তবে আত্মসমর্পণের পথে নয়। এই সমাজের মধ্যেই কিছু সহৃদয় বন্ধু এবং বিবেকী ও উদারমনা মানুষের ঐকান্তিক সহায়তায়, অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে আবার নিজের কলেজে ফিরে এলেন। পাহাড় প্রমাণ বাধা ডিঙিয়ে ডাক্তারির অসমাপ্ত পাঠ শেষ করলেন। সেই সময়ে অকৃত্রিম বন্ধু হিসেবে যারা তাঁকে পরম যত্নে ঘিরে থাকতেন, তাদের অনেকেই ভিন্ন রাজনীতির এমনকি দু একজন বিপরীত মতাদর্শেও বিশ্বাসী ছিলেন। তাদেরই একজন বলেছিলেন, “পথ ছেড়েছিস তো কি হয়েছে, মতটাও কি ছেড়েছিস?” মানবতাবাদে গভীর বিশ্বাসী, সদ্য পাস করা তরুণ চিকিৎসক স্থবির দাশগুপ্ত বুঝে নিলেন ডাক্তারীর মধ্য দিয়েও মানুষের সেবা এবং নিরন্তর বৈজ্ঞানিক অন্বেষণ - দুটোই অনায়াসে করা যেতে পারে। অমানুষিক পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজেকে গড়ে তোলায় ব্রতী হলেন তিনি। শল্য চিকিৎসায় হাউসটাফ শিপ্ চলতে চলতেই অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে স্নাতকোত্তর প্রবেশিকা পরীক্ষা দিলেন। কিন্তু ইউনিভার্সিটির বিচিত্র কান্ড কারখানার জন্য সে পথে আর বেশি দূর এগোনো হলো না।
তবে মনে তখনও গেঁথে রয়েছে প্রিভেন্টিভ অ্যান্ড সোশ্যাল মেডিসিনের এক রসিক শিক্ষকের কথা, “ডাক্তারি বিদ্যা হলো একটা মানবিক বিদ্যা! আর তা যদি না হয় তাহলে এটা কোন বিদ্যাই না...!” স্বভাবে বামপন্থী, প্যাথলজির এক অধ্যাপক তাকে বারবার বলেছিলেন, “স্পেশালাইজেশন ভালো কিন্তু স্পেশালাইজেশনের ক্রেজ টা ভালো না। এটা সুস্থ সমাজের লক্ষণ না। আমাদের বেশি বেশি করে দরকার জিপি অর্থাৎ গৃহ চিকিৎসক”। কথাটার মর্মোদ্ধার করতে লেগে গিয়েছিল অনেকগুলি বছর। সেই সময়ের কলকাতার এক বিখ্যাত ক্যান্সার সার্জনের অধীনে কাজ শুরু করলেন তিনি। চিকিৎসা বিজ্ঞানের শিল্পকলার সঙ্গে মানবিক বিদ্যা যেখানে একই ধারায় এসে মেলে - এমন একটি জগতের দরজা তার সামনে হঠাৎ খুলে গেল। তবে শিক্ষক সার্জন কিন্তু সতর্কবাণী শুনিয়ে রেখেছিলেন "তোমাকে আন লার্ন এবং রি লার্ন করতে হবে"। অগত্যা কাজের মধ্যে ডুবে থাকা ছাড়া উপায় নেই। নিজেকে ক্রমাগত ভাঙা, গড়া এবং ভাঙার পালা চলছে তো চলছেই।
বাল্যবন্ধু ও চিকিৎসক কিশোর নন্দীর অকৃপণ সহায়তায় শুরু হলো প্র্যাকটিসের তোড়জোর।
দুই বন্ধুর মধ্যে এক অদ্ভুত বোঝাপড়া ছিল এই যে, ডাক্তারিটা যেভাবে ইন্ডাস্ট্রি হয়ে যাচ্ছে এবং দালাল-প্রথায় কলুষিত হচ্ছে, সেখানে খুব সূক্ষ্মভাবে এই কর্পোরেট চিকিৎসা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রোগী-কেন্দ্রিক একটি নতুন ধারণার চোরা স্রোত বইয়ে দিতে হবে। যাকে বলা যায় সাব-ভার্সন বা অন্তর্ঘাত।
ছকে বাধা চিকিৎসার নিয়ম মেনে চলতে চলতে চিন্তার প্রসারতা যেন কোথাও সীমাবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। বিংশ শতকের এক প্রখ্যাত দার্শনিক ইভান ইলিচের বই, মেডিকেল নেমেসিস তার চিন্তার জগতে নতুন বাঁক এনে দিল। অক্লান্ত পড়াশোনা এবং অন্বেষণ এর মাধ্যমে তিনি উপলব্ধি করলেন ক্যান্সার আসলে একটি ইন্ডাস্ট্রিতে পরিণত হয়েছে। ক্যান্সারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে গিয়ে চিকিৎসা ব্যবস্থায় এক ধরনের জঙ্গিবাদ ঢুকে পড়েছে। কিন্তু যুদ্ধ হলে তাদেরই লাভ যারা যুদ্ধাস্ত্র বিক্রি করে। তাই যুদ্ধের অনুষঙ্গ। কিন্তু ক্যান্সারের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ করা যায় না কারণ সেটা “জীবনের গমন পথের একটি বিশেষ প্রকাশ মাত্র”। তার বিরুদ্ধে জঙ্গিপনা মানে জীবনের বিরুদ্ধে একপ্রকার যুদ্ধ ঘোষণা করা। এই অনুভব থেকেই তিনি লিখে ফেললেন সেই সময়ের আলোড়ন সৃষ্টিকারী একটি প্রবন্ধ, দ্যা পলিটিকাল ইকোনমি অফ ব্রেস্ট ক্যান্সার। সেটা প্রকাশিত হলো ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ সোশ্যাল সায়েন্সে’র পত্রিকায়। এই লেখা পড়ে মুগ্ধ হয়ে, তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করলেন ক্যান্সার জগতের এক ব্যতিক্রমী সুমহান চিকিৎসক, অধ্যাপক এবং সুলেখক ডক্টর মনু লীলাধর কোঠারি। তিনি অনুরোধ করলেন তার রচিত একটি বই দা আদার ফেস অফ ক্যান্সার, বাংলায় অনুবাদ করার জন্য। প্রায় দেড় বছরের পরিশ্রমের ফসল হিসেবে, মিত্র ঘোষ থেকে প্রকাশিত হলো ‘ক্যান্সারের অন্য পরিচয়’। এছাড়াও তিনি লিখেছেন ক্যান্সার : পুরনো ভয়, নতুন ভাবনা।
বাণিজ্য বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে প্রবল পেশাজীবী হয়ে ওঠা তার স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিল। সেই কারণে আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল তার জীবনে মরীচিকা মাত্র। অবশ্য এ নিয়ে কোন অভিযোগ ছিল না তার স্ত্রী রুমা দেবীর। কারণ তার নিখাদ ভালোবাসার গুণে জীবনে শান্তি এবং স্বস্তির কোন খামতি ছিল না। অতি সামান্য দক্ষিণার বিনিময়ে বিরাট দায়িত্বের বোঝা কাঁধে নিয়েছিলেন বারাসাত ক্যান্সার হাসপাতালে। ২০০১ সালে সার্জেন স্যারের সঙ্গে যৌথভাবে মেদিনীপুরের এগরায় নিম্নবিত্তের জন্য একটি আদর্শ হাসপাতাল গড়ে তোলার কাজে নেমেছিলেন। সেই সময়ে চলছিল বাম জমানা। সর্বগ্রাসী পার্টির প্রমোদ তরণীতে না চড়লে কোন সামাজিক প্রকল্পই দিনের আলো দেখতে পেত না। পার্টির হোমরা-চোমরা রা এসে বলেছিল, এসব আপনাদের কম্ম নয়। পুরোটাই আমাদের হাতে ছেড়ে দিন। সেই সঙ্গে ছিল দালাল রাজের রমরমা। তাই রণে ভঙ্গ দেয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না।
এর কয়েক বছর পরেই ২০০৪ সাল নাগাদ তিনি যখন ডক্টর মনু কোঠারির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন, তখন থেকেই তার মনোভূমিতে এক বিরাট পরিবর্তনের বাতাস বইতে শুরু করে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের দর্শনকে ঘিরে এতদিনের লালিত অনেক ধারনাই আমূল বদলে যেতে শুরু করে। অসম্ভব প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের অধিকারী ডঃ মনু কোঠারি র ব্যাখ্যায় উঠে আসে বেদান্ত- উপনিষদের কথা। আবার কখনো উদ্ধৃত করেন এঙ্গেলস এর বিখ্যাত রচনা দা নেগেশন অফ দা নেগেশন। নিজে গান্ধীবাদী হওয়া সত্বেও স্মরণ করিয়ে দেন মাও’য়ের সেই অমোঘ উক্তি, আমাদের জ্ঞানের উৎস কি? আবার কখনো বলেন সদর দপ্তরে কামান দাগাও কথাটা ঠিকই ,তবে অভিমুখ ঠিক থাকা চাই। তিনি শেখালেন ক্যান্সার আমাদের দেহ থেকে জন্ম নেয়। সে প্রকৃতির সৃষ্টি এবং "প্রাণ জীবনের অন্য এক রূপ"। তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলেনা। ক্যান্সার বিজ্ঞান যে কর্পোরেটদের হাতে ইতিমধ্যেই ‘একটি বিশালকার বিশ্ব রাজনীতিতে পরিণত হয়েছে, যে রাজনীতি ভালবাসতে শেখায় না ঘৃণা করতে শেখায়’, ডক্টর স্থবির দাশগুপ্তর এই বিশ্বাস আরও মজবুত হয় মনু কোঠারির বিদগ্ধ আলোচনায়। তিনি স্মরণ করিয়ে দিতেন প্রখ্যাত দার্শনিক কার্ল পপারের সেই বিখ্যাত উক্তি, knowledge advances - not by repeating known things but by refuting false dogmas.
সেই সঙ্গে সতর্কবাণীও ছিল- “যাদের হাতে ক্ষমতা আছে তারা তোমার কথা শুনতেও চাইবে না। কিন্তু থামলে তো চলবে না ব্রাদার। এটাই আমাদের কাজ”।
সেই কাজেই আমৃত্যু নিজেকে ব্যস্ত রেখেছিলেন স্থবির দাশগুপ্ত। ২০২০ সালের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয়েছিল তার বই, ‘স্বাস্থ্য নিয়ে বাদ বি সংবাদ’। কর্পোরেট দুনিয়ার প্রবল গ্রাসে তখন গোটা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাটাই একটি প্রবঞ্চনা শিল্পে পরিণত হয়ে চলেছে বিনা বাধায় এবং এবং বিনা কোন উচ্চকিত প্রতিবাদে। সেই অসহনীয় নৈশব্দের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন তিনি। চিকিৎসায় প্রযুক্তির আধিপত্য এবং মানবতাবিরোধী অভিযান সম্পর্কে তিনি যেসব সম্ভাবনার কথা ওই বইটিতে বলেছিলেন তা প্রায় বর্ণে বর্ণে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল কয়েক মাস পরেই আবির্ভূত হওয়া করোনাকালে।
সে ছিল এক অদ্ভুত সময়। বিচিত্র সব স্বাস্থ্যবিধির নিগড়ে বেঁধে ফেলা হয়েছিল মানুষের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবন। চরম বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছিলেন সমাজের সবচেয়ে নিচু তলার মানুষেরা। স্বাস্থ্য নিরাপত্তার অজুহাতে মৌলিক অধিকার পর্যন্ত খর্ব করা হয়েছিল। চিকিৎসক মহলের প্রভাবশালী এবং বলিয়ে-কইয়ে যারা ছিলেন, তারা প্রায় সকলেই সরকারি ভাষ্য কে বিনা প্রশ্নে সমর্থন করেছিলেন।এই কলকাতায়, যেসব গুটিকয় ব্যতিক্রমী চিকিৎসক এর বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন এবং যাদের কণ্ঠস্বর প্রমাণ করেছিল আধুনিক ডাক্তারি থেকে এখনো বিবেক, মানবতাবোধ, যুক্তি এবং কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে যায়নি, তাদের অগ্র-পথিক ছিলেন স্থবির দাশগুপ্ত। গড়ে তুলেছিলেন গ্লোবাল ন্যাশনাল অ্যালায়েন্স ফর পাবলিক হেলথ সংক্ষেপে গ্রাফ। জনস্বাস্থ্য নীতির চর্চায় জনতার মতামত যে আবশ্যিক শর্ত এবং তাদের প্রতিনিধিত্ব অপরিহার্য, এটাই ছিল এই সংগঠন গড়ে তোলার পিছনে মূলভাবনা। সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা এবং অভিভাবক ছিলেন তিনি।
জন-স্বাস্থ্যের নাম করে ভবিষ্যতে আমাদের মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে যে প্রচন্ড আঘাত আসতে চলেছে, সেই বিষয়ে জনগণকে সচেতন করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন তিনি। অধিকার রক্ষা কর্মীদের সঙ্গে যৌথভাবে কাজের সমন্বয়ে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু গত ২৪ শে আগস্ট অনুষ্ঠিত শেষ সভায় অসুস্থতার কারণে তিনি যেতে পারেননি। কয়েকদিন পরেই ভর্তি হয়েছিলেন তার পরিচিত একটি নার্সিংহোমে। পরে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন অন্য একটি বড় হাসপাতালে। সেখানেই তার প্রয়াণ ঘটে ৫ই সেপ্টেম্বর।
অনেক কথাই হয়তো বলার ছিল। তিনি দ্রুত-গতি সময়ের সঙ্গে যেন পাল্লা দিয়ে হাঁটছিলেন। ২০২২ সালে প্রকাশিত হলো দেহ দখলের জৈবিক ও সামাজিক পটভূমি নিয়ে লিখিত তার বই দখলসম্ভবা। এই বছরের (২০২৩) জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয়েছে তার স্মৃতিতে জাগরুক চরিত্র গাঁথা হিসেবে লেখা একটি বই, ‘শীতলপাটি বিছিয়ে যারা’। অনেকেই হয়তো জানেন না, ছড়া কাটতেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। ২০১০ সালে প্রকাশিত 'স্থবিরের ছড়াছড়ি' বইতে তিনি লিখে গিয়েছেন -
ছুটি চাইছো, চাইছো ছুটি
এড়ানো দায় ।
মুগ্ধ হলে, মুখটা কি আর,
ফেরানো যায়।