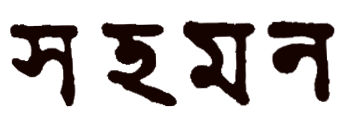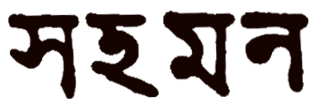গ্রিনল্যান্ডকে কেন্দ্র করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান চাপের মুখে ডেনমার্কের বর্তমান অবস্থা অনেকটা ‘ভস্মে ঘি ঢালার’ মতো। দ্বীপটিতে আরও সৈন্য মোতায়েন এবং ইউরোপীয় মিত্রদের প্রতীকী সমর্থন আদায়ের মধ্য দিয়ে ডেনমার্ক যে আতঙ্ক প্রকাশ করছে, তা মূলত এক ঐতিহাসিক পরিহাস। সার্বভৌমত্ব, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এবং আন্তর্জাতিক আইনের বুলি আজ ডেনিশ রাজনীতিকদের কণ্ঠে অত্যন্ত জরুরি হয়ে উঠেছে। অথচ ট্রাম্পীয় আমল থেকে শুরু হওয়া গ্রিনল্যান্ড দখলের এই মার্কিন আকাঙ্ক্ষা কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়, বরং এটি একটি সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বদর্শনের যৌক্তিক বহিঃপ্রকাশ, যেখানে আন্তর্জাতিক রীতিনীতির চেয়ে কৌশলগত নিয়ন্ত্রণই মুখ্য।
২১ লক্ষ বর্গকিলোমিটারের বেশি আয়তনের গ্রিনল্যান্ড ভৌগোলিক ও কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঐতিহাসিকভাবে ১০ম শতাব্দীতে ভাইকিংদের (ভাইকিংরা ছিল মূলত উত্তর ইউরোপের স্ক্যান্ডিনেভিয়া অঞ্চলের (বর্তমান নরওয়ে, সুইডেন এবং ডেনমার্ক) মানুষ। অষ্টম থেকে একাদশ শতাব্দী (৭৯৩ – ১০৬৬ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত তাদের আধিপত্য ছিল, যে সময়টাকে ইতিহাসে 'ভাইকিং যুগ' বলা হয়) আগমনের মাধ্যমে ইউরোপীয়দের সাথে এর যোগাযোগ শুরু হয় এবং ১৮১৪ সালে এটি ডেনমার্কের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসে। বর্তমানে এর জনসংখ্যা মাত্র ৫৭,০০০-এর কাছাকাছি, যার সিংহভাগই আদিবাসী ইনুইট। গ্রিনল্যান্ডের অর্থনীতি মূলত মাছ ধরা এবং ডেনমার্কের বার্ষিক ভর্তুকির ওপর নির্ভরশীল হলেও, এর ভূগর্ভে থাকা বিশাল খনিজ সম্পদ, বিরল মৃত্তিকা মৌল এবং তেলের ভাণ্ডার একে বিশ্বশক্তির শিকারে পরিণত করেছে। বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বরফ গলতে থাকায় আর্কটিক অঞ্চলে নতুন বাণিজ্যিক পথ ও সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে গ্রিনল্যান্ড এখন দাবার প্রধান ঘুঁটি।
ডেনমার্কের এই মুহূর্তের সংকটটি কেবল বাহ্যিক হুমকির নয়, বরং এটি তাদের নিজস্ব দ্বিমুখী নীতির প্রতিফলন। গত কয়েক দশক ধরে ডেনমার্ক নির্দ্বিধায় সেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বদর্শনকে পুষ্ট করেছে, যা আজ তাদের নিজেদের ওপরই প্রয়োগ করা হচ্ছে। ডেনমার্ক ইরাক আক্রমণে অংশ নিয়েছিল কোনো বৈধ আইনি ম্যান্ডেট ছাড়াই, আফগানিস্তানে দুই দশকের নিষ্ফল যুদ্ধে শামিল হয়েছিল এবং লিবিয়ায় মুয়াম্মার গাদ্দাফিকে ক্ষমতাচ্যুত করতে বিমান হামলায় নেতৃত্ব দিয়েছিল। সিরিয়াতেও ডেনমার্কের পরোক্ষ হস্তক্ষেপ একটি গণ-অভ্যুত্থানকে ভয়াবহ ছায়াযুদ্ধে পরিণত করতে সাহায্য করেছে। তখন সার্বভৌমত্ব বা আন্তর্জাতিক আইনের বুলি ডেনমার্কের নীতিতে অনুপস্থিত ছিল। আজ যখন গ্রিনল্যান্ড নামের নিজস্ব ভূখণ্ড একই ভূ-রাজনৈতিক যুক্তির শিকার, তখন ডেনমার্কের কাছে আন্তর্জাতিক আইন হঠাৎ পবিত্র হয়ে উঠেছে। গাজার ক্ষেত্রে ডেনমার্কের ভূমিকা এই নৈতিক স্খলনকে আরও নগ্ন করে দেয়। ইসরায়েল যখন গাজাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করছে এবং জাতিসংঘ একে ‘গণহত্যা’ হিসেবে চিহ্নিত করার উপক্রম করছে, তখন ডেনিশ নেতৃত্ব নীরব। ডেনমার্কের প্রতিরক্ষা সংস্থাগুলো আজও এফ-৩৫ যুদ্ধবিমানের যন্ত্রাংশ সরবরাহ করছে, যা গাজায় বোমাবর্ষণে ব্যবহৃত হচ্ছে। এমনকি নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক গ্রেপ্তারি পরোয়ানা কার্যকর করার প্রশ্নেও প্রধানমন্ত্রী মেটে ফ্রেডেরিকসেনের অস্পষ্ট অবস্থান প্রমাণ করে যে, ডেনমার্কের কাছে আইন হলো শর্তসাপেক্ষ এবং নীতি হলো নমনীয়। গ্রিনল্যান্ড আজ ডেনমার্কের সামনে একটি আয়না ধরেছে। বছরের পর বছর ধরে সাম্রাজ্যবাদী সহিংসতা যখন অন্য দেশ বা অঞ্চলে ঘটত, ডেনমার্ক তাকে সমর্থন দিয়ে গেছে। তারা ভেবেছিল আইনের এই অবক্ষয় কেবল দূরের কোনো জনপদকে ক্ষতবিক্ষত করবে। কিন্তু আজ তারা বুঝতে পারছে, সাম্রাজ্যবাদের সাথে মৈত্রী সুরক্ষা নিশ্চিত করে না। আর্কটিক অঞ্চলে সার্বভৌমত্বকে পবিত্র মনে করা আর প্যালেস্টাইন বা মধ্যপ্রাচ্যে তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করা—এই দ্বিমুখী নীতি এখন বুমেরাং হয়ে ফিরে আসছে। ডেনমার্ক ও সামগ্রিক ইউরোপের জন্য গ্রিনল্যান্ড আজ কেবল একটি আঞ্চলিক ইস্যু নয়, বরং একটি কঠোর বিচারদিবস। আন্তর্জাতিক আইন কেবল তখনই রক্ষা পায় যখন তা সবার জন্য সমানভাবে প্রয়োগ করা হয়, নতুবা ক্ষমতার পালাবদলে ছোট দেশগুলো তাদের নিজেদের তৈরি করা গর্তেই নিমজ্জিত হয়।
ডেনমার্কের বর্তমান নৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটকে আরও গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, দেশটি আজ তার নিজের তৈরি করা একটি ‘ফ্রাঙ্কেনস্টাইন’ বা দানবের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। গত কয়েক দশকের ডেনিশ পররাষ্ট্রনীতি পর্যালোচনা করলে একটি চরম বৈপরীত্য ধরা পড়ে, যা এখন গ্রিনল্যান্ড ইস্যুতে তাদের অসহায় করে তুলেছে। ডেনমার্ক দীর্ঘকাল ধরে নিজেকে একটি শান্তিপ্রিয় এবং আইনের শাসনে বিশ্বাসী রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বদরবারে তুলে ধরেছে। কিন্তু বাস্তবে, ওয়াশিংটনের প্রতিটি যুদ্ধংদেহী পদক্ষেপে কোপেনহেগেন ছিল প্রথম সারির সহযোগী। ২০০৩ সালে ইরাক আক্রমণের সময় যখন কোনো আন্তর্জাতিক বৈধতা ছিল না, তখনও ডেনমার্ক সেই আগ্রাসনে শামিল হয়ে প্রমাণ করেছিল যে, তাদের কাছে ‘সার্বভৌমত্ব’ বিষয়টি কেবল পশ্চিমা মিত্রদের জন্য সংরক্ষিত, গ্লোবাল সাউথ বা মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর জন্য নয়। আফগানিস্তানে দুই দশকের রক্তক্ষয়ী এবং শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ যুদ্ধে ডেনমার্কের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল মূলত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের পাহারাদারি। লিবিয়া এবং সিরিয়ার ক্ষেত্রে ডেনমার্কের ভূমিকা আরও প্রশ্নবিদ্ধ। লিবিয়ায় ‘গণতন্ত্র রক্ষা’র নামে ন্যাটো যে বিমান হামলা চালিয়েছিল, তাতে ডেনিশ বিমানবাহিনী অগ্রণী ভূমিকা পালন করে একটি স্থিতিশীল রাষ্ট্রকে গৃহযুদ্ধের নরককুণ্ডে পরিণত করেছে। সিরিয়াতে ডেনমার্কের হস্তক্ষেপ সরাসরি একটি আঞ্চলিক অস্থিরতাকে দীর্ঘস্থায়ী প্রক্সি যুদ্ধে রূপ দিয়েছে, যার ফলস্বরূপ লক্ষ লক্ষ মানুষ উদ্বাস্তু হয়েছে। তখন ডেনমার্ক একবারও ভাবেনি যে, বলপ্রয়োগের মাধ্যমে সীমান্ত বা শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের এই সংস্কৃতি একদিন তাদের নিজেদের বাড়ির দরজায় অর্থাৎ গ্রিনল্যান্ডে কড়া নাড়বে।আজ যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একই ‘কৌশলগত প্রয়োজনীয়তা’ বা ‘নিরাপত্তা স্বার্থ’-এর দোহাই দিয়ে গ্রিনল্যান্ডের ওপর থাবা বসাতে চাইছে, তখন ডেনমার্ক হঠাৎ করে আন্তর্জাতিক আইনের পবিত্রতা এবং ছোট দেশগুলোর আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার নিয়ে চিৎকার শুরু করেছে। এটি কেবল দ্বিচারিতা নয়, এটি একটি বড় শিক্ষা যে—আন্তর্জাতিক আইন যখন কেবল শক্তিশালী দেশের স্বার্থে ব্যবহৃত হয়, তখন তা সময়ের আবর্তে রক্ষকের পরিবর্তে ভক্ষক হয়ে দাঁড়ায়। ডেনমার্ক এখন যে ভয়ের রাজত্বে বাস করছে, তা মূলত তাদের নিজেদের সাহায্যেই গড়ে তোলা একটি নিয়মহীন বিশ্বব্যবস্থার ফল। গ্রিনল্যান্ড আজ ডেনমার্কের জন্য কেবল একটি ভূখণ্ড হারানোর ভয় নয়, বরং তাদের দশকের পর দশক ধরে চলা সুবিধাবাদী রাজনীতির একটি করুণ পরিণতি।
ডেনমার্কের এই দ্বিমুখী নীতির গভীরতা বুঝতে হলে উত্তর ইউরোপের অন্যান্য ছোট রাষ্ট্রগুলোর (যেমন নরওয়ে, নেদারল্যান্ডস বা বেলজিয়াম) সাথে এর তুলনা করা প্রয়োজন। এটি দেখায় যে ডেনমার্ক কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং একটি সামগ্রিক ইউরোপীয় প্রবণতার অংশ।নরওয়ের অবস্থান ডেনমার্কের মতোই স্পর্শকাতর । নরওয়েও ন্যাটোর একনিষ্ঠ সদস্য এবং রাশিয়ার সাথে তাদের সীমান্ত থাকায় তারা ঐতিহাসিকভাবেই মার্কিন নিরাপত্তার ওপর নির্ভরশীল। তবে নরওয়ের সাথে ডেনমার্কের পার্থক্য হলো আর্কটিক অঞ্চলে তাদের সরাসরি সম্পৃক্ততা। ডেনমার্কের মতো নরওয়েও লিবিয়া এবং আফগানিস্তান যুদ্ধে সক্রিয় ছিল। তারাও ‘মানবিক হস্তক্ষেপের’ নামে সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘনের প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়েছে। নরওয়ে তাদের জ্বালানি সম্পদ এবং আর্কটিক সীমান্ত রক্ষায় রাশিয়ার সাথে একটি সূক্ষ্ম ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু ডেনমার্ক গ্রিনল্যান্ডকে ‘নিরাপদ’ ভেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে কার্যত তার প্রতিরক্ষা তুলে দিয়েছিল, যা এখন বুমেরাং হয়ে দাঁড়িয়েছে।অন্যদিকে, নেদারল্যান্ডসের হেগ শহরকে বলা হয় ‘আন্তর্জাতিক আইনের রাজধানী’। অথচ এই দেশটি যখন মার্কিন নেতৃত্বাধীন ইরাক যুদ্ধে রাজনৈতিক সমর্থন দিয়েছিল, তখন তা ছিল আন্তর্জাতিক আইনের চরম লঙ্ঘন। ডেনমার্কের মতো নেদারল্যান্ডসও এখন গাজা ইস্যুতে আইনি প্যাঁচে পড়েছে। সম্প্রতি ডেনমার্কের আদালত যেমন এফ-৩৫ যন্ত্রাংশ রপ্তানি নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়েছে, নেদারল্যান্ডসের আদালতও একইভাবে সরকারকে নির্দেশ দিয়েছিল ইসরায়েলে যুদ্ধবিমানের অংশ পাঠানো বন্ধ করতে।নেদারল্যান্ডস এবং ডেনমার্ক—উভয় রাষ্ট্রই দেখিয়েছে যে ছোট দেশগুলো যখন শক্তিশালী রাষ্ট্রের অপরাধে মৌন সম্মতি দেয়, তখন তারা আসলে সেই কাঠামোকেই দুর্বল করে যা তাদের নিজেদের সুরক্ষার গ্যারান্টি দেয়। ডেনমার্কের এই সংকট ইউরোপের বাকি ছোট রাষ্ট্রগুলোর জন্য একটি সতর্কবার্তা। তারা যখন ভাবত আন্তর্জাতিক আইন কেবল 'অন্যদের' শাসনের জন্য, তখন তারা অজান্তেই এমন এক বিশ্বব্যবস্থা তৈরি করেছে যেখানে 'জোর যার মুলুক তার'। গ্রিনল্যান্ড আজ কেবল ডেনমার্কের একার সমস্যা নয়; এটি সেই সব ছোট রাষ্ট্রের নিয়তি যারা ক্ষমতার মোহে নিজের আদর্শিক ভিত্তি বিসর্জন দিয়েছে।
গ্রিনল্যান্ডকে কেন্দ্র করে বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক লড়াইটি আসলে একটি ‘নতুন শীতল যুদ্ধ’, যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার লক্ষ্য হলো আর্কটিক অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া। ডেনমার্ক এই দুই দানবের মাঝে পড়ে এখন তার অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে গ্রিনল্যান্ড কেবল এক টুকরো ভূখণ্ড নয়, বরং এটি উত্তর আমেরিকার নিরাপত্তার প্রথম দেওয়াল। গ্রিনল্যান্ডের পিতুফিক (বা থুলি) এয়ার বেস হলো আমেরিকার দূরতম উত্তরের সামরিক ঘাঁটি। এখানে রয়েছে অত্যাধুনিক রাডার ব্যবস্থা, যা রাশিয়া থেকে আসা যেকোনো মিসাইল বা ক্ষেপণাস্ত্র হামলা শনাক্ত করতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভয় হলো, যদি তারা গ্রিনল্যান্ডের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ না পায়, তবে রাশিয়া বা চীন সেখানে প্রভাব বিস্তার করে আমেরিকার ‘পিছনের দরজা’ খুলে দিতে পারে।রাশিয়া গত এক দশকে আর্কটিক অঞ্চলে তাদের সামরিক উপস্থিতি অভাবনীয়ভাবে বাড়িয়েছে। তারা সেখানে সোভিয়েত আমলের পরিত্যক্ত ঘাঁটিগুলো পুনরায় সচল করেছে এবং অত্যাধুনিক আইসব্রেকার (বরফ কাটার জাহাজ) বহর তৈরি করেছে। রাশিয়ার লক্ষ্য হলো ‘নর্দান সি রুট’ নিয়ন্ত্রণ করা, যা সুয়েজ খালের বিকল্প হিসেবে এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে বাণিজ্যিক দূরত্ব কমিয়ে দেবে। গ্রিনল্যান্ড এই রুটের ঠিক পাশেই অবস্থিত হওয়ায় রাশিয়াও এখানে ডেনমার্কের দুর্বলতার সুযোগ নিতে চায়। লড়াইয়ে তৃতীয় খেলোয়াড় হিসেবে আবির্ভাব ঘটেছে চীনের। চীন নিজেকে একটি ‘আর্কটিক-সংলগ্ন রাষ্ট্র’ হিসেবে দাবি করে গ্রিনল্যান্ডের খনিজ ও অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগ করতে চেয়েছিল। ডেনমার্ক যখন মার্কিন চাপে চীনের সেই বিনিয়োগ প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়, তখন থেকেই ডেনমার্কের ওপর মার্কিন নির্ভরতা একপ্রকার ‘বাধ্যতামূলক’ হয়ে দাঁড়ায়।একটি কৌশলগত বিশ্লেষণে দেখা যায়, ডেনমার্ক এক অদ্ভুত সংকটে আটকা পড়েছে। ডেনমার্ক তার নিরাপত্তার জন্য আমেরিকার ওপর নির্ভরশীল, কিন্তু সেই আমেরিকাই এখন ডেনমার্কের সার্বভৌমত্ব (গ্রিনল্যান্ড) গ্রাস করতে চাইছে। বরফ গলার ফলে গ্রিনল্যান্ডের সম্পদ আহরণ সহজ হচ্ছে, যা এই দ্বীপটিকে আরও বেশি ‘লোভনীয়’ করে তুলছে। এটি ডেনমার্কের জন্য আশীর্বাদ হওয়ার বদলে রাজনৈতিক অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদি ডেনমার্ক তার সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে চায়, তবে তাদের কেবল সামরিক শক্তি বাড়ালে চলবে না, বরং গ্রিনল্যান্ডের স্থানীয় ইনুইট জনগোষ্ঠীর আস্থা অর্জন করতে হবে। আমেরিকা ‘আদিবাসীদের অধিকার’ বা ‘অর্থনৈতিক মুক্তির’ দোহাই দিয়ে গ্রিনল্যান্ডকে ডেনমার্ক থেকে আলাদা করার উস্কানি দিয়ে যাচ্ছে। গ্রিনল্যান্ড এখন আর কেবল ডেনমার্কের অংশ নয়, এটি বিশ্ব শক্তির ভারসাম্যের একটি কেন্দ্রবিন্দু। ডেনমার্ক যদি অতীতে অন্যান্য দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সোচ্চার হতো, তবে আজ আন্তর্জাতিক মঞ্চে তারা আরও শক্তিশালী নৈতিক অবস্থান পেত। এখন তাদের নিজেদের অস্তিত্বই বড় বড় শক্তির দয়ার ওপর নির্ভর করছে।
গ্রিনল্যান্ডের আদিবাসী ইনুইট (Inuit) জনগোষ্ঠীর স্বাধীনতা আন্দোলন এবং এতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত ভূমিকা বর্তমান ভূ-রাজনীতির একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর অধ্যায়। ডেনমার্কের জন্য এটি ‘ছেঁড়া চুলে খোঁপা বাঁধা’র মতো— একদিকে ডেনমার্ককে দেখাতে হচ্ছে তারা ইনুইটদের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, অন্যদিকে ভয় পাচ্ছে যে এই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাই হয়তো আমেরিকার জন্য দ্বীপটি দখলের পথ প্রশস্ত করবে।আজকের গ্রিনল্যান্ডে ইনুইট ও সংখ্যালঘু ভাইকিংদের ঐতিহাসিক সম্পর্কটি একটি বড় রাজনৈতিক অস্ত্র। ডেনমার্ক (ভাইকিংদের উত্তরসূরি) দাবি করে যে তারাও এই ভূমির প্রাচীন অংশীদার। ইনুইটরা দাবি করে যে, ভাইকিংরা ছিল অস্থায়ী বসতি স্থাপনকারী যারা টিকে থাকতে পারেনি, কিন্তু ইনুইটরাই এই চরম পরিবেশে হাজার বছর ধরে গ্রিনল্যান্ডকে রক্ষা করে আসছে। গ্রিনল্যান্ডের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৯০ শতাংশই ইনুইট। ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত গ্রিনল্যান্ড ছিল ডেনমার্কের একটি উপনিবেশ। এরপর এটি একটি ডেনিশ কাউন্টিতে পরিণত হয় এবং ১৯৭৯ সালে ‘হোম রুল’ বা সীমিত স্বায়ত্তশাসন পায়। ২০০৯ সালে একটি গণভোটের মাধ্যমে গ্রিনল্যান্ড ‘সেলফ-রুল’ লাভ করে, যার ফলে তারা অভ্যন্তরীণ প্রায় সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা পায়। তবে প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্রনীতি এখনও ডেনমার্কের নিয়ন্ত্রণে। ইনুইটদের বড় অংশ মনে করে, ডেনমার্কের বার্ষিক ভর্তুকি (প্রায় ৬০০ মিলিয়ন ডলার) ছাড়াই তারা খনিজ সম্পদ ও পর্যটন খাতের আয়ের ওপর ভিত্তি করে একটি পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকতে পারবে।মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি ডেনমার্কের সার্বভৌমত্বে আঘাত না করে বরং গ্রিনল্যান্ডের স্থানীয় জনগণের মধ্যে ‘বন্ধুত্ব’ বাড়ানোর নীতি গ্রহণ করেছে। ২০১৯ সালে যখন ডোনাল্ড ট্রাম্প গ্রিনল্যান্ড কেনার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তখন ডেনমার্ক একে ‘হাস্যকর’ বলে উড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু আমেরিকা এরপর কৌশল পরিবর্তন করে।১৯৫৩ সালে বন্ধ হয়ে যাওয়ার দীর্ঘ ৬৭ বছর পর প্রথমবার আমেরিকা গ্রিনল্যান্ডের রাজধানী নুউকে (Nuuk) ১০ জুন, ২০২০-তে তাদের কনস্যুলেট পুনরায় চালু করেছে। আমেরিকা ডেনমার্ককে এড়িয়ে সরাসরি গ্রিনল্যান্ডের শিক্ষা, জ্বালানি ও খনিজ খাতে অনুদান ও বিনিয়োগের প্রস্তাব দিচ্ছে।অনেক বিশ্লেষক মনে করেন, আমেরিকা তলে তলে ইনুইট নেতাদের এই বার্তা দিচ্ছে যে— “তোমরা ডেনমার্ক থেকে আলাদা হও, আমরা তোমাদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করব।” অর্থাৎ, ডেনমার্কের নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে গ্রিনল্যান্ড শেষ পর্যন্ত আমেরিকার একটি ‘প্রোটেক্টরেট’ বা আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হতে পারে।ডেনমার্ক এখন এক অদ্ভুত সংকটে। তারা যদি ইনুইটদের স্বাধীনতার পথে বাধা দেয়, তবে আন্তর্জাতিক মহলে তারা ‘উপনিবেশবাদী’ হিসেবে চিহ্নিত হবে। আবার যদি তারা স্বাধীনতা দিয়ে দেয়, তবে গ্রিনল্যান্ড সরাসরি আমেরিকার কক্ষপথে চলে যাবে। ডেনমার্কের এই দ্বিধাটিই আমেরিকা ব্যবহার করছে। তারা ইনুইটদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের সমর্থক হিসেবে নিজেকে জাহির করে আসলে ডেনমার্ককে আর্কটিক অঞ্চল থেকে সরিয়ে দিতে চায়।আমেরিকা চায় গ্রিনল্যান্ডকে একটি স্বাধীন কিন্তু সম্পূর্ণ নির্ভরশীল রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে, অনেকটা পুয়ের্তো রিকো বা গুয়ামের মতো। এতে আমেরিকার সুবিধা হলো, ন্যাটোর জটিল নিয়ম না মেনে তারা সরাসরি সেখানে বড় বড় সামরিক ঘাঁটি ও মিসাইল সাইলো স্থাপন করতে পারবে। গ্রিনল্যান্ডের বিরল মৃত্তিকা মৌলের (Rare Earth Elements) ওপর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ পাবে, যা চীনের ওপর আমেরিকার নির্ভরতা কমাবে। ইনুইটদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা যতটা না জাতীয়তাবাদী, তার চেয়ে বেশি ভূ-রাজনৈতিক সুযোগের শিকার। ডেনমার্ক তার অতীতের সাম্রাজ্যবাদী আচরণের কারণে আজ নৈতিকভাবে দুর্বল। ডেনমার্ক যে সার্বভৌমত্বের বুলি আওড়াচ্ছে, তা গ্রিনল্যান্ডের আদিবাসীদের কাছে অনেক সময় ‘ভণ্ডামি’ মনে হয়, কারণ ডেনমার্ক নিজেই অতীতে অন্য দেশের সার্বভৌমত্ব ধ্বংসে আমেরিকাকে সাহায্য করেছে। গ্রিনল্যান্ড শেষ পর্যন্ত ডেনমার্কের অধীনে থাকবে নাকি আমেরিকার নতুন ‘নক্ষত্র’ হিসেবে উদিত হবে, তা নির্ভর করছে এই বিশাল দ্বীপের বরফ কত দ্রুত গলে এবং ইনুইটরা আমেরিকার এই ‘মরণফাঁদ’ চিনতে পারে কি না তার ওপর।
গ্রিনল্যান্ডের খনিজ সম্পদ বর্তমান বিশ্বের ‘সবুজ জ্বালানি বিপ্লব’ এবং প্রযুক্তিগত যুদ্ধের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। কেন আমেরিকা বা চীনের মতো পরাশক্তিগুলো বরফে ঢাকা এই দ্বীপের জন্য মরিয়া ? স্মার্টফোন, ইলেকট্রিক গাড়ির ব্যাটারি, উইন্ড টারবাইন এবং উন্নত যুদ্ধবিমান (যেমন F-35) তৈরির জন্য ১৭টি বিশেষ খনিজ উপাদান অপরিহার্য, যাকে বলা হয় রেয়ার আর্থ এলিমেন্ট। বর্তমানে বিশ্বের প্রায় ৯০% রেয়ার আর্থ নিয়ন্ত্রণ করে চীন।দক্ষিণ গ্রিনল্যান্ডের কাভানেফিয়েল্ড (Kvanefjeld) অঞ্চলে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ রেয়ার আর্থ ভাণ্ডার রয়েছে। আমেরিকা চায় এই খনিগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে, যাতে প্রযুক্তির জন্য তাদের আর চীনের ওপর নির্ভর করতে না হয়।গ্রিনল্যান্ডে প্রচুর পরিমাণে ইউরেনিয়াম এবং লিথিয়াম রয়েছে। লিথিয়ামকে বলা হয় ‘সাদা সোনা’ (White Gold), কারণ টেসলার মতো কোম্পানিগুলোর বৈদ্যুতিক গাড়ির ব্যাটারি তৈরিতে এটি অপরিহার্য। অন্যদিকে, পারমাণবিক শক্তির জন্য ইউরেনিয়াম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গ্রিনল্যান্ডের এই সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকা মানে ভবিষ্যতের বিশ্ব জ্বালানি বাজারের চাবিকাঠি হাতে থাকা। গ্রিনল্যান্ডের খনিজ সম্পদের অবস্থানগুলো মূলত উপকূলীয় অঞ্চলে, যা বরফ গলার ফলে এখন আগের চেয়ে অনেক সহজে উত্তোলনযোগ্য হয়ে উঠছে।গ্রিনল্যান্ডের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে জিংক এবং সীসা ।পশ্চিম উপকূলে তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের বিশাল মজুত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।দক্ষিণ গ্রিনল্যান্ড রেয়ার আর্থ এবং ইউরেনিয়ামের প্রধান উৎস। এই সম্পদগুলো নিয়ে গত কয়েক বছর ধরে একটি তীব্র ছায়াযুদ্ধ চলছে। চীন শুরুতে গ্রিনল্যান্ডের খনিগুলোতে বড় বিনিয়োগের চেষ্টা করেছিল। তাদের লক্ষ্য ছিল খনিগুলো কিনে নিয়ে বৈশ্বিক সাপ্লাই চেইন নিজেদের কবজায় রাখা। আমেরিকা বুঝতে পেরেছিল যে চীন গ্রিনল্যান্ডে ঢুকে পড়লে আমেরিকার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। তাই তারা ডেনমার্কের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে চীনা বিনিয়োগ বন্ধ করে দেয়। এখন আমেরিকা সরাসরি ‘গ্রিনল্যান্ড মিনারেলস রিসোর্স ইনিশিয়েটিভ’-এর মাধ্যমে সেখানে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। এই বাস্তবতায় ডেনমার্ক এক অদ্ভুত সংকটে পড়েছে। গ্রিনল্যান্ড যদি এই সম্পদগুলো আহরণ করা শুরু করে, তবে তারা আর্থিকভাবে এতটাই শক্তিশালী হবে যে তাদের আর ডেনমার্কের বার্ষিক ভর্তুকির প্রয়োজন হবে না। অর্থাৎ, খনিজ সম্পদ মানেই গ্রিনল্যান্ডের স্বাধীনতা। ডেনমার্ক তাই একদিকে পরিবেশ রক্ষার দোহাই দিয়ে খনি উত্তোলনে কড়াকড়ি করতে চায়, আবার অন্যদিকে আমেরিকার চাপও উপেক্ষা করতে পারে না।গ্রিনল্যান্ডের ইনুইটদের মধ্যে এই খনি নিয়ে মতভেদ আছে। একদল মনে করে খনিগুলো খুললে কর্মসংস্থান হবে এবং স্বাধীনতা আসবে। অন্যদল মনে করে খনি উত্তোলনের ফলে তাদের আদিম পরিবেশ এবং মাছ ধরার ঐতিহ্য নষ্ট হবে। আমেরিকা এই বিভাজনকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করতে চায়।গ্রিনল্যান্ড এখন আর কেবল মাছ ধরার দ্বীপ নেই; এটি আক্ষরিক অর্থেই একটি ‘খনিজ সোনার খনি’। আমেরিকার গ্রিনল্যান্ড দখলের ইচ্ছা কোনো পাগলামি নয়, বরং এটি একটি সুদূরপ্রসারী অর্থনৈতিক ও সামরিক চাল। ডেনমার্ক যদি গ্রিনল্যান্ডের এই সম্পদের সঠিক ব্যবস্থাপনা করতে না পারে এবং ইনুইটদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত না করে, তবে খনিজ সম্পদের এই টানাপোড়েনই ডেনমার্কের হাত থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গ্রিনল্যান্ডকে চিরতরে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে।
গ্রিনল্যান্ডকে কেন্দ্র করে ডেনমার্কের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতেও এখন এক উত্তাল সময় চলছে। ডেনিশ পার্লামেন্ট (Folketinget) এবং জনমতের মধ্যে এই সংকট নিয়ে গভীর মেরুকরণ তৈরি হয়েছে। একদিকে ডেনমার্ক তাদের ঐতিহাসিক মর্যাদা রক্ষা করতে চাইছে, অন্যদিকে বাস্তব রাজনীতি তাদের এক কঠিন প্রাচীরের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।ডেনমার্কের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গ্রিনল্যান্ড নিয়ে বিভাজন এখন স্পষ্ট।দক্ষিণপন্থী ডেনিশ পিপলস পার্টির মতো দলগুলো মনে করে, ডেনমার্ক সরকার আমেরিকার সামনে অত্যন্ত নমনীয় অবস্থান নিয়েছে। তাদের মতে, ডেনমার্ক যদি নিজের ভূখণ্ড রক্ষা করতে না পারে, তবে ন্যাটোর সদস্য হিসেবে তাদের আত্মসম্মান ধুলোয় মিশে যাবে। তারা গ্রিনল্যান্ডে আরও বেশি ডেনিশ সামরিক বাজেট বরাদ্দের দাবি তুলছে। সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট বা বর্তমান সরকারি জোট মনে করে, আমেরিকার সাথে সরাসরি সংঘাতে যাওয়া হবে আত্মঘাতী। তারা কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা মেটাতে চায়। তবে তাদের ওপর চাপ বাড়ছে যে, তারা কেন আমেরিকার কাছে গ্রিনল্যান্ডের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ করে দিচ্ছে। ডেনমার্কের সাধারণ মানুষের মধ্যে গ্রিনল্যান্ড নিয়ে আগে যে উদাসীনতা ছিল, তা এখন ‘জাতীয় আতঙ্কে’ পরিণত হয়েছে। ডেনিশ নাগরিকরা প্রথাগতভাবে আমেরিকাকে পরম মিত্র হিসেবে দেখে অভ্যস্ত। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আমেরিকার ‘গ্রিনল্যান্ড কেনা’ বা সেখানে ডেনমার্কের অনুমতি ছাড়াই হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা সাধারণ ডেনিশদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। তারা মনে করছে, আমেরিকা আর রক্ষক নয়, বরং এক আগ্রাসী শক্তিতে পরিণত হয়েছে। আসার কথা ডেনমার্কের তরুণ প্রজন্মের একটি অংশ এখন সরকারের দ্বিমুখী নীতি নিয়ে সোচ্চার। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও বুদ্ধিজীবী মহলে আলোচনা হচ্ছে যে— ডেনমার্ক যখন ইরাক বা লিবিয়া ধ্বংস করতে আমেরিকাকে সাহায্য করেছিল, তখন তারা ভাবেনি যে একই 'গায়ের জোরের নীতি' তাদের নিজেদের ওপর প্রয়োগ করা হবে। তবে সবচেয়ে বড় উত্তেজনা তৈরি হয়েছে ডেনমার্ক এবং গ্রিনল্যান্ডের জনগণের মধ্যকার সম্পর্কে।ডেনিশ জনগণ ভয় পায় যে গ্রিনল্যান্ড যদি স্বাধীন হয়ে যায়, তবে ডেনমার্ক তার বৈশ্বিক গুরুত্ব হারাবে এবং একটি সাধারণ ছোট ইউরোপীয় দেশে পরিণত হবে। গ্রিনল্যান্ডের মানুষ মনে করছে ডেনমার্ক তাদের ব্যবহার করছে কেবল দর কষাকষির জন্য। ডেনিশ পার্লামেন্টে যখন গ্রিনল্যান্ড নিয়ে আলোচনা হয়, তখন অনেক সময় গ্রিনল্যান্ডের প্রতিনিধিরা অভিযোগ করেন যে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। ডেনিশ পার্লামেন্ট সম্প্রতি একটি নতুন ‘Foreign Investment Screening Act’ পাস করেছে। এর উদ্দেশ্য ছিল চীনা বিনিয়োগ আটকানো, কিন্তু বর্তমানে এটি আমেরিকার বিরুদ্ধেও ব্যবহার করা যাবে কিনা তা নিয়ে বিতর্ক চলছে। ডেনমার্ক এখন এমন এক আইনি ফাঁদে পড়েছে যেখানে এক মিত্রকে (চীন) আটকাতে গিয়ে অন্য মিত্রের (আমেরিকা) কাছে বন্দি হয়ে পড়ছে।ডেনমার্কের জনমত এখন এক চরম দোটানায়। তারা বুঝতে পারছে যে আন্তর্জাতিক আইন বা সার্বভৌমত্বের যে বুলিতে তারা বিশ্বাস করত, তা আজ অর্থহীন হয়ে পড়ছে। গ্রিনল্যান্ড ইস্যুটি ডেনমার্কের সাধারণ মানুষের কাছে কেবল রাজনীতির বিষয় নয়, এটি তাদের জাতীয় অহংবোধে এক বিশাল আঘাত।
ডেনিশ পার্লামেন্টের অভ্যন্তরীণ বিতর্কের মূল নির্যাস হলো— ডেনমার্ক কি কেবল আমেরিকার একটি ‘আজ্ঞাবহ প্রদেশ’ হয়ে থাকবে, নাকি তারা ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাহায্য নিয়ে একটি স্বতন্ত্র অবস্থান তৈরি করবে? কিন্তু সমস্যা হলো, ইউরোপীয় ইউনিয়নও এই ইস্যুতে ডেনমার্ককে কেবল ‘প্রতীকী সমর্থন’ দিচ্ছে, কারণ জার্মানি বা ফ্রান্সের মতো দেশগুলোও এই আর্কটিক রাজনীতিতে নিজেদের স্বার্থ খুঁজছে। ডেনমার্কের এই চরম সংকটে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (EU) ভূমিকা অনেকটা ‘ধরি মাছ না ছুঁই পানি’র মতো। আপাতদৃষ্টিতে ব্রাসেলস ডেনমার্কের সার্বভৌমত্বের প্রতি সমর্থন জানালেও, বাস্তবে ফ্রান্স বা জার্মানি কেন সরাসরি আমেরিকার বিরুদ্ধে গিয়ে ডেনমার্কের পাশে দাঁড়াচ্ছে না, তার পেছনে রয়েছে গভীর ভূ-রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কারণ। ইউরোপীয় ইউনিয়নের বড় দেশগুলো গ্রিনল্যান্ডকে কেবল ডেনমার্কের অভ্যন্তরীণ বিষয় হিসেবে দেখে না। ফ্রান্স এবং জার্মানি উভয়েই আর্কটিক অঞ্চলে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে চায়। ফ্রান্স নিজেকে একটি বৈশ্বিক শক্তি হিসেবে মনে করে। তারা মনে করে ডেনমার্ক যদি গ্রিনল্যান্ডের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারায়, তবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন হিসেবে সেখানে সরাসরি হস্তক্ষেপ করার একটি সুযোগ তৈরি হতে পারে। ডেনমার্ককে অতিরিক্ত সাহায্য করার বদলে ফ্রান্স চাইবে গ্রিনল্যান্ড যেন ‘ইউরোপীয় কনসোর্টিয়াম’-এর অধীনে আসে, কেবল ডেনমার্কের অধীনে নয়। জার্মানির শিল্পখাত গ্রিনল্যান্ডের খনিজ সম্পদের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল হতে চায়। তারা আমেরিকার সাথে সংঘাতে গিয়ে এই সুযোগ হারাতে রাজি নয়। ইউরোপের অধিকাংশ দেশ ন্যাটোর মাধ্যমে তাদের নিরাপত্তার জন্য আমেরিকার ওপর নির্ভরশীল। জার্মানি বা ফ্রান্স যদি গ্রিনল্যান্ড ইস্যুতে ডেনমার্কের পক্ষে কড়া অবস্থান নেয়, তবে তা ন্যাটোর ঐক্যে ফাটল ধরাতে পারে। ইউক্রেন যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রাশিয়ার মোকাবিলা করতে ইউরোপের দেশগুলো এখন আমেরিকার সাথে কোনো ধরনের বড় বিবাদে জড়াতে চাইছে না। ডেনমার্কের গ্রিনল্যান্ড রক্ষা করার চেয়ে তাদের কাছে ন্যাটোর সংহতি রক্ষা করা বেশি জরুরি। ইউরোপীয় ইউনিয়নের কোনো নিজস্ব সেনাবাহিনী নেই। ফলে আমেরিকার মতো একটি সামরিক মহাশক্তির বিরুদ্ধে ডেনমার্ককে সুরক্ষা দেওয়ার মতো বাস্তব ক্ষমতা ইইউ-এর নেই। ডেনমার্ক নিজেই ইইউ-এর প্রতিরক্ষা নীতির অনেক ক্ষেত্রে ‘অপট-আউট’ (Opt-out) করে রেখেছিল দীর্ঘকাল। এখন বিপদে পড়ে ইইউ-এর সাহায্য চাওয়াটাকে অনেক ইউরোপীয় নেতা ডেনমার্কের ‘সুবিধাবাদ’ হিসেবে দেখছেন। ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ প্রায়ই ইউরোপের ‘কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন’-এর কথা বলেন। কিন্তু গ্রিনল্যান্ডের ক্ষেত্রে ডেনমার্ককে সাহায্য করার মানে হলো সরাসরি ওয়াশিংটনের সাথে টক্কর দেওয়া। ইউরোপীয় দেশগুলো জানে যে, গ্রিনল্যান্ডে আমেরিকার স্বার্থ এতটাই গভীর যে সেখানে ডেনমার্কের পক্ষ নেওয়া মানে হলো নিজের দেশের অর্থনীতি ও নিরাপত্তাকে ঝুঁকিতে ফেলা।বর্তমানে ইউরোপের পুরো মনোযোগ ইউক্রেন এবং গাজা সংকটের ওপর। ডেনমার্ক যেমন গাজা ইস্যুতে ইসরায়েল ও আমেরিকার সুরে সুর মিলিয়ে চলেছে, তেমনি অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলোও একই পথের পথিক। ফলে ডেনমার্ক যখন এখন নিজের সার্বভৌমত্বের জন্য হাহাকার করছে, তখন বাকি ইউরোপীয় দেশগুলো একে কেবল একটি ‘আঞ্চলিক সীমান্ত বিতর্ক’ হিসেবে হালকা করে দেখছে। ডেনমার্ক আজ একা। ইউরোপীয় ইউনিয়ন কেবল একটি ‘প্রতীকী ঢাল’ হিসেবে কাজ করছে, কিন্তু আমেরিকার তলোয়ার ঠেকানোর শক্তি বা ইচ্ছা তাদের নেই। ফ্রান্স ও জার্মানির নিষ্ক্রিয়তা প্রমাণ করে যে, বড় শক্তির খেলায় ছোট দেশগুলোর সার্বভৌমত্ব সবসময়ই দরকষাকষির পণ্য। ডেনমার্ক যে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার অংশ হিসেবে এতদিন অন্য দেশের ওপর আগ্রাসন সমর্থন করেছে, সেই ব্যবস্থাই আজ তাকে নিঃসঙ্গ করে দিয়েছে।
ডেনমার্ক যখন ওয়াশিংটন এবং ব্রাসেলস—উভয় দিক থেকেই আশানুরূপ সাড়া পাচ্ছে না, তখন আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনীতির দাবার বোর্ডে নতুন কিছু সমীকরণ উঁকি দিচ্ছে। এর মধ্যে রাশিয়ার তথাকথিত ‘শান্তি প্রস্তাব’ এবং নর্ডিক কাউন্সিলের মাধ্যমে একটি আঞ্চলিক জোট গঠনের চেষ্টা অন্যতম।রাশিয়া খুব ভালো করেই জানে যে গ্রিনল্যান্ড নিয়ে ডেনমার্ক এবং আমেরিকার মধ্যে ফাটল তৈরি হয়েছে। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে মস্কো ডেনমার্ককে একটি পরোক্ষ ‘শান্তি ও নিরপেক্ষতা’র প্রস্তাব দিতে পারে। রাশিয়া প্রচার করতে পারে যে, ডেনমার্ক যদি গ্রিনল্যান্ডকে একটি ‘অসামরিক অঞ্চল’ (Demilitarized Zone) হিসেবে ঘোষণা করে এবং মার্কিন ঘাঁটি সরিয়ে দেয়, তবে রাশিয়া সেখানে কোনো আক্রমণ করবে না এবং ডেনমার্কের সার্বভৌমত্বকে স্বীকৃতি দেবে।এটি আসলে ডেনমার্ককে ন্যাটো থেকে বিচ্ছিন্ন করার একটি কৌশল। রাশিয়া জানে ডেনমার্ক এই প্রস্তাব গ্রহণ করবে না, কিন্তু এই আলোচনার মাধ্যমেই তারা ডেনিশ রাজনীতিতে আমেরিকা-বিরোধী জনমতকে আরও উসকে দিতে চায়। ইউরোপীয় ইউনিয়ন বা ন্যাটোর ওপর ভরসা হারিয়ে ডেনমার্ক এখন তার প্রতিবেশী নর্ডিক দেশগুলোর (নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যান্ড এবং আইসল্যান্ড) দিকে ঝুঁকছে। ডেনমার্কের লক্ষ্য হলো একটি ‘আর্কটিক নর্ডিক ডিফেন্স অ্যালায়েন্স’ গড়ে তোলা। যেহেতু এই দেশগুলোর সংস্কৃতি ও স্বার্থ প্রায় একই, তাই তারা যৌথভাবে বড় শক্তিগুলোর (আমেরিকা ও রাশিয়া) চাপ মোকাবিলা করতে পারে। সমস্যা হলো, নরওয়ে ও আইসল্যান্ডও ন্যাটোর সদস্য এবং আমেরিকার ওপর নির্ভরশীল। ফলে তারা ডেনমার্ককে মৌখিক সমর্থন দিলেও আমেরিকার বিরুদ্ধে গিয়ে কোনো সামরিক পদক্ষেপ নেবে না। ডেনমার্কের কিছু বিশ্লেষক এখন একটি চরম ও ঝুঁকিপূর্ণ বিকল্প নিয়ে আলোচনা করছেন— গ্রিনল্যান্ডকে একটি আন্তর্জাতিক ট্রাস্টিশিপ বা সুইজারল্যান্ডের মতো নিরপেক্ষ অবস্থানে নিয়ে যাওয়া। এতে আমেরিকা বা রাশিয়া—কেউই এককভাবে গ্রিনল্যান্ড দখল করতে পারবে না। এটি কার্যত ডেনমার্কের সার্বভৌমত্বের অবসান ঘটাবে। কারণ, নিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য গ্রিনল্যান্ডকে ডেনমার্কের হাত থেকে পুরোপুরি বের করে একটি আন্তর্জাতিক কমিটির অধীনে দিতে হবে। রাশিয়া এবং চীন বর্তমানে আর্কটিক অঞ্চলে একে অপরের পরিপূরক। রাশিয়া যদি ডেনমার্ককে গ্রিনল্যান্ডে কিছুটা ছাড় দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়, তবে তার বিনিময়ে তারা চাইবে ডেনমার্ক যেন আর্কটিকের ‘নর্দান সি রুট’-এ রুশ আধিপত্য মেনে নেয়। এটি ডেনমার্কের জন্য এক ‘শয়তানের সাথে চুক্তি’র মতো হবে, যা তাদের ন্যাটোর শত্রু বানিয়ে ছাড়বে। এখানেই ডেনমার্কের জন্য সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি। ডেনমার্ক যখন ফিলিস্তিন বা মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার অন্যায় পদক্ষেপগুলোকে সমর্থন দিয়েছিল, তখন তারা আন্তর্জাতিক আইনের ‘নিরপেক্ষতা’র শক্তিকে ধ্বংস করতে সাহায্য করেছিল। আজ যখন তারা রাশিয়ার প্রস্তাব বা নর্ডিক সংহতির কথা বলছে, তখন বিশ্ব দরবারে তাদের সেই নৈতিক গ্রহণযোগ্যতা আর নেই। তাদের মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, আইন বা নীতি কেবল নিজের বিপদের সময় মনে পড়লে চলে না।২০২৬ সালে এসে আর্কটিক কাউন্সিল (Arctic Council) এক নজিরবিহীন অস্তিত্ব সংকটের মুখে দাঁড়িয়েছে। একসময় এই কাউন্সিলকে বিশ্ব রাজনীতির বাইরে ‘শান্তির অঞ্চল’ হিসেবে দেখা হতো, কিন্তু গ্রিনল্যান্ড ইস্যু এবং রাশিয়ার সভাপতিত্ব নিয়ে তৈরি হওয়া উত্তেজনা একে একটি স্নায়ুযুদ্ধের রণক্ষেত্রে পরিণত করেছে।
চলতি বছরে আর্কটিক কাউন্সিলের রুটিন অনুযায়ী রাশিয়ার নেতৃত্বের ভূমিকা পালনের কথা। কিন্তু ইউক্রেন যুদ্ধের পর থেকে নর্ডিক দেশগুলো এবং আমেরিকা রাশিয়ার সাথে সব ধরনের সরাসরি সহযোগিতা স্থগিত করে রেখেছে। মস্কো স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে, তাদের বাদ দিয়ে আর্কটিক কাউন্সিল যদি কোনো সিদ্ধান্ত নেয়, তবে তারা একে ‘অবৈধ’ ঘোষণা করবে। রাশিয়া এখন চীনকে সাথে নিয়ে একটি সমান্তরাল ‘আর্কটিক জোট’ গড়ার হুমকি দিচ্ছে, যা কাউন্সিলের মূল কাঠামোকে ভেঙে ফেলতে পারে। ডেনমার্ক কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে একদিকে চায় রাশিয়ার আগ্রাসন ঠেকাতে, অন্যদিকে তারা ভয় পাচ্ছে যে কাউন্সিল ভেঙে গেলে গ্রিনল্যান্ডের ওপর আন্তর্জাতিক আইনি সুরক্ষা আরও দুর্বল হয়ে পড়বে।বর্তমানে কাউন্সিলটি কার্যত দুই ভাগে বিভক্ত। একপাশে রাশিয়া, অন্যপাশে বাকি সাতটি সদস্য দেশ (ডেনমার্ক/গ্রিনল্যান্ড, আমেরিকা, কানাডা, নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যান্ড এবং আইসল্যান্ড)—যাদের ‘আর্কটিক-সেভেন’ বলা হচ্ছে। ২০২৬ সালের বৈঠকগুলোতে যদি রাশিয়াকে অন্তর্ভুক্ত না করা হয়, তবে আন্তর্জাতিক আর্কটিক আইন (যেমন—সমুদ্র সীমা নির্ধারণ বা পরিবেশ রক্ষা) বজায় রাখা অসম্ভব হয়ে পড়বে। এর ফলে গ্রিনল্যান্ডের জলসীমায় রুশ সাবমেরিন বা যুদ্ধজাহাজের আনাগোনা বৃদ্ধির আইনি প্রতিবাদ করার সুযোগ ডেনমার্ক হারাবে।এই উত্তেজনার মধ্যে গ্রিনল্যান্ডের স্থানীয় সরকার (Naalakkersuisut) দাবি তুলেছে যে, ডেনমার্কের ছায়া হয়ে নয়, বরং তারা নিজেই আর্কটিক কাউন্সিলে স্বাধীন সদস্য বা বিশেষ মর্যাদা সম্পন্ন পর্যবেক্ষক হিসেবে থাকতে চায়। ওয়াশিংটন গোপনে গ্রিনল্যান্ডের এই দাবিকে সমর্থন দিচ্ছে। কারণ গ্রিনল্যান্ড যদি আলাদাভাবে কাউন্সিলে বসে, তবে আমেরিকা ডেনমার্ককে এড়িয়ে সরাসরি গ্রিনল্যান্ডকে প্রভাবিত করতে পারবে। এটি ডেনমার্কের সার্বভৌমত্বের কফিনে শেষ পেরেক হতে পারে।বিশেষজ্ঞদের মতে, ২০২৬ সালের শেষ নাগাদ আর্কটিক কাউন্সিল হয়তো কেবল কাগজ-কলমে টিকে থাকবে। বাস্তবে এটি একটি সামরিক জোটে পরিণত হবে যেখানে, আমেরিকা গ্রিনল্যান্ডকে তার ‘উত্তর গোলার্ধের দুর্গ’ হিসেবে ব্যবহার করবে।রাশিয়া এবং চীন উত্তর সমুদ্র পথ (Northern Sea Route) নিয়ন্ত্রণ করবে।ডেনমার্ক হয়তো কেবল গ্রিনল্যান্ডের ‘নামমাত্র অভিভাবক’ হিসেবে থেকে যাবে। ২০২৬ সালে আর্কটিক কাউন্সিলের এই স্থবিরতা ডেনমার্কের জন্য এক চরম শিক্ষা। তারা যে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার ওপর আস্থা রেখেছিল, তা আজ বড় শক্তির লড়াইয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ। ডেনমার্ক এখন বুঝতে পারছে যে, যখন আইনের চেয়ে শক্তি বড় হয়ে দাঁড়ায়, তখন ছোট দেশগুলোর জন্য কোনো ‘কাউন্সিল’ বা ‘টেবিল’ সুরক্ষার গ্যারান্টি দিতে পারে না। গ্রিনল্যান্ড আজ কেবল একটি দ্বীপ নয়, এটি একটি ভেঙে পড়া বিশ্বব্যবস্থার প্রতীক। ডেনমার্কের সামনে এখন কোনো সহজ পথ নেই। রাশিয়ার প্রস্তাব আসলে একটি মরণফাঁদ, আর নর্ডিক কাউন্সিল হলো একটি দুর্বল ঢাল। ডেনমার্ক এখন এমন এক বাস্তবতার মুখোমুখি যেখানে তাকে হয় আমেরিকার ‘আজ্ঞাবহ কলোনি’ হিসেবে টিকে থাকতে হবে, অথবা গ্রিনল্যান্ডের ওপর থেকে তার ঐতিহাসিক নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দেওয়ার মানসিক প্রস্তুতি নিতে হবে।
গ্রিনল্যান্ডকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া ভূ-রাজনৈতিক উত্তাপ ২০২৬ সালে নর্ডিক দেশগুলোর সামরিক বাজেটে এক ঐতিহাসিক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। দীর্ঘকাল ধরে এই অঞ্চলটি শান্তিবাদী হিসেবে পরিচিত থাকলেও, বর্তমান পরিস্থিতি তাদের ‘অস্ত্র সজ্জা’র এক প্রতিযোগিতায় নামিয়ে দিয়েছে।ডেনমার্ক তাদের ইতিহাসের অন্যতম বৃহৎ প্রতিরক্ষা বাজেট ঘোষণা করেছে। ২০২৬ সালের মধ্যে ডেনমার্ক তাদের প্রতিরক্ষা ব্যয় জিডিপির ৩ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য নিয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ৫ শতাংশ ব্যয়ের দাবির মুখে ডেনমার্ক দ্রুত তাদের সামরিক সক্ষমতা বাড়াতে বাধ্য হচ্ছে। গ্রিনল্যান্ড ও উত্তর আটলান্টিক অঞ্চলের নিরাপত্তা জোরদারে ডেনমার্ক অতিরিক্ত প্রায় ২ বিলিয়ন ডলার (১৩ বিলিয়ন ক্রোনার) বরাদ্দ করেছে। এর মাধ্যমে রাজধানী নুউকে নতুন আর্কটিক কমান্ড হেডকোয়ার্টার স্থাপন এবং গ্রিনল্যান্ডে স্থায়ীভাবে ডেনিশ নৌবাহিনীর উপস্থিতি বাড়ানো হচ্ছে। ডেনমার্ক আমেরিকা থেকে আরও ১৬টি F-35 যুদ্ধবিমান ক্রয়ের চুক্তি সম্পন্ন করছে, যাতে তাদের মোট বহর ৪৩টিতে দাঁড়ায়।নরওয়ে ২০২৬ সালের বাজেটে তাদের প্রতিরক্ষা ব্যয়কে ন্যাটোর নির্ধারিত ২ শতাংশের ওপরে নিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। বাজেট বৃদ্ধি: ২০২৬ সালের জন্য নরওয়ে প্রায় ১৮০ বিলিয়ন ক্রোনার বরাদ্দ করেছে। এর প্রধান কারণ হলো রাশিয়ার সাথে তাদের আর্কটিক সীমান্ত রক্ষা এবং নতুনভাবে রাশিয়ার ‘নর্দান ফ্লিট’-এর মোকাবিলা করা। নরওয়ে তাদের সাবমেরিন বহর এবং ড্রোন নজরদারি প্রযুক্তি আধুনিকীকরণে বড় অংকের বিনিয়োগ করছে।ফিনল্যান্ড ও সুইডেন ন্যাটোতে যোগদানের পর থেকে এই দুই দেশের সামরিক বাজেটে আকাশচুম্বী পরিবর্তন এসেছে। রাশিয়ার সাথে দীর্ঘ সীমান্ত থাকায় ফিনল্যান্ড ২০২৬ সালের মধ্যে তাদের সামরিক ব্যয় জিডিপির ৩.৩ শতাংশ করার পরিকল্পনা নিয়েছে। তারা মূলত স্থলভাগের আর্টিলারি এবং ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় জোর দিচ্ছে।সুইডেন তাদের নৌবাহিনীকে আধুনিকীকরণ করছে যাতে বাল্টিক সাগর এবং আর্কটিক সাগরে রাশিয়ার আধিপত্য কমানো যায়। ২০২৬ সালে নর্ডিক এবং বাল্টিক রাষ্ট্রগুলো সম্মিলিতভাবে একটি ৫০০ মিলিয়ন ডলারের সামরিক সহায়তা প্যাকেজ তৈরি করেছে, যা ন্যাটোর মাধ্যমে সমন্বিত হচ্ছে। এটি কেবল ইউক্রেন যুদ্ধের জন্য নয়, বরং এই দেশগুলো এখন নিজেদের একটি একক ‘প্রতিরক্ষা ব্লক’ হিসেবে দেখছে, যাতে এককভাবে আমেরিকা বা রাশিয়ার চাপের মুখে নতি স্বীকার করতে না হয়। এই বিপুল পরিমাণ সামরিক ব্যয় নর্ডিক দেশগুলোর অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। মুদ্রাস্ফীতি এবং জনসেবা খাতের বাজেট কাটছাঁট করে এই অর্থ জোগাড় করা হচ্ছে। ডেনমার্কের জন্য এটি এক চরম নৈতিক পরাজয়— যে রাষ্ট্র একসময় জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য পরিচিত ছিল, আজ তারা নিজেদেরই তৈরি করা এক অনিরাপদ বিশ্বব্যবস্থায় টিকে থাকতে গিয়ে ‘অস্ত্রের ভাণ্ডারে’ পরিণত হচ্ছে। গ্রিনল্যান্ডকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা ২০২৬ সালে ডেনমার্কের অর্থনীতি ও জনজীবনে এক গভীর সংকটের ছায়া ফেলেছে। সামরিক বাজেটের নজিরবিহীন বৃদ্ধি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাণিজ্য যুদ্ধের হুমকি ডেনিশ জনগণের দীর্ঘদিনের নিশ্চিত ও কল্যাণমুখী জীবনযাত্রাকে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।ডেনমার্কের কেন্দ্রীয় ব্যাংক (Danmarks Nationalbank) এবং অর্থনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ২০২৫-২৬ সালে প্রতিরক্ষা ব্যয় জিডিপির ৩ শতাংশ ছাড়িয়ে যাওয়ায় দেশের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন সক্ষমতার ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হয়েছে।সামরিক খাতে অতিরিক্ত বিনিয়োগের ফলে বাজারে অর্থের প্রবাহ বাড়লেও উৎপাদনশীল খাত স্থবির হয়ে পড়েছে। এর ফলে ২০২৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে ভোক্তা পণ্যের দাম এবং মুদ্রাস্ফীতি প্রায় ১ শতাংশ বেড়ে যাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। যেখানে ২০২৪-২৫ সালে ডেনমার্কের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ছিল ৩.৭ শতাংশ, সেখানে ২০২৫-২৬ সালে তা নেমে মাত্র ১.৫ শতাংশে দাঁড়াবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ডেনমার্ক তার শক্তিশালী সমাজকল্যাণমূলক ব্যবস্থার (Welfare State) জন্য বিশ্বজুড়ে পরিচিত। কিন্তু সামরিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা মেটাতে গিয়ে এই খাতে বড় ধরনের কোপ পড়েছে। সরকার যখন প্রায় ৫০ বিলিয়ন ডেনিশ ক্রোনার অতিরিক্ত সামরিক খাতে বরাদ্দ করেছে, তখন স্বাস্থ্যসেবা এবং শিক্ষা খাতের অনেক দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা স্থগিত বা সংকুচিত করতে হয়েছে। সাধারণ ডেনিশরা এখন হাসপাতালের দীর্ঘ সিরিয়াল এবং উন্নত শিক্ষার সুযোগ কমা নিয়ে চিন্তিত। সামরিক অবকাঠামো নির্মাণ এবং প্রতিরক্ষা শিল্পে জনবল নিয়োগের ফলে গ্রিন সেক্টর (পরিবেশবান্ধব শিল্প) এবং ডিজিটাল সেক্টরে তীব্র শ্রমিক সংকট দেখা দিয়েছে।২০২৬ সালের শুরুতেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ডেনমার্কসহ ইউরোপীয় দেশগুলোর ওপর ২৫ শতাংশ পর্যন্ত আমদানি শুল্কের হুমকি দিয়েছেন।ডেনমার্কের ডেইরি, ফার্মাসিউটিক্যালস এবং ফার্নিচার শিল্প ব্যাপকভাবে মার্কিন বাজারের ওপর নির্ভরশীল। ২৫ শতাংশ শুল্ক কার্যকর হলে ডেনিশ কোম্পানিগুলো প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়বে, যা হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থানকে ঝুঁকির মুখে ফেলবে। আমেরিকা থেকে আসা ইলেকট্রনিক্স এবং প্রযুক্তি পণ্যের দাম ইতিমধ্যে বাড়তে শুরু করেছে, যা সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমিয়ে দিচ্ছে। ডেনমার্কের সাধারণ জনগণের মধ্যে এই সংকট নিয়ে এক অদ্ভুত ‘নৈতিক পরাজয়’ এবং ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। ২০২৬ সালের ডেনিশ গোয়েন্দা সংস্থার (DDIS) রিপোর্টে প্রথমবারের মতো আমেরিকাকে ‘জাতীয় নিরাপত্তার জন্য সম্ভাব্য হুমকি’ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সাধারণ ডেনিশরা আগে আমেরিকাকে রক্ষক মনে করত, এখন তারা ওয়াশিংটনকে একটি ‘শিকারী শক্তি’ (Predatory Power) হিসেবে দেখছে।কোপেনহেগেন ও অন্যান্য বড় শহরগুলোতে সামরিক ব্যয় বৃদ্ধির বিরুদ্ধে এবং পরিবেশ রক্ষার দাবিতে ছোট বড় বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। গ্রিনল্যান্ডে শত শত এলিট সৈন্য মোতায়েনের বিষয়টিকে অনেক ডেনিশ নাগরিক ‘অর্থহীন শক্তির আস্ফালন’ বলে মনে করছেন।আর্কটিক অঞ্চলে সামরিকায়ন বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিবেশবাদী সংগঠনগুলো তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে। সামরিক মহড়া এবং নতুন ঘাঁটি নির্মাণের ফলে গ্রিনল্যান্ডের স্পর্শকাতর ইকোসিস্টেম এবং আদিবাসী ইনুইটদের জীবিকা হুমকির মুখে পড়ছে। ২০২৬ সালের এই বৈরী পরিবেশে পরিবেশ রক্ষা নয়, বরং ‘অস্ত্রের রাজনীতি’ই ডেনমার্কের প্রধান নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে।২০২৬ সালে ডেনমার্কের জন্য গ্রিনল্যান্ড কেবল একটি সার্বভৌমত্বের লড়াই নয়, এটি তাদের পুরো অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো রক্ষার লড়াই।