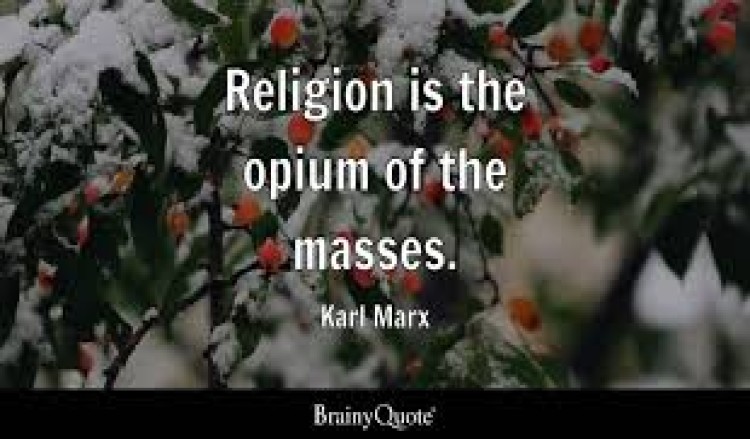গবেষক জর্জ রুদ ফরাসি বিপ্লব প্রসঙ্গে লিখেছেন, অর্থনৈতিক সঙ্কট, সামাজিক অসংহতি, রাজনৈতিক অস্থিরতা বিপ্লবের আবশ্যিক শর্ত হলেও, বিভিন্ন শ্রেণীগুলোর মধ্যে একটা সাধারণ সংহতি, একটা সাধারণ ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা জন্ম না নিলে বিপ্লব সম্পন্ন হয় না। বুর্বো রাজতন্ত্রের ও অভিজাতদের বিরুদ্ধে ১৭৮৯ সালে যে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল সেই বিপ্লবী শক্তি ছিল অসংখ্য স্বার্থে বিভক্ত। কৃষক, মজুর, শহুরে জনতা, বুর্জোয়া। আবার কৃষকদের মধ্যে ছিল ভূমি হীণ, স্বল্প জমি, মাঝারি জমির মালিক। জনতার মধ্যে ছিল কর্মহীন বেকার, মজুরি ভোগী, ভবঘুরে, ভিক্ষুক, শহুরে লুম্পেন। বুর্জোয়ার মধ্যে ছিল বৃত্তিজীবী শিক্ষক অধ্যাপক আইনজীবী সাংবাদিক ; সওদাগরি বুর্জোয়া, ছোটো হস্তশিল্প, ছোটো মাঝারি দোকানদার। এই সমগ্র জনতাকে একটা সাধারণ ইচ্ছার অনুবর্তী করার কাজটা ছিল কঠিন। এখানেই বিপ্লবী তত্ত্ব ও দর্শনের গুরুত্ব।
দর্শন কাজ করে দুভাবে। প্রথমতঃ সুদীর্ঘকাল চলে আসা একটা সিস্টেম চেতনায় একটা জড়তা ইনার্সিয়া জন্ম দেয়। বলা ভালো মানুষ কে একটা নিয়মে অভ্যস্ত করে তোলে। প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে চলতে চায়। এমনই তো হয়। সেই বিজ্ঞাপন মনে করুন, প্রশ্ন করছে "আপনি কেন খান?" ..... "আপনি?" .... "আর আপনি?" আর উত্তরগুলো মনে করুন "ছোটবেলা থেকেই খেয়ে আসছি" ..... "দাদু ঠাকুমাকেও খেতে দেখেছি" ..... "আমি তো এমনি এমনিই খাই"। এই হলো ইনার্সিয়া, সব্বাই করে বলে সব্বাই করি তাই। অ্যালান বল এটাকেই মহিমান্বিত করে বলেছেন পলিটিক্যাল কালচার। পাহারাদার লাগে না, লাঠি বেত লাগে না। সিস্টেম নিজেই চলতে থাকে। পাওয়ারের হেজিমনি।
শাসকের পশ্চাতে যদি ঐশ্বরিক ক্ষমতা জুড়ে দেওয়া যায় কাজটা সহজ হয়। ধরা ধামে ঈশ্বরের দুজন প্রতিনিধি, পার্থিব জীবনে রাজা ও অপার্থিব জগতে ধর্মীয় গুরু। কোথাও তিনি পোপ, কোথাও পয়গম্বর, কোথাও বা ব্রাহ্মণ পন্ডিত। এই প্রতিনিধি দের উপেক্ষা অবজ্ঞা করা মানে ঈশ্বরের প্রতি অবজ্ঞা। যেহেতু এদের নিয়োগ পত্র দিয়েছেন ঈশ্বর, অতএব এরা ঈশ্বরকে কৈফিয়ত দেবেন, মানুষ এদের নামে ঈশ্বরের কাছে নালিশ জানাতে পারেন। বিচার কর্তা খোদ ঈশ্বর। এভাবে সিস্টেম কে বৈধতা দান করা। সেই বৈধতার ভূত ঘাড়ে চেপে বসে আছে। আছে ই বা বলি কি করে, নিজেই তো রেখেছি। এটাই আদিকল্প, কালচার, ইনার্সিয়া যা কিছু বলা যায়।
"ভগবানই জেনো প্রভু, অতএব চুপ, কথা বলো নাকো কভু" ..... "ঈশ্বর সব ন্যায় অন্যায়ের হিসাব রাখছেন। তার চোখকে ফাঁকি দেবে কে?" ..... "শেষের সেদিন কি ভয়ঙ্কর, সবাই তখন কইবে কথা, তুমি একা নিরুত্তর" ..... "যে সয় সে রয়, যে না সয়, সে নাশ হয়"। নিপীড়িত যন্ত্রণা বিদ্ধ ক্ষতে এই বাণী বুঝি শুশ্রূষার প্রলেপ। " ঈশ্বরের পুত্র তীব্র ব্যথায় কাতর হননি, বলেছিলেন, তুমি এদের ক্ষমা কোরো"। কতবার ক্ষমা করা যায় প্রভু? সাতবার আমি ক্ষমা করেছি। "ঈশ্বরের পুত্র বললেন, সত্তর গুণ বার। অর্থাৎ প্রত্যেক বার।" এই ঘটমান বর্তমান বাহ্য জগতের বাইরে ত্যাগের জগৎ, মৃত্যুর মধ্যে পরম শান্তি, অনাবিল সুখের স্বপ্নে বিভোর থাকা।
হ্যাঁ, ঠিকই। আপনি বলতেই পারেন, মার্কস এই কারনেই ধর্মকে আফিম বলেছেন। আবার স্মরণ রাখবেন, এই আফিম কিন্তু যন্ত্রণা বিদারী ওষুধের কাজও করে। তা মার্কস এও বলেছেন, বঞ্চিত অসহায় মানুষের নালিশ জানাবার কেন্দ্র ধর্ম। ক্রীতদাস বিদ্রোহ, লেভেলার ডিগার আন্দোলন, জার্মানির কৃষক বিদ্রোহের নেতা টমাস মুনজের, এদের প্রেরণা এসেছে ধর্মীয় সাম্যের ধারনা থেকে।
বিপ্লবী দর্শনকে ধর্মের নতুন ব্যাখ্যা হাজির করতে হবে। আমরা সকলেই ঈশ্বরের সন্তান। আমাদের ওপর পীড়নের অর্থ ঈশ্বরের ওপর পীড়ন। ঈশ্বর সবচেয়ে বড়ো সাম্যবাদী। তিনি সকল সন্তান কে সম দৃষ্টি দিয়ে দেখেন। অতএব সাম্য প্রতিষ্ঠা ও বৈষম্য দূরীকরণ ঐশ্বরিক কর্তব্য। মৃত্যু চিন্তা অহেতুক, কারন তা জীবনের মতোই স্বাভাবিক। জন্মিলে মরিতে হবে। প্রতিদিন আমরা ঘুমাই, আবার জেগে উঠি। মৃত্যুও ঘুম, চির ঘুম, আর কোনও দিন জাগবো না। ঈশ্বর এই জগতে মানব জনম দিয়ে পাঠিয়েছে ভোগের জন্য। জগতকে রূপে রসে শব্দে গন্ধে সাজিয়ে দিয়েছেন আমাদের জন্য। এসব ভোগ করা আমাদের ঐশ্বরিক কর্তব্য।
"এই পৃথিবীর যাহা সম্বল,
বাসে ভরা ফুল রসে ভরা ফল,
সু স্নিগ্ধ মাটি সুধা সম জল পাখির কন্ঠে গান
সকলের এতে সম অধিকার, এই তার ফরমান
ভগবান ভগবান।"
শাসকের ঈশ্বরকে নিপীড়িতের ঈশ্বরে পরিণত করে ছিল বিপ্লবী দর্শন। ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচারণ নয়। ঈশ্বরের নতুন ব্যাখ্যা। তবেই তো আদিকল্প ভেঙে পড়েছিল। অমন যে নিরক্ষর লেঠেল তিতুমীর, সেও টেক্সটের নতুন ব্যাখ্যা দেন : "আমরা সকলেই আল্লাহর বান্দা"। জমিদার, ধর্মীয় পুরোহিত মৌলবী এক বাক্যে গুরুত্ব হারালো। "প্রত্যেক মুসলমান ভাইয়ের একবার মক্কায় হজ করতে যাওয়া কর্তব্য"। মক্কা কোথায় চাষা জানেনা। কিন্তু মনোজগতে সে মক্কায় বিচরণ করে। ভৌগোলিক বন্ধন শিথিল হয়। অর্থ থাকলে আমিও হাজী হতে পারতাম। একটা আত্মসম্মান, আত্মবিশ্বাসের বোধ জন্ম নেয়। প্রচলিত সামন্ততান্ত্রিক বন্ধনগুলো এভাবেই একটু একটু করে শিথিল হলো। আদিকল্প ভেঙে গেলো। তবেই না গোবরডাঙা নারকেলবেড়িয়ার তিতুমীরের বিদ্রোহ ইতিহাস সৃষ্টি করলো। আমরা শুধুই জানলাম, বোঝালাম ধর্ম হলো আফিম। টেক্সটকে বিনির্মাণ করতেই জানলাম না।
দর্শনের এই কাজটি রুশো ভলতেয়ার মন্টেস্কু দিদেরো করেননি। করেছেন একদল অখ্যাত নাম না জানা হ্যান্ডবিল পুস্তিকা রচয়িতা। তারা বিপ্লবী দর্শনের সুসিদ্ধ সহজপাচ্য খাদ্য পরিবেশন করেছিলেন। মানুষ গোগ্রাসে এগুলো গিলেছে। তবেই না আদিকল্প হুড়মুড় করে ভেঙে পড়েছিল। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ পথে। বাস্তিল দূর্গ বৈধতা হারিয়েছে। ভার্সাই প্রাসাদ বৈধতা হারিয়েছে। অভিজাতদের প্রাসাদ বৈধতা হারিয়েছে। এমনকি চার্চ যাজক বৈধতা হারিয়েছে। এটাকেই লেনিন ব্যাখ্যা করেছেন : Theory also becomes a material force as soon as it is gripped by the masses. জনগন গ্রহণ না করলে বিপ্লবী তত্ত্ব কথা অসার, হেলে জলঢোঁড়া।
এবারেই এসে পড়ছে বিপ্লবী দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়। এই হরেক কিসিমের সামাজিক বর্গ গুলিকে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও অভিমুখে চালিত করা, একটা সাধারণ ইচ্ছা, সাধারণ আকাঙ্ক্ষার অনুবর্তী করা। এক্ষেত্রেও সহজপাচ্য তত্ত্বগুলি খেয়াল করুন। সমাজের ৯৫ শতাংশ ব্যক্তিই তৃতীয় এস্টেটের অন্তর্গত। অতএব তৃতীয় এস্টেটের ইচ্ছাই জাতির ইচ্ছা। জাতির ইচ্ছাই আইন। ভিন্ন ভিন্ন বর্গগুলির ভিন্ন ভিন্ন আকাঙ্ক্ষা। তাকে সাধারণ ইচ্ছায় রূপ দেওয়া কঠিন কাজ। তিনটি শব্দবন্ধে সমস্ত আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হলো : স্বাধীনতা - সাম্য - মৈত্রী। শ্লোগান টি বিমূর্ত বলেই এর মধ্যে সকল আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হয়েছিল।
অতএব আদিকল্পের অবসান ও সাধারণ আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছার নির্মাণ বহুধা বিভক্ত তৃতীয় এস্টেটকে একটি ঐক্যবদ্ধ শ্রেণীর রূপদান করেছিল। অথচ বাস্তবে শিল্পপতি বুর্জোয়া তখনও শৈশবাবস্থায়। বুর্জোয়া শ্রেণী নিজেই বহুধা বিভক্ত। তথাপি বুর্জোয়া বিপ্লব ঘটেছিল, কারণ বিপ্লবী তত্ত্ব ও দর্শন সুচারু ভাবে নিজ কাজ সম্পন্ন করে ছিল। বলতে পারি, বৈষয়িক জগতে বুর্জোয়া বিকাশ না ঘটলেও, চিন্তার জগতে পূর্ণ মাত্রায় বিকশিত হয়েছিল। যেটা ইংল্যান্ডে ছিল বিপরীত। সেখানে বৈষয়িক জগতে, অর্থনীতিতে বুর্জোয়া বিকাশ পূর্ণ মাত্রায় ঘটলেও বিপ্লবী দর্শন ও চিন্তন ছিল অনুপস্থিত।
এই সঙ্গে মনে রাখতে হবে, ফ্রান্সে সেই সময়ে প্রচলিত রাজনৈতিক সংকটের চরিত্রটি, যা ছিল বিপ্লবের সহায়ক। প্রধানতঃ মন্ত্রিপরিষদ প্রস্তাবিত বিল অভিজাত নিয়ন্ত্রিত প্রাদেশিক পার্লামেন্টে পাশ হলে, রাজা বিলে স্বাক্ষর করে আইন পাস করতেন। এর ফলে আইনের ওপর অভিজাতদের নিয়ন্ত্রণ থাকতো। তৃতীয় এস্টেট করভারে জর্জরিত হলেও, অভিজাতদের ওপর কোনো কর আরোপ হয়নি। আইন পাশের অন্য দুটি পদ্ধতি থাকলেও তা অনুসৃত হতো না। ১) রাজার বিশেষ ক্ষমতা বা অর্ডিন্যান্স এবং ২) আইনসভা স্টেটস জেনারেলের অধিবেশন। ১৭৫ বছর স্টেটস জেনারেলের অধিবেশন ডাকা হয় নি। একটি অর্থনৈতিক অচলাবস্থার সামনে প্রচলিত আইন ব্যবস্থাটি অকেজো হয়ে যায়। বিপ্লবী পরিস্থিতি সম্পর্কে লেনিন বলেন, প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থা তখন শাসকের নিজের কাছেই অকেজো হয়ে যায়।
ফ্রান্সের প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে আমেরিকা স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষণা করে। ফ্রান্স এই যুদ্ধে আমেরিকাকে বিপুল অর্থ সাহায্য করে, যখন ফ্রান্সের নিয়মিত বাজেট ঘাটতি ছিল ২০ শতাংশ। সবটাই ধার করা অর্থ। একেই বুঝি বলে, নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ। ইংল্যান্ডের ভাতে পড়লো মাছি। কিন্তু ফরাসি অর্থনৈতিক সঙ্কট হলো পাহাড় প্রমাণ। তৃতীয় এস্টেটের ওপর আর কর আরোপ অসম্ভব। একমাত্র সম্পদের শীর্ষে থাকা অভিজাতদের ওপর সামান্য কর আরোপ হলে সমস্যা উৎরে যেতে পারতো। অনিবার্য ভাবেই অর্থমন্ত্রীর এই প্রস্তাব প্রাদেশিক পার্লামেন্টে বাতিল হলো। এমনকি তারা ওই অর্থমন্ত্রীকে পদচ্যুত করে। একের পর এক অর্থমন্ত্রী একই প্রস্তাব দেয়। প্রাদেশিক পার্লামেন্টে প্রস্তাব খারিজ হয়, অর্থমন্ত্রী পদচ্যুত হয়। তুর্গো, কালন, লোমেনি দ্য ব্রিয়াঁ, নেকর সকল অর্থমন্ত্রী একেরপর এক পদচ্যুত হন। এটাই অচলাবস্থা। রাজা তখন বাধ্য হলেন বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে অর্ডিন্যান্স জারি করতে। অভিজাতদের দাবি অর্ডিন্যান্স নয়, স্টেটস জেনারেলের অধিবেশন ডাকতে হবে। রাজা অভিজাত উভয়ের কাছেই পুরাতন শাসনযন্ত্র অচল। এটাই তো রাজনৈতিক সঙ্কট। অভিজাত শ্রেণী রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ফরাসি বিপ্লব শুরু করে প্যাট্রিসিয়ান রা, কিন্তু সেই বিদ্রোহের হাল ধরলো প্লিবিয়ান রা। অভিজাতদের বিদ্রোহ বুর্জোয়া বিপ্লবের রূপ নিলো।
বুর্জোয়া শ্রেণী অপরিণত, অবিকশিত। কিন্তু দর্শন ও চিন্তনের ক্ষেত্রে পূর্ণমাত্রায় বিকশিত। সেই সাথে শাসক শ্রেণীর রাজনৈতিক অচলাবস্থা, পরে পাওয়া চোদ্দ আনা বিপ্লবী পরিস্থিতি। সুতরাং প্রথম বুর্জোয়া বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল ফ্রান্সে।
এখানেই আসছে দ্বিতীয় প্রসংগ। এই বিপ্লব সফল হওয়া, স্থায়ী হওয়া সম্ভব ছিল না। যে বুর্জোয়া অর্থনৈতিক বনিয়াদের ওপর বুর্জোয়া রাজনীতি সংস্কৃতি নির্ভর করবে সেই বনিয়াদ অনুপস্থিত। নিরালম্ব, ঝুলন্ত বুর্জোয়া রাজনৈতিক ব্যবস্থা। ফলে এই ব্যবস্থা টিঁকতে পারে না। নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র, রোবসপিয়ের যুগের প্রজাতন্ত্র, ডাইরেক্টরীর শাসন, কনস্যুলেট শাসন, নেপোলিয়ন বোনাপার্টের সম্রাটের শাসন : দু বছর/তিন বছর এক একটি শাসন স্থায়ী হয়। একমাত্র নেপোলিয়নের একনায়কতন্ত্র পনের বছর স্থায়ী হয়েছিল। তারপর পুনরায় ফিরে আসে বুর্বো রাজতন্ত্র ১৮১৫ সালে। ১৮৩০ এ আবার বিপ্লব, নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র, ১৮৪৮ এ আবার বিপ্লব, প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। ১৮৫২ প্রজাতন্ত্র উৎখাত ও লুই বোনাপার্টের একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। ভিত্তি ছাড়া উপরিসৌধ দাঁড়ায় না, তাই বারবার রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন। ভিত ছাড়া উপরিসৌধ গড়ে ওঠে, শুধু উপরিসৌধে বিপ্লব সাধনও হতে পারে। কিন্তু সেই বিপ্লব স্থায়ী হয় না।
ওদিকে ইংল্যান্ডে অস্বাভাবিক দ্রুত গতিতে বুর্জোয়া অর্থনৈতিক বিপ্লব সংঘটিত হলো। কিন্তু মাত্র একটি বার অলিভার ক্রমওয়েলের প্রজাতন্ত্র গড়ে উঠলেও, দ্রুত নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে প্রত্যাবর্তন করে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটি নরমপন্থী মধ্যপন্থা অনুসরন করে ইংল্যান্ডের বুর্জোয়া শ্রেণী। কোনো কপিবুক বিপ্লব আমরা দেখতে পাইনা।
ফরাসি বিপ্লবের পটভূমিতে সময় পাত্রপাত্রী পাল্টে দিন। ইউরোপের সবচেয়ে শিল্পে অনুন্নত দেশ রাশিয়া। সময়টা বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার বিপর্যয়। এখানেও বৌদ্ধিক জগতে গণতন্ত্র ও সাম্যবাদ চর্চার অস্বাভাবিক অগ্রগতি হয়। এখানেই বিপ্লব সম্পন্ন হলো। ভিত্তি ছাড়া নিরালম্ব। শিল্পায়ন তখনও স্বপ্ন। শিল্প শ্রমিক তখনও একটি দুর্বল শ্রেণী। শ্রমিক শ্রেণীর পার্টিটা অশ্রমিক পেটি বুর্জোয়া প্রধান। শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী তত্ত্ব, ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করে পেটি বুর্জোয়া। কতো বিচিত্র রাজনৈতিক গোষ্ঠী যৌথভাবে ক্ষমতাচ্যুত করে জারতন্ত্র কে। সেনাবাহিনী নিজেই রণাঙ্গনে রুশ বিপর্যয়ের জন্য জারতন্ত্র কে দায়ী করে। তারা বন্দুক ঘুরিয়ে ধরে শাসকের দিকে। শাসকের পীড়নের যন্ত্র টা শাসকের কাছেই অকেজো হয়ে যায়। ফলতঃ অতি সহজেই জারতন্ত্র ভেঙে পড়ে ১৯১৭ র মার্চ মাসে।
সমস্যা দেখা যায় পরবর্তী ধাপে। যে অভিন্ন দাবীতে সমাজের অসংখ্য বর্গ ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল, বিপ্লবের পর তার রূপায়ণে। যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে ছেলেদের ঘরে ফেরাও। রুশ সাম্রাজ্যের নিপীড়িত জাতিগুলির স্বায়ত্তশাসন চাই। কৃষকদের হাতে জমি চাই। শ্রমিকদের হাতে কারখানার নিয়ন্ত্রণ চাই। বলাই বাহুল্য পাঁচমিশালী স্বার্থের অস্থায়ী সরকার এই দাবি পূরণে আগ্রহ দেখাবে না। দেখায় নি। বরং অস্থায়ী সরকার ভেবেছিল যুদ্ধ ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করতে পারলে সেনার শৃঙ্খলা ও জনতার আস্থা অর্জন সম্ভব হবে। এক তরফা যুদ্ধ বিরতি ঘোষণার পরিবর্তে কেরেনেস্কি নির্দেশ দিলেন "Russia having thrown off the chains of slavery, has firmly resolved to defend, at all costs, it's rights, honour, and freedom. Warriors, our country is in danger ! Liberty and revolution are threatened. The time has come for the army to do it's duty." ফরাসি বুর্জোয়া নেতা রোবসপিয়ের, সেডান যুদ্ধে র আগে লুই বোনাপার্ট বিপ্লব ও দেশপ্রেমের দোহাই দিয়ে ঠিক এমন ভাষণ দিয়েছিলেন। এখানে এসেই অখন্ড ইচ্ছা ভেঙে পড়ে। মনে রাখতে হবে, বলশেভিক পার্টি তখনও নতুন বিপ্লবী গণতান্ত্রিক সরকারের প্রধান শক্তিশালী দল নয়। শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে নিশ্চিত ভাবে এই দল শক্তিশালী ছিল। এপ্রিল মাসে লেনিন বলশেভিকদের নেতৃত্বে নতুন সরকারের কাছে বিপ্লবের দাবি গুলি পুণঃপুণঃ উত্থাপন করেন। ক্ষমতাসীন সরকার যে আসলে শ্রমিক কৃষক ও নিপীড়িত জাতিগুলির প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ দৃষ্টি পোষণ করে না তা ধীরে ধীরে স্পষ্ট করাই ছিল এপ্রিলের ওই দলিলের গাইড লাইন। জরুরি ভিত্তিতে নিবিড় কর্মসূচি। ভাবা যায়, আইন সভায় ১০৯০ সদস্যের মধ্যে লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টির প্রতিনিধি ছিল মাত্র ১৩৭ জন। পেট্রোগ্রাদ সোভিয়েতের এক নরমপন্থী নেতা সেরেতেল্লি বলশেভিকদের হীনবল দেখে সোভিয়েতের প্রথম কংগ্রেসের ভাষণে বলেন : "as there is no political party in Russia which at the present time would say, 'Give us the power.' " ঠিক সেই সময় লেনিন তাঁর আসন থেকে বলে ওঠেন : "Yes, there is !" এটা ছিল ১৯১৭ র জুন মাস।
লেনিন বুঝেছিলেন, জনগণের মধ্যে বলশেভিক পার্টির প্রস্তাব ও দাবিগুলি যতই সমর্থন লাভ করুক না কেন, ক্ষমতাসীন গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী দের প্রতি সাধারণ মানুষের সমর্থন ও আনুগত্য বজায় আছে। এই আনুগত্য যতক্ষণ থাকবে, ততদিন ক্ষমতা দখলের চেষ্টা হবে হঠকারীতা ও অ্যাডভেঞ্চারিজম। তাই তিনি বলশেভিক পার্টির গণ আন্দোলন ও গণ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে বিপ্লবের প্রধান দাবি গুলি অস্থায়ী সরকারের কাছে পেশ করতে থাকলেন। গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী দের মুখোশ একটু একটু করে জনগণের কাছে খসে পড়তে থাকে। লেনিনের মতে, এভাবে ক্ষমতাসীন সরকারের বৈধতা যত কমবে, সরকার কে উচ্ছেদ করা ততই সহজ হবে। একসময় বৈধতা হারিয়ে সরকার টা শুধু বল প্রয়োগের শক্তি হিসেবে টিঁকে থাকে। তখন সামান্য শক্তি প্রয়োগ করলেই সরকার হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। "দ্বৈত শাসন" প্রসঙ্গে তিনি বলেন, শাসন ক্ষমতায় আইনত কেরেনেস্কি সরকার থাকলেও জনগণের মধ্যে এই সরকারের কোনো সমর্থন বা ভিত্তি নেই। সোভিয়েত গুলি পরিচালিত হচ্ছে শ্রমিক সৈনিক প্রতিনিধিদের দ্বারা। ক্ষমতাসীন সরকারের আর কোনো বৈধতা নেই। ফলতঃ সবচেয়ে কম রক্তপাতের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হলো রুশ বিপ্লব, মাত্র দশটি দিন।
যে শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি বিপ্লব সম্পন্ন করলো তারা তখনও রুশ সমাজের সংখ্যালঘু শ্রেণী। বলশেভিক পার্টির যথাযথ সাংগঠনিক কার্যক্রম ও যথাযথ শ্লোগান নির্বাচনের ফলে অধিকাংশ জনগণের সমর্থন লাভে সক্ষম হয়। সহজেই বিপ্লব সম্পন্ন হলো ; কিন্তু এই বিপ্লব স্থায়ী হতে পারে না। কারণ পুঁজিবাদের বিকাশের পর্বটি সাঙ্গ হয় নি। এদিকে পার্টি ক্ষমতাসীন হবার ফলে একদিকে বহু সুবিধাভোগী অশ্রমিক এসময় দলে অনুপ্রবেশ করে। সরকারের কাজের প্রয়োজনেও দলে টেকনোক্র্যাট, ব্যুরোক্র্যাটদের গুরুত্ব বাড়তে থাকে। পার্টির নানা কমিটিতে জাঁকিয়ে বসে।
পুঁজিবাদের বিকাশের পর্বটি অতি দ্রুত সাঙ্গ করার জন্য লেনিন প্রাক বিশ্বযুদ্ধ জার্মানির স্টেট ক্যাপিটালিজমের মডেল টি গ্রহণ করেন। অস্বাভাবিক দ্রুত গতিতে শিল্পায়ন, ৩৫০/৪০০ শতাংশ হারে। জার্মানিতে একটি একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো, পরিচালিত হয় সামরিক অভিজাত, য়ুঙ্কার, আমলাতন্ত্র দ্বারা। সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্র পরিচালনা করে শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র। অতএব এই পথেই দ্রুত শিল্পায়ন সম্ভব। গৃহীত হলো ১৯২৩ সালে NEP (নিউ ইকনমিক পলিসি)। বিপদ টা অনুমান করুন। স্টেট ক্যাপিটালিজমের পথ, রূপায়নের দায়িত্ব শ্রমিক শ্রেণীর। তার আগে তো পার্টি পার্টি ও রাষ্ট্রে শ্রমিক শ্রেণীর আধিপত্য সুনিশ্চিত করা জরুরি। বুর্জোয়া পথে যাত্রা, পেটি বুর্জোয়ার নেতৃত্ব। শরীর টা গাধার বটে, ডাকটাও গাধার। তারপরও মানতে হবে ওটা ঘোড়া। নেপ থেকেই শুরু হয়েছিল পুঁজিবাদের পথে যাত্রা শুরু। লেনিন ১৯২২ থেকেই রোগ শয্যায়, ১৯২৪ সালে তিনি মারা যান। তিনি কিন্তু নেপ এর পথে যাত্রা শুরুর আগে পার্টিতে শ্রমিক শ্রেণীর আধিপত্যমূলক সংখ্যা গরিষ্ঠতার কথা বলেছিলেন। অরণ্যে রোদন।
আসলে বিপ্লবী তত্ত্ব চর্চা করলেন অশ্রমিক, অ শিল্প বুর্জোয়া শ্রেণী। ফরাসি বিপ্লবের দশা আর রুশ বিপ্লবের দশায় কোনও পার্থক্য দেখিনা। বেস সুপার স্ট্রাকচার তত্ত্ব যান্ত্রিকভাবে অনুসরণ বিপদজনক। বেস - সুপার স্ট্রাকচার দুটি পৃথক অটোনমি। স্বাধীন ভাবে এদের বিকাশ ঘটে। কিন্তু এই দুটির বিকাশের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য থাকা জরুরি। এই জরুরি সম্পর্কটি অস্বীকার করলে ভাবের ঘরে চুরি। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক চেতনা পুষ্ট ফরাসি বিপ্লব, বেসের অভাবে কালে কালে বোনাপার্টের একনায়কতন্ত্র কে ডেকে এনেছিল। অল পাওয়ার টু দ্য সোভিয়েতস শ্লোগান শেষ অবধি অল পাওয়ার টু দ্যা স্টেট হয়ে গেলো তো। শ্রমিক শ্রেণীর পার্টিটাই ঠিক মতো গড়ে উঠলো না। আর মাও সেতুং সমগ্র বিপদ প্রত্যক্ষ করলেন, উন্নয়নের সোভিয়েত মডেলকেই বর্জন করলেন। উচ্চ মাথা বিশিষ্ট ম্যানেজারিয়াল সিস্টেম বর্জন করার পথে যাত্রা করেন। কিন্তু শেষ অবধি সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ব্যর্থতায় প্রতি বিপ্লব জয়ী হলো। সোভিয়েত ইউনিয়নের উন্নয়নের মডেলকেই বেছে নিয়েছিলো।
মাও সেতুঙ সমাজতন্ত্রের এই শোচনীয় পরিনতি অনুমান করতে পেরেছিলেন। "জনগণের মধ্যে দ্বন্দ্ব সমূহের সঠিক প্রয়োগ" নিবন্ধে লেখেন, শ্রেণী সংগ্রাম কোনও অর্থেই শেষ হয়ে যায়নি। বরং সময় বিশেষে তা অনেক বেশি তীব্র হয়। অর্থনৈতিক উৎপাদন ক্ষেত্রে, শিক্ষা, চিন্তা, মেধা, প্রশাসন, আইন নানান ক্ষেত্রে এই শ্রেণী সংগ্রাম চলতে থাকে। এই সংগ্রামে শেষাবধি কে জয়ী হবে বুর্জোয়া না প্রলেতারিয়েত তা এখনও নির্দিষ্ট নয়। অর্থাৎ শ্রেণী সংগ্রাম একটি নিরন্তর প্রক্রিয়া। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিপ্লবের পরবর্তী গঠন ও উন্নয়ন পর্বে শ্রেণী সংগ্রাম উপেক্ষিত হয়। তথাকথিত উন্নয়নের স্বার্থে অ শ্রমজীবী শ্রেণী গুলি পার্টি ও সরকারে প্রাধান্য বিস্তার করে। এর জন্যই তো কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া, হবু ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার দের মধ্যে শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে আত্মিক বিনিময়ে সাংস্কৃতিক বিপ্লব অনেকাংশেই সফল হয়েছিল। হাজার হাজার পড়ুয়া, যারা ভবিষ্যতের পেটি বুর্জোয়া, তারা ক্ষেত খামার কারখানায় শ্রমজীবীদের সাথে একাত্ম হলো। গোটা পশ্চিমী দুনিয়া অবাক বিস্ময়ে দেখলো। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের এই জোয়ার কে রুখতে পারে এই বিপ্লবের অতি সক্রিয়তা, বাড়াবাড়ি ও বিপথগামীতা। ঠিক সেটাই ঘটেছিল।
বিপ্লবী চিন দেশেও পুঁজিবাদ ছিল অপরিণত। কিন্তু চিনা কমিউনিস্ট পার্টির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে চিনা শাসক শ্রেণীর সংকট পড়ে পাওয়া চোদ্দো আনা বিপ্লবী পরিস্থিতি হাজির করে। তাই বিপ্লব সম্পন্ন হলেও তাকে ধারণ ও লালন করতে সমর্থ শ্রেণী ও বৈষয়িক ভিত্তি ছিল অনুপস্থিত। একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি। আজকের চিনকে কেউ সমাজতন্ত্র বলেন কিনা জানা নেই। ঝান্ডা লাল হলেই তো সমাজতন্ত্রী বা কমিউনিস্ট হয় না। স্মরণে রাখবেন, হিটলারের নাৎসি পার্টির পতাকার রঙ ছিল লাল। বিপ্লবী পরিস্থিতি থাকলেও, বিপ্লব না হয়ে প্রতি বিপ্লব হতে পারে। একটা বিপ্লবী তত্ত্ব যথেষ্ট নয়, তাকে কে ব্যাখ্যা করছে, কে ধারন করছে সেটা বড়ো প্রশ্ন। বিপ্লবী কে চিত্রকর হতে হয়। অনেক সময় বহু কিছু উদ্ভাবন করতে হয়। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সেই গল্পটা বলে শেষ করি : পড়ন্ত বিকেলে মোষের দল ফিরছে। শিল্পী বিনোদবিহারী আঁকছেন। সুন্দর সেই ছবি দেখে সাঁওতাল বালিকা বললো, এত্তো গুলান বুড়া ভঁইসের দলে একটা খাঁড়া (বাছুর) নাই? বলেই খিলখিল হেসে চলে গেলো। দলটার মধ্যে বাছুর ছিল না, শিল্পের বাস্তবতা বাছুর চাইছে। বিপ্লবী তো শিল্পী, বিপ্লবের ছবি আঁকেন। তাঁকে অনেক কিছু উদ্ভাবন ও সংযোজন করে নিতে হয়। কখন বলটা ইনসাইড ডজ, কখন আউট সাইড ডজ হবে, সবটা আগে বলা থাকে না। ডিফেন্স কখন কোন দিক থেকে আসবে, সেই অনুযায়ী ঠিক করতে হয়। তবেই তো মেসি মারাদোনা।