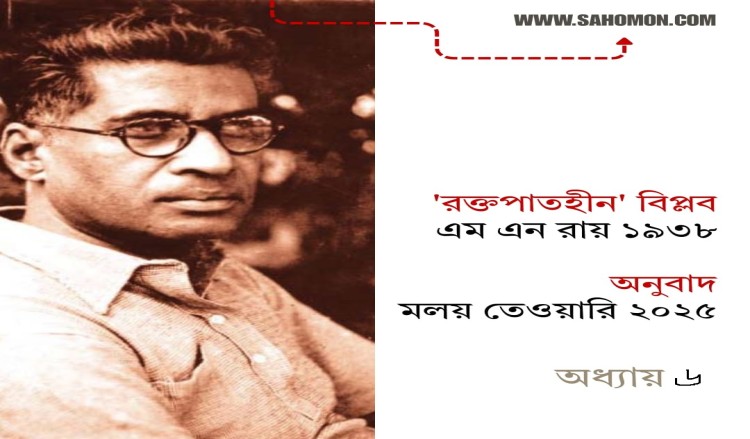অধ্যায় ৬
“রক্তপাতহীন” বিপ্লব
ফ্যাসিস্টরা দাবি করে যে তারা ইতালি ও জার্মানিকে বিপ্লব স্পন্দিত করেছে রক্তপাতহীনভাবে। কিন্তু তাদের বাস্তব রেকর্ড—শুধু ওই দুই দেশে নয়, অন্যান্য বহু দেশেই—তাদের এই দাবিকে মিথ্যা প্রমাণ করে। যাই হোক এই “সুপারম্যান”-দের উত্থানের কীর্তিকলাপ বিষয়ক কিছু তথ্য জানা এখানে আকর্ষণীয় হবে।
ইতালিতে মুসোলিনি জনপ্রিয় বিজয়ী সেনাবাহিনীর কমান্ডার হিসেবে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে রোম দখল করতে কুচকাওয়াজ করেননি। যখন “মার্চ অন রোম”-এর নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছিল তখন এই ফ্যাসিস্ট নায়ক মহাশয় নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করছিলেন। পুঁজিপতিদের কাছ থেকে প্রচুর অর্থ পেয়ে তিনি ব্ল্যাক শার্ট নামের ভাড়াটে সৈন্যদল গড়ে তুলেছিলেন। এই ভাড়াটে বাহিনী বিপ্লবী শ্রমিক ও কৃষকদের বিরুদ্ধে অগণিত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে তাদের বীরত্ব প্রদর্শন করেছিল। কিন্তু দুর্বল ও ভীত-সন্ত্রস্ত উদারনৈতিক বুর্জোয়া সরকারের কাছ থেকে বাস্তবে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার কাজটা কিন্তু ব্ল্যাক শার্ট বাহিনী করে নি। করেছিল নিয়মিত সেনাবাহিনী, যারা মুসোলিনিকে ক্ষমতায় বসিয়েছিল কারণ তিনি বিপ্লবী গণআন্দোলনের অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও নির্মম শত্রু হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করেছিলেন। যতক্ষণ পর্যন্ত না নিয়মিত সেনাবাহিনীর সম্মতি মিলেছে ততক্ষণ পর্যন্ত ফ্যাসিস্টদের রোম অভিযান শুরু হয় নি। সেনাবাহিনী যদি প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকত, তাহলে এই “রক্তপাতহীন বিপ্লব” কখনই হত না এবং ইতালির জনগণ মুসোলিনির একনায়কত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেত।
বিপ্লবী পরিস্থিতি মোকাবিলায় ব্যর্থ হওয়ায় শাসক শ্রেণি—জমিদার ও পুঁজিপতিরা—সিদ্ধান্ত নিলেন যে বর্তমান সরকারকে প্রতিস্থাপন করা হবে এমন একটি সরকার দ্বারা যা বিপ্লবী আন্দোলন দমন করতে বেশি কার্যকর হবে এবং একই সাথে তাদের আদেশের প্রতি বেশি বাধ্য থাকবে। নিয়মিত সেনাবাহিনীর অফিসাররা ছিল তাদেরই লোক, তারা তাদের হাতের মুঠোয় ছিল। কিন্তু বিপ্লবী পরিস্থিতিতে সাধারণ সৈন্যদের আনুগত্যের উপর নির্ভর করা চলে না। তাই শুধুমাত্র ওই নিয়মিত সেনাবাহিনী জনপ্রিয় বিপ্লবী আন্দোলন দমনের নির্ভরযোগ্য হাতিয়ার হতে পারে না। কিছু অংশের জনগণকে প্রতিবিপ্লবের পক্ষে জয় করতে হবে। ফ্যাসিস্টদের ছদ্ম-সিন্ডিক্যালিস্ট প্রচারণা ও জাতীয়তাবাদী উগ্রতা সেই উদ্দেশ্য সাধন করেছিল। মধ্যবিত্ত গুণ্ডা ও পিছিয়ে পড়া শ্রমিকদের মুসোলিনির ব্ল্যাক শার্ট ভাড়াটে বাহিনীতে ভর্তি করা হয়েছিল। পরিকল্পনা ছিল মুসোলিনিকে ক্ষমতায় বসানো, যাতে প্রতিবিপ্লবকে জনপ্রিয় আন্দোলনের মতো দেখায়। অবশ্য, এই নোংরা কাজ তার “সুপারম্যান”-দের দিয়ে করানোর কথা ভাবা হয়নি। নিয়মিত সেনাবাহিনী সদা প্রস্তুত ছিল পিছভরসা হিসেবে।
এই পরিস্থিতিতেই মুসোলিনিকে “ক্ষমতা দখল” করতে হয়েছিল। যেহেতু নিয়মিত সেনাবাহিনী ইতোমধ্যেই তাকে সুরক্ষা ও পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছিল, তাই কোনো কার্যকর প্রতিরোধের সম্ভাবনা ছিল না। ক্ষমতা তার পদ তলেই শায়িত ছিল। তবুও শেষ মুহূর্তে নায়ক মহাশয় ভয়ে কাঁপতে শুরু করলেন। রোম অভিযানের আদেশ দিয়েও তিনি নিজে নেতৃত্ব দেওয়ার ঝুঁকি নিলেন না। সেই বীরত্বের নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার সময় মিলানে নিরাপদে ঘুমাচ্ছিলেন নায়ক মহাশয়। রোম দখল হওয়ার পর তার কয়েকজন বিশ্বস্ত সহকারী তাকে টেলিফোনে বিজয়ের খবর দিয়ে দৃশ্যপটে উপস্থিত হতে বললেন। তখনও তিনি নিজের চামড়া বাঁচানোর কথা ভেবে উদ্বিগ্ন। স্পষ্টতই, তিনি এই অলৌকিক ঘটনা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। শেষমেষ জেনারেল স্টাফের কাছ থেকে ডাক পাঠিয়ে তাকে রাজি করানো হয়েছিল “রোমের বিজয়ী হিসেবে” স্লিপিং কারে করে আসতে।
তখন পর্যন্ত এই “বিপ্লব” রক্তপাতহীন ছিল। কিন্তু এই ট্র্যাজি-কমেডির সূচনা ছিল যথেষ্ট রক্তাক্ত। হাজার হাজার শ্রমিককে হত্যা করা হয়েছিল। শ্রমিকেরা সহিংসতা শুরু করেনি। তারা শান্তিপূর্ণভাবে সেইসব কারখানা দখল করে নিয়েছিল যেগুলো লাভজনক না হওয়ায় মালিকপক্ষ বন্ধ করে দিয়েছিল। যদি তাদের শান্তিপূর্ণভাবে কারখানা চালানোর অনুমতি দেওয়া হত, তাহলে কোনো রক্তপাত ছাড়াই একটি সত্যিকারের বিপ্লব ঘটত। কিন্তু তা তো হতে দেওয়া হয়নি। শ্রমিকরা শান্তিপূর্ণভাবে যা করতে চেয়েছিল—যেমন দেশের শিল্পব্যবস্থা চালু রেখে শ্রমিকদের জীবিকা নিশ্চিত করা এবং দেশের অর্থনীতিকে পঙ্গু হয়ে পড়া থেকে রক্ষা করা—পুঁজিপতিরা তা করতে ব্যর্থ হওয়ায়, দেশের প্রতিষ্ঠিত আইনকানুনকেও উপেক্ষা করে সংগঠিত সহিংসতার পথ বেছে নেওয়া হয়েছিল।
ক্ষমতায় আসার পর মুসোলিনি নতুন শাসনব্যবস্থার সবরকম বিরোধিতাকে দমনের জন্য ব্যাপক সহিংসতা চালিয়েছিলেন। ফ্যাসিবাদের বিজয় ছিল না কোনো বিপ্লব, না ছিল তা রক্তপাতহীন। এটি যে শাসনব্যবস্থাকে ধ্বংস করেছিল সেই শাসনের পক্ষ থেকে কোনো প্রতিরোধ ছিল না। তাই রক্তপাতের প্রয়োজন পড়েনি। অন্যদিকে, বিপ্লবী জনগণের প্রতিরোধ ছিল অস্ত্রহীন। তাই তাদের নিশানা করে পরিচালিত সহিংসতাকেও ব্যাপক রক্তপাতের রূপ নিতে হয়নি। কিন্তু হাজার হাজার নারী-পুরুষকে আজীবন কারাগারে নিক্ষেপ করাটা তরোয়াল দিয়ে হত্যার চেয়ে কম ‘রক্তাক্ত’ ব্যাপার তো নয়। এছাড়াও আরও হাজার হাজার মানুষকে গণহারে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল।
এবার জার্মানির প্রসঙ্গে আসা যাক। হিটলারের “সাংবিধানিকভাবে” ক্ষমতায় আসার দাবিটিও খণ্ডন করা দরকার। এই দাবির গুলগাপ্পা চরিত্র স্পষ্ট। প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান কার্যত স্থগিত থাকার সুবাদে হিটলারের ক্ষমতায় আরোহণ সহজ হয়েছিল। তিনি সংবিধান লঙ্ঘন করেননি। সে’কাজ তার হয়ে করে দিয়েছিল তার নিয়োগকর্তা ও পৃষ্ঠপোষকরা। তিনি ক্ষমতায় এসেই ভাইমার সংবিধান বাতিল করে উৎসব করেছিলেন, যা ইতিমধ্যেই জাঙ্কার-সামরিকবাদী ফন হিন্ডেনবার্গের নেতৃত্বাধীন “প্রজাতান্ত্রিক সরকার” দ্বারা কার্যত ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ইতালির মতো জার্মানিতেও ফ্যাসিস্টরা বড় পুঁজিপতিদের বেতনভুক্ত এজেন্ট হিসেবে ক্ষমতায় এসেছিল এবং সফল হয়েছিল কারণ তারা যে শাসনব্যবস্থাকে প্রতিস্থাপন করেছিল, তার পক্ষ থেকে বাস্তবে কোনো প্রতিরোধ ছিল না। জনগণের প্রতিরোধকে রাষ্ট্রশক্তি জোরপূর্বক দমন করেছিল যাতে করে ওদের ক্ষমতায় যাওয়ার পথ সুগম হয়। সেই যাত্রা ছিল এক দীর্ঘ সহিংসতার পথে। এই যাত্রা পরিচালনা করেছিল প্রতিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থার স্বঘোষিত শত্রুরা, শুধু তার সম্মতিতেই নয়, বরং তার সক্রিয় সহায়তায়।
কিন্তু হিটলার জার্মান সরকারের প্রধান হয়েছিলেন নির্বাচনে বিজয়ের ফলে। অর্থাৎ, তিনি ছিলেন জনগণের পছন্দ। তিনি “জনসমর্থন” নিয়ে ক্ষমতায় এসেছিলেন। এই সত্যটি কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায় সেই নির্বাচনেরই তথ্যে। ১৯৩৩ সালের মার্চের নির্বাচন, যা তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতায় বসিয়েছিল, তা ছিল এক ভাঁওতা। ইতিমধ্যেই হিন্ডেনবার্গের অনুগ্রহে তাকে চ্যান্সেলর বানানো হয়েছিল। হিন্ডেনবার্গ ছিলেন জার্মানির সমরবাদী শাসকদের প্রতিনিধি। হিরো মশাইকে এমন অবস্থানে বসানো হয়েছিল যাতে তিনি নির্বাচনে কারচুপি করে চিত্তাকর্ষক বিজয় নিশ্চিত করতে পারেন। বাস্তবে, তিনি হেরে গেছিলেন।
একমাত্র বিরোধিতা এসেছিল দুটি শ্রমিক শ্রেণির দল থেকে, যারা পূর্ববর্তী নির্বাচনে মোট ভোটের প্রায় চল্লিশ শতাংশ পেয়েছিল। নতুন নির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই জনপ্রিয় দলগুলিকে “আইনি” দমন-পীড়ন ও বেআইনি সন্ত্রাসের মাধ্যমে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কার্যত সরিয়ে রেখে। সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টিকে তখনও আনুষ্ঠানিকতার খাতিরে আইনগতভাবে থাকতে দেওয়া হলেও কমিউনিস্ট পার্টিকে সম্পূর্ণ দমন করা হয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টি ছিল দেশের তৃতীয় বৃহত্তম দল, সংসদে যার একশোটি আসন ছিল। শুধুমাত্র কমিউনিস্ট পার্টির দমনই প্রমাণ করে যে ফ্যাসিস্টদের “গণতান্ত্রিক বিজয়” পেতে আগে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করতে হয়েছিল। সকল বিশিষ্ট কমিউনিস্ট হয় কারাগারে ছিল নয়তো আত্মগোপনে। এর সদস্যরা ফ্যাসিস্ট গুণ্ডাবাহিনীর রক্তাক্ত সন্ত্রাসের শিকার হয়েছিল। সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টিও একইরকম সন্ত্রাসের শিকার হয়েছিল। ভোটকেন্দ্রগুলি ফ্যাসিস্ট গুণ্ডাদের সতর্ক প্রহরায় চলেছিল। কমিউনিস্ট বা সমাজতান্ত্রিকদের ভোট দিতে যাওয়াটা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। অনেকে ভোট দেয়নি; অনেককেই তাদের নিজের সিদ্ধান্তে ভোট দিতে দেওয়া হয়নি। যারা ফ্যাসিস্টদের ভোট দিয়েছিল, তাদের অনেকেই ভয়ে ভীত বাধ্য হয়ে তা করেছিল। হাজার হাজার কমিউনিস্ট ভোট দিতে পারেনি কারণ তারা আত্মগোপন করে ছিল। অন্যদিকে, যারা হিটলারকে ভোট দিতে চায়নি তাদের নাৎসি ঝটিকা বাহিনী জোর করে ধরে নিয়ে এসেছিল। বিরোধী দলগুলির সংবাদপত্রগুলিকে দমন করা হয়েছিল, তাদের প্রচার সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল, সভাগুলি বেতনভুক্ত গুণ্ডাদের দ্বারা ভেঙে দেওয়া হয়েছিল, তাদের সমর্থকদের ভয় দেখিয়ে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভোট দিতে বা ভোট না দিতে বাধ্য করা হয়েছিল। অন্যদিকে, রাষ্ট্রের সমগ্র প্রচারযন্ত্র ফ্যাসিস্টদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল।
এমন পরিস্থিতিতে ন্যায্য নির্বাচন সম্ভব নয়। এমন পরিবেশে অনুষ্ঠিত “নির্বাচনের” ফলাফল জনমতকে প্রতিফলিত করে না। কিন্তু এমন একটি ভাঁওতার মাধ্যমেও হিটলার বাস্তবে কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। প্রদত্ত ভোটের চল্লিশ শতাংশের বেশি পায়নি ফ্যাসিস্টরা। এটি সমগ্র ভোটারদের একটি ক্ষুদ্র অংশকেও প্রতিনিধিত্ব করে না, কারণ উপরে উল্লিখিত কারণে লক্ষাধিক ভোটার ভোট দিতে যায়নি বা যেতে পারেনি।
অন্যদিকে, অপরিসীম সন্ত্রাস ও অতিকঠিন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কমিউনিস্ট পার্টি সংসদে তাদের একশো আসনের মধ্যে আশিটি আসন ধরে রাখতে পেরেছিল। তাই তাদেরকেই নির্বাচনের প্রকৃত বিজয়ী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। কারণ স্বাভাবিক অবস্থায় এই দলটি আরও অনেক বেশি ভোট পেত। এটা দেখায় যে, সত্যিকারের গণতান্ত্রিক নির্বাচন হলে অপমানজনক পরাজয়ই ছিল হিটলারের ভবিতব্য। কমিউনিস্টদের তুলনায় কিছুটা স্বাধীনতা পাওয়ায় সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টি এই অসম যুদ্ধ থেকে আরও ভালো ফলাফল নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায় যে কমিউনিস্টরা সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট ও অন্যান্য ছোট ছোট ফ্যাসিবাদ-বিরোধী গোষ্ঠীগুলির সাথে মিলে নতুন সংসদের প্রায় অর্ধেক আসন জিতেছে। তথাকথিত বিজয়ী হিটলার এরকম একটি সংসদের সম্মুখীন হওয়ার সাহস পায়নি। আরও সহিংস কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল, গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার শেষ চিহ্নটুকুও বিলুপ্ত করা হয়েছিল, যাতে তার “সাংবিধানিক একনায়কত্বের” পথ পরিষ্কার হয়। সংগঠিত সন্ত্রাস সত্ত্বেও যে ভোটাররা ভোট দিয়েছিলেন এবং আরও অনেকে যারা ভোট দিতে পারেননি—এরকম প্রায় চল্লিশ লক্ষ ভোটারের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন সংবিধানসম্মতভাবে নির্বাচিত আশিজন কমিউনিস্ট প্রতিনিধি। কিন্তু তাদের সংসদে আসন গ্রহণ করতে দেওয়া হয়নি। উল্লেখযোগ্য সংখ্যার সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক প্রতিনিধিকেও ব্যক্তিগত অভিযোগ ও হয়রানি এড়াতে অনুপস্থিত থাকতে হয়েছিল। সংক্ষেপে, যে ছোট্ট সংসদ হিটলারকে একনায়কত্ব প্রদান করেছিল, তা ভোটারদের সত্তর শতাংশের বেশি প্রতিনিধিত্বকারী ছিল না, এবং ভোটারের একটি ক্ষুদ্র অংশ দ্বারা নির্বাচিত অর্ধেক প্রতিনিধিও হিটলারকে ভোট দেয়নি। তাই ফ্যাসিস্টরা ক্ষমতায় এলেও মোট ভোটারের পঁয়ত্রিশ শতাংশের বেশি সমর্থন তারা আদায় করতে পারেনি। এটা হিটলারের “সাংবিধানিক” ক্ষমতায় আরোহণের আসল প্রকৃতিকে প্রকাশ করে।
হিটলারের “গণতান্ত্রিক” বিজয়ের মিথ্যা গল্পটি আরও একটি ঘটনা দ্বারা প্রকাশ পায়। ১৯২৮ সাল থেকে ফ্যাসিস্ট ভোট ধারাবাহিকভাবে দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু যে নির্বাচনের মাধ্যমে হিটলারকে “সাংবিধানিক একনায়কত্বে” উন্নীত করা হয়েছিল, তার কয়েক মাস আগের নির্বাচনে ফ্যাসিবাদের অগ্রগতি গুরুতর ধাক্কা খায়। নাৎসিদের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা হঠাৎ করে প্রায় বিশ লক্ষ কমে গিয়েছিল। এ এক স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল যে কৃত্রিমভাবে সমর্থনপুষ্ট আন্দোলন তার শীর্ষবিন্দু অতিক্রম করেছে এবং পতনের দিকে এগোচ্ছে। পিছিয়ে পড়া মধ্যবিত্ত জনগণের মধ্যেকার বুদ্ধিমানরা ফ্যাসিবাদে বিশ্বাস হারাচ্ছিল। তারা নাৎসি জনপ্রিয়তার বুলি ও তর্জনগর্জন সর্বস্বতা বুঝতে পেরেছিল। পূর্ববর্তী নির্বাচনে নাৎসিরা বেশ কয়েকটি প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল। সেখানে তারা মন্ত্রিসভা গঠন করেছিল যে মন্ত্রীসভা ভোটারদের দেওয়া তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। ওদের অনুগামীদের আস্থা নড়বড়ে হয়ে যায়। এবং যদি ওদের পৃষ্ঠপোষকরা তড়িঘড়ি সাহায্য না করত, তাহলে ফ্যাসিবাদী আন্দোলনটি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ত। বুর্জোয়ারা তাদের হিরোকে ঠেলে গুঁতিয়ে ক্ষমতার সিংহাসনে তুলে দেওয়া দরকার বলে মনে করল, কারণ স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছিল যে মুখে যতই বাতেলা ঝাড়ুক না কেন হিরোর চ্যালাচামুণ্ডারা খোলা ময়দানে বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণির সাথে সম্মুখ সমরের সাহস দেখাতে পারছে না।
বার্ধক্যজীর্ণ হিন্ডেনবার্গকে তার প্রুশিয়ান গর্ব ত্যাগ করে ক্ষমতা সেই উদ্ধত ব্যক্তির হাতে তুলে দিতে বলা হয়েছিল, যিনি নির্বাচনে গুরুতর বিপর্যয়ের শিকার হয়েছিলেন এবং সংসদে সংখ্যালঘু ছিলেন। নির্বাচনে জনপ্রিয় সমর্থন পেয়ে হিটলার ক্ষমতায় আরোহণ করেন নি। বরং এই “ফালতু একটা বোহেমিয়ান ড্রিল-সার্জেন্ট”-কে অহংকারী ফিল্ড মার্শালের অনিচ্ছুক অভ্যর্থনার মাধ্যমে ক্ষমতায় বসানোর বার্তা দেওয়া হয়েছিল। এই দু’জনই একই প্রভুর সেবা করেছিল, যে প্রভুর আদেশে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি কলঙ্কিত গণতন্ত্রের দেবীকে “ড্রিল-সার্জেন্টের” হাতে সমর্পণ করেছিলেন লাঞ্ছিত হতে। এইভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠের গণতান্ত্রিক রায়ের বিরুদ্ধে ক্ষমতায় বসে, হিটলার নির্বাচনী বিজয়ের নাটক করার জন্য বিদ্যমান ব্যবস্থার সব ধরণের যন্ত্রপাতিকে আইনি ও বেআইনি উভয়ভাবেই ব্যবহার করেছিলেন। সভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে ধিক্কৃত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটিয়েছিলেন তিনি। সংগঠিত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম কমিউনিস্ট পার্টিকে নির্মূল করার একটি জুতসই অজুহাত খুঁজতে নাৎসিরা রাইখস্ট্যাগ ভবনে আগুন লাগিয়েছিল। এই অগ্নিসংযোগ ছিল “রক্তপাতহীন বিপ্লবের” সংকেত। হিটলার রাইখস্ট্যাগ পোড়ানোকে ঈশ্বরের ইশারা হিসেবে অভিহিত করেছিলেন। ঐশ্বরিক অনুমোদন নিয়ে তিনি সকল বিরোধিতাকে দমন করেছিলেন। তবুও জনগণ তাকে নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিতে অস্বীকার করেছিল। ঈশ্বর আধুনিক মেসিয়াহকে সাহায্য নাও করতে পারেন, কিন্তু বুর্জোয়ারা তাদের নায়ককে মহিমান্বিত করতে প্রস্তুত ছিল। তাদের মনোনীত হাতিয়ার হিসেবে তাকে যেকোনো উপায়ে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অবস্থানে উন্নীত করতে হয়েছিল, যাতে সে তার জন্য নির্ধারিত রক্তাক্ত কাজটি সম্পাদন করতে পারে। “রক্তপাতহীন বিপ্লব” অপ্রতিরোধ্য সহিংসতার প্রয়োগে সংঘটিত হয়েছিল এবং এর পরিণতি ছিল সবচেয়ে রক্তাক্ত। বুর্জোয়াদের অনুগ্রহে একনায়কত্বের ক্ষমতায় আসীন হয়ে হিটলার, তার ইতালিয় পূর্বসূরির মতোই, পৃষ্ঠপোষকদের ইচ্ছা পূরণ করে চলেছে।
“রক্তপাতহীন বিপ্লব” মানবতার সকল মহান আধ্যাত্মিক অর্জন ধ্বংস করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। “জার্মানি একটি ভয়ানক উদাহরণ প্রদর্শন করছে কল্পনাতীত ও অবিশ্বাস্য মাত্রায়। বিংশ শতাব্দীর জার্মানির জাতীয় সংস্কৃতির বিশুদ্ধতা রক্ষার আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত শিক্ষণীয় কাণ্ডকারখানার সমান্তরাল উদাহরণ খুঁজতে হলে প্রারম্ভিক মধ্যযুগীয় ইতিহাস খুঁজতে হবে।” (রবার্ট ব্রিফল্ট, “দ্য ন্যাশনালিস্ট ক্রেজ ইন কালচার”, “কারেন্ট হিস্ট্রি”, নিউ ইয়র্ক, আগস্ট ১৯৩৩)। সংস্কৃতির ইতিহাসের এই বিশিষ্ট পণ্ডিত আরও লিখেছেন: “সমস্ত বিদেশী সমালোচক ফ্যাসিস্ট ইতালির অসাধারণ শৈল্পিক ও সাহিত্যিক অনুর্বরতার উপর মন্তব্য করেছেন”।
আধুনিক সংস্কৃতির প্রতি ফ্যাসিস্টদের শত্রুতা অত্যন্ত উগ্র। এ হল সম্পূর্ণ বর্বরতায় পতনের প্রতীক। ফ্যাসিবাদের এই দিকটি সভ্য বিশ্বজুড়ে তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি করেছে। এমনকি যারা ফ্যাসিবাদের মৌলিক কাজ—অর্থাৎ পুঁজিবাদী সমাজের টলমলে কাঠামোকে শক্তিশালী করতে বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনকে নির্বিচারে দমন করা—এতে আপত্তি করে না, তারাও এই বর্বরতায় হতবাক হয়েছে।
এই ‘রক্তপাতহীন’ বিপ্লবের অলৌকিক কীর্তি দাবি করে যে “সুপারম্যানরা”, তাদের সম্পর্কে বলার চেয়ে কিছু নিরপেক্ষ প্রামাণিক উদার মতামত উদ্ধৃত করাই যথেষ্ট:
“জার্মানি আজ মাদকাসক্ত, খুনি, চোর, জালিয়াত ও নৈতিকভাবে অধঃপতিতদের দ্বারা শাসিত। এগুলি কেবল গালি নয়; এগুলি নাৎসি আন্দোলনের প্রধান নেতাদের সাধারণভাবে স্বীকৃত চরিত্রবৈশিষ্ট্য”। (দ্য নেশন, নিউ ইয়র্ক, ২ আগস্ট ১৯৩৩)
“এমন অপরাধ সংঘটিত হয়েছে যার ভয়াবহতা প্রতিবাদকে স্তব্ধ করে দেয়, কারণ সভ্য মন এর অবিশ্বাস্যতায় স্তম্ভিত হয়ে যায়। আরও কঠিন হয়ে ওঠে সেইসব লক্ষ লক্ষ জার্মানের ভবিষ্যৎ কল্পনা করা, যারা এতটাই সভ্য ও বুদ্ধিমান যে তারা কখনই এই উন্মাদ ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট রাষ্ট্রের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে না”।(হ্যারিসন ব্রাউন, 'সিক্স মান্থস অব হিটলারিজম', দ্য নেশন)
এই ইংরেজ সাংবাদিক, যিনি জার্মানিতে চার বছর বসবাস করেছিলেন, আরও লিখেছেন যে নাৎসি যুদ্ধ-প্রচার শান্তিবাদী সংগঠনের সদস্য হওয়াকে দীর্ঘমেয়াদি কারাদণ্ডে (আইনত!) শাস্তিযোগ্য অপরাধে পরিণত করেছে। বিখ্যাত জার্মান লেখক কার্ল ফন অসিয়েত্স্কি কেবল শান্তিবাদী হওয়ার কারণে নির্যাতন ও কারাবরণের শিকার হয়েছেন। গত বছরই তিনি শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন, কিন্তু এখনও তিনি কারাগারে, প্রকাশ্য বিচারের অধিকার থেকেও বঞ্চিত।
একজন উদারমনা আমেরিকান সাংবাদিক, যিনি ভার্সাই চুক্তির অবিচারে ভোগা জার্মান জনগণের প্রতি সহানুভূতিশীল, লিখেছেন:
“যুদ্ধপূর্ব সামরিকবাদ ও নৃশংসতার একটি আচরণ রাইখজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে, যার সাথে যুক্ত হয়েছে জাতিকে একটি উগ্র মতবাদের মধ্যে আত্মস্থ করার আধা-রহস্যময় প্রক্রিয়া। এই মতবাদ সেই সুপারম্যানরা লুফে নেন যাদের কাছে ইহুদি, অধ্যাপক, শান্তিবাদী, সমাজতন্ত্রী, র্যাডিক্যাল, উদারপন্থী ও গণতন্ত্রীরা মানবেতর”। (জন গান্থার, দ্য নেশন, নিউ ইয়র্ক, ৭ জুন ১৯৩৩)
বাভারিয়ার প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ড. ফ্রিৎস শোয়ায়ার, যাকে সরিয়ে এখন একজন ফ্যাসিস্ট প্রো-কনসাল পদস্থ হয়েছেন, তাঁর প্রাক্তন সহকর্মীকে একটি ব্যক্তিগত চিঠিতে লিখেছেন:
“আইন ও ন্যায়বিচারের কোনো চিহ্ন অবশিষ্ট নেই। ঐশ্বরিক ও মানবিক অধিকার পদদলিত করা হচ্ছে, আর নৈতিকভাবে অধঃপতিতরা নিজেদেরকে জার্মানির নৈতিক পুনর্জন্মদাতা বলে দাবি করছে, যদিও বাস্তবে তারা বলপ্রয়োগে নিজেদের ইচ্ছা অন্যদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে মাত্র এবং জঙ্গলের জানোয়ারের মতো নিজেদের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করছে”। এই সত্য মতামত প্রকাশের অপরাধে ড. শোয়ায়ারকে “রাষ্ট্রদ্রোহ”-এর দায়ে কারাদণ্ড দেওয়া হয়।
“এটা সম্পূর্ণ স্পষ্ট যে বর্তমান জার্মান সরকার পাষণ্ড ও প্রতিক্রিয়াশীলদের নিয়ে গঠিত, যারা ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টায় জার্মান সংস্কৃতির যা কিছু সুন্দর ও মূল্যবান তার সবকিছুকে ধ্বংস করছে”। (দ্য নিউ রিপাবলিক, নিউ ইয়র্ক, ২৬ এপ্রিল ১৯৩৩)। এই উদ্ধৃতিটি একটি বেনামী চিঠি থেকে নেওয়া। লেখক তাঁর নাম প্রকাশ করতে চাননি, কারণ সত্য বলার অপরাধে তিনি (একজন বয়স্ক অধ্যাপক) ফ্যাসিস্টদের বর্বর প্রতিশোধের শিকার হবেন। সত্য দমনের এই সন্ত্রাসী ব্যবস্থা এতই নিখুঁত যে, যারা নিজেরা জার্মানি থেকে পালিয়েছেন তাঁরাও সত্য বলতে ভয় পান। তাঁদের অনেকের আত্মীয়-স্বজন এখনও জার্মানিতে রয়েছে, এবং প্রতিশোধ প্রায়শই তাঁদের উপর নেওয়া হয়।
“রক্তপাতহীন বিপ্লব”-এর এই বর্বর সহিংসতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, “সুপারম্যানদের” মধ্যেও শেষ যে দু’একজন নিজেদের ভেতরে সভ্যভব্যতার লেশমাত্র টিকিয়ে রেখেছিলেন তারাও প্রতিবাদ শুরু করেন। জানা যায়, কাউন্ট ফন রেভেন্টলো হিটলারের কাছে ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের (নারী সহ) নাৎসি সদর দপ্তরে টেনে নিয়ে গিয়ে প্রহার ও (নারীদের) অকথ্য নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।
জার্মান প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম চ্যান্সেলর ফিলিপ শাইডেমান প্রাগের নির্বাসনে থেকে লিখেছেন:
“হিটলারের বার্লিন হলো অগ্নিসংযোগকারীর মশাল, যাকে নিয়ে অপরাধী ও মানসিকভাবে বিচ্যুত একটি গোষ্ঠী বারুদ আর আগুন নিয়ে খেলা করছে”। (দ্য টাইমস, লন্ডন, জুন ১৯৩৫)
এই মত প্রকাশের “অপরাধে” শাইডেমানের পরিবারের সকল সদস্যকে (নারীসহ) গ্রেফতার করে একটি ডিটেনশন ক্যাম্পে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছিল যেখানে “অপরাধী ও মানসিকভাবে বিচ্যুত” হিটলার ভক্তরা বয়স বা লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল বন্দীর ওপর মধ্যযুগীয় নির্যাতন পদ্ধতি প্রয়োগ করত।
“আডলফ হিটলার হলেন জীবনীকারদের হতাশা। কোনো জীবিত রাজনৈতিক নেতার জীবনী লেখা এমনিতেই যথেষ্ট কঠিন ব্যাপার। তদুপরি সেই নেতা যদি হন অর্ধ-পাগল সিজার, যিনি উন্মত্ত অনুগতদের উল্লাসে ক্ষমতায় আসীন; যখন তিনি একাধারে এক তুচ্ছ ব্যক্তি এবং এক মসিহা; যখন তাঁর আচরণ স্বাভাবিক আবার ভয়ঙ্কর, হাস্যকর আবার মহিমান্বিত, অশালীন থেকে বিকারগ্রস্ততার সীমায় পৌঁছে যাওয়া; এবং যখন তিনি অন্ধকার জগতের ভৌতিক কণ্ঠস্বরের নির্দেশ মানেন ও যারা অতিরিক্ত জানেন তাঁদের নির্মূল করে ফেলেন—তখন কোন জীবনীকারের পক্ষে তাঁর জীবন তুলে ধরা প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে”। (দ্য নিউ রিপাবলিক, নিউ ইয়র্ক, ১০ জুন ১৯৩৬)
“ফ্যুয়েরারের বক্তৃতা শুনলে মনে হবে আপনি এক মানসিক বিকারগ্রস্তের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। গত জুন মাসের ঘটনাবলী (যখন তিনি তাঁর এক সময়ের বিশ্বস্ত সহচরদের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করছেন) আমাদের বাধ্য করে তাঁকে এক বিপজ্জনক ‘প্যারানয়েড ম্যানিয়াক’ হিসেবে চিহ্নিত করতে। এক মহান ও অত্যন্ত সভ্য জাতি আজ এক অস্থির স্নায়বিক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তির দয়ার ওপর নির্ভরশীল, যে হিসেবকষা ক্রোধের বিস্ফোরণ ঘটাতে সক্ষম। আর তার পাশে যে একমাত্র ব্যক্তি হয়তো তাকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, তিনি হলেন গেরিং—যিনি নিজেই বলছেন যে তিনি নিজে ফ্যুয়েরারের থেকে বেশি নিষ্ঠুর ও বেপরোয়া”। (দ্যা নিউও স্টেটস্ম্যান অয়াণ্ড নেশন, লণ্ডন, ১৪ আগষ্ট, ১৯৩৪)
“ফ্যাসিবাদ হলো যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহ, এবং সহিংসতা ও আবেগোন্মত্ততার প্রতি আহ্বান। এর পরিণতি অনিবার্যভাবে নিষ্ঠুরতা, উন্মত্ততা ও গুণ্ডাতন্ত্রে গিয়ে পৌঁছায়”। (রবার্ট ডেল, ‘জার্মানি আনমাস্কড’)। এই কঠোর রায় সরকারি প্রকাশনাগুলির উদ্ধৃতি দ্বারা সমর্থিত। মিস্টার ডেল দেখিয়েছেন, নাৎসিরা যে বর্বরতাকে কখনো প্রয়োজনীয়তা বলে যুক্তি দেয়, আবার কখনো একে ‘ইহুদিদের বানানো মিথ্যা’ বলে নাকচ করে—সেই নিষ্টুরতাগুলি মোটেই আকস্মিক বা বাড়াবাড়ি নয়, বরং এগুলো হল নাৎসি নীতির স্বাভাবিক ও ইচ্ছাকৃত রূপ। “রক্তপাতহীন বিপ্লব”-এর একটি জনপ্রিয় গান হল, “ইহুদি রক্ত যদি ছুরির ফলায় ঝরত—আমাদের কুচকাওয়াজ হত দ্বিগুন তেজে দৃপ্ত”।
হিটলারের আত্মজীবনী অনুসারে, ফ্যাসিবাদের লক্ষ্য হলো দুর্বলদের ধ্বংস ও শক্তিশালীদের বিজয়। সামাজিক সমস্যার ফ্যাসিস্ট সমাধান হলো ইহুদিদের নির্মূল করা এবং বলপূর্বক পুঁজিবাদকে টিকিয়ে রাখা। এর রাজনৈতিক কর্মসূচি হলো সামরীকিকরণ ও দখলের যুদ্ধ। “উপনিবেশ দখল হয়েছিল ক্ষমতার অধিকারে। ইউরোপের প্রয়োজন ছিল কাঁচামাল ও উপনিবেশ, এবং বীরত্বের জীবনদর্শন অনুযায়ী, শ্বেতাঙ্গ জাতি ছিল শাসনের জন্য নির্ধারিত। কিন্তু যদি শাসক জাতি শান্তিবাদের ধারণায় উপনিবেশগুলিকে স্ব-শাসন দেয়, তাহলে তারা বলবে: ‘আমাদের আর ইউরোপের প্রয়োজন নেই’।” (হিটলার, মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সম্মেলনে, ২৬ জানুয়ারি ১৯৩৬)
হিটলারের নিজস্ব স্বীকারোক্তি অনুযায়ী, ইতিহাস তাকে একজন দক্ষ জনপ্রিয়তাবাদী ও নীতিহীন সুযোগসন্ধানী হিসেবেই স্মরণ করবে। তার মতে, জনগণকে নেতৃত্ব দেওয়ার সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি হলো তাদের প্রতারণা করা। তার উত্তেজনা সৃষ্টির নীতি হলো সরল স্লোগান বারবার আওড়ে যাওয়া যতক্ষণ না জনগণ তা বিশ্বাস করতে শুরু করে।
“তার সমগ্র জীবনদর্শন গঠিত হয়েছিল যুদ্ধপূর্ব ভিয়েনার ভবঘুরে দিনগুলিতে। তারপর থেকে কোনো বিকাশ ঘটেনি; কেবল পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া। প্রায় বিশ বছর ধরে তার কোনো বৌদ্ধিক চিন্তা নেই। রাজনীতি সম্পর্কে তার ধারণা বিচিত্র। অর্থনীতির গুরুত্বকে অস্বীকার করে, শ্রমিক শ্রেণিকে মূর্খ হিসেবে অবজ্ঞা করে—যাদের বুদ্ধির অতিরঞ্জন বাস্তবে কোনো মিথ্যা দিয়েই সম্ভব নয়—সে সাধারণ রাজনীতিবিদদের মতো চিন্তায় জর্জরিত হয়নি এবং অন্যায় ও অসমতার বিরুদ্ধে লড়াই করার কোনো প্রেরণা অনুভব করেনি। সেনাবাহিনী, পুঁজিপতি ও জাঙ্কারদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল হয়ে, সে সেই ব্যবস্থা বিলুপ্ত করতে চেয়েছে যা দুর্বল ও নিপীড়িতদেরকে শক্তিশালীদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার অস্ত্র দেয়। গণতান্ত্রিক সভ্যতার মৌলিক নীতিগুলো প্রত্যাখ্যান করে, সে জার্মানির প্রাচীন গৌরব ফিরিয়ে আনতে চেয়েছে—যেখানে শক্তিশালীরা শাসন করবে আর দুর্বলরা হবে প্রজা”।(রুডল্ফ ওল্ডেন, “হিটলার”)
অবশেষে, একজন গবেষকের সাম্প্রতিক বই থেকে কিছু উদ্ধৃতি যিনি “পক্ষপাতহীনভাবে” জার্মানির অবস্থা পর্যবেক্ষণে ষোল মাস কাটিয়েছিলেন। হিটলারের ব্যক্তিগত জীবন বিষয়ে গুজব সম্পর্কে বিশ্বকে সতর্ক করে তিনি লিখেছেন:
“সে নিজেকে একজন ক্রুসেডার হিসেবে দেখে এবং সর্বদা মানবজাতিকে রক্ষার চিন্তা করে। এজন্যই বলশেভিজম থেকে বিশ্বকে রক্ষার কথা বলার সময় সে এমন রহস্যময় উন্মাদনার অবস্থায় পৌঁছায়।” (স্টিভেন এইচ. রবার্টস, “দ্য হাউস দ্যাট হিটলার বিল্ট”)
হিটলারের জনসভায় আবেগতাড়িত উন্মাদনা, কান্না বা পাগলের মতো ফাকা দৃষ্টির বর্ণনা দিতে গিয়ে প্রফেসর রবার্টস গোয়েরিংয়ের উদ্ধৃতি দেন:
“কোনো কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেই এডলফকে আমরা কাঁদতে দেখি।”
সমস্ত সহানুভূতি সত্ত্বেও প্রফেসর রবার্টস গোয়েবলসকে ইউরোপের সবচেয়ে বিপজ্জনক মানুষ হিসেবে ঘোষণা করতে বাধ্য হন:
“কারণ এই মানুষটি মানবজাতিকে ঘৃণা করে অথচ ষাট লক্ষ মানুষের নিয়ন্ত্রণ তার হাতে আছে। বামনাকৃতি গোয়েবলসের মানবজাতির প্রতি বিদ্রূপাত্মক ঘৃণা তার স্নায়বিক পীড়া ও শারীরিক ত্রুটিজনিত ক্ষোভের মিশ্রণ থেকে জন্মেছে। সে সর্বদা তিক্ততার প্রবক্তা। সমগ্র জার্মানি জুড়ে আমি কাউকেই তার সম্পর্কে স্নেহের সাথে কথা বলতে শুনিনি।”
এমনই হলো সেই “সুপারম্যান”-রা, যারা আজ জার্মানির ভাগ্যের নিয়ন্তা। তাদের মতো শাসকরা ইতালি ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে ক্ষমতায় আছে। আর পুরো ইউরোপ যে এই বর্বরতার পূজারি উন্মাদদের কবজায় চলে যাবে না—তার কোনো গ্যারান্টি নেই। আজ ফ্যাসিবাদের ভূত ইউরোপীয় সভ্যতাকে ধ্বংসের হুমকি দিচ্ছে। হিটলার এই জঘন্য ভূতের প্রতিনিধি।
“সে এমন এক ঘটনা যাকে হত্যা করতে হয় অথবা তার হাতে নিহত হতে হয়”। (কনরাড হাইডেন, “হিটলার”)
শেষ লেখার সূত্র।