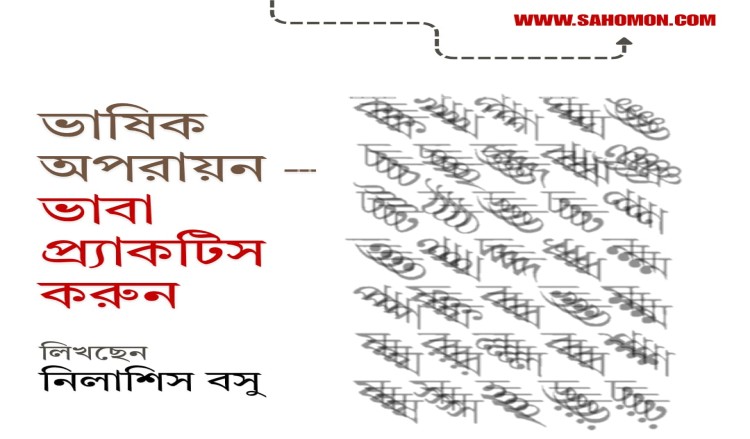ধানবাদের একজন পরিচিত বাঙালি একবার আমাকে বলেছিলেন, “আসল বাঙালি আমরাই, আমাদেরটাই আসল বাংলা, তোমরা সব নকল”। আমার বঙ্গ সংস্কৃতির কর্তৃত্বের অহং বোধের ওপর কথাটা করাৎ শব্দে বজ্রাঘাত করেছিল। তথাকথিত মান্য বাংলা বা প্রমিত বাংলার যে ঠিকা আমরা নিয়ে রেখেছি, সেটাকে নাড়িয়ে দিয়েছিল কথাটা।
বর্তমানে বাংলা ভাষা নিয়ে যে নতুন বিতর্ক শুরু হয়েছে, সেই প্রসঙ্গেই কয়েকটা কথা বোধহয় সবার সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া দরকার। ‘ভাষা’ শব্দটার উৎপত্তি যদিও ভাবের প্রকাশ বোঝাতেই হয়েছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে ভাষা হয়ে উঠেছে মানুষের অস্তিত্বের একক। তাই ভাষিক চেতনা মানুষের অবচেতনেও সবসময়েই কার্যকর থাকে। আজকের নব ভারতের নব রাজত্বে, হঠাৎ বাংলা ও বাঙালির ওপর আক্রমণ হচ্ছে আর সেটা নিয়ে চারপাশ সরগরম, বিষয়টা এতো মোটা দাগে দেখলে, এর সূক্ষতাকে আমরা এড়িয়ে যাব।
আমি কোনও ভাষাতাত্ত্বিক নই, সেই জ্ঞানের পরিসর আমার সীমিত; কোনও ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা এই লেখার উদ্দেশ্যও নয়, কিন্তু স্বাভাবিক গতিতেই সেই আলোচনা আসবে। কারণ বর্তমান ভারতের শাসকরা যেভাবে দাঁত নখ বের করে আক্রমণ শানাচ্ছে আর সেই আক্রমণের পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠেছেন এই বাঙলার কিছু মানুষ, যারা মনে করেন, তাঁরাই ভাষিক ঠিকাদার। তাঁরাই ঠিক করে দেবেন ভাষার নিক্তি মাপার একক কী হবে! যারা বাঙলাভাষী মানুষদের ওপর আক্রমণ করছে, তাদের উদ্দেশ্য নিয়ে সংশয় নেই। কিন্তু বাংলা ভাষার ঠিকাদারি যারা কুক্ষিগত করেছেন, এবং বিভিন্ন যুক্তির অবতারণা করে সেই আক্রমণকে জায়েজ ঠাউরাচ্ছেন, সেখানে অবশ্যই কিছু কথা থেকে যায়।
আগেই বলেছি, নিছক ভাবের প্রকাশ থেকে ভাষার উত্তরণ হয়েছে মানুষের অস্তিত্বের খুঁটি হিসাবে। মানুষ তার সত্ত্বার পরিচিতিকে ভাষিক একক দিয়ে রক্ষার চেষ্টা করে। অন্যান্য রাজ্য নয়, এই বৃহৎ বঙ্গেই একসময় এমন কিছু ভাষা ছিল, যা আজ হয় বিলুপ্ত, নাহলে বিলুপ্তপ্রায়; যেমন – একসময় পুরুলিয়া, বীরভূম, বাঁকুড়ার ওঁরাও জনগোষ্ঠীর মানুষদের ভাষা ছিল ‘কারুখ’। এখন বিলুপ্ত। লোধা জনগোষ্ঠীর মানুষের ভাষা ছিল ‘লোধা’। এখন কিছু সাংস্কৃতিক শব্দ আর নাম বাদে এই ভাষার কোনও অস্তিত্ব নেই। জলপাইগুড়ির টোটো’দের ব্যবহৃত ‘টোটো’ ভাষা চরম সংকটের মুখে, বিলুপ্তপ্রায় অবস্থায় পৌঁছে গেছে। পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ডের মাহালি আদিবাসী গোষ্ঠীর ভাষা ছিল ‘মাহালি’। বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ‘মাল পাহাড়িয়া’ ভাষার আর কোনও অস্তিত্ব নেই। এখন প্রশ্ন হল, এই ভাষাগুলো বিপন্ন বা লুপ্ত হয়ে গেছে, তাতে কার কী? আদতে ভাষাগুলোর অস্তিত্বের সংকট, বা লুপ্ত হয়ে যাওয়ার অর্থ, ওই ভাষাভাষী মানুষদের অস্তিত্বটাই লুপ্ত হয়ে গেছে বা লুপ্তপ্রায়। জীবন্ত ভাষা মানেই, তা একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক যাপনের চলমান, ক্রমবর্ধমান ও পরিবর্তিত দলিল। এই সামগ্রিক প্রক্রিয়াটাই সংকটে। তাই ভাষিক সংকট সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বের সংকট।
বাংলার ওপর বর্তমান আক্রমণের প্রেক্ষিতে এতগুলো কথা কেন বললাম? উক্ত ভাষাগুলো লোপ পাওয়ার পিছনে কি বাংলার আগ্রাসন নেই? অবশ্যই আছে। অনেকেই রে রে করে তেড়ে আসতে পারেন, তবে এটা বাস্তব। আসলে আমি বলতে চাইছি প্রশ্নটা এককেন্দ্রিকতার। আজ বাংলা ভাষা ও ভাষাভাষীদের ওপর আক্রমণের সূত্রটাও এখানেই লুকিয়ে আছে। কীরকম? একটু দেখে নেওয়া যাক।
‘বাংলাদেশী ভাষা’ দিল্লী পুলিশের সৌজন্যে এই শব্দবন্ধ ও তৎজনিত বিতর্ক বেশ কয়েকজন বঙ্গীয় বুদ্ধি বৃত্তির কেউকেটাকে মাঠে নামিয়েছে, যাঁরা সোচ্চারে বলে চলেছেন, ঠিকই তো, এখানকার বাংলা ভাষা তো আলাদা। ঠিক ‘ওইভাবে’ তো আমরা কথা বলিনা! আমাদের জীবিকার ভাষা তো ওটা নয়! ‘বাংলাদেশী ভাষা’ হিসাবে যেটা বলা হচ্ছে, ঠিকই বলা হচ্ছে, কারণ তার মধ্যে ভারতীয়ত্ব নেই। প্রশ্নটা এখানেই। ভারতীয়ত্বের ছাঁকনিতে বাংলা বা অপরাপর ভাষাগুলোকে দেখা হবে, নাকি বিভিন্ন ভাষিক পরিচিতির ঐক্যের মিশ্রিত রূপ ভারতীয়ত্ব? আমি সোচ্চারে দ্বিতীয়টার পক্ষে। স্বাধীনতাত্তোর ভারতীয় জাতীয়তাবাদ নির্মাণের যে প্রকল্প, সেই প্রকল্পেরও মূল ভাব এটাই ছিল। বিবিধের কারণেই মিলন। বলা যেতে পারে, মিলনের মূল সূত্রটাই বহুমাত্রিকতা। এখন এখানে সমস্যাটা কোথায়? সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের যুক্তি, ‘ঠিক ওইরকম ভাষা আমরা ব্যবহার করি না’! বিজেপি’র এক তরুণ নেতা খানিক জ্যোতিদান করেছেন এনাদের যুক্তিতে, তিনি ‘বাঙালি’ ও ‘বাং-আলি’ এই দুইয়ে ফারাক করতে বলেছেন।
আর এই প্রেক্ষিতেই ‘জলের ওপর পানি না পানির ওপর জল’ এই নিয়ে বিশ্লেষণের অন্ত নেই। এখন বিষয় হল, না জানাটা কারও দুর্বলতা হতে পারে, কিন্তু দোষ নয়। কিন্তু জেনেও ভুলভাবে কোনওকিছুকে পরিবেশন করলে সেটার পর্দার আড়ালের উদ্দেশ্য বিধেয় নিয়ে সংশয় জাগে বৈকি। ‘পানি’ শব্দটার ব্যুৎপত্তিগত উৎস যে সংস্কৃত ‘পানীয়’র প্রাকৃত রূপ, সেটা এই বিদ্বদজনেরা জানেন না, এমনটা মনে হয়না। ‘জল’ শব্দটারও উৎপত্তি সংস্কৃত থেকে। আর যেটা পানযোগ্য সেটাই পানীয়। সেখান থেকেই এসেছে পানি। সেইকারণেই পানি শব্দটার ব্যবহার অন্যান্য ভাষাতেও দেখা যায়; তাহলে এটা বাংলাদেশী হয়ে গেল কীভাবে! এখনও পর্যন্ত প্রাপ্ত, বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন যদি চর্যাপদকে ধরে নেওয়া হয়, সেটার একটা দু’টো পদের উদাহরণ দেখে নেওয়া যাক।
“চারি পান্তে করি পানি,
তাহি নাহি গৃহ বাহির।”
(শবরপা, পদ ১৫)
অর্থ - চারিদিকে পানি (জল) থাকলেও, এর কোনও ঘর নেই, বাহিরও নেই।
“পানি পাতি নাহি ছায়া
মরু দেশে কেমন আশা?”
(লুইপা, পদ ৩৮)
অর্থ – পানি নেই, পাতাও নেই, ছায়াও নেই, এমন মরুভূমিতে কোন আশায় বাঁচা যায়?
“কাহা পানি, কাহা জ্বলা,
নাহি দিশা নাহি পাড়া।”
(কাহ্নপা, পদ ৪১)
অর্থ – কোথাও পানি, কোথাও আগুন, না দিক আছে, না তীর।
চর্যাপদে এরকম আরও বহু পদ আছে, যেখানে পানি শব্দের নিদর্শন পাওয়া যায়। এ তো গেল চর্যাপদ। এবার আরও কিছু নিদর্শন দেখে নেওয়া যাক। চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ভক্ত কবি বিটঠল দাসের লেখা একটি পদ –
“চোখে পানি গড়াই রে গৌর চরণে সাধ।
দীন হীন জানি মোকে, কবে তোর হইব দাস।।”
শাক্ত কবি রামপ্রসাদ সেন একটি পদে লিখছেন –
“দূরে জল, কাছে পানি,
মাকে ডাকি তবু মেলে না মানি।”
রামপ্রসাদ কিন্তু জল ও পানি দু’টো শব্দই ব্যবহার করছেন, এবং সেখানে কোনও বিভেদ নেই।
এবার একটু মঙ্গলকাব্যে চোখ রাখা যাক। মনসা পাঁচালির সবথেকে পুরানো কবি, বর্তমান উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বাসিন্দা, বিপ্রদাস পিপিলাই পঞ্চদশ শতকে লিখছেন মনসাবিজয় কাব্য। সেখানে আছে –
“বেহুলা বৈঠা ধরে নামিলো যাত্রা,
পানিতে ভাসে নগর, দিশে না পাত্রা।”
আবারও ফিরতে হচ্ছে একটু ভাষাগত আলোচনায়। যে কোনও ভাষার ক্রমবিকাশের ইতিহাস ঘাঁটলেই দেখা যাবে, ভাষা পুষ্ট হয় অপরাপর ভাষাগুলোর শব্দকে গ্রহণ করে। স্বকীয় ভাষিক ব্যঞ্জনাকে অক্ষুণ্ণ রেখে সে প্রতি মুহূর্তে প্রতিশব্দ আহরণ করে, বা সৃষ্টি করে। এইকারণেই ভাষা আত্মিকরণ করে, বিচ্ছিন্ন করে না। ভাষার চলমানতা ও বিকাশ এইভাবেই অক্ষুণ্ণ থাকে। নাহলে ভাষা বদ্ধ জলা হয়ে যাবে, একসময় মজে শুকিয়ে যাবে। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেও এর কোনও ব্যত্যয় ঘটেনি। হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে বিবর্তিত হওয়া বাংলা ভাষা স্বাভাবিকভাবে অন্যান্য শব্দ আত্মিকরণের মধ্য দিয়েই পুষ্ট হয়েছে। তাই যাঁদের মত, ‘আব্বা’ আমাদের শব্দ নয়, আমরা তো ‘বাবা’ বলি। তাঁদের এটা কে বোঝাবে ‘বাবা’ শব্দটাও বাইরে থেকে আসা। এইসব নবত্থিত বাংলা সংস্কৃতির ঠিকাদারদের এটা জানিয়ে দেওয়া দরকার, বাংলা ভাষার যে সংরূপেরই তাঁরা দোহাই দিন না কেন, তার ভারতীয় সংরূপের প্রতি নিজেদের গলা বিদীর্ণ করুন না কেন, সমস্ত সংরূপেই বহু ভাষা থেকে গৃহীত শব্দাবলীই তাঁদের ভরসা। শুধু আরবি কিংবা ফারসি নয়, তুর্কি, পর্তুগিজ, ফরাসি, ডাচ, ইংরেজি, তিব্বতীয়, বর্মী, চীনা, সিংহলী ও অন্যান্য ম্যান্ডেরিন সহ বহু বহিঃভারতীয় ভাষা, এবং সঙ্গে সংস্কৃত, পাকৃত, পালি, তামিল, তেলেগুর মতো দ্রাবিড়িয় ভাষার মিলিত বর্তমান সংরূপই হল আজকের তথাকথিত প্রমিত বাংলা।
এবার আমি একটা বিতর্কিত বিষয় উত্থাপন করব। অমিত মালব্য ‘বাংলা বলে কোনও ভাষা নেই’, বা দিল্লী পুলিশের ‘বাংলাদেশী ভাষা’ ব্যবহারের আগের পর্যায়ে, যখন বাংলাভাষী শ্রমিকদের ওপর আক্রমণ, তাঁদের হয়রান করা, কাউকে কাউকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া, পে লোডারে করে ছুঁড়ে ফেলার মতো বর্বরোচিত ঘটনা ঘটছিল, এবং তখনই ধীরে ধীরে সার্বিক আক্রমণের ছক সাজানো চলছিল, সেইসময়েই এই বঙ্গের একজন প্রথিতযশা, নমস্য, বর্ষীয়ান ভাষাবিদ একটি মন্তব্য করেন। তাঁর সেই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে আমি আদতে ফিরে যেতে চাইছি, যেটা দিয়ে শুরু করেছিলাম, অর্থাৎ কেন্দ্রিকতা। তাঁর মন্তব্যের নির্যাস ছিল, যেহেতু এখনও পর্যন্ত শ্রমিকদের ওপর আক্রমণ করা হচ্ছে, সেই অর্থে কোনও মধ্যবিত্ত, বা সমাজের মাথায় বসা ‘বাবু’দের দিকে আক্রমণ ধেয়ে আসেনি, সুতরাং এটাকে ভাষার ওপর আক্রমণ বলা যায়না। এখানে ভাষার প্রশ্নটাকে দূরে রাখতে চাওয়ার কারণ কী? নিঃসন্দেহে শ্রমজীবী মানুষের ওপর আক্রমণ, এবং তার পিছনের অর্থনীতি একটা বড়ো কারণ। কিন্তু সেই শ্রমজীবী জনতা কি তাহলে এই ভাষার প্রতিনিধি নন!
এইখানেই সংশয়! সংস্কৃতির ওপরে যে শ্রেণিভিত্তিক উচ্চবর্গীয় ও উচ্চবর্ণীয় কর্তৃত্বকে আরোপ করা হয়েছে, বাম মহলের চেতনাসম্পন্ন প্রগতিশীলদের কাজ তো সেই কর্তৃত্বের কেন্দ্রকে অস্বীকার করা, তাকে ভাঙা! কিন্তু আমাদের অবচেতনও কি তাহলে সেই কর্তৃত্বের কেন্দ্রিকতাকে মেনে নিচ্ছে! আর নিচ্ছে বলেই আজকে বাংলা ভাষা আদতে কী, এবং সেটার কর্তৃত্ব যে আমার, সেটাই জানান দিতে পশ্চিমবঙ্গের একটা অংশের সাহিত্যিক, সমালোচকদের সুরটা বর্তমান ভারতের শাসকদের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। তাঁরাও ‘বাংলাদেশী ভাষা’র অস্তিত্ব প্রমাণে জান লড়িয়ে দিচ্ছেন, কেউ কেউ চারপাশে যাদের দেখছেন, তাদের ঠিক বাঙালি বলে তাঁর মনে হচ্ছে না!
এখানেই আদতে আছে প্রান্ত আর কেন্দ্রের লড়াই। এখন যদি প্রশ্ন তোলা হয়, যে বাংলা ভাষার কথা বলা হচ্ছে, অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের ‘মান্য বাংলা’, সেই মান্যতা দিলেন কারা? কোন অধিকারে দিলেন? আমি এখন যে বাংলায় লিখছি, সেই বাংলাতে লিখলে, তবেই সেটা গ্রহণযোগ্য এমনটা কেন হল? কলকাতা যখন বঙ্গ সংস্কৃতির কেন্দ্র হয়ে উঠল, তখন স্বভাবতই সে চাইল প্রান্তকে গিলে খেতে। সমান্তরাল এবং ঐশ্বর্যশালী সাংস্কৃতিক যাপনসমূহকে ধ্বংস করতে উঠেপড়ে লাগল, সবাইকে তার মতোই হতে হবে, নাহলে সে মান্যতা পাবেনা! তাকে হয়ে থাকতে হবে দ্বিতীয় শ্রেণির, তাকে হতে হবে উপ; প্রধানের ধ্বজা কিন্তু একজনের হাতেই থাকবে। অথচ কলকাতার মূল যে বাংলা ছিল এখন সেই ভাষাতে কলকাতায় বসবাসকারী কেউই কথা বলেন না। কর্তৃত্বকে কুক্ষিগত করার তাড়নায় নিজেকে এমন একটা কৃত্রিমতার মোড়কে সে আবদ্ধ করল, নিজের সাংস্কৃতিক যাপনের শিকড়টাই গেল ছিন্ন হয়ে, ঐতিহাসিকতা গেল বিলীন হয়ে। শান্তিপুরি বাংলাকে মান্য বাংলার কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত করে, বাংলার বাকি সমস্ত সংরূপকে বলা হল উপভাষা! রাঢ়ী, বঙ্গালী, বরেন্দ্রী, ঝাড়খণ্ডী, এবং কামরূপী বা রাজবংশী এইসব সংরূপগুলোকে উপভাষা বলা হল ঠিকই, কিন্তু কে কার উপ? কেনই বা উপ হয়ে থাকবে তারা? তারপর ‘বঙ্গালী’ নামক যে তথাকথিত উপভাষা, সেই ভাষিক সংরূপেও যে বহু ধারা, চট্টগ্রামের একটা ধারা, সিলেটের একটা ধারা, ময়মনসিংহ, যশোর প্রতিটা ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা ধারার জোরালো অস্তিত্ব। শুধু বঙ্গালী নয়, সমস্ত সংরূপেই অজস্র রূপের মিশ্রণ ঘটেছে। আর এটাই ভাষার বুনিয়াদকে শক্তিশালী করেছে, প্রাণোচ্ছল করেছে, টিকিয়ে রেখেছে। এই সামগ্রিকতাই বাংলা ভাষা। স্থানিক, সাংস্কৃতিক, উচ্চারণ ভেদে পৃথক হয়েছে বিভিন্ন সংরূপ। আজ যারা ভাষিক প্রবাহতে বাঁধ দিতে তৎপর, যারা বদ্ধ জলায় আবদ্ধ করতে চায় বাংলাকে, তারা কি জানে না, সামগ্রিক এই বিপুল ঐশ্বর্যকে বাদ দিয়ে বাংলা ‘ভাষা’ হয়না! এই সমস্ত সংরূপের ঐক্যবদ্ধতাই বাংলা ভাষা। সেখানে অপরাপর ভাষাগুলো থেকে গৃহীত শব্দ থাকবে, পৃথক উচ্চারণ ভঙ্গী থাকবে, পৃথক যাপন চিত্র থাকবে। এই ধারাবাহিক প্রবাহ না থাকলে ভাষাটাই মৃতপ্রায় হয়ে যাবে। অথচ অমিত মালব্যদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যটাই কিন্তু আমি যেটা বললাম তার সম্পূর্ণ বিপরীত তত্ত্বায়নের ওপরে দাঁড়িয়ে আছে। তাই তিনি জোর গলায় বললেন, এতরকম বৈচিত্র আছে বলেই বাংলা কোনও ভাষা নয়। শুধুমাত্র বিরোধী তত্ত্বায়ন নয়, পিছনের উদ্দেশ্যটার বিষয়ে আরেকটু পরে আসছি।
তবে সবক্ষেত্রেই মূলে আছে কেন্দ্রিকতার প্রশ্ন, কর্তৃত্বকে কুক্ষিগত করার প্রশ্ন। সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সিংহাসন যখন আমার দখলে, তখন কাউকে একটা অপর বানাতে হবে, তার দিকে দাগতে হবে কামান। এই ক্ষেত্রে সবথেকে সহজলভ্য লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে প্রান্ত; বলা ভালো ক্ষমতার সচতুরভাবে অঙ্গুলিহেলনে বলপূর্বক করে রাখা প্রান্তিকতাকে আঘাত করতে হবে, তাহলে নিজেদের আসন টলায়মান হবেনা।
তাই আজ যখন ‘মুসলমানদের ভাষা’ আর বাংলার মধ্যে তফাতের চেষ্টা হচ্ছে, তখন ভাষাবিদ দীনেশ চন্দ্র সেনের একটি লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি। “বাঙ্গালা ভাষা মুসলমান প্রভাবের পূর্বে অতীব অনাদরে ও উপেক্ষায় বঙ্গীয় চাষার ন্যায় গানে কথঞ্চিৎ আত্মপ্রকাশ করিতেছিল। পণ্ডিতেরা নস্যাদার থেকে নস্য গ্রহণ করে শিখা দোলাইয়া সংস্কৃত শ্লোকের আবৃত্তি করতে ছিলেন এবং ‘তৈলাধার পাত্র’ কিংবা ‘পাত্রধার তৈল’ এই লইয়া ঘোর বিচারের প্রবৃত্ত ছিলেন। সেখানে বঙ্গভাষার স্থান কোথায়? ইতরের ভাষা বলিয়া বঙ্গভাষাকে পণ্ডিতমণ্ডলী দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতেন, হাড়ি-ডোমের স্পর্শ হইতে ব্রাহ্মণরা যেরূপ দূরে থাকেন বঙ্গভাষা তেমনই সুধী সমাজের কাছে অপাংক্তেয় ছিল, তেমনই ঘৃণা, অনাদর, উপেক্ষার পাত্র ছিল।” (দীনেশ চন্দ্র সেন, বঙ্গভাষার ওপর মুসলমান প্রভাব) এমনকি মুসলমান শাসকদের উৎসাহেই কৃত্তিবাসের ‘শ্রীরাম পাঁচালি’ এবং কাশীরামের ‘ভারত পাঁচালি’ যখন লেখা হয়, সেটাও ব্রাহ্মণ সমাজ মেনে নেয়নি। দু’জনকেই সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মন্যসমাজ ‘রৌরব নরকে অধিবাসী’ বলে প্রচার করে। এমনকি তাঁদের বিরুদ্ধে ছড়া বাঁধা হয় – “কৃত্তিবেসে কালিদেসে আর বামুন ঘেঁষে / এই তিন সর্বনেশে”। সুতরাং আজ ‘বাং-আলি’ বা ‘বাংলাদেশী ভাষা’ হিসাবে দাগিয়ে দেওয়ার যে অপচেষ্টা, সেটার ঐতিহাসিকতা আদতে লোকজ উপাদানের বিরুদ্ধে শাসকের এককেন্দ্রিক কর্তৃত্বের রাশ ধরে রাখা, এবং একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে অপরায়নের যে খেলা এদেশে শুরু হয়েছে, তার সামগ্রিক ছকেরই অংশ।
বাংলা ভাষার শিকড়ের দিকে যদি তাকানো যায়, তার ঐতিহাসিকতাকে যদি বিশ্লেষণ করা যায়, তাহলেই দেখা যাবে, তার শিকড় কিন্তু অন্ত্যজের কুঁড়ে ঘরে। চর্যাপদের পদকর্তারা কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদী সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো যোদ্ধা। নিছক অন্ত্যজের সুহৃদ তাঁরা ছিলেন না, নিজেরাই ছিলেন অন্ত্যজের স্বর। এই শিকড়কে যারা অস্বীকার করতে চায়, তাদের লক্ষ্য বাংলা’র প্রাকৃত শিকড়কে উপড়ে, তাকে দরবারি ভাষা বানানো। আর দরবারি ভাষার ভবিতব্য সর্বদাই ভয়ংকর। সেটাই আজ করার চেষ্টা হচ্ছে। ভাষার ধারক ও বাহক কিন্তু সবসময়েই সমাজের শ্রমজীবী অন্ত্যজ মানুষ। কারণ ভাষার কথ্য রূপই আদতে তার যাপনের আলেখ্য। সেখানে আঘাতের অর্থ হল ভাষার শিকড়ে আঘাত। সেই কারণেই কবি লিখেছিলেন, “ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়্যা নিতে চায়”, খেয়াল করুন এখানে কিন্তু মুখের ভাসা কেড়ে নেওয়াটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ, অর্থাৎ কথ্য ভাষা, যেটা আদতে ব্যক্তির মাতৃভাষা, তার অস্তিত্বের পরিচায়ক। তাছাড়া ভারতীয় উপমহাদেশে কথ্যরূপ এবং কলার সমস্ত সংরূপই সাহিত্য। সেটা নিছক ইউরোপের ‘লিটারেচর’ নয়। এখানের সাহিত্যের সমস্ত আদি নিদর্শনের নাম তাই হয়েছে শ্রুতি। কলার সবধরনের প্রকাশ ভঙ্গীই সাহিত্য। তাই যারা বলেন সাহিত্যের ভাষাই আদতে ‘প্রমিত’, তাদের কে বলেছে লেখ্য রূপটাই একমাত্র সাহিত্য! ইউরোপ এইটুকু শিখিয়ে দিল, আর আমরা শিখে নিলাম, যেটা লেখা হয় সেটাই শুধু সাহিত্য! তাহলে বৌদ্ধ শ্রমণরা কী করেছেন? সেগুলো সাহিত্য নয়? এদেশে কথকতার যে বিপুল ভাণ্ডার সেটা সাহিত্য নয়? আর প্রমিত বাংলার কথা বলছেন, শমিক ভট্টাচার্যরা এই যে গগনবিদারি রব তুলছেন, যে প্রমিত বাংলায় কথা বলা হয়, সেই একই ভঙ্গীতে কি লেখা হয়? আমি এখানে যে ভঙ্গীতে লিখছি, আমার বাচনভঙ্গী কি এক? তাই ভাষার ক্ষেত্রে বাচনটা সবথেকে জরুরী, লিখনটা নয়। আদতে ঔপনিবেশিক চেতনায় জারিত হয়ে, যে ভারতীয়ত্ব খোঁজার চেষ্টা ওনারা করছেন, সেটা সংঘের ভারত বিনির্মাণ প্রকল্পেরই অংশ।
ভাষার ভিতরেও এই যে সূক্ষ অপরায়ন ঘটাতে চাইছে বিজেপি-আরএসএস, আমি ওপরে এতসব কথার অবতারণা করলাম, এগুলোর কিছুই কি তারা জানে-বোঝে না? অবশ্যই জানে-বোঝে, এবং কখনও আমার-আপনার থেকে সেই জানা-বোঝার পরিসরটা অনেক সময়েই বেশি। তাই তাদের কাঙ্খিত লক্ষ্যকে পূরণ করতে গেলে এই সামাজিক বাস্তুতন্ত্রকে ধ্বংস করতে হবে। সেই কারণেই দরকার বেশ কিছু সামাজিক বাস্তুকার, যারা ভিতরে এই সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংটা করবে। দায়িত্বটা ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজন নামীদামী বঙ্গভাষী মানুষ কাঁধে তুলে নিয়েছেন। এবার শুরু হয়েছে আমাদের অবচেতনকে ধরে নাড়িয়ে দেওয়া! অপরায়নের একটা সুপ্ত ধারণা তো আমাদের মধ্যেও আছে। প্রমথ চৌধুরীর মত সাহিত্যিক একসময় মন্তব্য করেছিলেন, “বাংলা ভাষা আহত হয়েছে সিলেটে, আর নিহত হয়েছে চট্টগ্রামে”। এই অপরায়নের চোরা স্রোতকেই সুনামিতে পরিণত করতে চাইছে বিজেপি। তাহলে তাদের যে ফ্যাসিবাদী এজেন্ডা – এক দেশ, এক প্রধান, এক বিধান, এক নিশান, সবকিছুকেই এক করার যে মোদীয় স্বপ্ন, সেই স্বপ্নপ্রকল্পের নতুন অধ্যায় ভাষা। একবার ফিরে দেখুন নয়া জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০’র খসড়ায়। ত্রিভাষা নীতি, ইতিমধ্যেই এই নীতি প্রণয়ন করতে গিয়ে দ্রাবিড়িয় ভাষা রাজ্যগুলোর সঙ্গে কার্যত যুদ্ধ চলছে মোদী সরকারের। বাংলার ক্ষেত্রে ওরা একটু অন্য পথ ধরল। নিজেদের প্রকল্পকে বাস্তবায়িত করতে্ ‘অনুপ্রবেশ’ নামক ওদের প্রচারকে সুচতুরভাবে মিশিয়ে দিল ভাষিক পরিচিতির সঙ্গে। সর্বদাই যে কাজ করতে আরএসএস সবথেকে পটু, সেটা ওরা আবারও করবে, এই বিষয়টাকে ধরে ওরা গণউন্মত্ততা তৈরি করবে। সময়কালটাও খেয়াল করুন। বিহারে এসআইআর’র অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা গেছে, পরের কোপটা বাংলার ওপর পড়বে, এবং সেটাই হতে চলেছে। তার আগে ভাষিক অপরায়নের উন্মাদনা তৈরি করে ঘর গোছানোর কাজ চলছে।
তাই আজ যারা মনে করছেন, ভাষাকে খণ্ডিত করবেন নিজেদের কর্তৃত্বের স্বার্থে, ভাষিক বহুমাত্রিকতাকে অস্বীকার করে এককেন্দ্রিকতা চাপিয়ে দেবেন, অপরায়নের ত্রিশূল বাগিয়ে বিবিধের যাপনকে ধ্বংস করবেন, তাদের খেলার এই সূক্ষতাকে আজকে ধরতে হবে। নিছক বাংলা ভাষা আক্রান্ত, বাংলাভাষী আক্রান্ত বললে হবে না। কারণ আমরা নিজেরা কী করেছি? পূর্ব বাংলার মানুষের কথ্য ভাষাকে আমরা বিনোদনে ‘কমিক রিলিফ’ হিসাবে ব্যবহার করেছি। আমরা প্রতিবেশীকে চিনিনি। অবচেতনে তাকে অপর করেই রেখেছি। একদেশদর্শীতা আমাদের শিখিয়েছে, আমিই সেরা। আর এটা আমরা করেছি, নিজেদের মধ্যেই। সেই পথ ধরেই আজ একাংশের শিল্পী, সাহিত্যিক ভেসেছেন ‘অমিত–জোয়ারে’। তাই এই লড়াই লড়তে হলে, আমাদের নিজদের মনের উঠানটাকে একটু বড়ো করতে হবে, নিজেকে ঊর্ধ্বতন ভাবার চেতনা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। ‘উপ’ নয়, সমানাধিকার দিতে হবে ভাষিক সমস্ত সংরূপকে। আর ভাষাকে লালন করতে হয়, হানাদারদের থেকে তাকে বাঁচাতে গেলে, প্রতিক্রিয়ায় নিজেও হানাদারের ভূমিকা পালন করে, অপরাপর ভাষাগুলোকে হেয় করার মানসিকতা ত্যাগ করতে হয়। নাহলে ওদের এই লড়িয়ে দেওয়ার চক্রান্তটাই সফল হবে।
আর যে সাহিত্যিককুল বাংলাভাষায় ‘বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ’ নিয়ে বড়োই চিন্তিত, তাঁরা নিশ্চিত জানেন, সহিত থেকেই সাহিত্য। তাই সহিত হতে হবে। এটাই রবি ঠাকুর বলে গেছিলেন –
“কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি,
সে কবির বাণী-লাগি কান পেতে আছি।”
ভাষার ক্ষেত্রেও একথা সমান সত্য। মাটিকে চিনুন, শিকড়কে চিনুন, প্রতিবেশীকে চিনুন, নিজেকে ঠিক চিনতে পারবেন। তখন আর গোয়েবলসীয় অপরায়নের পাঁকে গা ভাসাতে হবে না।