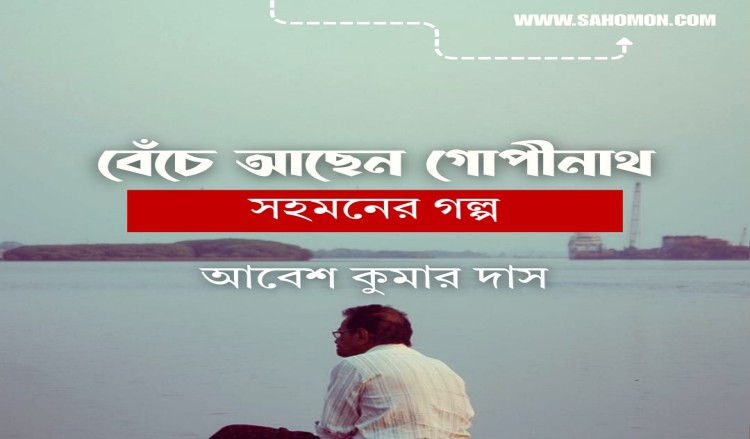দু’ হাজার সাত।
মনে পড়ল, রণেনবাবুর ঠিক আধা-আধি বয়স তখন আমার।
অদ্ভুত মজা লাগছিল খেলাটায়। যত বোরিং হবে ভেবেছিলাম লোকাল ট্রেনের এই তিপ্পান্ন মিনিটের জার্নিটা, তার কিছুই টের পেলাম না। স্ট্যাটগুলো চেক করছিলাম। আর চমকে চমকে উঠছিলাম। ঠিক বিলেতের মাঠে ভারতের জয়জয়কারের বছরগুলোতেই আমাদের বয়সের পারস্পরিক সম্পর্কদের খেয়াল করে। এইট্টি সিক্সেও কপিলদেবের ভারত যেবার পরপর দুটো টেস্ট জিতল লর্ডস আর লিডস থেকে, সে বছরও আমার বয়সের ডিজিট দুটোকে উলটে দিলেই বেরিয়ে পড়ত রণেনবাবুর তৎকালীন বয়স। তখনও স্কুলেই আমি। যদিও ক্লাস নাইনের পড়ুয়াকে আর দেওয়ার মানেই হয় না ক্লাস সিক্সের স্ট্যান্ডার্ডের অঙ্ক। তবু রণেনবাবু কি আর খেয়াল করেননি বিষয়টা? কে জানে...
ভাবতে ভাবতেই টের পাচ্ছিলাম।
যত বোরিং হবে ভেবেছিলাম লোকাল ট্রেনের এই তিপ্পান্ন মিনিটের জার্নিটা, তেমন কিছুই হয়নি খেলাটায় মেতে গিয়ে।
চারটে ষোলোর আপ ব্যান্ডেল লোকালের ফোর্থ কামরার জানলা থেকে তক্ষুনি সরে গেল শেওড়াফুলির পাঁচের প্ল্যাটফর্মের ল্যাজা।
কতদিন পর চড়ছি এই লাইনের লোকাল ট্রেনে! মনে করার চেষ্টা করছিলাম। এককালে নিয়মিতই যাতায়াত ছিল। প্রথমে কলেজলাইফের ক’ বছর। তারপর চাকরিজীবনের গোড়ার দিকটাও। মফস্সলেরই তো ছেলে আমি আসলে। সে যতই এ-ওয়ান সিটির বাসিন্দা হয়ে যাই না কেন হালে। হুগলি নদীর দুই তীরের এই মফস্সলি স্টেশনেরা কি মনে রেখেছে রক্তিম গুহ নামের সেই ছিপছিপে ছেলেটাকে?
এক্ষুনি চোখে পড়ছিল যেমন। ঘরবাড়ির আড়ালে চকিতেই অদৃশ্য হয়ে যাওয়া আড়াআড়ি পুবমুখো রাস্তাটাকে। ক’ পা গেলেই ফেরিঘাট। এই লাইনে নদী স্টেশনের সব চাইতে কাছে আসে শেওড়াফুলিতেই। আবার ওপারে গেলে ব্যারাকপুর স্টেশন অনেকটাই দূরে ঘাট থেকে। ডেলি প্যাসেঞ্জারির সেই দিনগুলোকে মনে পড়ে যাচ্ছিল। তখন তো হুট বলতেই অবরোধ। নদীর দু’দিকে দুটো ডিভিশন আর লাগোয়া ফেরিঘাটগুলোর ভরসায় জোড়াতালি দিয়ে চালাতে হত। হাওড়া ডিভিশনে গোলমাল মানেই তড়িঘড়ি নদী পেরোও আর লাগোয়া স্টেশন থেকে গাড়ি ধরো শিয়ালদার। উলটোটাও ঘটত হামেশাই। তখন আর-এক জ্বালা। নয় বগির গাড়িতে চিড়েচ্যাপটা হও ডবল ভিড়ে। এভাবে কলেজলাইফে তা-ও চলে। চাকরির জায়গায় কি আর দেওয়া যায় দু’দিন অন্তরই এক অজুহাত? তা-ও আমাদের সেক্টরে। সেই মহানগরে একটা সস্তার ঠিকানা খুঁজে নেওয়া আমার।
ভাগ্যিস নিয়েছিলাম। তাই তো যতদিনে রণেনবাবুর ঠিক আধা-আধি বয়সে পৌঁছলাম, স্পোর্টস জার্নালিস্ট হিসেবে মোটামুটি ছড়িয়েছে নামটা। মনের মতো ট্র্যাক ধরে ফেলেছি। তারপর বাকি থাকে শুধু নিজের এলেমে এগিয়ে চলা। এসব সেই সময়ের কথা, ওয়াড়েকর আর কপিলদেবের পর বিলেত থেকে যখন আবার রাবার জিতে ফিরছে ভারত। যদিও ক্যাপটেন হিসেবে সেই শেষ সিরিজ দ্রাবিড়ের। ব্যাটিং-এ মনোযোগের যুক্তি দেখিয়ে নিজেই সরে দাঁড়াবেন অতঃপর। দায়িত্ব যাবে অনিল কুম্বলের কাছে। এদিকে আমিও পাব ঘরের মাঠে পাকিস্তান সিরিজ কভার করার দায়িত্ব। সেকেন্ড টেস্ট ছিল ইডেনেই।
পরপর মনে পড়ছিল দিনগুলো। জন্মভূমি নিয়ে বস্তাপচা সেন্টিমেন্ট ধরে বসে থাকলে কি আর পৌঁছনো হত আজ এখানে? কামারপাড়ার শরিকি বাড়ির ভাগ নিয়ে খুড়তুতো ভাইদের সঙ্গে কামড়াকামড়ি করতে হত হয়তো। কালেভদ্রে দেখা হলে ভাইপোদের চোখেমুখে যেখানে ফুটে উঠতে দেখি সমীহ, সৌরভের সঙ্গে তোমার ফটোটা দেখলাম জেঠু সেদিন...
মুখে স্মিত হাসি ঝুলিয়ে রাখলেও নাকটা উঁচু হয়ে ওঠে এসব মুহূর্তে।
মফস্সলের বাংলা মিডিয়াম থেকে স্রেফ নিজের এলেমে উঠে এসেছি এতদূর।
স্কুলে শেখা বহু বিদ্যেকেই সময় মতো আনলার্ন না করতে পারলে...
তাছাড়া শিকড়ের টান আমার মধ্যে নেই কে বলল?
এই যে গাড়িটা বিগড়োতে লোকাল ট্রেনে চড়ে বসেছি আজ, এ-ও তো একরকম সেই টানেই। মাঝেমধ্যে পুরনো পরিচিতদের মধ্যে গিয়ে পড়া বেশ উপভোগই করি। অমন সমীহমাখা চাহনি কি আর পাশের ফ্ল্যাটের পড়শির চোখে দেখতে পাব?
তাই তো টমের আপত্তি কানেই তুলিনি তখন।
আমার ছেলে টম। তমোঘ্ন গুহ। ভেবেচিন্তেই নামটা রেখেছি আমরা। মানে আমি আর পারমিতা। আমাদের লক্ষ্যই ছিল যাতে কাগজপত্রে বাঙালি নামও থাকে একটা ওর। আবার চটজলদি একখানা অ্যাংলিসাইজড ভারশনও হয় নামটার। হাওড়া থেকে ট্রেনে যাওয়ার কথায় চোখ কপালে তুলে ফেলেছিল টম, লোকাল ট্রেন? মাই গুডনেস। হ্যাভ ইউ গন ক্রেজি পাপা? এক নব্বই বছরের বুড়োর জন্য আজ ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে-র গোটা দিনটা...
আসলে কাল রাতেও ঠিকঠাকই ছিল সব। আজ বেলার দিকে আমার ড্রাইভার গৌতমই প্রথম খেয়াল করে। চাকার তলায় চুঁইয়ে চুঁইয়ে জমা হয়েছে তেল। হুইল সিলিন্ডারের প্রবলেম। এই নিয়ে চুঁচড়ো অবধি পাড়ি দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। আবার পনেরোই অগাস্টের চক্করে কোথায় পাই হুট বলতেই মেকানিক! পেলেও দু’-তিন ঘণ্টার কমে কিছুই হত না। ফ্যাসাদে পড়ে গিয়েছিলাম। কাল রাতে জানলেও পত্রপাঠ বাতিল করতাম প্রোগ্রাম। সকালেও কথা হয়েছে দেবুদার সঙ্গে। যাব বলে আশ্বস্ত করেছি। একদম ইলেভেন্থ আওয়ারে ক্যানসেল করা খারাপ দেখাত। সত্যিটা বললেও ভাবত অজুহাত দিচ্ছি বুঝি। হাজার হোক, পুরনো মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া। আজ আছে কাল নেই মানুষটা। এক-আধটা মধ্যবিত্ত মূল্যবোধকে চেষ্টা করেও ঠিক ঝেড়ে ফেলা যায় না।
অগত্যা...
বোধহয় এতকাল পর লোকাল ট্রেনে চড়ার সুবাদেই বালি পেরোতে না পেরোতেই মনে পড়তে লেগেছিল পুরনো কথা।
নাইনটিন এইট্টি থ্রি। সেই প্রুডেনশিয়াল কাপ জেতার বছর। ক্লাস সিক্সে তখন আমরা। বোর্ডে অঙ্ক করাচ্ছিলেন দেশবন্ধু মেমোরিয়ালের গেমটিচার রণেনবাবু। আর সারির মাঝামাঝি একটা বেঞ্চিতে আমি আর তমাল মশগুল হয়ে গিয়েছিলাম ওয়াড়েকরের একাত্তরের টিমের ইংল্যান্ড থেকে রাবার জিতে আনার গল্পে। আসলে বিশ্বকাপ জেতার তালেগোলে তখন প্রায়দিনই খবরের কাগজের পাতায় উঠে আসছে পুরনো ইতিহাসের টুকরোটাকরা। সাফল্যের খতিয়ান তো তেমন ভারী হয়নি তখনও ভারতীয় ক্রিকেটে। তার মধ্যেই চর্চা চলছে কোনটা বেশি কৃতিত্বের সেই নিয়ে।
নীচু গলায় বলছিলাম গর্বের সুরে, জানিস আমার জন্ম ওই একাত্তরেই...
তমালের বাহাত্তর বলে নিজের জন্মসালটার মাহাত্ম্য নিয়ে ক্রেডিট নিচ্ছিলাম আর কি।
আচমকাই একটা চকের টুকরো এসে পড়ল মাথায়।
চমকে তাকাতেই দেখি ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছেন রণেনবাবু।
বুকের মধ্যেটা ছ্যাঁত করে উঠলেও একটা ভরসা ছিলই যে আলোচনার বিষয়বস্তুটা শুনলে একটু ধমকধামকেই রেহাই দেবেন স্যার। যেহেতু ক্রিকেট নিয়ে মানুষটার পাগলামির হদিস ওই বয়সেই পাওয়া হয়ে গিয়েছিল। কিছুটা কথাবার্তায় আর বাকিটা বাড়িতে বাবা-কাকাদের মুখে। সত্যি বলতে ওই একটা কারণে গোটা চুঁচড়ো জানত রণেনবাবুকে। কত আর লোক তখন টাউন শহরটায়! সবাই সবার মুখ চেনে। যত বড় হয়েছি তারপর খালি আরও আরও অবাক হয়েছি মানুষটাকে দেখে। ক্রিকেটের কবেকার কোন আদ্যিকালের কী কী রেকর্ড না কণ্ঠস্থ ছিল তাঁর! ভাবলে আজও অবাক লাগে, অমন একটা আধা মফস্সলে বসে কীভাবে অত খোঁজখবর রাখতেন সেদিন রণেনবাবু!
কিন্তু যেটা ঘটতে যাচ্ছিল তার জন্য মোটে প্রস্তুত ছিলাম না সেদিন।
আমাদের কথা শুনে একটু বাঁকা হেসে হঠাৎ পাক্কা অঙ্কস্যারের অবতারেই আবির্ভূত হলেন রণেনবাবু, বেশ বেশ। আচ্ছা বল তো রক্তিম, বিলেত থেকে ভারতের বিশ্বকাপ জেতার এই বছরে আমার বয়স তোর বয়সের ঠিক চারগুণ হলে ওয়াড়েকরের ওভাল টেস্ট জেতার বছরে আমাদের দু’জনের বয়সের ফারাক কত ছিল?
শুনতে যত সোজাই লাগুক আজ, সেই বিয়াল্লিশ বছর আগে সেদিন সেই মুহূর্তে স্রেফ ঘেমে নেয়ে গিয়েছিলাম। খালি মনে হচ্ছিল আর বুঝি রক্ষে নেই। ওই হাতের একটা থাবা পড়লে আর দেখতে হবে না।
যদিও সেসব কিছুই হয়নি। মাথা নেড়ে গম্ভীর মুখে শুধু বলেছিলেন রণেনবাবু, অজিত ওয়াড়েকরের গল্প জানিস? যে মানুষটা কিনা প্রথম ভারতীয় ক্যাপটেন হিসেবে ইংরেজদের হারিয়েছিলেন তাদের ঘরের মাঠেই। পড়াশুনোতেও গুড বয় ছিলেন কিন্তু উনি। মনে রাখিস কথাটা। সবই করতে হবে জীবনে। শুধু সময় ভাগ করে নেওয়া চাই...
অজিত ওয়াড়েকর ততদিনে প্রাক্তন ক্রিকেটার। আমি অন্তত কমেন্ট্রিতে শুনিনি তাঁর নাম। কিন্তু যেভাবে কথাগুলো বলছিলেন রণেনবাবু, সন্দেহ হল, বোধহয় লোকটা তাঁর আইডল ছিল। হতে পারে। মনে মনে হিসেব করার চেষ্টা করছিলাম একাত্তর সালে কত বয়স ছিল রণেনবাবুর।
সন্দেহটার নিরসন ঘটতে যদিও দু’ বছর পেরিয়ে গেল।
ততদিনে শুকতারা আর খবরের কাগজের দৌলতে ভারতীয় ক্রিকেটের কিছু কিছু ইতিহাস জানা হয়েছে আমারও।
ইন্টার স্কুলের খেলার ফাঁকে সুযোগ বুঝে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আচ্ছা স্যার, পাতৌদি আর ওয়াড়েকরের মধ্যে কাকে বড় মনে হয় আপনার?
টসে হেরে ডাফ স্কুলের বিরুদ্ধে তখন ব্যাট করছি আমরা। সেকেন্ড ডাউনে নেমে চার বলের বেশি টিকতে পারিনি। খাতাই খোলেনি। খেলার আকর্ষণ ওখানেই মরে গিয়েছিল আমার। বসে বসে উশখুশ করছিলাম। ক্রিজে তখন অর্ধেন্দু আর স্নেহময়। আমার প্রশ্নে ভুরু কুঁচকে তাকালেন রণেনবাবু, হঠাৎ এমন প্রশ্ন?
না মানে, আমতা-আমতা করি আমি, আপনি সেই যে বলছিলেন না একদিন ওয়াড়েকরের কথা। কিন্তু বিদেশ থেকে তার আগেই তো রাবার জিতে এনেছিলেন পাতৌদি। তাও তিন-তিনখানা টেস্ট নিউজিল্যান্ডে...
তখনই ছিটকে এল দাগের বাইরে বলটা।
সপাটে কভার ড্রাইভ করেছিল অর্ধেন্দু।
মাঠের ধার থেকে চেঁচিয়ে উঠলাম আমরা। যতই মন সরে যাক খেলা থেকে ওটুকু দেখাতেই হয়। প্রশ্নটা চাপা পড়ে গেল সেই হুল্লোড়ে। তিন উইকেটে আট থেকে ইনিংসের হাল ধরেছিল অর্ধেন্দু। আরও একটা উইকেট পড়েছে তারপর। তুখোড় বল করছিল ডাফের ঢ্যাঙা সেই শ্যামলা ছেলেটা। কী আউটস্যুইং হাতে! বলের লাইন বুঝতেই পারলাম না। ব্যাট ছোঁয়াতেই অক্কা। পঞ্চাশ পেরোবে নাকি দেশবন্ধু ভয় ধরে গিয়েছিল তখন। সেখান থেকে অর্ধেন্দুর সুবাদে চার উইকেটে সত্তর পেরিয়ে গেল। এই ছেলেটার কথা ভাবলেও খারাপ লাগে। ক্লাস সেভেনে পড়ে। এত ভাল ক্রিকেট খেলে। কিন্তু আর ক’দিন চালাতে পারবে কে জানে! অর্ধেক দিন ভরপেট খাওয়াই জোটে না ওদের। তাতে মাঝেমধ্যেই বন্ধ হয়ে যায় বাবার মিল।
এই অর্ধেন্দুর বাড়ির অবস্থা তো জানিস, সংবিৎ ফিরতে ঘুরে তাকাই। রণেনবাবু বলে চলেন, ছেলেটার হাতে খেলা আছে। অথচ...
আমিও যে ঠিক এই কথাগুলোই ভাবছিলাম মুখ ফুটে বলি না আর। শুনতে থাকি, কী জানিস, পড়াশুনোই বল আর খেলাধুলো, মানুষের পরিবেশ আর পরিস্থিতিকে বাদ দিয়ে তার যোগ্যতার বিচার করা যায় না। পাতৌদি লোকটা ছিল নবাব। অবশ্যই লড়াই ছিল তাঁরও। তবে মধ্যবিত্তর সংগ্রাম একেবারে অন্য জিনিস...
আমি তো ভেবেছিলাম তালেগোলে চাপাই পড়ে গেল বুঝি প্রশ্নটা। অর্ধেন্দুর কথা থেকেই যে রণেনবাবু আবার ঢুকে পড়বেন পাতৌদি বনাম ওয়াড়েকরে, ভাবতেও পারিনি। যদিও সোজাসুজি কোনও রায় দেননি উনি সেদিন। যেটা শুনতে চাইছিলাম আমি। ওই বয়সে আসলে অমন স্পষ্ট জবাবই শুনতে চায় মানুষ। ধোঁয়াটে কথায় বিরক্তি আসে। কিন্তু আশ্চর্য, সেদিন সেই ভাসা ভাসা কথাগুলো থেকেই কীভাবে যেন বুঝে নিয়েছিলাম যা বোঝার।
কোথাও এসে দাঁড়াল ট্রেনটা।
তাকিয়ে দেখি মানকুণ্ডু।
টুক করে একটা মেসেজ ঠুকে দিলাম দেবুদাকে। চুঁচড়ো স্টেশনে আসার কথা ওর। দেবুদার স্কুটিতেই যাব। ট্রেনে আসছি যে হাওড়া থেকেই জানিয়ে দিয়েছিলাম। গাড়িটা যে আনা গেল না তার জন্য আবার খচখচ করে উঠল মনটা। দেবুদা বোধহয় দেখেনি আমার এই গাড়িটা।
ভোঁ দিয়ে উঠল ডাউন ব্যান্ডেল লোকাল।
ভাবতে চেষ্টা করছিলাম আজ যেখানে পৌঁছেছি কীসের টানে সেখান থেকে একবাক্যে রাজি হয়ে গেলাম দেবুদার কথায়। রণেনবাবু মনে রাখতেই পারেন তাঁর করিতকর্মা ছাত্রটিকে। ছাত্রগর্বে গর্বিত হওয়ারই কথা মফস্সলের এসব সাবেকি বাংলা মিডিয়ামের পুরনো আমলের মাস্টারমশাইদের। আমার রিপোর্টিং নিয়ে ফেসবুকের ক্রিকেট ফ্যানপেজগুলোতেও যেখানে রীতিমতো কথা চলে হালে। সেসব যদিও জানার কথা নয় তাঁর। তবে কাগজের খেলার পাতাটা তো দেখেনই। আমার নামটা নিয়মিতই চোখে পড়ার কথা। কিন্তু আমি, স্বনামধন্য স্পোর্টস জার্নালিস্ট রক্তিম গুহ, কীসের টানে ছুটে চলেছি আজ চুঁচড়োয়? কী পাওয়ার আছে আর নব্বই বছরের বুড়ো মানুষটার কাছ থেকে আমার?
ভাবতে ভাবতেই মনে হচ্ছিল বোধহয় সুতোটাকে এখনও টিকিয়ে রেখেছে ক্রিকেটই।
খেলাটা তো বটেই, উপরন্তু তার ইতিহাস তথা পরিসংখ্যান নিয়েও রণেনবাবুর আগ্রহ কীভাবে যেন সঞ্চারিত হয়েছিল আমার মধ্যেও।
তাই সত্যিটা হল আজ যেখানে পৌঁছেছি, তাতে আমার জীবনে একটা প্রভাব রয়েই গিয়েছে মানুষটার।
যদিও খেলাটাকে নিয়ে একটা অন্যরকম মূল্যবোধ ছিল রণেনবাবুর। গেমটিচার হিসেবে যা বুনে দেওয়ার চেষ্টা করতেন তিনি আমাদের মনেও। সেসব অবশ্য বিসর্জন দিয়েছি আগেই। নইলে আর আসতে হত না এতদূর। রণেনবাবুদের যুগ আর নেই। বরং সেকালের মূল্যবোধদের মধ্যে রয়ে যাওয়া অনেকানেক ফাঁকিদের খুঁজে খুঁজে বের করার চেষ্টাই চালাই আমরা ইদানীং। বেনিফিট ম্যাচ কী বস্তু জানে আজকের প্রজন্ম? কেন জানে না? যেহেতু অঢেল পয়সা এসে গিয়েছে এখন ক্রিকেটে। ওসব করে আর সাহায্য তুলে দিতে হয় না প্রাক্তন ক্রিকেটারদের। বোর্ড রীতিমতো পেনশন দেয় তাঁদের। তার মূল্যটা তো দিতেই হবে অন্যভাবে। তাই ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ না থাকলে বিরিয়ানির গল্প বা দাড়ির রং দিয়ে পাতা ভরাতে হয় আজকাল আমাদেরও। ওটাই খায় যেহেতু বাজারে। লোকাল ক্রিকেটের খবর পরিবেশনের জায়গা কই আজকাল কাগজে?
সেই দিনটার কথা মনে পড়ছিল আবারও। মাঠের ধারে বসে বসে অনেক কথাই বলছিলেন রণেনবাবু। জিজ্ঞাসা করেছিলেন, লক্ষ্মীদাস জয়ের নাম শুনেছিস?
নীরবে মাথা নেড়েছিলাম।
আটাত্তর করে ততক্ষণে থামতে হয়েছে অর্ধেন্দুকে। শেষ কয়েক ওভারের খেলা চলছিল। চোখকান বুজে হাঁকড়াচ্ছিল তুহিন। যা যোগ হয় বোর্ডে তা-ই লাভ। বোলিং তত সুবিধের নয় আমাদের।
রণেনবাবু বলছিলেন, দেখ, গেমটিচার হিসেবে কোনও খেলাকেই খাটো দেখাতে পারি না আমি। কিন্তু ক্রিকেটকে তো আলাদা একটা আসনে বসাতেই পারি। কখন খারাপ লাগে জানিস? তুলনা করতে গিয়ে যখন লোকজন ফুটবলের সঙ্গে দেশপ্রেম আর ক্রিকেটের সঙ্গে ইংরেজ-ভক্তিকে গুলিয়ে ফেলে। যদিও দুটো খেলারই জন্ম বিলেতে...
বুঝতে পারছিলাম আমাকে পেয়েই কথাগুলো বলছিলেন স্যার।
আমাকে বরাবর একটা অন্য চোখেই দেখতেন।
একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন, ন্যাশনালিস্ট মুভমেন্টের যুগ সেটা। কংগ্রেসের নেতাদের গ্রেফতারির প্রতিবাদে বত্রিশের ইংল্যান্ড ট্যুর বয়কট করেন লক্ষ্মীদাস জয়। নইলে হয়তো ভারতবর্ষের খেলা সেই প্রথম টেস্টে মাঠে থাকতে পারতেন উনিও। এটা কি কম বড় ঘটনা? আসলে কী জানিস, ইস্ট ইয়র্ককে হারিয়ে মোহনবাগানের সেই এগারোর শিল্ড জেতার ঘটনাই স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিল ফুটবলকে। ক্রিকেটে সাফল্য আসতে সেখানে দেরি হয়েছে। আর-একটা ব্যাপার হল এ খেলা চালিয়ে যেতে অনেক টাকাপয়সার দরকার। সবার পক্ষে সম্ভব নয় আমাদের দেশে। তা-ও তো একনাথ সোলকার উঠে আসেন এদেশ থেকেই। দেখি, কী করতে পারি অর্ধেন্দুটার জন্য...
দিনটাকে ভুলতে পারিনি আরও একটা কারণে।
ক্লাসে অমনোযোগী হয়েও যা হয়নি দু’ বছর আগে, খেলার শেষে ঠিক সেটাই ঘটেছিল সেদিন মাঠে।
ঘটনাটা যদিও অতি তুচ্ছ আজকের বিচারে।
প্রথমে অর্ধেন্দুর দায়িত্বশীল আটাত্তর আর শেষের দিকে তুহিনের অন্ধের মতো ব্যাট চালিয়ে গোটা তিনেক ছক্কার দৌলতে একশো সাতষট্টি অবধি পৌঁছেছিলাম আমরা। আগেই বলেছি বোলিং তত সুবিধের ছিল না দেশবন্ধুর। ম্যাচের দ্বিতীয় হাফে মাঠে শুধুই থ্যাড থ্যাড আওয়াজ। আটজনে বল করেও ডাফের বেঁটেখাটো ওপেনারটাকে আর কিছুতেই টলানো গেল না। যখন আর ঠিক এক রানই করতে হবে ওদের সেই মালও দাঁড়িয়ে নিরানব্বইতে। একে তো ডাফের ছেলেগুলোকে বিশেষ উঁচু নজরে দেখতাম না আমরা। তাতে আট উইকেটে হারতে চলেছি। আবার সেঞ্চুরিও হয়ে যাবে দেশবন্ধুর বিরুদ্ধে সেটাই মন থেকে মেনে নিতে পারছিলাম না। ঠিক তখনই আমাকেই বল করতে ডাকল তূর্য। সেই পড়ে পাওয়া সুযোগ ছাড়ার প্রশ্নই ছিল না। ইচ্ছাকৃতভাবেই অফস্টাম্পের দু’ হাত বাইরে দিয়ে করেছিলাম ডেলিভারিটা। স্নেহময়ের গ্লাভসের নাগাল এড়িয়ে যখন সীমানার দিকে গড়িয়ে যাচ্ছিল বলটা, কী নৃশংস উল্লাস যে টের পাচ্ছিলাম মনে মনে...
যদিও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি সেই অনুভূতি।
মাঠের মধ্যে ঢুকে এসে বিরাশি সিক্কার এক চড় আমার গালে বসিয়ে দিয়েছিলেন রণেনবাবু। দু’-এক মুহূর্ত স্রেফ অন্ধকার দেখেছিলাম চোখে। আস্তে আস্তে যখন স্পষ্ট হল দৃষ্টি, দেখেছিলাম কী নিবিড় ঘৃণা মানুষটার দু’ চোখের তারায়...
ক্রিকেটের তথাকথিত স্পিরিটকে তুলোধোনা করে যখন পোস্ট পড়ে আজকাল সোশ্যাল মিডিয়ায়, শয়ে শয়ে কমেন্ট জমা হয় সেসব থ্রেডে, স্পিরিট-পন্থী কেউ ভুল করেও মুখ দেখিয়ে ফেললে তার আত্মারামকেই খাঁচাছাড়া করার তোড়জোড় শুরু হয়, চল্লিশ বছর আগের ঘটনাটাকে স্মরণ করে মাঝেমধ্যে সময়ের চাইতে এগিয়ে থাকা পুরুষ মনে হয় নিজেকে।
মুচকি হাসি খেলে যায় ঠোঁটের কোনায়...
পেছনের সিটে বসে বসে শুনছিলাম দেবুদার কথা।
শরীর বহুদিন থেকেই অশক্ত হয়ে আসছিল রণেনবাবুর। এদিকপানে নাকি একেবারেই নিস্পৃহ হয়ে গিয়েছেন। বন্ধুবান্ধব যারা ছিল চলে গিয়েছে একে একে সবাই। এমনকি বয়সে ছোট অনেককেও চোখের সামনে দিয়ে যেতে দেখেছেন। সমসাময়িক আর কেউ নেই আশপাশে। সারাদিন ইজিচেয়ারে বসে থাকেন ইদানীং মানুষটা। আর নিয়ম করে ‘এবার গেলেই হয়’ বা ‘আর কীসের জন্য বেঁচে থাকা’ গোছের কথা আওড়ান।
তা-ও তো দেবুদারও রিটায়ারমেন্টের সময় হয়েই এল।
এরপর আরও টাইম দিতে পারবে স্যারকে।
যদিও এসবের কিছুই তত অস্বাভাবিক মনে হচ্ছিল না আমার।
এই বয়সে এমনই হওয়ার কথা।
হালকা চালেই জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কেন খেলা দেখেন না স্যার আর? সময় কেটে যায়। এখন তো বছরভরই ম্যাচ থাকে...
কিন্তু যেটা শুনলাম প্রস্তুত ছিলাম না তার জন্য। বছর দশের বেশিই হয়ে গিয়েছে নাকি খেলা দেখা একদমই ছেড়ে দিয়েছেন মানুষটা। চুঁচড়োর রাস্তায় সার সার টোটোগুলোকে কায়দা করে কাটাতে কাটাতে বলছিল দেবুদা, কোহলিকে টেস্টে ক্যাপটেন হতে দেখেছে নাকি বাবা, ঠিক মনে পড়ে না...
আমি আশা করছিলাম খবরের কাগজ নিশ্চয় পড়েন। অন্তত উলটেপালটে তো দেখার কথাই। চোখ এখনও মোটের উপর ভালই আছে শুনছি যেখানে। আমার রিপোর্টিং থেকেই নিশ্চয় যা জানার জানা হয়ে যায়। এই বয়সে কি আর টিভির সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকার ধকল সয়? কিন্তু সেখানেও চমকে উঠতে হল। খাদিনা মোড় থেকে বাঁক নিতে নিতে নিজেই জানাল দেবুদা, খেলার পাতাটাও আর উলটোয় না রে বুঝলি। মোটামুটি যবে থেকে দেখা ছেড়েছে তখন থেকেই ধর...
সত্যিই ধাক্কা লাগল বুকে এবার।
বুঝতে পারছিলাম না এত ঝামেলা করে আসাটা ঠিক হল নাকি আদৌ।
টমের কথাগুলো বাজছিল কানে। একটু একটু বিরক্তি ধরছিল দেবুদার উপর। এই যেখানে পরিস্থিতি বেকার কেন আসতে বলল আমায়? নিজেরও বোঝা উচিত ছিল যদিও। আজকের দুনিয়ায় স্রেফ প্রাগৈতিহাসিক এই মানুষটা। কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মুখে না পড়তে হলেই বাঁচি এখন। যা যা বলে যাচ্ছিল দেবুদা, সেসব শুনেই আরও হচ্ছিল আশঙ্কাটা।
কোভিডের ঠিক আগে আগে নাকি গাড়িভাড়া করে শ্রীরামপুর নিয়ে যাওয়া হয় রণেনবাবুকে। কোনও নিকটাত্মীয়ের বাড়ির বিয়ের অনুষ্ঠানে। সেই শেষ চুঁচড়োর বাইরে বেরোনো স্যারের। তখন আজকের চাইতে শক্ত ছিলেন অনেকটাই। কিন্তু হলে কী হয়। সেখানেও কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন এক। গাড়ির জানলা থেকে স্পেনসারের আউটলেট দেখে বেজায় খাপ্পা হয়ে উঠেছিলেন নাকি শ্রীরামপুরের মানুষজনের উপর। ইতিহাস-বিস্মৃত জাতি-টাতি বলে ভারতীয়দের গাল পাড়তে লেগেছিলেন বিয়েবাড়িতে।
ভুরু কুঁচকোই শুনে, কেন?
যেহেতু বাবার মনে ছিল মার্কস অ্যান্ড স্পেনসারের নামটা, সামনে ফাঁকা রাস্তা পেয়ে পেছনে তাকিয়ে অল্প হাসে দেবুদা, সেই যে চুয়াত্তরের ট্যুরে সুধীর নায়েকের মোজা চুরির ঘটনাটা ঘটেছিল যাদের ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে। বাবার মনে হয়েছিল ওরাই বুঝি...
আর ফরমালিটির তোয়াক্কা না করেই হাহা করে হেসে উঠি আমি।
দেবুদাও হাসছিল যদিও।
মনে মনে হিসেব চলছিল আমার। বছর দশেক। ঠিক দশ বছর ধরলেও দু’ হাজার পনেরো হয়। মনে হচ্ছে শচীনের খেলা ছাড়ার পরপরই খুব বেশিদিন আর...
জানতাম যে ওয়াড়েকর আর গাভাসকারের পর শচীন তেন্ডুলকরই ছিল মানুষটার শেষ রোল মডেল। মনে পড়ে যাচ্ছিল ঠিক যে বয়সটায় এসে দাঁড়িয়েছি আজ, মোটামুটি সেই বয়সেই শচীনকে প্রথম দেখেছিলেন রণেনবাবু। কী উত্তেজিতই না ছিলেন! নব্বইতে হায়ার সেকেন্ডারি আমার। ততদিনে ঘটে গিয়েছে সেই ঘটনাটা। ওয়াকার ইউনিসের বলে রক্তাক্ত নাক নিয়েও পালটা মার দিতে থাকা শচীনের। আমাদের টেস্ট পরীক্ষার ঠিক আগে আগের ঘটনাটা। মনে পড়ছে ইনভিজিলেশন দিয়ে বেরোনোর মুহূর্তেও ডেকে বলেছিলেন আমায়, দারুণ একটা জুয়েল পেয়েছে ইন্ডিয়ান ক্রিকেট। মিলিয়ে নিস...
তারপর তো স্কুল থেকে বেরিয়ে এলাম আমরা।
মেয়াদ ফুরিয়ে আসছিল রণেনবাবুরও।
টুকটাক দেখা হত রাস্তাঘাটে। বলতেন একদম ঠিক সময়ে রিটায়ার করছেন। টিভিতে চুটিয়ে খেলা দেখবেন এরপর থেকে শচীনের।
গন্তব্যের কাছাকাছি চলে এসেছিলাম আমরা।
অ্যাকসিলারেটর শ্লথ করে আবার ঘাড় ঘোরায় দেবুদা, শোন, বাড়ি ঢোকার আগেই বলে নি। এমনি এমনি আসতে বলিনি তোকে। বাবা হয়তো কথাটা জিজ্ঞাসা করবেন। মিথ্যে বলতে হবে কিন্তু তোকে...
প্রস্তুত হয়েই ছিলাম প্রশ্নটার জন্য। এ ঘরে ঢোকার আগেই চেক করে নিয়েছি প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো। আজকের দিনে কোনও ব্যাপারই নয় যা। রণেনবাবুদের যুগ আর নেই। স্মার্টফোনের পর্দায় আঙুলের ক’টা টোকাতেই আজকাল বেরিয়ে আসে রাশি রাশি খতিয়ান।
যদিও দরকারই পড়ত না এসবের।
দেবুদা তো মিথ্যেই বলতে বলছিল আমায়।
সেটা কি খুব বড় কিছুও আমাদের কাছে? জানি না এত কিছু ভেবেছে নাকি দেবুদা। তবে পরপর সত্যি বলতে বলতেই অক্লেশে মিথ্যের নির্মাণ ঘটিয়ে ফেলাই কারবার আমাদের। হালে একটা পরিসংখ্যান খুব চলছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। বুমরা খেললে যত না টেস্ট জেতে ভারত, না খেললে তার চাইতে বেশি। সাধে কি আর ওই কথাটা বলেছিলেন নেভিল কার্ডাস!
সেই আমাকেই কিনা অনুরোধ করা মিথ্যে বলতে?
কিন্তু থমকে গিয়েছিলাম দেবুদার পরবর্তী কথাগুলোয়।
তার চাইতেও বেশি থমকেছি অবশ্য এইমাত্র স্যারকে দেখে। পরক্ষণেই সামলে নিয়েছি যদিও। আসলে সেই পেটানো মজবুত শরীরটাই ধরা ছিল স্মৃতিতে। শেষ যখন দেখেছি তখনও বয়স অনুপাতে বেশ শক্তই ছিলেন মানুষটা। ইজিচেয়ারে এলিয়ে পড়ে থাকা শীর্ণকায় শরীরটাকে দেখে তাই হোঁচটই লাগছিল প্রথম দর্শনে। উপরন্তু মুখচোখ কেমন সাদা সাদা হয়ে গিয়েছে স্যারের। খুব কালো বলা না গেলেও ফরসা কোনওদিনই ছিলেন না মানুষটা। মনে হয় হিমোগ্লোবিনের ঘাটতিতেও ভুগছেন।
দেবুদার কথাগুলো মনে পড়ে যাচ্ছিল আবার।
গত দু’ বছরে অন্তত পনেরোটা লোক আশ্বস্ত করেছে রণেনবাবুকে। বেঁচে আছেন অজিত ওয়াড়েকর। তবু কেন যেন কথাটা ঠিক বিশ্বাস হয়নি স্যারের। বছর দশেক হতে চলল খবরের কাগজের খেলার পাতাটা আর উলটেও দেখতেন না। আর ওয়াড়েকর তো আর রাজেশ খান্না ছিলেন না যে চুঁচড়োর দোকানবাজারে কথা হবে তাঁর চলে যাওয়া নিয়ে। সবটা মিলিয়ে খবরটা সময় মতো জানতে পারেননি স্যার।
ভাগ্যিস পারেননি।
তাই এখনও ঠেকিয়ে রাখা গিয়েছে।
সাম্প্রতিক ক্রিকেটের খবর আর না রাখলেও বছর দুয়েক ধরেই নাকি এই ব্যাপারটা দেখা দিয়েছে স্যারের। প্রায়শই খোঁজ নেওয়া বেঁচে আছেন নাকি ওয়াড়েকর। ভাবগতিক দেখে ডাক্তারও পরামর্শ দিয়েছে দেবুদাকে। ওয়াড়েকরের মৃত্যুসংবাদ যেন কিছুতেই দেওয়া না হয় মানুষটাকে।
শুনতে শুনতে ভাবছিলাম।
বোধহয় আশপাশের চেনা দুনিয়াটা থেকে নিজের সমবয়সি এমনকি অনুজদেরও অনেককে হারিয়ে আজ মানুষটা নিজের কালের শেষ প্রতিনিধি হিসেবে আঁকড়ে ধরেছেন ওয়াড়েকরকে।
ভুরু কুঁচকে বলেছিলাম, কিন্তু আমার কথাও কি বিশ্বাস করবেন স্যার?
করবে, আমার হাত দুটো আঁকড়ে ধরেছিল দেবুদা। অধীর গলায় বলেছিল, কাগজ না পড়লেও খুব বলে আজকাল তোর কথা। নিজেই বলেছে চাকরির খাতিরে যা-ই করতে হোক আমার ছাত্র কখনও মিথ্যে বলবে না আমাকে। তাই তো ডেকেছি তোকে...
শেষের এই কথাগুলোই থমকে দিয়েছিল আমায়।
ব্যক্তিগত সম্পর্কের সুবাদেও কেউ আজ আর বিশ্বাস করে আমাদের কথা?
বুঝতে পারছিলাম সত্যিই দিন ফুরিয়েছে রণেনবাবুর।
এখন দাঁড়িয়ে আছি তাঁর ঘরে স্যারের ঠিক মুখোমুখি।
দু’-একটা কুশল বিনিময়ের পরই যথারীতি প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিয়েছেন স্যার, একটা কথা বল তো রক্তিম। সত্যি বলবি কিন্তু। আচ্ছা, ওয়াড়েকর কি বেঁচে আছেন এখনও?
প্রস্তুত হয়েই ছিলাম এই প্রশ্নটার জন্য।
সাংবাদিক আর সান্ত্বনার মধ্যিখানে এখন ঠিক একটা মিথ্যের ব্যবধান।
না তাকিয়েও জানি অধীর উৎকণ্ঠায় আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে এই মুহূর্তে দেবুদা।
সোজাসুজি চোখ রাখলাম এবার রণেনবাবুর চোখে। হেসে বললাম, আপনি শুধু ওয়াড়েকরের কথাই কেন ভাবছেন? জানেন কি পঁচানব্বই পেরিয়েও এখনও বেঁচে আছেন গোপীনাথ? এই মুহূর্তে ভারতের লিভিং ওল্ডেস্ট টেস্ট ক্রিকেটার। অ্যাচিভমেন্ট খুব কম ছিল কি সেই মানুষটারও? ভারতের জেতা প্রথম টেস্টম্যাচে দলে ছিলেন উনি...
কী বলছিস, দেখতে পাচ্ছি একরাশ বিস্ময় ফুটে উঠেছে নবতিপর মানুষটার চোখেমুখে। গলার নিস্পৃহ সেই স্বর এই মুহূর্তে উত্তেজিত, গোপীনাথ বেঁচে আছেন? কোয়েম্বাতারো গোপীনাথ?
হ্যাঁ স্যার, বেঁচে আছেন গোপীনাথ। তাহলে আর কী বলছি আপনাকে, আমি হাসি, আর শুধু কি গোপীনাথ? পতনকরও বেঁচে আছেন স্যার। চন্দ্রকান্ত পতনকর। নরি কনট্রাক্টর বেঁচে আছেন। বেঁচে আছেন চাঁদু বোরদেও। সবাই আপনার চাইতে বড় বয়সে। দেখুন, একদিন যেতে হবে আমাদের সবাইকেই। কিন্তু আগে থাকতেই কেন ভাববেন...
যে হাসিটা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে দেখছি স্যারের মুখে, তার দিকে তাকিয়ে থেমে গেলাম আপনা থেকেই।
বুঝতে পারছিলাম প্রয়োজন ফুরিয়েছে আর বেশি কথা বাড়ানোর।
হাবিজাবি লিখে তো অনেক খরচা করলাম নিউজপ্রিন্ট।
বুঝতে পারছিলাম অল্প কথাতেই হয় কাজের কাজ।
আর, সত্যি বলতে বলতেও মহাসত্যের পথে এগিয়ে যেতে পারে সাংবাদিক।