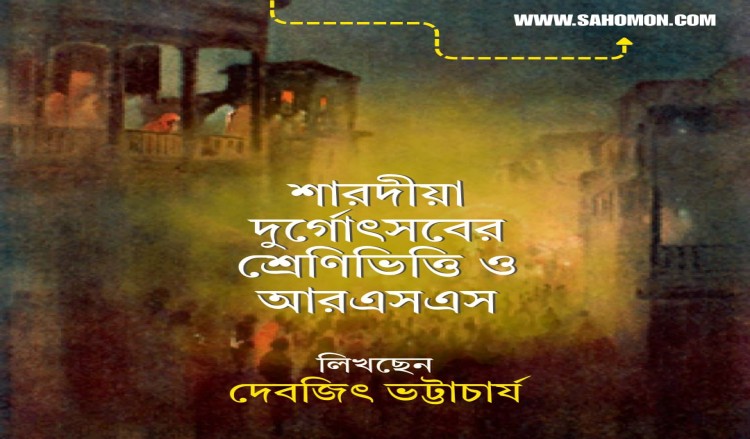এক ফর্সা নারী, কাঁধ থেকে কোমর পর্যন্ত পাঁচ-পাঁচ দশটা হাত। প্রত্যেক হাতে রয়েছে নানা ধরনের ধারালো অস্ত্র। তাঁর পায়ের তলায় এক গোঁফ ওয়ালা পেশীবহুল পুরুষ, গায়ের রং কালো, হাত দুটো, মাথায় ঝাঁকড়া কালো চুল। ফর্সা নারীর হাতের ধারালো অস্ত্র গিয়ে বিঁধেছে কালো পেশীবহুল পুরুষটির বুকে, গলগল করে রক্ত বেরিয়ে আসছে। এই চিত্র 'বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ উৎসব' হিসেবে কয়েক দশক ধরে চিহ্নিত হওয়া দুর্গোৎসবের। বাঙালি জাতি সত্ত্বা, সংস্কৃতি এক বৃহত্তর পরিসরের ভাবনা। বহু আচার-অনুষ্ঠান, চিন্তা-ভাবনা, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি ইত্যাদি সবই বাঙালি জাতি সত্ত্বার অবিচ্ছেদ্য অংশ। এর মধ্যে কালো পেশীবহুল পুরুষটি ও তাঁর জাতির মানুষেরাও আছেন। অর্থাৎ, বাঙালি একটি সমাজ।
বাঙালি সমাজে কয়েক'শ বছর ধরে কালো পুরুষটিকে অসুর-মহিষাসুর যা অশুভ শক্তি, এই রূপেই চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু, অসুর জাতির অস্তিত্ব সিন্ধু-হরপ্পা ইত্যাদি প্রাচীন সভ্যতায় পাওয়া গেছে। বর্তমানে এঁদের দক্ষিণ এশিয়ার ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল প্রভৃতি দেশগুলোতে ভালো পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায়। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, বিহার, উড়িষ্যা, ছত্তিশগড় প্রভৃতি জায়গার পাহাড়, পর্বত, বনাঞ্চল জুড়ে অসুর জাতির লোকেরা বসবাস করেন। যাঁদেরকে আদিবাসী বা এই দেশের আদিবাসিন্দাও বলা হয়। বাবাসাহেব আম্বেদকরের ভাষায় বিশ্লেষণ করলে বলা যায় - যারা সুরা (মদ) পান করতেন তারা সুর (আর্য বা দেবতা), আর যারা সুরা (মদ) পান করতেন না তারা অসুর (অনার্য)। বর্তমানে অসুর জাতির মানুষের নানা আক্ষেপ রয়েছে, 'বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ উৎসব' দুর্গোৎসব পালন করা নিয়ে। তাঁরা একটি সাক্ষাৎকারে বলেন, এটি জাতি হিংসার একটি উৎসব, এটি বিদেশি আর্য জাতির সংস্কৃতি, এদেশের সংস্কৃতি নয়, বাঙালি জাতির নিজস্ব সংস্কৃতি নয়। পেশীবহুল কালো পুরুষটিকে অস্ত্রের আঘাতে হত্যা করা ফর্সা মেয়েটি আদপে বিদেশি আক্রমণকারী আর্য জাতির আর কালো পুরুষটি এদেশীয় অনার্য জাতির। বিদেশি আর্য জাতি দখল করেছে তাঁদের এই দেশকে, হত্যা করেছে তাঁদের পশু ও প্রকৃতিপ্রিয় রাজা মহিষাসুরকে, যিনি এদেশীয় অসুর জাতিকে বিদেশি যাযাবর আক্রমণকারী আর্য জাতির হাত রক্ষা করে রেখেছিলেন। বিশেষজ্ঞদের মতে - এই অসুর জাতির মধ্যে বর্তমানে অনেকগুলো উপজাতি আছে। যেমন– আগারিয়, বিরজিয়া, কোল-অসুর, লোহরা-অসুর এবং পাহাাড়িয়া অসুর। এঁদের আবার আলাদা আলাদা গোত্র আছে। যেমন- আইন্ধ, বাড়োয়া, কছুয়া, কেরকেট্টা, শিয়াত, নাগ, তিরকি, টপ্পো প্রভৃতি। এঁরা প্রধানত, সিংবোঙ্গা ও মারাং বোঙ্গার পূজা ও দাঁশাই, সারজুন, সোহরাই, করম প্রভৃতি নানা ধরনের পশু, প্রকৃতি ও কৃষিকেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক উৎসব পালন করেন।
যত সময় গড়িয়েছে বিদেশি আর্য জাতির নানা আচার, আচরণ, ধর্মীয় উৎসবের জোরের কাছে অসুর জাতি বা আদিবাসীদের ধর্ম, সাংস্কৃতিক উৎসবগুলোকে বারবার হত্যা করা হয়েছে। এই মত, এ বিষয় নিয়ে গবেষণা, চর্চা করা অনেক বিশেষজ্ঞদের। তাঁরা বলছেন, শরৎ কালে দুর্গাপূজা বা শারদীয়া উৎসবকে টেনে আনা হয়েছে এই দেশের পাহাড়, জল-জঙ্গল-জমির মালিকদের আচার, আচরণ, ধর্ম, সংস্কৃতিগুলোকে হত্যা করবার সুপরিকল্পনায়। কারণ, যুগ যুগ ধরে শরৎ কাল জুড়ে আদিবাসী বা অনার্য জাতির পশুপূজা, প্রকৃতিপূজা ও কৃষিকেন্দ্রিক নানা পরবগুলো অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। যেমন - আড়ং, গড়ং, রান্নাপূজা, দাঁশাই, গাসি প্রভৃতি। এর পরিবর্তে ব্রিটিশরা প্রথম শরৎ কালের দূর্গাপূজাকে উৎসবে পরিণত করায় জোর দেয়। তার আগে পর্যন্ত যে কয়েকটি দূর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রায় সব ক'টি বসন্ত কালে, তাই এটিকে বাসন্তী পূজা বলা হত। অথবা, শরৎ কালে হলেও তা হয়েছে ঘরোয়াভাবে, ধুমধাম করে উৎসবের আকারে নয়। যদিও দূর্গাপূজার দেবী, মূর্তি, রূপ ইত্যাদি সম্বন্ধেও গবেষকদের মত আছে। তাঁরা বলছেন, গ্রীস ও ব্যাবিলনের দুই বিদেশি দেবীকে নকল করে আর্যরা এদেশে দুর্গার ছবি তৈরি করেছেন। তাই আর্য জাতির বৈদিক সভ্যতায় দেবীর কথা যা কিছু আছে তা অনেক পরে, সবটাই আছে পুরাণে, বেদে নেই। আসলে আর্যরা ছিলেন নারী বিদ্বেষী, পিতৃতান্ত্রিক যাযাবর জাতি, কেবলই যুদ্ধে পারদর্শী। তাঁদের কোন লিপি ছিল না, লেখবার পুরানো টেকনোল্যজিও জানতেন না। এ কথা ভাষাবিদ আলবেরুনি যখন ১০৩০ খ্রিস্টাব্দে ভারতে আসেন, তখনকার লেখা বই 'কিতাব উল হিন্দ' থেকে জানা গেছে, এমনটাই মত বিশেষজ্ঞদের। বিদেশি আর্য'রা হয়ে উঠলো এদেশের ব্রাহ্মণ, যা কিছু শিখেছেন তা সবটাই সুলতানি আমলে। সেই সময় থেকে দূর্গা-মূর্তি পূজার প্রচলন হয়(মোঘল আমল)। এই দেশে তার আগে দেবীর মূর্তি হিসেবে যা কিছু পাওয়া যায়, যাকে ব্রাহ্মণ'রা দূর্গা মূর্তি বলে অভিহিত করেছেন, সেইগুলো আসলেই প্রাচীন যক্ষী মূর্তি।
মুখের কথায় শোনা যায়, ১৫০০ সালের দিকে মালদহ দিনাজপুরের মহারাজ দেবীর স্বপ্নাদেশে দুর্গাপূজা চালু করেন। লিখিত ইতিহাস বলে, বিভিন্ন ঘট, শালগ্রাম শিলা ইত্যাদির পূজা ধরে শরৎকালে বাংলায় প্রথম দুর্গাপূজা ঘরোয়াভাবে প্রচলন করেন উচ্চবর্ণ-জমিদার কংশ নারায়ণ ও ভবানন্দ মজুমদার (১৬০১-১৬০৬ সাল নাগাদ)। এটির হিংসাত্মক রাজনৈতিক রূপ পায় ব্রিটিশ ও তার দালাল উচ্চবর্ণ-জমিদার, রাজা নবকৃষ্ণ দেবের হাত ধরে। এটি প্রথম অনুষ্ঠিত হয় ১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধে বাংলার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় এবং ব্রিটিশের ভারত দখলের 'বিজয়ের উৎসব' পালনের আছিলায়। ঐতিহাসিকরা এটিকে ব্রিটিশ (তৎকালীন সময়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি) প্রধান লর্ড ক্লাইভের 'পলাশী যুদ্ধের বিজয় উৎসব' হিসেবেও চিহ্নিত করেছেন। যা পালিত হয় প্রধানত এদেশের উচ্চবর্ণ-জমিদারদের প্রতিনিধিত্বে। পুরাণ অনুযায়ী, শরৎ কালের এই দুর্গাপূজা বা দুর্গোৎসব আদতে রামচন্দ্রের 'অকাল বোধন'। রামচন্দ্র হলেন একজন আর্যপুত্র(ক্ষত্রিয়-বীর)। এ বিষয়ে গবেষকদের মতে, তিনি একজন বিদেশি রাজা ছিলেন, রাজ্য জয়ে তার পূর্বপুরুষেরা ভারতে আগমন করেন। আর্যাবর্ত বা উত্তর ভারত জয়ের পর দাক্ষিণাত্যের দিকে রওনা দিলে যোদ্ধা রামচন্দ্র স্থানীয় রাজা রাবণের প্রতিরোধের মুখে পড়েন। রামচন্দ্র স্থানীয় কিছু শক্তির সঙ্গে জোট বেঁধে রাবণ রাজ্য আক্রমণ করেন এবং দাক্ষিণাত্যকে দখল করেন। প্রাচীন বাংলার রাজা মহেষকে আর্য-নারী দেবী দুর্গা সব রাজন্যবর্গের সহযোগিতা নিয়ে পরাজিত করেন। প্রকৃত অর্থে, মহেষ ছিলেন একজন দ্রাবিড়, অনার্য রাজা। তিনি স্বদেশকে বিদেশি শক্তির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করে পরাজিত হন। তাই বিজয়ী শক্তি তাকে অসুর বা অশুভ শক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। তবে এ সবটাই হল পৌরাণিক ইতিহাস। বস্তুবাদী ইতিহাস চর্চায় অসুর জাতির অস্তিত্বের খোঁজ পাওয়া গেলেও আর্য দেবতা রামচন্দ্র ও দেবী দূর্গার খোঁজ মেলেনি। বাল্মীকির রামায়ণ অনুযায়ী, রামচন্দ্র যুদ্ধে যাওয়ার আগে পূজা করেছিলেন সূর্যের। তবে পরবর্তীকালে লেখা কৃত্তিবাস ওঝার রামায়ণে তা বদল ঘটে, সেখানে উল্লেখ করা হয় রামচন্দ্রের 'অকাল বোধন'-এর ইতিহাসের। বলা হয়, রামচন্দ্র যুদ্ধে যাওয়ার আগে প্রথমে আর্য-বীর, তাঁর পূর্বপুরুষদের মুখে জল দেন(যে রীতি মেনে মহালয়ার দিনে তর্পণ করা হয়), পরে আর্য-দেবী দূর্গার পূজা করেন। এই দেবী যুদ্ধে অনার্য রাজা মহেষকে হারিয়েছিলেন, হত্যা করেছিলেন সেই অঞ্চলের অনার্য জাতিকে। তাই রামচন্দ্র, অনার্য বা অসুর জাতির বংশধর রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়ার আগে শরৎকালে দেবী দূর্গার শরণাপন্ন হন, 'অকাল বোধনে'র সূচনা করেন। এই অকাল বোধনে এখানে যখন দূর্গোৎসব পালিত হয় তখন গোটা উত্তর ভারত জুড়ে নবরাত্রি পালিত হয়।
বাংলায় মোঘলদের সহযোগিতায় প্রথম শরৎকালের দুর্গাপূজা পালনের সূচনা হয়। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলার পতনের (১৭৫৭) বিজয় উৎসব হিসেবে ব্রিটিশ ও উচ্চবর্ণের-জমিদারেরা দূর্গাপূজাকে শারদীয় উৎসবের রূপ দেয় এবং এটিকে জাতি-বর্ণ হিংসার রাজনৈতিক আঙিনায় নামিয়ে আনেন। ব্রিটিশরা মুসলমান শাসনকে সমান করে দেখান অনার্যদের সঙ্গে এবং উচ্চবর্ণ-জমিদারদের সাথে তাঁদের জ্ঞাতির(একই জাতির) সম্পর্ক আছে তা দেখান আর্যতুত রক্তের পরিচয়ে। এই সময় থেকে প্রচার শুরু হয়, এদেশের অশুভ শক্তি, মুসলমানদের অত্যাচার থেকে ব্রিটিশরা রক্ষা করতে এসেছেন তাঁদের আর্যতুত ভাই ব্রাহ্মণদের বা উচ্চবর্ণ হিন্দুদের। এই সময়ের দুর্গাপূজায় ব্রিটিশদের দ্বারা লাভবান হয়েছিলেন প্রধানত, উচ্চবর্ণ-জমিদারেরা। তাঁদের দুর্গাপূজায় নিম্নবর্ণ, আদিবাসী বা অসুর জাতির মানুষের আসবার অনুমতি ছিল না, পূজার সারাটা সময় চলত, মদ্যপান, বাইজি নাচ, বুলবুলির লড়াইয়ের মত নানা ধরনের উচ্চবর্ণ-বিত্তবানদের ভোগ ও বিলাসিতার বহুবিধ নোংরা সংস্কৃতি। ১৭৯২ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর 'ক্যালকাটা ক্রনিকাল' পত্রিকায় শারদীয়া দূর্গোৎসব প্রসঙ্গে কয়েকজন উচ্চবর্ণ-জমিদারদের নাম উঠে আসে, যাঁরা প্রত্যেকেই দুর্গাপূজা করে ব্রিটিশদের দ্বারা নানা ধরনের সুবিধা পেতেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় - দর্পনারায়ণ ঠাকুর, প্রাণকৃষ্ণ সিংহ, নারায়ণ মিত্র, নবকৃষ্ণ দেব, রামহরি ঠাকুর প্রমুখের কথা। তখনকার শারদীয়া দূর্গোৎসবকে বলাই হত কোম্পানির দূর্গাপূজা, এ নিয়ে লেখালেখিও করেন অনেকে। ১৭৯২ থেকেই বারোয়ারি পূজা সূচনা হয়। এর মধ্যে চলতে থাকে ব্রিটিশ ও তাদের পদদলিত নব্য উচ্চবর্ণ-জমিদারশ্রেণি স্বার্থের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কাজ ও হিন্দু পুনরুত্থানবাদী আন্দোলনের তোড়জোড়। ১৮২০ সালে দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে, উচ্চবর্ণ-জমিদারদের ব্রিটিশ তোষামোদের রাজনীতি দেখে, ইয়ং বেঙ্গলের ছাত্ররাও বিরোধিতায় সরব হন। ব্রিটিশরা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের পর (১৮৫৭) বিদেশি লগ্নির পরিমাণ বাড়তে থাকে, ১৯০০ সালের গোড়া থেকে উচ্চবর্ণ-জমিদার শ্রেণির দুর্গোৎসব 'সর্বজনীন' রূপ পায়, ব্যাপকভাবে বাণিজ্যিকীকরণ ঘটতে শুরু করে। পাশাপাশি হ্রাস পেতে থাকে নিম্নবর্ণ, দলিত ও অসুর, আদিবাসী বা অনার্য জাতির ধর্মীয় আচার, আচরণ, সংস্কৃতি পালনের সুযোগ, সুবিধা ও তাদের নিজস্ব সম্পদের উপর মালিকানার অধিকারগুলো।
হিন্দু পুনরুত্থানবাদী আন্দোলনের মতাদর্শগত জোরে, ১৯০৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ব্রিটিশের তাঁবেদারি করা উচ্চবর্ণ-জমিদারশ্রেণির রাজনৈতিক সংগঠন হিন্দু মহাসভা। ১৯২৫ সালের 'অকাল বোধন' বা শারদীয়া দুর্গোৎসবের বিজয় উৎসবের দিনে আর.এস.এস-এর প্রতিষ্ঠা হয়, ব্রিটিশের তাঁবেদারি গোষ্ঠী উচ্চবর্ণ-জমিদারশ্রেণির সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠন হিসেবে। লক্ষ্য স্থির হয়, ভারতের আর্য জাতির শ্রেষ্ঠত্বের ব্রাহ্মণ্যবাদী দর্শনকে সামনে রেখে, সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি হয় হিটলার ও মুসোলিনীর ফ্যাসিবাদের দর্শনকে সামনে রেখে, ফ্যাসিবাদী সাংগঠনিক পদ্ধতিতে। ১৯৪৭ সালের তথাকথিত স্বাধীনতা বা দেশ ভাগের পর বাংলার দুর্গোৎসব হয়ে উঠে ভারতের আমলাতান্ত্রিক শাসকশ্রেণিগুলোর বাংলা দখলের অন্যতম রাজনৈতিক অস্ত্র। আগে সরাসরিভাবে যা করতো ব্রিটিশ ও ব্রিটিশের তাঁবেদারি করা জমিদারশ্রেণি, তাই নতুন কায়দায় করতে শুরু করে এদেশের সংসদীয় রাজনৈতিক দলগুলো, তথাকথিত আধুনিক ভারতে। ১৯২৫ থেকে ১৯৪৭ সালের মাঝামাঝি সময় জুড়ে ব্রিটিশের দৌলতে উচ্চবর্ণ-জমিদারদের নেতৃত্বে নানা ধরনের ধর্মীয় আচার-আচরণকে কেন্দ্র করে দাঙ্গার সৃষ্টি হয়। যা ভারতের ব্রিটিশ বিরোধী প্রকৃত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুলোতে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের সৃষ্টি করে, প্রগতিশীল আন্দোলন বিকাশে প্রধান বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। উচ্চবর্ণ-জমিদারশ্রেণির ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুত্ব সমাজ প্রতিষ্ঠার সাংস্কৃতিক সংগঠন আর.এস.এস, তাদের রাজনৈতিক লক্ষ্যে দুটি দিক স্পষ্ট করে; এক, ব্রিটিশের ভারত ছেড়ে যাওয়ার বিরোধিতা; দুই, ভারতকে উচ্চবর্ণ-বিত্তবানশ্রেণির জাতি রাষ্ট্র, ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। এই কারণেই আগে থাকতে 'অকাল বোধন'-এ বিদেশি আর্যদের দেবতা রামচন্দ্র ও দেবী দুর্গার এদেশীয় অসুর জাতি, আদিবাসী বা অনার্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয়ের পরের দিনটি, বিজয়ের দশমীকে আর.এস.এস-এর প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এসবের মধ্য থেকে তাদের লক্ষ্য আরও স্পষ্ট হয় - বিদেশি পুঁজির একচেটিয়া রাজত্বের দ্বারা বাংলা তথা ভারতের বহুত্ববাদী আচার, আচরণগুলোকে ধ্বংস করে, হিন্দু ধর্মের নানা আচারকে রাম, দুর্গার মত আর্য শ্রেষ্ঠত্বপূর্ণ দেব-দেবীর দ্বারা গিলে খেয়ে বাংলা তথা ভারতীয় সমাজকে লিখিতভাবে একরোখা ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। যেখানে রাজনীতি হবে বিদেশি পুঁজি, বৃহৎ পুঁজি নির্ভরতার ও ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু রাষ্ট্রের ধারণাগুলো বিকশিত হওয়ার স্বার্থে, এর বিপক্ষে যাঁরা থাকবেন তাঁদের ঠান্ডা করতেই প্রয়োজন সমাজের সামরিকীকরণ (ফ্যাসিবাদীকরণ), ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু রাষ্ট্র। অর্থাৎ, ভারতে, বিদেশি পুঁজি, বৃহৎ পুঁজি ও উচ্চবর্ণ-জমিদারশ্রেণি, আর্য জাতি স্বার্থের ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু রাষ্ট্রের ময়দানি সেবাদাস ও লেঠেল বাহিনী হবে নিম্নবর্ণ, দলিত ও অসুর জাতি, আদিবাসী বা অনার্য জাতির শোষিতশ্রেণির মানুষেরা।
ভারতীয় সমাজ শ্রেণিভিত্তিক, এই শ্রেণির ভিত্তি সামন্ততান্ত্রিক-বর্ণ সংগ্রামের অধীনস্থ। তাই নিম্নবর্ণ, দলিত ও আদিবাসী বা অনার্য জাতির সিংহ ভাগ মানুষকে দেখা যায় গ্রামের ছোট-ভূমিহীন কৃষক, ক্ষেতমজুর হিসেবে। শহরে তাঁদের দেখা যায় শ্রমিক হিসেবে। কৃষক, শ্রমিক পরিবারের সন্তানদের পুলিশ, মিলিটারি বাহিনীতে যোগ দেওয়া ময়দানি যোদ্ধা রূপে। অথচ, বড় ও মাঝারি জমির মালিক উচ্চবর্ণ, শহরের সংগঠিত ও অসংগঠিত শিল্প সংস্থার মালিকানাও আছে উচ্চবর্ণের হাতে। পুলিশ ও মিলিটারি বাহিনীর উপর তলার অফিসারদের অধিকাংশই উচ্চবর্ণ-জমিদার পরিবার থেকে আসছে। এমনকি, বিচারব্যবস্থা, আমলাতন্ত্রের মধ্যেও একাধিপত্যরাজ উচ্চবর্ণের হাতে রয়েছে। একই রকমভাবে হিন্দু ধর্মের যে যে বড় ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো অনুষ্ঠিত হয়, মন্দির, প্রাসাদগুলো আছে তা নিম্নবর্ণ, দলিত ও আদিবাসী বা অনার্য জাতির ক্লান্তিহীন শ্রমের ফসল। কিন্তু, সেই সব জায়গায় উচ্চবর্ণ, ব্রাহ্মণ্যবাদী আমলাতান্ত্রিক শাসকশ্রেণিগুলোর সব দিক থেকে একশো শতাংশ সংরক্ষণ থাকলেও বাকি অংশের জন্য কিছু নেই। কংগ্রেসের রাহুল গান্ধীর মত নেতারাও বেকায়দায় পরে রাম মন্দির প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে ধারাবাহিকভাবে এসব প্রশ্ন তুলছেন। অথচ, কেন্দ্রে তাঁদের দলও ইতিহাসের পাতায় একই রাজনীতি করে এসেছে, যার ধ্বংসাবশেষের উপরে চড়েই আর.এস.এস ও বিজেপি আজ ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুত্ব ফ্যাসিবাদী রাজনৈতিক এজেন্ডাগুলোর প্রচার ও প্রসার ঘটিয়ে চলেছে।
এসব থেকে রাজ্য সরকারগুলো বাইরে? না। কারণ, আমলাতান্ত্রিক শাসকশ্রেণিগুলোর এজেন্ডা এগিয়ে নিয়ে যেতে তাঁরাও রাজ্যভিত্তিক ক্ষমতায় এসেছে। তা এ রাজ্যের দুর্গাপূজার দিকে নজর দিলেও অনুমেয়। পূর্বের কংগ্রেস ও বাম জমানায় নিম্নবর্ণ, দলিত ও আদিবাসী বা অসুর জাতির ধর্ম, সংস্কৃতি পালনের সুযোগ নিমিত্ত মাত্র ছিল। অথবা ছিল না বললেও চলে। আঞ্চলিক দলের ভিত্তিগত কারণ হিসেবে, তৃণমূল সরকারের আমলে এই সুযোগ খানিকটা এলেও উচ্চবর্ণের-বিত্তবানদের একাধিপত্যরাজের ধর্মীয় সংস্কৃতি পালনের বহর প্রবলভাবে বেড়েছে বাংলা ও বাঙালি সমাজে। পশ্চিমবঙ্গের সংসদীয় রাজনীতি আর.এস.এস-এর এজেন্ডায় পরিপূর্ণ, এখনের রাজনীতি বৃদ্ধির গতি বিদেশি পুঁজি, বৃহৎ পুঁজির বাজারভিত্তিক ও ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু রাষ্ট্রকেন্দ্রিক হয়ে উঠছে। এই যেমন - রাজ্যে বিগত ১৩ বছরে দূর্গাপূজার পরিমাণ প্রায় তিনগুণ বেড়েছে। রাজ্য বিদ্যুৎ দপ্তরের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০১১ সালে কলকাতা-সহ গোটা রাজ্যে দুর্গাপূজা কমিটি ছিল ২০,৯৭০টি। ২০২৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৫,৮৫৭টি(দূর্গাপূজা কমিটিগুলোকে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার তথ্যানুযায়ী)। পাশাপাশি সংসদীয় রাজনীতির সাথে উচ্চবর্ণ-বিত্তবানদের ধর্মের সংযোগ প্রকাশ্যে বেড়ে চলেছে। উচ্চবর্ণের ধর্মীয় উৎসবে সরকারগুলোর বিনিয়োগের পরিমাণও কয়েকগুণ বেড়েছে, যার জ্যান্ত উদাহরণ হল উচ্চবর্ণ-বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব, দুর্গাপূজা বা দুর্গোৎসব। এখন প্রায় বড় বড় সব পূজাই সার্বজনীন, বিভিন্ন দেশি-বিদেশি ব্যবসায়িক সংস্থার বিনিয়োগের মাধ্যমে চলছে। বিগত কয়েক বছর আগে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রীরা পূজা কমিটিগুলোর দখল নিয়েছিল। বাম জমানায় এর আলাদা কিছু ছিল না, দূর্গাপূজার সাথে শাসক দল ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সংযোগ বাংলায় অনেক আগে থাকতেই (প্রকাশ্যে, আবার কখনও আড়ালে)। তবে তা এখন আরও রূপান্তরিত হয়ে নিকৃষ্ট রূপ ধারণ করছে, যত দেশি-বিদেশি পুঁজির বিনিয়োগের পরিমাণ বেড়েছে। এই বিদেশি পুঁজি রাজ্য সমেত সমগ্র দেশটাকে পরিষেবাভিত্তিক করে তুলেছে। সময় আন্দাজে রোজগারের পরিমাণ ব্যাপক হারে কমেছে, কাজ থেকেও ছাঁটাইয়ের সংখ্যা বাড়ছে, কৃষি ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে লাভের পরিমাণ কমে গেছে। ফলে মেলা, খেলা ও বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব তথা দূর্গোৎসব যেমন অনেকের কাঁচা টাকা রোজগার করবার মোক্ষম সময় বয়ে এনেছে, তেমনি বিদেশি পুঁজির বাজার তৈরির স্বার্থে পুঁজির পুনরুৎপাদন পদ্ধতিও এর দ্বারাই এখনও জিয়ে আছে। এর ফলে সংসদীয় রাজনীতি আরও বেহায়া, নির্লজ্জ ও নিকৃষ্টমানের হয়ে উঠেছে, ভেতরের নোংরামি সব প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসছে। তাই এবারের দূর্গাপূজা শুরুর আগে, মহালয়াতে(মাতৃপক্ষের সূচনা) এক উদারবাদী মেয়ের ভোরের বেলা মহালয়ার শব্দ আস্তে করতে বলায়, তাঁকে একধারে শাসকদলের দেখানো পথেই উচ্চবর্ণের বাঙালি'রা চেপে ধরেন, অন্যধারে মেয়েটিকে সামাজিকভাবে আরও কোণঠাসা করতে ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুত্বের দলগুলো এগিয়ে আসে। এঁদের দু'পক্ষ আসছে নির্বাচনে রাজ্য ক্ষমতা দখলের বিষয়ে নিজেদের মধ্যে নানা বৈরিতা দেখালেও, দু'পক্ষের ঘেঁটি আমলাতান্ত্রিক শাসকশ্রেণিগুলোর হাতের বাইরে নয়, ফলে এদের মধ্যে সমঝোতাই প্রধান ভূমিকায় কাজ করছে। ঐতিহাসিকভাবে সংসদীয় রাজনীতির মুখ্য ভূমিকায় থাকা রাজনৈতিক দলগুলোর শ্রেণিভিত্তি ও মতাদর্শ এদেশের উচ্চবর্ণ-জমিদারশ্রেণি, দেশি-বিদেশি বৃহৎ পুঁজি ও বর্ণ বিদ্বেষপূর্ণ ব্রাহ্মণ্যবাদী মতাদর্শের দ্বারা তৈরি হয়েছে। লক্ষণীয়, পশ্চিমবঙ্গের ২০২৫ সালে শারদীয়া দুর্গোৎসবে আর.এস.এসের ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুত্ব ফ্যাসিবাদী রাজনীতি, সংস্কৃতির প্রভাব অনেকটাই বেড়ে গেছে। যার প্রমাণ অনেক ক'টি পূজা কমিটিগুলো দিয়েছে। যেমন - সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার, নাকতলা উদয়ন সংঘ প্রভৃতি। এবারের পূজায় সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারে ২৪ ঘণ্টা 'অপারেশন সিঁদুর' দেখানো ও নানা কায়দায় তার প্রোপাগান্ডাময় প্রচার জাঁকজমকভাবে সাজিয়ে বাংলায় ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুত্ব ফ্যাসিবাদী রাজনীতি ও এর উত্তর ভারতীয় হিন্দি-হিন্দুত্ব-হিন্দুস্তানি সংস্কৃতি বিস্তারের প্রচেষ্টা চলেছে। এমন উদাহরণ মেলে - নাকতলার দিকে তাকালেও। সেখানে যোগী রাজ্যের মত করে পূজামণ্ডপ সাজিয়ে, অঘোরী সাধু, সন্ন্যাসী বা বাবাদের নাচের আয়োজন করা হয়। উত্তর ভারতীয় সংস্কৃতিতে ধর্ম, জাতকেন্দ্রিক রাজনীতির মেলবন্ধনের স্বাদ পূজার ভাসানের দিনে আরও ভালোভাবে পাওয়া যায়। যখন বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষ প্রতিমা নিরঞ্জন যাত্রাকে সরাসরি 'পরির্বতন যাত্রা' হিসেবে সম্বোধন করেন। আসলে ব্রিটিশের বিজয় উৎসব হিসেবে শুরু হওয়া শারদীয় দূর্গোৎসব শুরুর সময়কাল থেকে এখন পর্যন্ত মৌলিকভাবে একই আছে। শারদীয়া দূর্গোৎসব বিদেশি শক্তি ও উচ্চবর্ণ-জমিদারশ্রেণির রাজনৈতিক স্বার্থে পালিত হয়, এখনও তা সেই পথ ধরে এগিয়ে চলছে। উল্টে এখন এই উৎসবের অনেক কিছুই আরও হিংস্রতর, ভয়ানক হয়ে উঠছে, সেই সময়ের থেকে। আগেকার শারদীয়া দুর্গোৎসব জমিদারেরা, রাজারা ব্রিটিশের সঙ্গে একত্রিতভাবে করতেন। অথবা এই পূজার মাধ্যমে ব্রিটিশের সামনে ক্ষমতা প্রদর্শন করে দেখাতেন, যাতে ভালো কিছু সুযোগ মেলে ব্রিটিশের তরফ থেকে। এখনের দুর্গোৎসবও সেই স্বার্থে(ইউনেস্ক, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, আইএমএফ, এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাংক প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী সংস্থাকে দেখাতে) আরও উন্নত কায়দাতেই শাসকদলের কাউন্সিলর, এম.এল.এ, এমপি ও বিরোধীদলের নেতারা করেন, জমিদারি স্বত্বার শক্তি প্রদর্শন করে এবং রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো(মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী) এইসব পূজার প্রধান পুরোহিতে পরিণত হয়ে, প্যান্ডেল, মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে প্রমাণ করেছে যে, ভারত রাষ্ট্র লিখিতভাবে ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু রাষ্ট্র হওয়ার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে।
এবারের দুর্গোৎসবের দশমীতে আর.এস.এসের একশো বছর পূর্ণ হল। দশমীর দিনটিকে আর.এস.এস বিজয় হিসেবে দেখে, দেখাতে চায় দেশের সকল জনগণকে। ওই দিনে নানা বীরত্বপূর্ণ কর্মসূচি রাখে যা আর্য জাতি বা ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরে। আর.এস.এসের মতাদর্শগত শ্রেণিভিত্তি আর শারদীয়া দুর্গোৎসব পালনের দর্শনগত দিকের শ্রেণিভিত্তি আলাদা নয়। এই ধরনের ব্রাহ্মণ্যবাদী জাতি হিংসার চিত্র ও চরিত্র নিয়ে গভীরভাবে ভাববার সময় এসেছে। যখন আর.এস.এসের নেতৃত্বে এদেশের নিম্নবর্ণ, দলিত ও আদিবাসী, অসুর জাতির সন্তানদের সমস্ত অধিকারগুলো কেড়ে নিতে পাহাড়, জঙ্গল, জল, জমি থেকে সমতল জুড়ে রাষ্ট্র যুদ্ধ জারি রেখেছে, তখন গৌরবের সাথে শারদীয়া দুর্গোৎসব পালন সেই সমাজের অকাল পতন ডেকে আনতে খুব একটা বেশি সময় নাও নিতে পারে।