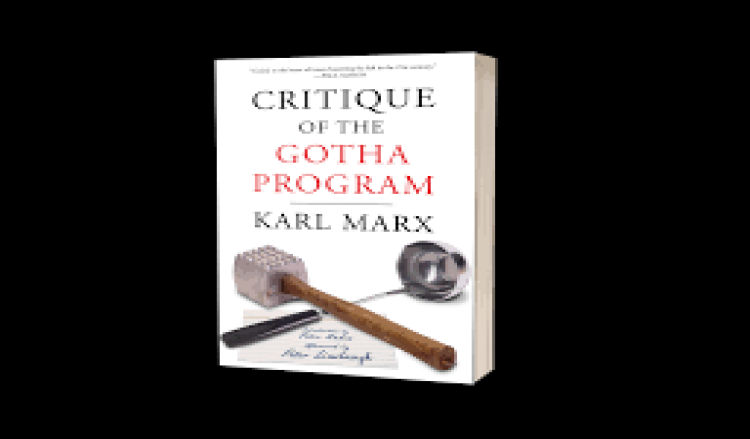পিটার হুডিসের আর একটা লেখা সম্প্রতি হাতে এল—Thoughts on Marx, Marxism, and Culture—মার্ক্স ফোরাম নামক অনলাইন আলোচনার একটি ইমেল গ্রুপে চিঠি চালাচালির আকারে একজন সদস্যের মেল থেকে। আমাকেও বাধ্য হয়ে এ সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করার জন্য ডেস্কটপের কিবোর্ডে আঙুল টেপাটেপি শুরু করতে হল।
[১]
যথারীতি হুডিস সংস্কৃতি প্রসঙ্গে কার্ল মার্ক্সের বক্তব্যের সমর্থনে ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস ও পরবর্তী প্রসিদ্ধ মার্ক্সবাদী চিন্তানায়কদের অবস্থানকে কঠোর সমালোচনার সাবান জল ঢেলে ধুয়েমুছে দিতে চেয়েছেন। গোড়াতেই তিনি মার্ক্সের Theories of Surplus Value বইয়ের প্রথম খণ্ড থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন: “Humanity itself is the basis of material production, as of any other production that it carries on. All circumstances, therefore, which affect man, the subject of production, more or less modify all his functions and activities, and therefore too his functions and activities as the creator of material wealth, of commodities. In this respect it can in fact be shown that all human relations and functions, however and in whatever form they may appear, influence material production and have a more or less decisive influence on it.” [Marx 1969, 288].
এই অধ্যাপক ভদ্রলোক জানেন যে উপরের এই বক্তব্যটা মার্ক্সবাদের বহুচর্চিত ভিত-উপরকাঠামো বিশ্লেষণী মডেলের সঙ্গে খাপ খায় না। তিনি এও জানেন যে মার্ক্স তাঁর ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত Contribution to a Critique of Political Economy বইয়ের ভূমিকায় একটি অতি বিখ্যাত প্যারাগ্রাফে ভিত-উপরকাঠামো সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য একেবারে থিসিসের আকারে লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন। এই বক্তব্য তিনি আর কখনই সংশোধন করেননি, বা বলেননি যে ওখানে তিনি যা বলেছেন তা ভুল বা অন্তত একপেশে ছিল। এই থিসিসের পরবর্তী স্পষ্ট অভিব্যক্তি রয়ে গেছে মার্ক্সের ১৮৬৭ সালে প্রকাশিত পুঁজি গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের একটি পাদটীকায় (যার কথা হুডিস বলেছেন) এবং তার দুই পৃষ্ঠা পরেই আরও একবার (যেটা তিনি আর লক্ষই করেননি, কিংবা, দেখে থাকলেও তিনি বেমালুম চেপে গেছেন)। [Marx 1974, 86 and 88] তবে এ তেমন কিছু ছিল না। মার্ক্স তাঁর কোনো রাজনীতি বিষয়ক রচনায় এর আর পুনরুল্লেখ করেননি বলে তিনি তাঁর খুশি চেপে রাখতে পারেননি। বরং তিনি উপরে উদ্ধৃত বক্তব্যকেই মার্ক্সের আসল মত এবং মাপকাঠি ধরে নিয়ে ভিত-উপরকাঠামো সম্পর্কে মার্ক্সের অত্যন্ত সুপরিচিত সেই থিসিসকে মার্ক্সের বদলে অন্যদের (বিশেষ করে, এঙ্গেলসের) ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে উদ্যোগ নিলেন। তার পর আমাদের গম্ভীরভাবে আমাদের জানিয়েছেন, “Nevertheless, the formulation was codified as a central principle in Engels’ late writings (after Marx’s death) and was promoted as part of a photocopy theory of knowledge by Plekhanov, Kautsky, the early Lenin, and many others who claimed to follow in their footsteps.”
অবশ্য তিনি ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনকে খানিক ছাড় দিতে রাজি আছেন, সেটা বন্ধনীতে লিখে দিয়েছেন: “In his “Abstract of Hegel’s Science of Logic” of 1914 Lenin broke from this vulgar materialist approach, which he had advanced six years earlier in Materialism and Empirio-Criticism, writing “Man’s consciousness not only reflects the objective world, but creates it”. তাঁর একটাই দুঃখ, “Lenin of course never published his philosophic notebooks, and the base-superstructure relation was largely interpreted in a casual-determinist manner, by orthodox Marxists, with the economic base posited as the independent variable and the superstructure as the dependent one.”
[২]
সমস্যা আছে। অনেক সমস্যা আছে কমরেড হুডিস যার খেয়াল রাখেননি।
পশ্চিম দেশের অগ্রগণ্য বুদ্ধিজীবী হিসাবে তিনি নিশ্চয়ই জানেন, কারও উদ্ধৃতি প্রদানের, এমনকি উদ্ধৃতি না দিয়েও কারও নাম করে একটা অভিযোগ উত্থাপন বা বয়ান উল্লেখেরও কিছু নৈতিক দায়বদ্ধতা থাকে। যা বলছেন সে সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হতে হবে, ঠিক বলছেন কিনা। সেগুলি একে একে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।
১। কার্ল মার্ক্স এঙ্গেলসের সঙ্গে মিলিত ভাবে ১৮৪৫-৪৬ সালে জার্মান মতাদর্শ নামে যে দার্শনিক বইটা লিখেছিলেন, তাতেও—ভিত উপরকাঠামো হিসাবে উল্লেখ না করলেও প্রায় সমধর্মী বক্তব্য রেখেছিলেন। এঙ্গেলসের স্পর্শ দোষ আছে বলে যদি সেটা তাঁর কাছে গ্রহণ যোগ্য না হয়ে থাকে সেটা বলে রাখা উচিত ছিল। অগ্রাহ্য করা বোধ হয় উচিত হয়নি। ১৮৪৮ সালের কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতেও অনুরূপ বক্তব্য ছিল তাঁদের। সেটা আবার মূলত মার্ক্সেরই রচনা এবং একেবারে কঠোর রাজনৈতিক বিষয়ে লেখা। অর্থাৎ, অন্তত কুড়ি বছর ধরে মার্ক্স তাঁর বিভিন্ন রচনার পাঠককে এই ভিত উপরকাঠামো সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ও সতর্ক করতে চেয়েছিলেন।
২। মার্ক্সের মৃত্যুর পরে এঙ্গেলস কোন অথবা কোন কোন রচনায় মার্ক্সের সেই বয়ানকে বিধান সদৃশ বানিয়েছিলেন (codified), যদি এই বিশ্লেষক জানিয়ে রাখতেন ভালো হত। কেন না, আমাদের চোখে এরকম কিছু পড়েনি। মার্ক্সের অনেক বক্তব্যকে অনেক জায়গাতেই এঙ্গেলস উল্লেখ করেছেন মার্ক্সের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ, কিন্তু আলাদা গুরুত্ব দিয়ে, কিংবা বলা ভালো, মার্ক্সের চাইতেও বেশি গুরুত্ব দিয়ে, ১৮৮৩-৯৫ সময়কালের নিজের কোনো সুপরিচিত মুদ্রিত রচনায় ভিত উপরকাঠামো সম্পর্কে এরকম কিছু বলেছেন বলে আমাদের জানা নেই। হুডিস বলে দিলে আমরা উপকৃত হতে পারতাম।
৩। বাস্তবে আমরা যেটা জানি তা হল, একটা সময় (১৮৮০-র দশকের শেষ দিক থেকে) যখন ইউরোপের অধিকাংশ কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবী মার্ক্সের ভিত উপরকাঠামো সংক্রান্ত বক্তব্যকে যান্ত্রিক ভাবে অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদে পর্যবসিত করছিলেন, তখন সেই এঙ্গেলসই অন্তত পাঁচটি বড় বড় চিঠিতে তার বিরুদ্ধে সকলকে সতর্ক করেছিলেন। তার রেফারেন্স আমরা দিতেই পারি। কিন্তু সেগুলো এত সুবিদিত যে আপাতত দিচ্ছি না। স্তালিনেরও যত বদনামই হোক, তিনিও Marxism on the Problems of Linguistics পুস্তিকায় ভিত এবং উপরকাঠামোর মধ্যে সম্পর্ককে যান্ত্রিকভাবে, একপেশে দৃষ্টিতে, একৈকিক সম্পর্কে (one-to-one correspondence), দেখার বিরোধিতাই করেছিলেন। ফলে, হুডিসের যে কথা—“The notion that the “superstructure”—politics, civil society, juridical relations, culture, religion, etc.—is a mere reflection of the economic base became a virtual article of faith among innumerable post-Marx Marxists”—এর কোনো বাস্তব তথ্যগত জমি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কথাটা নিতান্তই ভদ্রলোকের অন্যদের মুখে গুঁজে দেওয়া। হয়ত অজ্ঞাতসারেই। এক অন্ধ ঝোঁকের বশে।
৪। সুতরাং আমরা একইভাবে দাবি জানাতে পারি, এঙ্গেলস, প্লেখানভ, লেনিন, স্তালিন, প্রমুখ মার্ক্সবাদী নেতারা কে কোথায় photocopy theory of knowledge তুলে ধরেছেন, আমাদের দেখানো হোক। যদি চিন্তা করার ক্রিয়া বোঝাতে “প্রতিফলন” (reflection) শব্দটাতেই তাঁর আপত্তি থেকে থাকে—থাকতেই পারে, তাতে অন্যায় কিছু নেই—সেক্ষেত্রে তো তাঁর মার্ক্স থেকেই সমালোচনা শুরু করা উচিত। মার্ক্স তাঁর পুঁজি গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় জার্মান সংস্করণের পশ্চাদ্ভূমিকায় খুব স্পষ্ট করেই হেগেলের ভাববাদের পাশাপাশি তাঁর বস্তুবাদী চিন্তার বৈশিষ্ট্য বোঝাতে গিয়ে চিন্তাভাবনাকে মস্তিষ্কে বহির্জগতের প্রতিফলন হিসাবে বেশ জোরের সঙ্গে দাবি করেছেন।
কিন্তু না, আমরা খুব আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করি, এই শুধু-মার্ক্সপন্থী বিদ্বানরা মার্ক্সের অপ্রকাশিত লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিতে বেশি পছন্দ করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসুবিধা হয় বলেই কিনা জানি না, মার্ক্সের প্রকাশিত রচনাবলিকে এনারা সাধ্য মতো এড়িয়ে চলেন। আর যেখানে মার্ক্সের কোনো সুপরিচিত মুদ্রিত বয়ানের সঙ্গে এঙ্গেলস বা অন্যদের বক্তব্য হুবহু মিলে যায়, অথচ যেটা তাঁর নাপছন্দ, সেখানে তিনি মার্ক্সের যুক্ত থাকার কথাটা ভুলে থাকতে ভালোবাসেন।
এটা কি আলোচনার একটা ধারা হতে পারে?
এবার একটা অন্য প্রসঙ্গ তোলা যাক।
ভিত উপরকাঠামোর মধ্যে সিধা কারণ কার্য সম্বন্ধ রয়েছে—এরকম কথা কি তবে মার্ক্সবাদীদের মধ্যে কেউই বলেননি? হ্যাঁ বলেছেন। যিনি বলেছেন তাঁর নাম আবার ঘটনাচক্রে কার্ল মার্ক্স। বলেছেন সেই পুঁজি গ্রন্থের প্রথম খণ্ডেই। না কোনো পাদটীকায় নয়, একেবারে মূল পাঠের শরীরেই: “This juridical relation, which thus expresses itself in a contract, whether such contract be part of a developed legal system or not, is a relation between two wills, and is but the reflex of the real economic relation between the two. It is this economic relation that determines the subject-matter comprised in each such juridical act.” [Marx 1974, 88] হায় মার্ক্স! আপনি আমাদের এ কী বিপদে ফেলে গেলেন? এটা যে এঙ্গেল্সের কারসাজি প্লেখানভের ভুল ব্যাখ্যা বলে চালাব, তারও উপায় রাখলেন না! কেন না, এর দুটো জার্মান সংস্করণই আপনি আপনার জীবদ্দশায় বের করে রেখে গিয়েছিলেন।
ও হ্যাঁ, একটা উপায় হয়ত আছে। আমাদের বাঙালি শুধু-মার্ক্স-পন্থী বুদ্ধিজীবী প্রদীপ বক্সী তবু একটা রাস্তা খুলে রেখেছেন। পুঁজি গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ বেরয় মার্ক্সের মৃত্যুর পর এবং সেখানে নাকি এঙ্গেলসের পরিচালনায় অনেক জায়গাতেই মার্ক্সের আসল বক্তব্য পালটে দেওয়া হয়। সুতরাং মূল জার্মানে নিশ্চয়ই এরকম নেই। আর জার্মান ভাষা কজন জানে যে মূল জার্মান পাঠ খুলে এই জায়গাটা মিলিয়ে নেবে?
আমিও প্রথমে সেরকমই ভেবেছিলাম। পরে দেখি, কী সর্বনাশ, ইন্টারনেট-এর দৌলতে সেই সুযোগও এখন হাতছাড়া।
গুগলের সাহায্যে নেট হাতড়ে খুঁজে দেখা গেল, একেবারে আদি (1867) জার্মান সংস্করণের সংশ্লিষ্ট জায়গায় মার্ক্স এমন একটা বয়ান লিখে রেখে গেছেন, যাকে এঙ্গেল্সের ভাবশিষ্যরা ইংরেজিতে নির্ভেজাল আক্ষরিক অনুবাদ করেছিলেন: “Diess Rechtsverhältniss, dessen Form der Vertrag ist, ob nun legal entwickelt oder nicht, ist nur das Willensverhältniss, worin sich das ökonomische Verhältniss wiederspiegelt. Der Inhalt dieses Rechts-oder Willensverhältnisses ist durch das ökonomische Verhältniss selbst gegeben.” [Marx 1867, 45] জার্মান ভাষা অল্প বিস্তর জানি বলে অনুবাদের সঙ্গে মূল পাঠ মিলিয়ে নিতে খুব বেশি অসুবিধা হল না। আর তখনই মনে হল -- হায়, হের কার্ল মার্ক্স! আপনি আপনার এই নির্ভেজাল ভক্তরূপী শুধু-মার্ক্স বিদ্বানদের বেইজ্জতির আয়োজন একেবারে এতটা পাকা করে রেখে গেলেন!
[৩]
কমরেড হুডিস খেয়াল করেছেন কিনা জানি না, কার্ল মার্ক্সও অনেক জায়গায় ভুল বক্তব্য রেখেছেন। আমরা সচরাচর সেগুলো উল্লেখ করি না প্রয়োজন হয় না বলে। মার্ক্সের সঠিক বক্তব্যের পরিমাণ এত বেশি যে তাকে আত্মসাৎ করতে করতেই আমাদের মতো ক্ষুদ্র মানবের পাতি জীবনকাল শেষ হয়ে যায়, তাই দুচারটে ছোটখাটো ভুল চোখে পড়লেও তা নিয়ে মাথা ঘামানোর আমাদের সময় বা সুযোগ হয় না। কিন্তু তাতেও ভুলটা ভুলই থাকে। যেমন, মার্ক্স যাজক ম্যালথুসের জনসংখ্যা তত্ত্ব সম্পর্কে সঠিক সমালোচনা করেও ডারউইনের তত্ত্বে তার প্রয়োগের ব্যাপারে যে একাধিকবার শ্লেষাত্মক সমালোচনা করেছেন, সেটা তথ্যগতভাবে সম্পূর্ণ ভুল ছিল। হুডিসকে খুশি করার জন্য বলে রাখি, একই ভুল এঙ্গেলসও করেছিলেন। সম্ভবত মার্ক্সের ভাবনাধারণার প্রভাবের ফলেই।
একইভাবে হুডিস তাঁর উপরোক্ত প্রবন্ধের গোড়ায় মার্ক্সের Theories of Surplus Value বইয়ের প্রথম খণ্ড থেকে যে বয়ানটি উদ্ধৃত করেছেন, সতর্ক মার্ক্সবাদী পাঠক মাত্রই বুঝতে পারবেন, কথাটা মার্ক্সের হলেও ভুল। তাঁর জীবদ্দশায় এই বইটি প্রকাশিত হলে আমার ধারণা, তিনি এই বক্তব্যটা পালটে ফেলতেন। তাঁর ভিত উপরকাঠামোর মূল থিসিসের সঙ্গে মিলিয়েই বয়ানটি শুধরে দিতেন। কেন না, সেই থিসিস মার্ক্সবাদের একটা অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। একে বাদ দিলে বিশ্ব ইতিহাসের এক লম্বা সময়ের বড় বড় রাজনৈতিক ঘটনাবলির কোনো সাধারণ ব্যাখ্যাই দাঁড়ায় না। আর একে গ্রহণ করলে রাষ্ট্র, ধর্ম, রাজনীতি, যুদ্ধ, বিপ্লব—ইত্যাকার সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনাবলি একটা বোধগম্য ব্যাখ্যার অন্তর্গত হয়ে ওঠে। তবে শিল্প সাহিত্য সঙ্গীত ইত্যাদির ব্যাখ্যায় আরও সতর্ক ভাবে এগোতে হয়। বুদ্ধিমান মার্ক্সবাদীদের কাছে এগুলো সবই মার্ক্সবাদের অআকখ।
সেই জন্যই হুডিসকে স্মরণ করিয়ে দেব, তিনি মাঝখানে চেক দার্শনিক কারেল কসিক-এর যে গুরুত্বপূর্ণ রচনা থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন, সেটা আসলে এঙ্গেলসের বক্তব্যেরই রকমফের (কসিকের এই গুরুত্বপূর্ণ বইটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আমি কমরেড হুডিস-এর প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ)। আর সেই বইটা ভালো করে পড়লে, সেখানেই তিনি মার্ক্সের সেই থিসিসের সমর্থনে অত্যন্ত জোরালো বক্তব্য দেখতে পেতেন। আপাতত শুধু মাত্র একটা উদ্ধৃতি দিয়ে রাখি। কসিক প্রথমে প্লেখানভ এবং ল্যাব্রিওলার অনুসরণে অর্থনৈতিক উপকরণ এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে পার্থক্যের প্রকরণটি মেনে নিয়েছেন, যদিও তাঁদের ব্যাখ্যার সঙ্গে একমত হননি। [Kosik 1976, 61-62] তার পর বলেছেন: “. . . the economic structure will continue to maintain its primacy as the fundamental basis of social relations.” [Ibid, 63] আর একটু এগিয়ে তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, “Materialist monism [= Marxism] considers society to be a whole which is formed by the economic structure, i.e., by the sum total of relations that people in production enter into with respect to the means of production. It can provide a basis for a complete theory of classes, as well as an objective criterion for distinguishing between structural changes that affect the character of the entire social order, and derivative, secondary changes that only modify the social order without fundamentally altering its character.” [Ibid, 64]
অর্থাৎ, মার্ক্সের সেই উদ্ধৃতিটিকে সত্য বলে ধরলে আর কসিক থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া যায় না, আবার পক্ষান্তরে কসিকের কথা মানলে মার্ক্সের সেই জীবদ্দশায় অপ্রকাশিত বক্তব্যকে মেনে নেওয়া যায় না।
মুশকিল হচ্ছে, শুধু-মার্ক্স-স্তম্ভের উপরে মার্ক্সীয় মতাদর্শকে দাঁড় করাতে গিয়ে হুডিস এবং তাঁর মতো সমচিন্তকরা এরকম উল্টোপাল্টা কথার প্যাঁচে জড়িয়ে পড়ছেন। আমরা আশা করব, যাঁরা তাঁদের এই সব কথায় কান পাতছেন বা মাথা নাড়ছেন, তাঁরাও সমস্ত বিষয়টা আরও ভালো করে ভেবে দেখবেন এবং চার দিক থেকে মিলিয়ে নেবেন।
সূত্রোল্লেখ
Karel Kosík (1976), Dialectics of the Concrete, Dordrecht-Holland: D. Reidel, 1976.
Karl Marx (1969), Theories of Surplus Value, Part 1 [1861-63]; Moscow: Progress Publishers.
Karl Marx (1974), Capital, Vol. I; Moscow: Progress Publishers.
Karl Marx (1867), Das Kapital, Band I; from Internet Archive: visit –
https://archive.org/details/daskapitalkritik67marx/page/n3/mode/2up