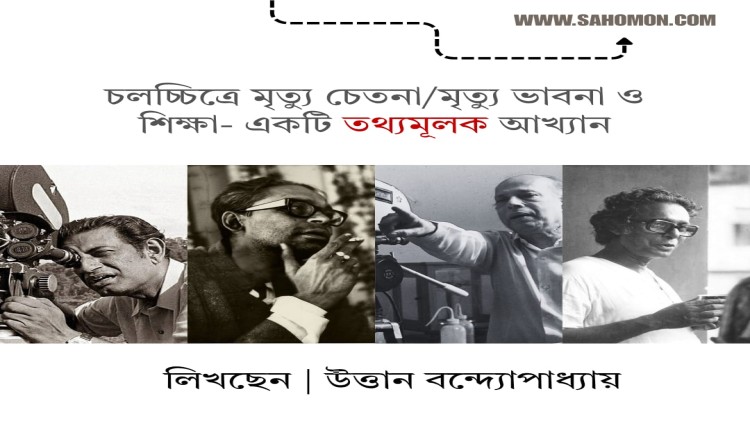(এক)
একটা ব্যাপার নিয়ে খুব ভাবছি। 'মৃত্যু দর্শন' বা 'মৃত্যু শিক্ষা' বা 'মৃত্যু চেতনা' নিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রচুর লেখা, গান , কবিতা, গল্প ও উপন্যাস এবং পরিবেশ সম্পর্কিত ও মনন সম্পর্কিত প্রবন্ধ আছে। কিন্তু কীভাবে এই মৃত্যু দর্শন সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটক, তপন সিংহ, আদুর গোপালকৃষ্ণান, জি অরভিন্দন এবং গিরীশ কাসারাভাল্লির ছবিতে তা রেখাপাত করেছে।
মৃত্যু সম্পর্কিত শিক্ষা চিকিৎসা বিজ্ঞানে তেমন সচল নেই। তাই থেরাপিউটিক এর দিকে যেমন চিকিৎসা বিজ্ঞান নিজের জয়গান গায়, প্যালিয়েটিভ বিষয়ে ভীষণ অনীহা দেখায় কারণ বাণিজ্যে শ্রেষ্ঠীদের মদত নেই এসবে।
মৃত্যু বিষয়কে তাই এড়িয়ে যায় - এসব নিয়ে সাইকিয়াট্রিস্ট দেরও জ্ঞান , মেধা অত্যন্ত কম।
ভোগবাদের চড়কিপাকে ঘুরতে থাকলে মৃত্যুচিন্তা ভুলে থাকা যায়। অথচ মানুষের মূল অনিরাপত্তা - দলছুট্ হয়ে যাওয়ার ভয়, যার মূল বীজ রোপিত আছে মৃত্যুচিন্তায়।
তবে মৃত্যু শিক্ষা যে চিকিৎসা বিজ্ঞানের পঠনপাঠনে এমনকি ফরেনসিক মেডিসিন বা সাইকিয়াট্রি তেও তেমন নেই বা শেখানো হয় না তার মূল কারণ এই জ্ঞানচর্চায় শ্রেষ্ঠীদের কোন মুনাফার ক্ষেত্র নেই। তাই প্যালিয়েটিভ কেয়ারের চিকিৎসা ব্রাত্য করা হয়েছে। ইদানিং আবার প্যালিয়েটিভ কেয়ারেও থেরাপিউটিকের মতন কেমোথেরাপির আমদানি করা হয়েছে। আরো কম্প্রোমাইজ করো শরীরটাকে - এইভাবে মুনাফা লোটো । এটাও একটা পুঁজিবাদী আখ্যান। এখানেই প্রশ্ন করা যায় যে চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাফল্যের অনুপাত সমানুপাতে রোগির স্বার্থ বনাম বাণিজ্যিক মুনাফা কতটা সমানুপাতিক ! এ প্রশ্ন ভাবতেই হবে।]
ভারতীয় সিনেমায় মৃত্যু বা মৃত্যু চেতনার প্রতিফলন ঋত্বিক ঘটক, সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন এবং তপন সিংহের সিনেমায় অত্যন্ত গভীরভাবে ফুটে উঠেছে। তাঁদের কাজগুলোতে মৃত্যু শুধুমাত্র একটি শারীরিক ঘটনা নয়, বরং এটি এক গভীর মানসিক এবং দার্শনিক মাত্রা পায়। তাঁদের ছবিতে মৃত্যু চেতনার দর্শন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ফুটে উঠেছে। তাদের কাজের মধ্যে এই থিমটি কখনো ব্যক্তিগত, কখনো সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এসেছে।
১. ঋত্বিক ঘটক:
ঋত্বিক ঘটকের সিনেমাগুলোতে মৃত্যু চেতনা বারবার উঠে এসেছে দেশভাগের যন্ত্রণা এবং শরণার্থীদের জীবনের মধ্য দিয়ে। উদাহরণস্বরূপ, "মেঘে ঢাকা তারা"-তে নীতার চরিত্রের আত্মত্যাগ এবং তার শেষ সংলাপ "আমি বাঁচতে চাই"—মৃত্যুকে এক করুণ অথচ প্রতীকী রূপ দেয়। তখন মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার যন্ত্রণা অনবদ্যভাবে ফুটে ওঠে। আবার, "কোমল গান্ধার"-এ মৃত্যু শুধু শারীরিক নয়, বরং সংস্কৃতি, সম্পর্ক এবং ঐতিহ্যের মৃত্যু হিসেবে প্রতিফলিত হয়।
ঋত্বিক ঘটকের সিনেমায় মৃত্যু চেতনা প্রায়শই রাজনৈতিক এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে এসেছে। তাঁর "যুক্তি তক্কো আর গপ্পো" ছবিতে ব্যক্তিগত এবং জাতীয় সংকটের মধ্যে মৃত্যু একটি প্রতীকী রূপ পায়। দেশভাগের ফলে উদ্বাস্তু জীবনের যন্ত্রণা এবং মৃত্যুর আতঙ্ক তাঁর ছবিতে বারবার ফিরে আসে।
২. সত্যজিৎ রায়:
সত্যজিৎ রায়ের সিনেমাগুলোতে মৃত্যু এক অন্তর্নিহিত মানসিক ও দার্শনিক স্তর নিয়ে আসে। উদাহরণস্বরূপ, "অপুর সংসার"-এ অপর্ণার মৃত্যু অপুকে মানসিকভাবে ভেঙে দেয়, কিন্তু এটি তাকে জীবনের গভীরতর উপলব্ধির দিকে ঠেলে দেয়। আবার, "শতরঞ্জ কে খিলাড়ি"-তে মৃত্যু ও পতন দেখানো হয়েছে ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে।
সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে মৃত্যু চেতনার দর্শন বেশ সূক্ষ্ম এবং মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপিত। উদাহরণস্বরূপ, "অশনি সংকেত" ছবিতে দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে মানুষের মৃত্যু এবং তার সামাজিক প্রভাব ফুটে উঠেছে। আবার, "অপরাজিত" ছবিতে অপু তার মায়ের মৃত্যুতে একাকীত্ব ও মানসিক ধাক্কার সম্মুখীন হয়। এই মৃত্যু চেতনা ব্যক্তিগত এবং গভীরভাবে আবেগময়।
৩. মৃণাল সেন:
মৃণাল সেনের সিনেমায় মৃত্যু চেতনা সমাজের দৈনন্দিন বাস্তবতা এবং শ্রেণি সংগ্রামের প্রতীক। উদাহরণস্বরূপ, "কলকাতা ৭১"-এ মৃত্যু শুধুমাত্র ব্যক্তি নয়, বরং একটি পুরো প্রজন্মের স্বপ্নের মৃত্যু হিসেবে প্রতিফলিত হয়। "কলকাতা ৭১"-এ তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে দারিদ্র্য এবং বৈষম্য মানুষের জীবনে মৃত্যু এবং বেঁচে থাকার প্রশ্নকে প্রাসঙ্গিক করে তোলে। তাঁর "ভুবন সোম"-এও মৃত্যুর ধারণা এক সামাজিক রূপ পায়।
তাঁর চলচ্চিত্রে মৃত্যু কেবল একটি শারীরিক ঘটনা নয়, বরং সমাজের অবক্ষয়ের প্রতীক।
৪. তপন সিংহ:
তপন সিংহের সিনেমাগুলোতে মৃত্যু চেতনা অনেক মানবিক ও নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখানো হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, "অতিথি"-তে একটি শিশুর মৃত্যু জীবনের অমোঘ বাস্তবতা এবং মানবিক সম্পর্কের জটিলতা বোঝায়। ছবিতে অতিথি চরিত্রটি মৃত্যুর মাধ্যমে জীবনের গভীর সত্যকে উপলব্ধি করায় এবং সমাজের মূল্যবোধকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। তাছাড়া, "হাটে বাজারে"-তেও মৃত্যু সমাজ ও অর্থনৈতিক বাস্তবতার প্রতীক হয়ে ওঠে।
তপন সিংহের সিনেমায় মৃত্যু চেতনা প্রায়শই ব্যক্তিগত এবং সম্পর্কের গভীরতায় প্রভাব ফেলে। তাঁর ছবিতে মৃত্যু একটি আবেগঘন এবং নৈতিক দিক নিয়ে আসে।
এই চারজন পরিচালকের কাজের মধ্য দিয়ে মৃত্যু চেতনা কখনো ব্যক্তিগত, কখনো সামাজিক, আবার কখনো ঐতিহাসিক বা দার্শনিক স্তর পেয়েছে। তাঁদের কাজগুলো ভারতীয় সিনেমাকে এক গভীর শিল্পরূপ দিয়েছে।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু চেতনা গভীর দার্শনিক এবং মানবিক উপলব্ধির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। তিনি মৃত্যুকে কখনো বিচ্ছেদ, কখনো মুক্তি, কখনো অনন্ত জীবনের এক অমোঘ সত্য হিসেবে দেখেছেন। এই চেতনার প্রতিফলন তাঁর গান, কবিতা এবং গল্পে যেমন দেখা যায়, তেমনি ভারতীয় সিনেমায় ঋত্বিক ঘটক, সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন এবং তপন সিংহের কাজে কিছুটা অনুরূপ ধাঁচে ফুটে উঠেছে।
ঋত্বিক ঘটকের সিনেমায় মৃত্যু চেতনা প্রায়শই রাজনৈতিক এবং ঐতিহাসিক বাস্তবতার সঙ্গে জড়িত।
"মেঘে ঢাকা তারা" ছবিতে নীতার শেষ মুহূর্তের সংলাপ "আমি বাঁচতে চাই"–এ মৃত্যুর প্রতি এক চরম উপলব্ধি ফুটে ওঠে। এটি রবীন্দ্রনাথের "মরণ রে, তুঁহু মম শ্যাম সমান" গানের দার্শনিক সুরের মতো—যেখানে মৃত্যু একদিকে যন্ত্রণার, আবার অন্যদিকে শাশ্বত সত্য।
"সুবর্ণরেখা"-তে মৃত্যুকে সমাজের অবক্ষয়ের প্রতীক হিসেবে দেখানো হয়েছে, যেখানে মৃত্যু শুধুমাত্র ব্যক্তিগত নয়, বরং ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মৃত্যু। এটি রবীন্দ্রনাথের "যা হারিয়ে যায় তা সুরের মতো ফিরে আসে" ভাবনার সঙ্গে মিল খুঁজে পায়।
সত্যজিৎ রায়ের সিনেমায় মৃত্যু চেতনা অত্যন্ত মানবিক ও দার্শনিক।
"অপরাজিত" ছবিতে অপু তার মায়ের মৃত্যুতে এক গভীর শূন্যতার মধ্যে পড়ে, যা রবীন্দ্রনাথের "তোমারই মৃত্যুতে আমি বাঁচি" দর্শনের সঙ্গে এক অদ্ভুত সাযুজ্য তৈরি করে। মৃত্যু এখানে আত্মোপলব্ধির একটি মাধ্যম।
"চারুলতা" বা "ঘরে বাইরে"-এর মতো ছবিতেও সম্পর্কের ক্ষয় বা মানসিক মৃত্যুর প্রসঙ্গ উঠে আসে, যা রবীন্দ্রনাথের "শুভ মৃত্যু" ধারণার সঙ্গে মিল খুঁজে পায়।
মৃণাল সেনের কাজগুলো সমাজের বাস্তবতার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত।
"কলকাতা ৭১" ছবিতে মৃত্যু দারিদ্র্য, ক্ষুধা আর বৈষম্যের প্রতীক। এটি রবীন্দ্রনাথের "মৃত্যু যেন একটি অন্তর্গত মুক্তি" ভাবনার বিপরীতে দাঁড়িয়ে সমাজের কঠোর বাস্তবতাকে তুলে ধরে।
"ভুবন সোম"-এও মৃত্যু চেতনা এক দার্শনিক স্তর পায়, যেখানে ব্যক্তিগত পাপ বা নৈতিকতার প্রশ্ন উঠে আসে, যা রবীন্দ্রনাথের আত্মিক শুদ্ধির দর্শনের সঙ্গে তুলনীয়।
তপন সিংহের সিনেমায় মৃত্যু চেতনা ব্যক্তিগত ও সম্পর্কের গভীরতায় প্রভাব ফেলে।
"অতিথি" ছবিতে অতিথির উপস্থিতি এবং তার মৃত্যুকে জীবনের এক গভীর উপলব্ধি হিসেবে দেখানো হয়েছে, যা রবীন্দ্রনাথের "মৃত্যু জীবনের ছন্দে বাঁধা" ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।
"হাটে বাজারে" ছবিতে মৃত্যু সমাজের অর্থনৈতিক চাপ এবং মানবিক সম্পর্কের সংকটকে প্রকাশ করে, যা রবীন্দ্রনাথের জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্বের গভীর দার্শনিক চেতনার কথা মনে করিয়ে দেয়।
সারসংক্ষেপ:
রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু চেতনা যেমন গভীর দার্শনিক ও আবেগময়, তেমনি এই চার পরিচালক তাঁদের সিনেমায় মৃত্যুকে কখনো ব্যক্তিগত, কখনো সামাজিক বা রাজনৈতিক স্তরে উপস্থাপন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের "মৃত্যু মানে মুক্তি" এবং "মৃত্যু মানে উপলব্ধি" দর্শন তাঁদের কাজের মধ্যে বারবার ফিরে আসে।
(দুই)
মৃত্যু চেতনা, মৃত্যু শিক্ষা বা মৃত্যু দর্শন নিয়ে আদুর গোপাল কৃষ্ণান, অরভিন্দন ও গিরীশ কাসারাভাল্লির সিনেমাগুলিতে গভীর দার্শনিক মনন দেখা যায়।
১. আদুর গোপাল কৃষ্ণান: তাঁর সিনেমা "নিজালক্কুথু" (2002) মৃত্যুদণ্ড প্রথা এবং তার নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। এখানে এক জল্লাদের মানসিক দ্বন্দ্ব এবং তার কাজের ফলে তার নিজের পরিবারের ওপর পড়া প্রভাব দেখানো হয়েছে। এটি মৃত্যুর চূড়ান্ততা এবং এর সামাজিক ও নৈতিক প্রভাবের গভীর আলোচনা।
২. জি অরভিন্দন: তাঁর "কাঞ্চন সীতা" (1977) একটি কাব্যিক সিনেমা, যেখানে রামায়ণের কাহিনি ব্যবহার করে জীবনের অস্থায়িত্ব এবং ধর্মীয় অর্থে ত্যাগের দার্শনিক দিক তুলে ধরা হয়েছে। যদিও এটি সরাসরি মৃত্যুকে কেন্দ্র করে নয়, তবুও ত্যাগ ও চূড়ান্ত পরিণতির সাথে জড়িত অনুভবগুলি স্পষ্ট।
৩. গিরীশ কাসারাভাল্লি: তাঁর "গুলাবি টকিজ" (2008) সিনেমায় মৃত্যুর চেতনা সরাসরি না থাকলেও, মানুষের অস্তিত্ব, স্থানান্তর, এবং সময়ের সঙ্গে সম্পর্কিত দার্শনিক প্রশ্নের গভীরতা দেখা যায়। তাঁর কাজগুলিতে সামাজিক ও দার্শনিক স্তরে জীবনের ক্ষণস্থায়িত্বের ভাবনার ছাপ স্পষ্ট।
(তিন)
মৃত্যুশিক্ষা: পৃথিবীর বিখ্যাত সিনেমায় মৃত্যু চেতনার আখ্যান
মৃত্যু মানব জীবনের একটি অবধারিত সত্য। এটি নিয়ে ভাবনা, অনুভূতি, এবং দার্শনিক উপলব্ধি সাহিত্য, কবিতা, এবং সিনেমায় বারবার ফুটে উঠেছে। পৃথিবীর বিখ্যাত সিনেমাগুলোতে মৃত্যু চেতনা বিভিন্নভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, যা দর্শকদের জীবন, মৃত্যু, এবং অস্তিত্ব নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে।
১. "দ্য সেভেন্থ সিল" (১৯৫৭) - ইঙ্গমার বার্গম্যান
এই ক্লাসিক সিনেমায় নাইট (ম্যাক্স ফন সিডো) মৃত্যুর সঙ্গে দাবা খেলেন। এটি জীবনের অর্থহীনতা এবং মৃত্যুর অমোঘতা নিয়ে গভীর দার্শনিক প্রশ্ন উত্থাপন করে। বার্গম্যানের এই কাজ মৃত্যুকে এক রহস্যময় এবং অনিবার্য শক্তি হিসেবে উপস্থাপন করেছে।
২. "ইকিরু" (১৯৫২) - আকিরা কুরোসাওয়া
জাপানি পরিচালক আকিরা কুরোসাওয়ার এই সিনেমায় কেনজি ওয়াতানাবে একজন আমলাতান্ত্রিক ব্যক্তির ভূমিকায় অভিনয় করেন, যিনি মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে জীবনের প্রকৃত অর্থ খুঁজে পান। এটি মৃত্যুকে জীবনের উদ্দেশ্য খোঁজার এক অনুপ্রেরণা হিসেবে দেখায়।
৩. "দ্য ট্রি অব লাইফ" (২০১১) - টেরেন্স ম্যালিক
এই সিনেমায় মালিক জীবন, মৃত্যু, এবং সৃষ্টির রহস্য নিয়ে এক কাব্যিক এবং দার্শনিক আখ্যান উপস্থাপন করেছেন। এখানে মৃত্যুকে জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে, যা জীবনের সৌন্দর্য এবং দুঃখকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে শেখায়।
৪. "অ্যামেলি" (২০০১) - জাঁ-পিয়ের জুনেট
এই ফরাসি সিনেমায় অ্যামেলি পুলেইন (অড্রে টাউটো) মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়া এক বৃদ্ধকে তার জীবনের শেষ ইচ্ছা পূরণে সাহায্য করেন। এটি মৃত্যুকে ঘিরে মানবিক সম্পর্ক এবং জীবনের মূল্যবোধ নিয়ে আলোচনা করে।
৫. "দ্য ডিসকোর্সেস অব অ্যাট দ্য এন্ড অব লাইফ" (২০১৭) - জন ব্রুস ও পাওয়েল ওজটাস্ক
এই সিনেমায় এক ব্যক্তি তার মৃত্যুর আগে জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। এটি মৃত্যুকে জীবনের এক শিক্ষা হিসেবে উপস্থাপন করে, যা মানুষকে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে মূল্য দিতে শেখায়।
পরিশেষে পৃথিবীর বিখ্যাত সিনেমাগুলোতে মৃত্যু চেতনা বিভিন্নভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এগুলো দর্শকদের জীবন, মৃত্যু, এবং অস্তিত্ব নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে। মৃত্যুকে জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দেখিয়ে, এই সিনেমাগুলো আমাদের জীবনের মূল্যবোধ, মানবিক সম্পর্ক, এবং জীবনের উদ্দেশ্য খোঁজার গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষা দেয়।