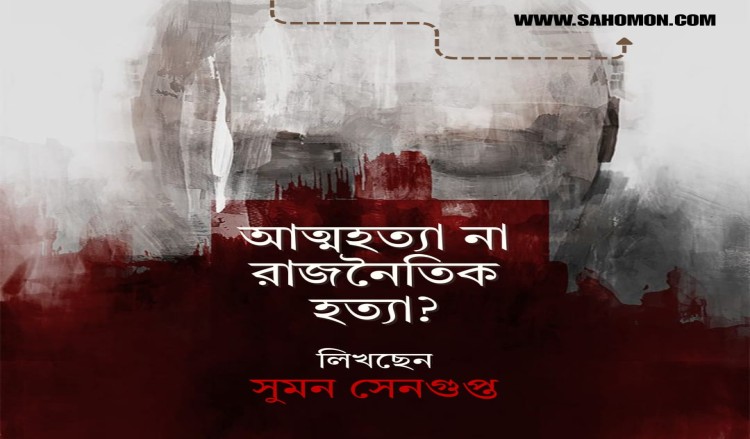সারা দেশে এখন ভোট নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। দেশের সর্বোচ্চ আদালত থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের মধ্যে একটাই আলোচনা, নিজের বা নিজের প্রিয়জনদের নাম ভোটার তালিকায় আছে তো? প্রতিটি মানুষ দুশ্চিন্তায় আছেন। ভোটার তালিকা সংশোধনের যে বিশেষ নিবিড় প্রক্রিয়া নিয়েছে নির্বাচন কমিশন, তার গতিপ্রকৃতির দিকে নজর রাখছেন প্রতিটি মানুষ। কমিশন যে নথি যোগাড় করে রাখতে বলেছে, তা নিজের এবং পরিবারের অন্য সদস্যদের আছে কি না, তার খোঁজ করে চলেছেন। ঠিক একই রকম অবস্থা হয়েছিল, গতবার যখন নাগরিকপঞ্জী তালিকা সারা দেশে করা হবে বলে প্রচার হয়েছিল।
এরই মধ্যে খবর পাওয়া গেছে কলকাতার রিজেন্ট পার্ক থানা এলাকায় একজন মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি এই বিশেষ নিবিড় সংশোধনী প্রক্রিয়া বাংলায় চালু হলে তাঁর নাম নাও থাকতে পারে এই আশঙ্কায় আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন। জানা গেছে যে আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে পূর্ব পাকিস্তান বা আজকের বাংলাদেশ থেকে তিনি এই দেশে এসেছিলেন। তা সত্ত্বেও তাঁর মনে হয়েছে, তাঁকে এই দেশ নাগরিক বলে মান্যতা নাও দিতে পারে। তাঁর মনজগতে কী কী চলেছে তা আমাদের মত বাইরের মানুষদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়, কিন্তু তাঁর পরিবারের মানুষদের কথা অনুযায়ী তিনি এই গোটা বিষয়টা নিয়ে আতঙ্কিত ছিলেন। কোন নথি গ্রাহ্য হবে, কোন নথি হবে না তা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। সেই কারণেই তিনি আত্মহত্যা করেন বলে অনুমান করা হচ্ছে।
এইরকম একটি ঘটনার দায় কে নেবে? নির্বাচন কমিশন না সরকার? সরকার তো আমাদের মতো মানুষদের দ্বারাই নির্বাচিত। সেই সাধারণ মানুষকে যদি সরকার এখন বলে ‘আপনি যে নাগরিক, তার প্রমাণ দিন’, তাহলে তো একজন মানুষের আতঙ্কিত হওয়াটাই স্বাভাবিক। যে সময়ে তিনি এই দেশে এসেছিলেন, যে সময়ে তাঁকে এই দেশ স্থান দিয়েছিল, সেই সময়ে ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত অশান্ত ছিল। তা সত্ত্বেও এই দেশ যে বহু মানুষের জন্য দরজা খুলে দিয়েছিল, তার পিছনে কাজ করেছিল মানবিকতা। গত দশ বছরে থেকে আজ অবধি এই শব্দটিই অন্তর্হিত হয়েছে দেশের অভিধান থেকে।
আসামে যে নাগরিকপঞ্জীর তালিকা হয়েছে, তাতে ১৯ লক্ষ মানুষের বাদ পড়ার কথা না হয় আমরা জানি, কিন্তু তার বাইরেও যে কত অগণিত মানুষ নানাবিধ হয়রানির কথা কি আমাদের জানা আছে? বহু অসরকারি সংগঠন এই বিষয়ে আসামে কাজ করতে গিয়ে মানুষের দৈনিক হয়রানি দেখেছেন। নাগরিক অধিকার ও মানবাধিকার নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন সংগঠনের অন্যতম ‘সিটিজেন্স ফর জাস্টিস অ্যান্ড পিস’ একটি তথ্য প্রকাশ করেছিল ২০১৮ সালের জানুয়ারি মাসে প্রথম নাগরিকপঞ্জীর খসড়া তালিকা প্রকাশ থেকে ২০১৯ সালের জুন মাসের মধ্যে অন্তত ৫১ টি আত্মহত্যার ঘটনা নথিভুক্ত করা হয়েছে শুধু আসামে। বাড়ি, জমি জায়গা থেকে উৎখাত হবার ভয় এবং পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে ডিটেনশন ক্যাম্পে যাওয়ার আতঙ্ক থেকেই এই আত্মহত্যার ঘটনা হয়েছে বলে তাঁরা তাঁদের রিপোর্ট প্রকাশ করেছিল। একজন মানুষ কতটা উদ্বেগে থাকলে নিজের জীবন শেষ করে দিতে পারে, তার কোনও আন্দাজ কি আইন প্রণেতাদের আছে?
এই সরকার গত ১১ বছরে আসলে প্রতিটি নাগরিককে একলা করে দিয়েছে। প্রতিটি নাগরিককে তাঁর নিজের নাগরিকত্ব নিয়ে এতটাই ব্যস্ত রেখেছে, যে তিনি অন্য কিছু নিয়ে ভাবতেই যাতে না পারেন তার ব্যবস্থা করেছে। কখনো আধারের সঙ্গে ব্যাঙ্কের সংযোগ, কখনো ফোনের বা রেশন কার্ডের সঙ্গে আধারের সংযোগ করানোর নিদান দেওয়ার মধ্যে দিয়ে প্রতিটি নাগরিককে উদ্বেগে রেখেছে। ভোটার তালিকায় যে বিশেষ নিবিড় সংশোধনী চলছে তাতেও বহু মানুষ উদ্বিগ্ন হচ্ছেন তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ এই সাম্প্রতিক রিজেন্ট পার্ক থানার আত্মহত্যার ঘটনা। এই ঘটনা নিয়ে দেশের সর্বোচ্চ আদালতে শুনানি চলাকালীন বিচারপতি সূর্য কান্তও বলেন কোনও নাগরিককে এইভাবে উদ্বেগে রাখা ঠিক নয়।
যে দেশের সরকার, তার একজন নাগরিককে স্বস্তিতে ঘুমোতে দেয় না, তাঁকে আতঙ্কে রাখে সারাক্ষণ, সেই সরকারকে অমানবিক ছাড়া অন্য কিছু বলা যায় কি? যে দেশের সরকারি আইন একজন নাগরিককে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করে, সেই দেশের সরকারকে কি মানবিক বলা যায়? যখন আসামে নাগরিক পঞ্জীকরণ শুরু হয়েছিল, এইরকম বহু ঘটনা আমাদের সামনে এসেছিল। ৮৮ বছরের আশরফ আলি এবং তাঁর পরিবারের সকলের নাম নাগরিকপঞ্জীতে উঠেছিল। তারপরেও তাঁর এক প্রতিবেশী এই বিষয়টি নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে অভিযোগ করেন। বলা হয়, আবার ঐ অশীতিপর বৃদ্ধকে তাঁর নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে হবে। ঐ সময়টা ছিল রমজান মাস। একদিন বিকেলে তিনি বলেন, তিনি বাইরে যাচ্ছেন তাঁর রোজা ভাঙতে। তারপর জানা যায়, তিনি বিষ খেয়ে তাঁর জীবন শেষ করে রোজা ভেঙেছেন। তিনি ভয় পেয়েছিলেন, তাঁর নাগরিকত্ব নিয়ে যদি সরকার সন্দিহান হয়, তাহলে তাঁকে ডিটেনশন ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হবে। আমরা ভুলে যাইনি, ১১ বছরের ঝাড়খন্ডের কিশোরী সন্তোষীর কথা, যার পরিবারের আধারের সঙ্গে রেশন কার্ড সংযোগ না থাকার কারণে না খেতে পেয়ে ‘ভাত ভাত’ করতে করতে মারা যায়। যদিও সরকার এই মৃত্যুগুলোর জন্য কোনও দায় স্বীকার করেনি, কিন্তু এই মৃত্যুগুলো দেখিয়ে দেয় আমাদের দেশের সরকার কতটা অমানবিক।
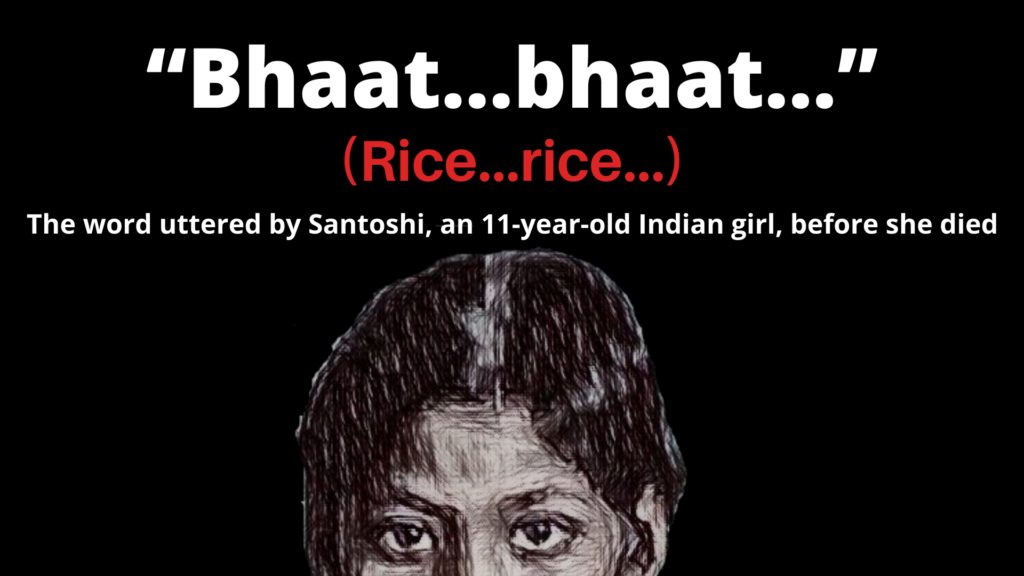
বিহারের পরে বাংলাতেও এই প্রক্রিয়া নেওয়া হবে। রাজনৈতিক নেতারা ইতিমধ্যেই সুর চড়াচ্ছেন। কোনও অনুপ্রবেশকারী বা রোহিঙ্গা মুসলমানের নাম যাতে না থাকে, সেই ব্যবস্থা নিতে হবে বলে ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারকে আর্জি জানিয়েছেন বাংলার প্রধান বিরোধী দল। বিতর্ক শুরু হয়েছে রাজনৈতিক স্তরে, কিন্তু এই বিষয়টা একজন সাধারণ নাগরিকের মনে কী প্রভাব ফেলছে তা কি রাজনৈতিক নেতারা বোঝেন? এই মৃত্যুকে কেউ যদি আত্মহত্যা না বলে সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক হত্যা বলা হয়, তা কি খুব ভুল হবে? এই রাজ্যের শাসকদলের দৃঢ় অবস্থানও কিন্তু ভরসা যোগাতে পারেনি ঐ মানুষটিকে। কতটা মানসিক উৎকন্ঠায় থাকলে একজন মানুষ নিজেকে শেষ করে দিতে পারে, তা কি অমানবিক এই রাষ্ট্র এবং সরকার জানে বা জানতে চায়। রাষ্ট্র একজন নাগরিককে চূড়ান্ত সুযোগ সুবিধা না দিতে পারুক, এইটুকু আস্বস্ত তো করতে পারে, যে তিনি এই দেশের বৈধ নাগরিক। স্বাধীনতার ৭৯ তম বর্ষে দেশের প্রতিটি নাগরিক কি এইটুকু আশা করতে পারেনা দেশের কাছে, দেশের সরকারের কাছে? যে সরকারকে তিনি নিজেই বেছে নিয়েছেন ভোটের মাধ্যমে সেই সরকার যদি বৈধ হয়, তাহলে সেই দেশের নাগরিক কী করে অবৈধ হয়ে যান, এই প্রশ্ন করার সময় এসেছে। নাকি ভোট চুরির এই অভিযোগের পরিবেশে সরকার নিজেই নিজেকে অবৈধ ভাবছে? তাহলেও যে প্রশ্নটা করতে হয়, একটি অবৈধ সরকার কী করে একজন নাগরিকের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে এমন অমানবিক আচরণ করতে পারে? সরকারি যে কোনও আইন কি সরকারকে অমানবিক হওয়ার ক্ষমতা দেয় ? দেশের পতাকা উত্তোলন হলো স্বাধীনতা দিবসে, রাজনৈতিক নেতা থেকে শুরু করে দেশের প্রধানমন্ত্রী মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য লাল কেল্লা থেকে ভাষণ ও দিলেন। আবারও একই ক্লিশে কথাগুলো বলে গেলেন। আবারও জনবিন্যাস পরিবর্তন নিয়ে কথা বললেন কিন্তু সরকারের এই বিষয়ে কী দায় তা এড়িয়ে গেলেন। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিরোধীদের আক্রমণ করলেন এই জনবিন্যাস পরিবর্তনকে সমর্থন যোগানোর জন্য, কিন্তু তাতেও কি একজন ব্যক্তি নাগরিককে মানসিক শান্তি দিতে পারলেন? তাতেও কি আসামের আশরফি আলির পরিবার বা কলকাতার রিজেন্ট এস্টেট থানা এলাকায় সদ্য আত্মহত্যা করে মারা যাওয়া মানুষদের পরিবারের লোকজন এতটুকুও আস্বস্ত হলেন ? তাই আজকে এই এত কলরবের মাঝখানে, এত স্বাধীনতা দিবস পালনের উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে এই আত্মহত্যাগুলোকে সরকারি মদতে রাজনৈতিক হত্যা বললে, খুব অতিশয়োক্তি হবে?