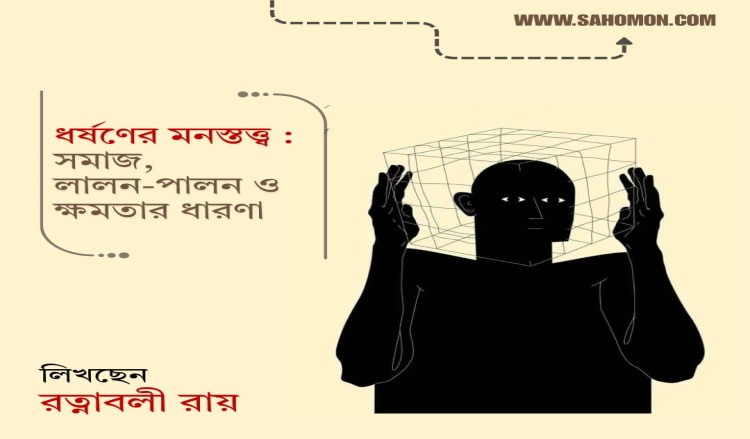বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সংজ্ঞা বলছে―ধর্ষণ হল যৌন হিংসার এমন একটি রূপ– যা সম্মতির বিরুদ্ধে
যৌন সম্পর্ক স্থাপন, জোরজবরদস্তি এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে সংঘটিত হয়। ২০১২ সালের নির্ভয়া আন্দোলনের পর আইনে কিছু ইতিবাচক বদল দেখা গেছে। তবুও এখনো আমাদের চারপাশে ধর্ষণের ঘটনা ব্যাপক হারে ঘটছে।
ধর্ষণ কেবলমাত্র শারিরিক বা যৌন-হিংসা নয়। এটি আসলে সমাজের শিকড়ে থাকা নানা মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক ও কাঠামোগত বিচ্যুতির প্রকাশ। আমাদের দেশে লিঙ্গ-সম্পর্কগুলি চালিত হয় পুরুষতন্ত্রের নিয়মে। যে পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোয় মেয়েদের কন্ঠস্বরকে দাবিয়ে রাখা হয়। ফলে আজকের দিনে ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে ধর্ষণের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিটি বোঝা অত্যন্ত জরুরি। কারণ এখান থেকেই তৈরি হতে পারে প্রতিরোধ ও পুনর্বাসনের নানা কৌশল। এই নিবন্ধে ধর্ষণের পেছনে থাকা নানা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই ব্যাখাগুলিকে ভারতের সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে দেখার চেষ্টা করেছি। পাশাপাশি এই বিষয়ে বিভিন্ন আইনে, নিয়মনীতিতে কী কী বদল আনা যায়, কমিউনিটি স্তরে কী করা যায়―সেসব নিয়ে কিছু ভাবনাও রেখেছি।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সংজ্ঞা বলছে―ধর্ষণ হল যৌন হিংসার এমন একটি রূপ– যা সম্মতির বিরুদ্ধে
যৌন সম্পর্ক স্থাপন, জোরজবরদস্তি এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে সংঘটিত হয়। ২০১২ সালের নির্ভয়া আন্দোলনের পর আইনে কিছু ইতিবাচক বদল দেখা গেছে। তবুও এখনো আমাদের চারপাশে ধর্ষণের ঘটনা ব্যাপক হারে ঘটছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের হচ্ছে না। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো (NCRB)'র তথ্য দেখায়―২০২১ সালে ৩১,৫১৬টি ধর্ষণের মামলা নথিভুক্ত হয়েছে। কিন্তু এটি হিমশৈলের চুড়ো মাত্র। বাস্তব ছবিটা এর চেয়ে অনেক বেশি ভয়ঙ্কর।
একজন ব্যক্তি কেন ধর্ষণ করে―বুঝতে হলে একটি আন্তঃবিভাজনমূলক (intersectional) মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন। যেখানে ব্যক্তিগত নানা বিচ্যুতি, সমাজ থেকে পাওয়া শিক্ষা, সংস্কৃতির প্রভাব, চিন্তা–চেতনার অসামঞ্জস্য― একসঙ্গে বিবেচনা করা হবে।
ধর্ষণের নানা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা
১। ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ মডেল
নারীবাদী তাত্ত্বিকরা সর্বপ্রথম এই মডেলটি উপস্থাপন করেছিলেন। তাঁদের মতে, ধর্ষণ আদতে যৌন আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ নয়। বরং এটি মূলত ক্ষমতা প্রদর্শনের একটি উপায়। নারীর উপর আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার অস্ত্র। ভারতের মতো পুরুষতান্ত্রিক সমাজে, যেখানে পৌরুষের একটি ধারণা হল―নারীদেহকে নিয়ন্ত্রণ করা―সেখানে এই মডেল বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। ব্রাউনমিলার (১৯৭৫) সহ একাধিক গবেষণায় দেখা যায়, ধর্ষণ কীভাবে একটি নির্দিষ্ট লিঙ্গকে পদানত করে রাখার অন্যতম মাধ্যম হয়ে উঠছে। যেমন অনেকক্ষেত্রেই ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে, ভারতবর্ষের সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক কাঠামোর মধ্যে। যার ভেতরে থইথই করছে জাত-পাতের বিভাজন। ফলে দেখা যাচ্ছে―উচ্চবর্ণের পুরুষরা দলিত, আদিবাসী কিংবা মুসলিম নারীদের উপর যৌন নির্যাতন চালিয়ে নিজেদের আধিপত্য কায়েম করছে।
২। সামাজিক শিক্ষার তত্ত্ব
ব্যান্ডুরার সামাজিক শিক্ষার তত্ত্ব অনুযায়ী, মানুষ আচার-ব্যবহার পাঠ পায়, অন্যকে দেখে, অনুকরণের মাধ্যমে। সমাজ ‘ভালো’ আচরণকে পুরষ্কৃত করে, ‘খারাপ’- আচরণের জন্য থাকে শাস্তি। এটাও এই শিক্ষারই অংশ। আমাদের দেশে যুগে যুগে স্বাভাবিক রোমান্টিকতার মোড়কে একধরনের পৌরুষকে তুলে ধরা হয়েছে। কোন পৌরুষ? যে পৌরুষ নারীর ওপর জোর খাটায়। মূলত তিনটি ক্ষেত্রে এটি ঘটতে দেখা গিয়েছে―পরিবারে, বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে আর মিডিয়ায়। ছেলেরা এটা খুব ছোটবেলা থেকে শেখে। বিশেষ করে যেসব পরিবারে নারী নির্যাতন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা―সেখানে তার কাছে এমন আচরণ স্বাভাবিক ও গ্রহণযোগ্য। ভারতবর্ষে পৌরুষের ধারণা নিয়ে ভার্মা প্রমুখের (২০১৩) একটি গবেষণায় দেখা গেছে, বহু ভারতীয় তরুণ মনে করে, মহিলাদের 'শাসন' করতে হলে কখনও কখনও জোর খাটানো দোষের কিছু না।
৩। চিন্তা-চেতনার অসামঞ্জস্য এবং আত্মপক্ষ সমর্থন
ধর্ষকদের মধ্যে অনেকসময় বিশ্বাস থাকে―নারীরা আসলে জোর খাটানো পছন্দ করে। মুখে প্রকাশ না করলেও অন্তরে তারা বিষয়টি যথেষ্ট উপভোগ করে। ফলে খোলামেলা পোশাক মানেই যৌনাচারের সম্মতি। এই ধরনের নানা 'ধর্ষণ-সংক্রান্ত মিথ' (rape myths) ভারতীয় সমাজের গভীরে বহমান। গোঁড়া ধর্মীয় পরিসরে, সিনেমার পর্দায় এমনকি আদালতের বক্তব্যেও এর ছাপ স্পষ্ট। ফলে এসব মিথ মানুষের কাছে সহজেই গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। ভারতীয় বিচারব্যবস্থায়, আদালতের অন্দরে, একাধিকবার এমন মন্তব্য শোনা গেছে―যা ধর্ষণের ভুক্তভোগীকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে। প্রশ্ন তোলা হয়েছে তার পোশাক বা আচরণ নিয়ে। এর ফলে এই বিকৃত ভাবনা আরও বৈধতা পেয়েছে।
৪) সাইকোপ্যাথি - ব্যক্তি প্রবণতা
সব ধর্ষকের মানসিক প্রতিবন্ধকতা থাকে না। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে ধর্ষণের সঙ্গে সাইকোপ্যাথি মানে যেখানে একজন মানুষের
সহানুভূতির অভাব, মিথ্যা বলা, ঠকানো এবং হিংস্র আচরণের প্রবণতা দেখা যায়।
এরা প্রায়ই অন্যের অনুভূতি বা অধিকারকে গুরুত্ব না দিয়ে আত্মকেন্দ্রিক ও অপরাধপ্রবণ আচরণ করে।
সিং প্রমুখের (২০২০) একটি গবেষণা বলছে―সাজাপ্রাপ্ত ধর্ষকদের মধ্যে উচ্চমাত্রার 'impulsivity' (আবেগনিয়ন্ত্রণহীনতা) ও 'callousness' (নিষ্ঠুরতা) লক্ষ্য করা গেছে। এর থেকেই বোঝা যায়―ধর্ষক মাত্রই পরিস্থিতির শিকার নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা ব্যক্তিত্বজনিত নানা প্রতিবন্ধকতা থেকেই এমন অপরাধ করে।
৫। পরিবেশগত কারণ ও মানসিক বিকাশ
শৈশবে যৌন বা শারীরিক নির্যাতনের অভিজ্ঞতা হলে, বাবা-মার থেকে দূরে থাকলে, তাদের পর্যাপ্ত ভালোবাসা ও মনোযোগ না পেলে ভবিষ্যতে একটি শিশুর মনে নানা জটিলতা তৈরি হতে বাধ্য। ছোটবেলা থেকেই তার মনে গেঁথে যেতে পারে যৌনহিংসামূলক আচরণের নানা উপাদান। ভারতের বহু অঞ্চলে শিশুদের জন্য লিঙ্গ-সংবেদনশীলতা কিংবা যৌন-শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। ফলে এমন একটি পরিবেশ তৈরি হয়, যেখানে জন্ম নেয় লিঙ্গ-যৌনতা সম্পর্কে কিছু ভ্রান্ত ধারণা। শিশুমন ধীরে ধীরে আগ্রাসী হয়ে ওঠে।
কিছু-ভাবনা
১। সংবেদনশীল লিঙ্গ-যৌনতার পাঠ
ইস্কুল-স্তরে লিঙ্গ-যৌনতার শিক্ষা দিতে হবে। যেখানে পারস্পরিক সম্মতি, শ্রদ্ধা এবং ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হবে। এই শিক্ষা বুনিয়াদি স্তর থেকেই শুরু হওয়া উচিত। যাতে মনের মধ্যে নানা ভ্রান্ত ধারণা গেঁথে যাওয়ার আগেই সচেতনতা তৈরি হয়। বিশেষত ছেলেদের ও তাদের অভিভাবকদের ক্ষেত্রে এটি ভীষণভাবে প্রযোজ্য। এনসিইআরটি (NCERT)-র পাঠ্যক্রম নতুনভাবে সাজিয়ে সেখানে লিঙ্গ-যৌনতা ও মনের বিকাশ সংক্রান্ত বিষয়গুলি যুক্ত করতে হবে।
২। পৌরুষ সংক্রান্ত চালু ধারণাগুলির সংস্কার
গণমাধ্যমে প্রচারাভিযান চালাতে হবে। এলাকার মানুষদের মধ্যে কথা বলতে হবে। টক্সিক পৌরুষের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে হবে। বর্তমানে 'বেল বাজাও'-এর মতো প্রচারাভিযান আশা দেখাচ্ছে। আরো বড় অংশের মধ্যে এই ধরনের উদ্যোগ নিয়ে যেতে হবে। আচরণবিধি নিয়ে নানা মনস্তাত্ত্বিক পরামর্শও থাকবে এর মধ্যে।
৩। অপরাধীদের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করা প্রয়োজন
একজন অপরাধীর মানসিক স্বাস্থ্যের মূল্যায়ন গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং বিচারব্যবস্থার অংশ হিসেবেই ধর্ষকদের মনস্তাত্ত্বিক মূল্যায়ন ও থেরাপির ব্যবস্থা থাকা উচিত। এটি অপরাধীর পুনর্বাসনের ক্ষেত্রেও যেমন জরুরি, ভবিষতে এমন ঘটনা যাতে না ঘটে―তার জন্যও প্রয়োজন। CBT Therapy পদ্ধতি, যৌন-অপরাধের পুনরাবৃত্তি কমানোয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই নিয়মনীতিকে ভারতীয় সমাজের উপযোগী করে প্রয়োগ করা যেতে পারে।
৪। আইনি সংস্কার ও ভুক্তভোগী কেন্দ্রিক ন্যায়বিচার
নির্যাতিতার ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করার প্রশ্নে বৈবাহিক ধর্ষণকে অপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত ও সংবেদনশীল অবস্থান থেকে করতে হবে। একইসঙ্গে আইন-পুলিশ-প্রশাসনের কাজে যুক্ত সমস্ত মানুষকে যৌন-হিংসার ট্রমা প্রশমন করার পদ্ধতি নিয়ে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। লিঙ্গ সংবেদনশীলতা নিয়ে শিক্ষা দিতে হবে। বিচারকদের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে লিঙ্গ ও মনস্তত্ত্ব বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। যাতে তাঁরা ধর্ষণ সংক্রান্ত সামাজিক মিথ ও পক্ষপাতদুষ্ট মনোভাব থেকে বেরিয়ে এসে ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করতে পারেন।
৫। কমিউনিটি স্তরে মানসিক স্বাস্থ্য কর্মসূচি
গ্রামাঞ্চলে, আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায়, ঘরে ঘরে মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থাকে নিয়ে যেতে হবে। এর ফলে নির্যাতিতা ও সম্ভাব্য অপরাধী―দুজনের জন্যই নিরাপদ পরিসর তৈরি হবে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা ট্রমা, মানসিক চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা এবং যৌন নির্যাতন নিয়ে নীরবতা ভাঙার দিকগুলিকে প্রাধান্য দিতে হবে।
ধর্ষণ কেবলমাত্র একটি আইনি সমস্যা নয়। ধর্ষণ একটি মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক বাস্তবতা। যা লিঙ্গভিত্তিক ক্ষমতার অসমবন্টনের মধ্যে গভীরভাবে প্রোথিত। ফলে ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে ধর্ষণ মোকাবিলার জন্য প্রয়োজন একটি মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া। যার সঙ্গে সংস্কৃতি ও সমাজের নিবিড় যোগ থাকবে। কমিউনিটি স্তরে প্রক্রিয়াটিকে নিয়ে যেতে হবে। বিভিন্ন নারীবাদী ও ট্রমা-সেন্সিটিভ নীতির ওপর দাঁড়িয়ে এই প্রক্রিয়া গড়ে তোলা হবে। কারণ ঘটনাটি কেন ঘটল সেটা না জানলে, তার সমাধান কোনোমতেই বের করা যাবে না।
লেখক মনোসমাজকর্মী
তথ্যসূত্র:
Bandura, A. (1977). Social Learning Theory. Prentice Hall.
Brownmiller, S. (1975). Against Our Will: Men, Women and Rape. Simon & Schuster.
Singh, R., Sharma, P., & Gupta, M. (2020). Psychological profiles of sexual offenders in Indian prisons. Indian Journal of Psychiatry, 62(3), 235-242.
Verma, R. et al. (2013). Masculinity, Son Preference & Intimate Partner Violence in India. ICRW & UNFPA.
NCRB (2021). Crime in India Report. Ministry of Home Affairs.