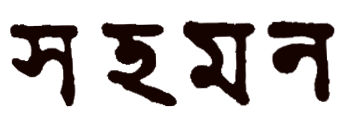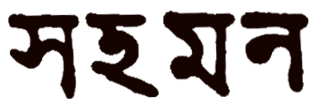অধ্যায় ১ - ফ্যাসিবাদ - দর্শন, আদর্শ ও অনুশীলন
অধ্যায় ২ - ফ্যাসিবাদী দর্শনের ভিত্তি
অধ্যায় ৩ - সুপারম্যানের উপাসনা
অধ্যায় ৪ - স্বস্তিকা চিহ্নের ছায়ায়
অধ্যায় ৫
জার্মানিতে ফ্যাসিবাদ “ন্যাশনাল সোশ্যালিজম” নামে এক প্রতারণাময় ও জনপ্রিয় নাম গ্রহণ করেছে। বাস্তবে তা সমাজবাদীও নয়, জাতীয়তাবাদীও নয়। রাজনৈতিকভাবে এ হল অবক্ষয়ী পর্যায়ের পুঁজিবাদী সমাজের শাসনব্যবস্থা। জার্মানিতে ফ্যাসিস্ট একনায়কত্ব ইতালির চেয়েও অধিক হিংস্রতা ও নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়েছে। কারণ, ইতালিতে ফ্যাসিবাদের বিজয়ের পর পুঁজিবাদ আরও ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়েছে। ফলত এই পতনশীল পুঁজিবাদের রক্ষকরা হতাশার দিগ্বিদিকশূন্য উন্মত্ততার দিকে ধাবিত হয়েছে।
ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র হল সংসদীয় গণতন্ত্রের মুখোশটা খুলে ফেলে বুর্জোয়া শ্রেণির খোলাখুলি একনায়কতন্ত্র চালানোর হাতিয়ার। এর একমাত্র কাজ হল, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ধ্বংসস্তূপের উপর উচ্চতর সভ্যতা গড়ে তোলার সংগ্রামে নিয়োজিত শ্রমিক শ্রেণিকে ও সংশ্লিষ্ট সামাজিক গোষ্ঠীগুলিকে নৃশংস ও রক্তাক্ত পথে দমন করা। ফ্যাসিবাদের ট্র্যাজেডি এটাই যে একটি আন্দোলন হিসাবে তা প্রধানত পুঁজিবাদী ব্যবস্থারই দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে নিয়ে গঠিত; এ এক বৈপরীত্য যে মুনাফালোলুপ পুঁজিবাদের শিকার যারা তারাই উন্মতত্তের মত তাদের নিজেদের ধ্বংসের কারণকেই বাঁচানোর অসাধ্য সাধনে লিপ্ত। এমন আন্দোলনে যে সত্যবাদিতা, সততা, আন্তরিকতা বা সাধারণ শালীনতারও কোনো স্থান থাকবে না তা খুবই স্বাভাবিক। অনিবার্যভাবে তা মিথ্যা, প্রতারণা ও ভণ্ডামির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। হিটলারের আত্মজীবনী “একটি এক লক্ষ চল্লিশ হাজার শব্দের বই যাতে এক লক্ষ ঊনচল্লিশ হাজার ভুল রয়েছে” বলে চিহ্নিত করেন লিওন ফয়েশটওয়াঙ্গার। এই মহান জার্মান লেখককে হিটলারের জার্মানি ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল, তাঁর রচনাগুলিকে “অ-জার্মান ধারণা” বলে দেগে দিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, ফ্যাসিবাদের প্রধান অস্ত্র হল বাগাড়ম্বর সর্বস্বতা।
যারা সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া, এবং সেই কারণে পুঁজিবাদী লুণ্ঠনের সবচেয়ে বড় শিকার, সেই শ্রেণির মানুষকে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে বাগাড়ম্বরপূর্ণ প্রতারণামূলক প্রচারের মাধ্যমে ফ্যাসিস্ট আন্দোলনে সংগঠিত করা হয়েছিল। ছদ্ম-সমাজবাদের পতাকাতলে তাদেরকে সংকটগ্রস্ত পুঁজিবাদের রক্ষাকারী ঝটিকা বাহিনী হিসাবে সাজানো হয়েছিল। এই অসম্ভব কাজটি সম্পাদন করা সম্ভব হয়েছিল কেবলমাত্র নির্লজ্জ মিথ্যা, নগ্ন প্রতারণা ও অতিরঞ্জিত জনমোহন বাগ্মিতার মাধ্যমে। পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে বলে দাবি করা এই আন্দোলন আসলে ছিল রাজনৈতিক, নাগরিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে—যেসব স্বাধীনতার ধারণা ঐতিহাসিকভাবে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সাথে যুক্ত। পুঁজিবাদ যখন একটি প্রগতিশীল সামাজিক শক্তি হিসাবে কাজ করছিল তখন এই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। ফ্যাসিবাদী আন্দোলন সংসদীয় গণতন্ত্রকে পুঁজিবাদের সমার্থক হিসাবে চিহ্নিত করেছিল এবং পুঁজিবাদী সমাজের সমস্ত অসঙ্গতির একমাত্র সমাধান হিসাবে এই সংসদীয় গণতন্ত্র ব্যবস্থার বিলোপের কথা বলা হয়েছিল। ফ্যাসিবাদ সংসদীয় গণতন্ত্রকে ধ্বংস করেছে, কিন্তু পুঁজিবাদ এখনও আগের চেয়ে বেশি শক্তিশালী হয়ে রয়েছে এবং শ্রমিক শ্রেণিকে আরও নিষ্ঠুরভাবে শোষণ করছে। বাস্তবিকই, এই উত্তাল বিপ্লবী সময়ে সংসদীয় গণতন্ত্রের বিলোপ পুঁজিবাদী আধিপত্য বজায় রাখার পক্ষে আরো অধিক গ্যারান্টি জোগায়।
সংসদীয় ব্যবস্থা দ্বারা প্রদত্ত আপেক্ষিক স্বাধীনতা শ্রমিক শ্রেণিকে সংগঠিত হতে এবং পুঁজিবাদ উৎখাতের ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে সক্ষম করে। তাই, বুর্জোয়াদের ক্ষমতা ও বিশেষাধিকার রক্ষার লড়াইয়ে বুর্জোয়া শ্রেণির প্রয়োজন হয়ে পড়ে নিজেদের অর্জনগুলিকেই বিলোপ করার। ফ্যাসিস্ট আন্দোলন সৃষ্টি করা হয় পুঁজিবাদের এই নোংরা কাজটি সম্পন্ন করার জন্য। বুর্জোয়া দার্শনিকরা এই আন্দোলনের আদর্শিক ভিত্তি স্থাপন করে। প্রাথমিকভাবে যাদের বিরুদ্ধে এরা গালিগালাজ করে, সেই লগ্নিপুঁজিপতি ও শিল্পপতিরাই এই মতবাদকে উদার হস্তে আর্থিক সহায়তা দেয়। যে আন্দোলন প্রকাশ্যে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার ডাক দেয় সেই আন্দোলনকে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র শুধু যে সহ্য করে নেয় তাই নয়, আসলে গোপনে সবরকম সাহায্য করে। বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পুলিশ ও সামরিক বাহিনী সরকার উৎখাতের জন্য গোপনে ফ্যাসিস্ট আন্দোলনের সাথে জোট বাঁধে। কৌশলী জনপ্রিয় বক্তৃতা, সস্তা ভাবাবেগ, অতি-উচ্চাভিলাষী প্রতিশ্রুতি (যেগুলি রক্ষা করার আদতে কোনো ইচ্ছা নেই), প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নীতিহীন অপপ্রচার, জাতীয় উন্মাদনা সৃষ্টি, বর্ণবিদ্বেষ উসকে দেওয়া—এইসব ও অন্যান্য নানা পদ্ধতি ব্যবহার করে অর্থনৈতিকভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে দেউলিয়া হয়ে যাওয়া নিম্ন মধ্যবিত্ত জনগণকে সম্মোহিত করা হয়। জনগণকে জনগণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। ফ্যাসিস্ট একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় ইতালির মতো নাটকীয় অভ্যুত্থানের মাধ্যমে অথবা জার্মানির মতো “সাংবিধানিক” ও “রক্তপাতহীন” উপায়ে।
ব্যাংকার ও শিল্পপতিরা—যারা ধ্বংসপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র-বুর্জোয়া জনগণকে জাতীয়তাবাদী উন্মাদনায় ফুটিয়ে তোলার জন্য আন্দোলনকে অর্থায়ন করেছিল—তারা কিন্তু জার্মানির পরাজয় ও অপমান থেকে বিপুল মুনাফা অর্জন করেছিল। ১৯২৩-২৪ সালের মুদ্রাস্ফীতির মহোল্লাসে প্ররোচিত করে তারা রিপাব্লিক গভমেন্টকে বাধ্য করেছিল যুদ্ধকালীন সময়ের বিশেষ অভ্যন্তরীণ ঋণের বোঝা মুছে ফেলতে। এই “দেশপ্রেম” ক্ষুদ্র-বুর্জোয়াদের সম্পূর্ণ দেউলিয়া হওয়ার দিকে ঠেলে দেয়। যদি এই অভ্যন্তরীণ ঋণ এতটা প্রতারণামূলকভাবে লোপ করা না হতো, তাহলে এর সুবিধাভোগীদের উচ্চ আয়ের উপর সরকারকে ভারী কর চাপাতে হতো। যুদ্ধ-মুনাফা-ভোগীদের ন্যায্য কর থেকে মুক্তি দিতে, সরকার মধ্যবিত্ত শ্রেণির কষ্টার্জিত সঞ্চয়—যা তারা যুদ্ধবন্ডে “দেশপ্রেমের কর্তব্য” হিসাবে বিনিয়োগ করেছিল—জবরদস্তি বাজেয়াপ্ত করে। এই বাজেয়াপ্তকরণ তাদের ধ্বংস করে দেয় এবং ন্যাশনাল-সোশ্যালিস্ট আন্দোলনের সামাজিক ভিত্তি স্থাপন করে। শেষ পর্যন্ত, ধ্বংসপ্রাপ্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণির সন্তানেরা স্বস্তিক চিহ্নের রহস্যময় বাদামি শার্ট পরিধান করে সেই সব লোকেদের সেবায় নিয়োজিত হয় যারা তাদের শ্রেণিকে লুন্ঠন ও বঞ্চিত করে সর্বস্বান্ত করেছিল।
যুদ্ধলব্ধ মুনাফায় আরো মোটাতাজা হয়ে ওঠা পুঁজিপতিরা প্রজাতান্ত্রিক সরকারের সাহায্য ও ষড়যন্ত্রে কর ফাঁকি দিয়েছিল, ফলে ভার্সাই চুক্তির সমস্ত অর্থনৈতিক বোঝা চাপানো হয় উৎপাদনশীল জনগণের উপর। এর ফলাফল ছিল জনসংখ্যার বৃহৎ অংশের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য, এবং অন্যদিকে একটি ক্ষুদ্র ধনী স্তরের আরও সম্পদশালী হয়ে ওঠা। দরিদ্রায়নের কারণে জনগণের কর দেওয়ার ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছিল। রাষ্ট্রীয় লগ্নি সম্পূর্ণভাবে ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে। বছরের পর বছর জার্মান সরকার দেউলিয়া অবস্থায় ছিল। সামাজিক সেবা ও অবসরপ্রাপ্ত/প্রতিবন্ধী সৈন্যদের পেনশন বাজেট কেটে রাষ্ট্রের চলতি ব্যয় হ্রাস করা সম্ভব হয়। কিন্তু যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ছিল। বিজয়ী শক্তিবর্গের দাবি মেটানোর একমাত্র উপায় ছিল যুদ্ধ থেকে মুনাফা লুটেছে যারা, যারা নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে বঞ্চিত করে পরাজয়ের দায় এড়াচ্ছে, সেইসব ধনীদের পকেটে হাত দেওয়া। এই পরিস্থিতিতে, অর্থবানদের দ্বারা অর্থায়িত হয়ে, ন্যাশনাল-সোশ্যালিস্ট আন্দোলনের রণধ্বণী “ভার্সাই চুক্তি জার্মানিকে ধ্বংস করছে” জনপ্রিয় হওয়া অনিবার্য ছিল। প্রজাতান্ত্রিক সরকার সেই চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল এবং এর দাবিগুলো পূরণ করার চেষ্টা করছিল; তাই, সেই সরকার হয়ে গেল জার্মান জনগণের শত্রু। সেই সরকারকে উৎখাত করতে হবে। “জাতীয় বিপ্লব” শুরু হয়েছিল এই প্রতিবিপ্লব দিয়ে।
শ্রমিক শ্রেণি এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির অর্থনৈতিক ধ্বংস জার্মানিতে এক তীব্র বিপ্লবী পরিস্থিতি তৈরি করেছিল। জনগণ আর কোনো বোঝা সহ্য করতে প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু উচ্চবিত্ত শ্রেণিও তাদের অবৈধ সম্পদের কোনো অংশ ছাড়তে রাজি ছিল না। জার্মানি আটকে পড়েছিল অভ্যন্তরীণ বিপ্লবের ভূত এবং বিদেশি সামরিক হস্তক্ষেপের হুমকির মধ্যে। শাসক শ্রেণি ন্যাশনাল-সোশ্যালিস্ট আন্দোলন তৈরি করেছিল এই উভয় বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার গ্যারান্টি হিসাবে। সমাজতন্ত্রের নামে প্রতারণামূলক বুলি শ্রমিক শ্রেণির পিছিয়ে পড়া অংশকে ধোঁকা দেবে; অন্যদিকে, উগ্র জাতীয়তাবাদের জিগির ভার্সাই চুক্তি বাস্তবায়নের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলবে।
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ধ্বংস করার পর, “জাতীয় বিপ্লব” পুঁজিবাদের কোনো ক্ষতি করেনি—ক্ষমতায় আসার আগে যা ন্যাশনাল-সোশ্যালিস্টদের অন্যতম ঘোষিত লক্ষ্য ছিল। নাৎসি রাষ্ট্রের প্রথম কাজ ছিল শ্রমিক শ্রেণির দলগুলিকে দমন করা, যার মাধ্যমে বিপ্লবের ঝুঁকি থেকে রক্ষা পাওয়ার সাময়িক গ্যারান্টি তৈরি হয়েছিল। এটা করার পর, নির্লজ্জভাবে উগ্র জাতীয়তাবাদী জিগিরের পথে এগিয়েছিল ওরা—জার্মান জনগণের কল্যাণে নয়, বরং শিল্পপতিদেরকে ভার্সাই চুক্তির বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত করতে। যদি বিজয়ী শক্তিবর্গ ক্ষতিপূরণ আদায় করতে চায় তবে তা শুধুমাত্র সেইসব লোকের কাছ থেকেই আসতে পারত যারা তা প্রদান করতে সক্ষম। জার্মান জনগণকে তো শুষে নেওয়া হয়েছিল শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত। “ভার্সাইয়ের ডিকটেট”—যদি মিত্রশক্তি তাদের দাবি চাপিয়ে দিতে চায়—তা থেকে মুক্তি সম্ভব ছিল কেবল সামরিক প্রতিরোধের ভান করার মাধ্যমে। একে নিদারুন পাগলামি মনে হলেও তা কিন্তু সফল হয়েছিল, কারণ মিত্রশক্তি অভিজ্ঞতা থেকে শিখেছিল যে সামরিক হস্তক্ষেপ লাভজনক নয়। এবং আর যাই হোক না কেন, জার্মানিতে বিপ্লবের ভূতকে তারাও ভয় পেত। ফলস্বরূপ, নাৎসি উগ্রতাবাদ বেলাগাম ছাড় পেয়েছিল। পুঁজিপতিদের কোনো ক্ষতি করার বদলে, ন্যাশনাল-সোশ্যালিস্ট আন্দোলনের উগ্রতাবাদ আসলে তাদের অর্থনৈতিক সংকট থেকে উদ্ধার করেছিল। জাতীয় সম্মান পুনরুদ্ধারের জন্য পুনরায় সশস্ত্রীকরণের কর্মসূচি মানে শিল্পের উন্নতি, যার মুনাফা গিয়েছিল পুঁজিপতিদের পকেটে। শূন্য কোষাগার নিয়ে, অলৌকিকত্বের বিশ্বগুরুও পুনরায় সশস্ত্রীকরণের দেনা পরিশোধ করতে পারত না। শিল্পপতি ও অর্থলগ্নিকারীরা তাদের নতুন সরকারকে অস্ত্র ও গোলাবারুদের অর্ডারের জন্য ঋণ দিয়েছিল। এভাবে ন্যাশনাল-সোশ্যালিস্ট রাষ্ট্র তাদের কাছে নিজেকে বন্ধক দিয়ে দেয়। এই পরিস্থিতিতে সমাজতন্ত্রের কোনো আলোচনা স্বভাবতই অনুমোদিত ছিল না। হিটলারবাদ তার প্রাথমিক দিনগুলির ছদ্ম-সমাজবাদী ভাবমূর্তি ঝেড়ে ফেলেছিল, অন্যদিকে তার জাতীয়তাবাদ হয়ে উঠেছিল নতুন জার্মান সাম্রাজ্যবাদের হাতিয়ার।
‘ন্যাশনাল সোশ্যালিজম’ বা ‘জাতীয় সমাজতন্ত্র’ নামটাই ভুল, নামটার মধ্যেই আছে শব্দগত বিরোধাভাস। সমাজতন্ত্রের কোনো সীমানা নেই। সমাজতন্ত্র জাতীয়তাবাদের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। ফ্যাসিস্টদের উগ্র, সাম্রাজ্যবাদী জাতীয়তাবাদের সাথে সমাজতন্ত্রকে জুড়ে দেওয়া তো আরওই অস্বাভাবিক। সমাজতন্ত্র ও শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলনের তীব্র বিরোধিতার প্রকৃত বাস্তবতার উপর এক প্রতারণামূলক আবরণ হল ন্যাশনাল সোশ্যালিজম। মার্ক্সবাদ ধ্বংস করাই ফ্যাসিস্ট আন্দোলনের ঘোষিত লক্ষ্য। আজ সাধারণভাবে স্বীকৃত যে, কার্ল মার্ক্স দ্বারা প্রণীত দার্শনিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক নীতির ভিত্তি ছাড়া কোনো সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন—অর্থাৎ পুঁজিবাদী শোষণ থেকে সমাজকে মুক্ত করার আন্দোলন—গড়ে উঠতে পারে না। “নিঃসন্দেহে, মার্ক্সের সমাজবাদ ছাড়া আর কোনো সমাজবাদ নেই যা আমাদের সময়ের রাষ্ট্রনায়কেরা হিসেবে আনতে পারেন”। শুধুমাত্র হ্যারল্ড লাস্কির মতো উদারপন্থী অধ্যাপকরাই এই মত পোষণ করেন এমন নয়, রক্ষণশীল কর্তৃপক্ষও এটি স্পষ্টভাবে স্বীকার করে। উদাহরণস্বরূপ, জার্মান সমাজবিজ্ঞানের প্রখ্যাত অধ্যাপক মুলার-লায়ার লিখেছেন: “মার্ক্সের অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদের তত্ত্ব সমাজবিজ্ঞানের একটি স্বতঃসিদ্ধে পরিণত হয়েছে”। এ থেকে স্পষ্ট যে, স্বল্প মাত্রার সামাজিক সংস্কার থেকেও কত দূরে এবং সামাজিক প্রগতির কতটা বিরোধী এক আন্দোলন এই ফ্যাসিবাদ, যা মার্ক্সবাদকে তার প্রধান শত্রু হিসেবে ঘোষণা করে।
মার্ক্সবাদের প্রতি ফ্যাসিবাদের এই উন্মত্ত ঘৃণাই তার সোশ্যালিজম-এর দাবিকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট। ক্ষমতায় আসার আগেই, ফ্যাসিবাদের প্রধান কাজ ছিল সব ধরনের হিংসার মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণিকে সন্ত্রস্ত করা, এবং এর সমস্ত সন্ত্রাসী কার্যক্রমে অর্থজোগান দিয়েছিল ঠিক সেই লোকেরা যারা সমাজবাদকে সবচেয়ে বেশি ভয় পায়। ক্ষমতায় এসে, ফ্যাসিবাদের প্রথম ও প্রধান কাজ ছিল শুধুমাত্র কমিউনিস্ট দলগুলিকেই নয়, বরং বিপ্লব-বিরোধী সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক দলগুলিকেও, এমনকি সংস্কারবাদী ট্রেড ইউনিয়নগুলিকেও রক্তাক্ত দমন করা। এর কঠোর নিষ্ঠুর থাবা নৃশংসভাবে নেমে এসেছিল উদারপন্থী বুদ্ধিজীবীদের উপরও, যারা শ্রমিক শ্রেণিকে সমর্থন ও সহানুভূতি দেখাত।
ন্যাশনাল–সোশ্যালিস্ট কর্মসূচির অন্যতম জাঁকজমকপূর্ণ ভণ্ডামি হল পুঁজিবাদকে নির্লজ্জ আধ্যাত্মিক রূপ দান। দরিদ্র নিম্ন মধ্যবিত্ত ও পিছিয়ে পড়া শ্রমিকদের কল্পনা জগতকে কব্জায় রাখতে নাৎসি আন্দোলন পুঁজিবাদ-বিরোধী জনপ্রিয় বুলি আওড়াত। পুঁজিবাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সকল শত্রুকে দমন করার পর নাৎসিরা “জাতীয় বিপ্লবের সমাপ্তি” ঘোষণা করে।
পুঁজিবাদের বিশেষাধিকারে সামান্যতম হস্তক্ষেপ করা চলবে না, আর তার রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রযুক্ত হবে নাৎসি একনায়কত্বের মাধ্যমে। ধোঁকা খাওয়া জনতার প্রতি এই নগ্ন বিশ্বাসঘাতকতাকে ঢাকতে ফ্যাসিস্ট তাত্ত্বিকরা পুঁজিবাদের দুটি বিভাগ উদ্ভাবন করে: “শোষণমূলক” ও “গঠনমূলক”। প্রথমটিকে দমন করা হবে, দ্বিতীয়টিকে রক্ষা ও উৎসাহিত করা হবে। এটা ছিল অর্থনৈতিক তত্ত্বের চরমতম জালিয়াতি। অর্থনীতির প্রাথমিক জ্ঞানই প্রমাণ করে যে শোষণ ছাড়া পুঁজিবাদ সম্ভব নয়। পুঁজিবাদের “গঠনমূলক” সাফল্য দাঁড়িয়ে আছে শ্রমিক শ্রেণিকে তাদের শ্রমের মূল্যের একটি অংশ থেকে বঞ্চিত করার উপর। আধ্যাত্মিক ‘রাইখ অব ন্যাশনাল সোশ্যালিজম’-এ পুঁজিবাদ ফুলে-ফেঁপে উঠুক—এই লক্ষ্যে অর্থনৈতিক তত্ত্বের নিজস্ব অবস্থানকেই বিকিয়ে দেওয়া হয়। ক্রুপ ফন বোলেন (তার বিশাল অস্ত্র কারখানা নিয়ে), থিসেন (লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের সাম্রাজ্য নিয়ে), ভোগলার (কয়লার রাজত্ব নিয়ে)—এদের মতো পুঁজিবাদী শোষণের হোতাদের “গঠনমূলক পুঁজি” হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়, এবং এভাবে তাদেরকে ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রের স্তম্ভ বলে গণ্য করা হয়। বাস্তবে, বৃহৎ শিল্প ও অর্থনৈতিক স্বার্থসমূহকে এই সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের বাইরে রাখা হয়েছে—যে অক্টোপাস তার রক্তাক্ত শুঁড় জার্মানির জাতীয় জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে প্রসারিত করেছে। ক্রুপ ফন বোলেনের সভাপতিত্বে গঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (বৃহৎ শিল্পপতিদের নিয়ে) একটি সুপার-স্টেট হিসাবে কাজ করে।
এই অভিনব “সমাজবাদ”-এর অধীনে, “স্বাধীনতা অপ্রয়োজনীয় এবং নাগরিকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কোনও অপরিহার্য অধিকার নয়”—আধুনিক কালে ‘দাস স্পেক জরাথুস্ট্র—হিটলার’। নাৎসি (ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট) দল জার্মান বুর্জোয়াদের একমাত্র দলে পরিণত হয়েছে, এবং নাৎসি রাষ্ট্র জার্মান পুঁজিবাদের বিশ্বস্ত তত্ত্বাবধায়ক। হিটলারের ক্ষমতায় আসার অল্পকাল পরেই, জার্মান পিপলস পার্টি (যে দল প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ভারী শিল্পের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করত) স্বেচ্ছায় বিলুপ্ত হয় এবং তার সদস্যদের নাৎসি পার্টিতে যোগ দিতে উপদেশ দেয়। এমনকি রাজতন্ত্রবাদীরাও “ন্যাশনাল সোশ্যালিজম”-কে তাদের প্রতিক্রিয়াশীল আদর্শের সমতুল্য মনে করে। তারা তাদের শক্তিশালী আধা-সামরিক সংগঠন ‘স্টিল হেলমেট’-কে নাৎসি ঝটিকা বাহিনীতে বিলীনন করে দেয়।
১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে, হিটলারের ট্যাঁকে গোঁজা পার্লামেন্ট ফ্রেডরিক দ্য গ্রেট-এর সমাধিক্ষেত্রে সমবেত হয়ে বাকসর্বস্বতার আবরণটাও ছুঁড়ে ফেলে প্রজাতন্ত্রকে কবর দিল এবং মরে ভুত হয়ে যাওয়া প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ততান্ত্রিক সামরিকবাদকে পুনরুত্থিত করল। পটসডামের রাজতন্ত্রবাদী পরিবেশে, প্রতিক্রিয়ার জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনে নিমজ্জিত হিটলার তার শিকারদের—দেউলিয়া মধ্যবিত্ত ও পিছিয়ে পড়া শ্রমিকদের—বিস্মৃত হলেন। একনায়কতান্ত্রিক ক্ষমতা চাওয়ার জন্য নাৎসি সংসদে দেওয়া ভাষণে তিনি হোহেনজোলার্ন রাজবংশের গুণকীর্তনে মাতোয়ারা হলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত রাজবংশের অধঃপতিত প্রতিনিধিরা বুঝতে পারল যে তারা বৃথাই স্বস্তিকা চিহ্নটা ধারণ করেননি। হিটলার “জার্মান জনগণের ত্রাণকর্তা” হিসাবে একনায়কত্বের ক্ষমতা গ্রহণ করলেন না, বরং সেই সকল শক্তির একনায়কত্বের হাতিয়ার হিসাবে ক্ষমতা গ্রহণ করলেন যারা শতকের পর শতক জুড়ে জনগণকে নির্মম শোষণ ও নিপীড়ন করে এসেছে।
অন্যদিকে, কমিউনিস্ট পার্টিকে নৃশংসভাবে দমন এবং নিরীহ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টিকেও ভেঙে দেওয়ার পর, নাৎসিরা সংস্কারবাদী ট্রেড ইউনিয়নগুলিকেও রেহাই দেয়নি। সেগুলোও ধ্বংস করা হয়, তাদের নেতাদের গ্রেফতার করা হয়, তাদের তহবিল বাজেয়াপ্ত করা হয়। কার্যত, শ্রম আন্দোলনের সকল নেতা ও সক্রিয় কর্মী—যারা সময়মতো দেশ ছাড়তে পারেননি—বিনা বিচারে, এমনকি আনুষ্ঠানিক অভিযোগ ছাড়াই কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। অনেককে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়, প্রায় সকলকেই কারাগারে অমানবিক নির্যাতন করা হয়। শ্রমিক শ্রেণির উপর এই বর্বর আক্রমণের পর একটি সরকারি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়: “ন্যাশনাল-সোশ্যালিস্ট সরকারের তিন মাস প্রমাণ করেছে, হিটলার তোমাদের বন্ধু, হিটলার তোমাদের স্বাধীনতার সমস্যা নিয়ে ভাবেন, হিটলার তোমাদের কাজ ও খাদ্য দেবেন”।
জার্মানিতে ধোঁকা খাওয়া বিভ্রান্ত জনতাকে ফ্যাসিবাদ যখন মনমোহন প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিল, অন্যদিকে ইতালিতে তখন ক্ষমতা দখলের বারো বছর অতিক্রান্ত করে ফ্যাসিস্টরা সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাষা বলছিল। ১৯৩৪ সালের শেষে, ফ্যাসিস্ট পার্টির মহাসচিব আকিলে স্টারাচে বেকার শ্রমিকদের এক সমাবেশে ঘোষণা করলেন: “মনে রাখো, ফ্যাসিবাদ তোমাদের সম্মান, চাকরি বা মুনাফার প্রতিশ্রুতি দেয় না—কেবলমাত্র কর্তব্য ও সংগ্রামের কথা বলে”। এর কয়েক ঘণ্টা আগেই, ডিউচে মহাশয় (মুসোলিনি) মিলানে আরেকটি শ্রমিক সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন। সেখানে তিনি ফ্যাসিস্ট অর্থনীতির “আদর্শবাদ” ব্যাখ্যা করেন: “যে অর্থনীতি কেবল ব্যক্তিগত লাভ নিয়ে ব্যস্ত ছিল তা প্রতিস্থাপিত হচ্ছে এমন একটি অর্থনীতি দ্বারা যার প্রধান লক্ষ্য সমষ্টির স্বার্থ রক্ষা করা। উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে শ্রমিকদের আরও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হতে হবে, এর শৃঙ্খলায় অংশ নিতে হবে। গত শতাব্দী যদি পুঁজিবাদের ক্ষমতার শতাব্দী হয়ে থাকে, তাহলে বর্তমান শতাব্দী হল শ্রমের ক্ষমতা ও গৌরবের শতাব্দী”। যে ব্যবস্থার মুখপাত্ররা একই দিনে দুই বিপরীত বার্তা দেয় সেই ব্যবস্থার একমাত্র নীতি হতে পারে অসততা ও নির্মমতা। শ্রমিকের সকল মুক্ত স্বাধীন সংগঠনকে নিষ্ঠুরভাবে ধ্বংস করে, ধর্মঘটের অধিকার লুপ্ত করে, “জাতীয় প্রয়োজন”-এর অজুহাতে মজুরি কেটে নিয়ে, মুসোলিনি শ্রমের “ক্ষমতা ও গৌরব”-এর ডম্ফই করছিল!
বড় পুঁজিপতিদের সমর্থনে ক্ষমতায় আসা মুসোলিনি - যারা কমিউনিজম ও শ্রমিক আন্দোলনের ভয়ে আতঙ্কিত ছিল - কখনোই শ্রমিকদের কল্যাণের দাবিতে সৎ ছিল না। ফ্যাসিস্ট পার্টির প্রাথমিক কর্মসূচি ছিল শ্রমিক সংগঠন ও জাতীয়তাবাদের এক অদ্ভুত মিশ্রণ। কিন্তু অচিরেই তা বিপ্লবী জোয়ারের বিরুদ্ধে পুঁজিবাদের রক্ষাকবচে পরিণত হয়। “জাতীয় সংহতি”-র নামে ছদ্ম-বামপন্থা থেকে চরম ডানপন্থায় ঝাঁপ দেওয়া হয়। মুসোলিনির কালো শার্টধারী বাহিনী মূলত মধ্যবিত্ত শ্রেণির গুন্ডাদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল, যাদের অর্থ ও অস্ত্র সরবরাহ করেছিল বড় শিল্পপতিরা। ক্ষমতায় আসার আগেই এই ভাড়াটে বাহিনীকে লেলিয়ে দেওয়া হয় সমাজতন্ত্রী ও ট্রেড ইউনিয়নগুলোর বিরুদ্ধে। ক্ষমতা দখলের পর শ্রমিক সংগঠনগুলোর অফিসে হামলা চালানো হয় এবং শ্রমিক আন্দোলনের প্রায় বিশ হাজার নেতাকর্মীকে হয় হত্যা না হয় কারাগারে নিক্ষেপ অথবা দেশছাড়া করা হয়।
ইতালিতে ফ্যাসিস্ট শাসনের দীর্ঘ পনেরো বছর পর শ্রমিকদের প্রকৃত অবস্থার চিত্র ফুটে উঠেছে একজন ফ্যাসিস্ট অর্থনীতিবিদের গবেষণায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইতালীর শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি অর্ধেকে নেমে যায়। ১৯১৯-২১ সালে যুদ্ধপূর্ব মজুরি স্তর ফিরে এসেছিল, যা ছিল শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবী কার্যকলাপের ফল, যার বিরুদ্ধে পুঁজিবাদের খুনি হাতিয়ার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল ফ্যাসিবাদ। কিন্তু এখন প্রকৃত মজুরি আবার যুদ্ধকালীন স্তরের কাছাকাছি নেমে গেছে (ড. পাওলা আরকারির “মজুরি ও জীবনযাত্রার ব্যয়”)। শ্রমিকদের এই বাড়তি শোষণের বিপরীতে ফ্যাসিবাদ ধনীদের করের বোঝা ক্রমাগত কমিয়ে দিয়েছে। উত্তরাধিকার কর ব্যাপকভাবে হ্রাস করা হয়েছে, অন্যদিকে পরোক্ষ করের পরিধি বাড়ানো হয়েছে। রাষ্ট্রীয় আয়ের ষাট শতাংশেরও বেশি আদায় করা হয় এমন করের মাধ্যমে যা শ্রমজীবী জনগণের উপর বর্তায়।
ফ্যাসিস্ট সরকার বড় জমিদারদের প্রতিও কম বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করেনি। ক্যাথলিক পপুলার পার্টিকে হিংসাত্মকভাবে দমন করেছিল, যে দলটি দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে জমি পুনর্বণ্টনের পক্ষে ছিল। আজও কৃষি জমির প্রায় চল্লিশ শতাংশ মাত্র শূন্য দশমিক পাঁচ শতাংশ কৃষি জনগোষ্ঠীর মালিকানাধীন। বাকি জমি প্রায় পাঁচ মিলিয়ন পরিবারের মধ্যে বণ্টিত, যার মধ্যে দুই মিলিয়ন ভাড়াটে। একটি কৃষক পরিবারের গড় জমির পরিমাণ দুই একরের সামান্য বেশি। কৃষির মোট উৎপাদনের এক তৃতীয়াংশেরও বেশি জমিদাররা ভাড়া হিসেবে নিয়ে নেয়। এর চেয়েও বড় অংশ রাষ্ট্র প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর হিসেবে নিয়ে যায়।
জার্মানিতে ফ্যাসিবাদ “জাতীয় সমাজতন্ত্র” নামক ভুয়া পতাকার নিচে পরিচালিত হলেও এর রেকর্ড মোটেই কম অন্ধকারময় নয়। আত্মনির্ভরতার চরম জাতীয়তাবাদী নীতি জীবনযাত্রার ব্যয় ক্রমাগত বাড়িয়ে তুলেছে। অন্যদিকে, কৃত্রিমভাবে রপ্তানি বাণিজ্য প্রসারিত করতে উৎপাদন খরচ কমানোর জন্য মজুরি কাটা হয়েছে। বেকারত্ব সমস্যার প্রচারিত সমাধান ছিল মজুরিকে অত্যন্ত নিম্ন স্তরে নামিয়ে আনা এবং বেকার শ্রমিকদের কুখ্যাত শ্রম শিবিরগুলিতে জোরপূর্বক পাঠানো, যেখানে তারা কার্যত বিনা মজুরিতে কাজ করত। “জার্মান জনগণ কম মজুরি, পার্ট-টাইম চাকরি ও উচ্চ জীবনযাত্রার বোঝা নিয়ে হাঁসফাঁস করছে; এবং নাৎসি শ্রমিক ফ্রন্ট, যা শ্রেণী সংগ্রাম বিলোপ করে নিয়োগকর্তা ও শ্রমিকদের বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতায় একত্রিত করবে বলে দাবি করেছিল, তা দ্রুত ভেঙে পড়ছে বলে জানা গেছে”।(“দ্য নিউ স্টেটসম্যান অ্যান্ড নেশন”, লন্ডন, ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪)। এই লেখাটির পর, শ্রমিক ফ্রন্টের পতন রোধ করা হয়েছে এই ফ্রন্টকে শ্রমিকদের জন্য এক প্রকার দাসত্ব ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করে। জাতীয় স্বার্থে এই শ্রেণী সহযোগিতার ব্যবস্থায় শ্রমিকদের প্রাপ্ত ভাগ হলো শৃঙ্খলা ও আত্মত্যাগ।
এমন পরিস্থিতির মধ্যেই জাতীয় সমাজতন্ত্রী দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপিত হয়েছিল। স্থানীয় দলীয় নেতৃত্বের সমাবেশের সামনে, যারা কি না “বিপ্লবের” প্রকৃত বিজয়ী বীর, নেতা মহাশয় ঘোষণা করেছিলেন যে, “ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট রেভল্যুশন জার্মানির সামাজিক কাঠামো আগামী হাজার বছরের জন্য স্থির নির্ধারিত করে দিয়েছে”। সুতরাং, জনগণের অবস্থাকে আমূল পুনর্বিন্যাসের উত্তরণশীল প্রক্রিয়া হিসেবে নয়, বরং অন্তত হাজার বছর ধরে স্থায়ী রূপে থাকার বিষয় হিসেবে ঘোষণা করা হল। হিটলার আরও উপদেশ দিয়েছিলেন যে, “জনগণকে বিপ্লবের কাছ থেকে খুব বেশি কিছু না চাইতে শিখতে হবে এবং সম্ভব ও অসম্ভবের মধ্যে পার্থক্য করতে হবে”। এই আশ্চর্যজনক ঘোষণাগুলোর উদ্দেশ্য ছিল নাৎসি কর্মসূচির ছদ্ম-সমাজতান্ত্রিক অংশে লালিত “দ্বিতীয় বিপ্লব”-এর ধারণাকে চিরতরে বিসর্জন দেওয়া। “ফ্যাসিবাদের সম্ভাব্য ও প্রকৃত অর্জন হলো কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প, চাবুক, স্বাধীনতা ধ্বংস, জনমননের অবনতি, কুচকাওয়াজ, সেনাবাহিনী ও বর্বরতায় প্রত্যাবর্তন”।(প্রাগুক্ত)
হিটলার তার নিজস্ব কর্মসূচির ছদ্ম-সমাজতান্ত্রিক দিকগুলোও প্রকাশ্যে প্রত্যাখ্যান করায় উৎসাহিত হয়ে তৎকালীন তৃতীয় রাইখের অর্থনৈতিক একনায়ক ডক্টর শাখট জাতীয় সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক তত্ত্বগুলোর বিরুদ্ধে ব্যাপক আক্রমণ চালান। তিনি “অর্থনৈতিক তত্ত্বায়ন”-এর তীব্র নিন্দা করেন এবং বলেন যে “আমরা অতীতে অর্জিত অভিজ্ঞতাগুলোকে প্রতিক্রিয়াশীল হিসেবে খারিজ করতে পারি না”। পুঁজিবাদই জাতীয় সমাজতান্ত্রিক জার্মানির অর্থনৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করবে। অতীত অভিজ্ঞতার একজন রক্ষক হিসেবে ড. শাখট যুক্তি দেন যে “আমাদের সময়ে তাত্ত্বিক অর্থনৈতিক কাঠামো তৈরি করা সঙ্গত নয়। জাতীয় সমাজতন্ত্র শুধু কর্মকে স্বীকৃতি দেয়, পরিকল্পনাকে নয়। আমরা অস্পষ্ট ভাসা ভাসা তত্ত্ব দ্বারা পরিচালিত হতে দেব না”। নাৎসি পার্টির অর্থনৈতিক তাত্ত্বিক গটফ্রিড ফেডার সেই সময় একটি নিবন্ধ লিখেছিলেন যেখানে তিনি দলের কর্মসূচির অর্থনৈতিক ধারাগুলো পুনর্ব্যক্ত করেছিলেন। ক্ষমতায় আসার আগে দলের একটি মৌলিক অর্থনৈতিক দাবি ছিল “সুদ-দাসত্বের বিলোপ”। ফেডার নির্বোধভাবে সেই দাবিটি স্মরণ করিয়ে দেন এবং ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট সরকারকে ব্যাংক ডিসকাউন্ট হার কমানো এবং ব্যাংকের বন্ধক সুদের সাধারণ হ্রাসের নির্দেশ দেওয়ার আহ্বান জানান। তিনি ঘোষণা করেন: “জার্মান অর্থনীতি উচ্চ অর্থলগ্নিকারীদের দ্বারা আরও বেশি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, যারা মধ্যশ্রেণীর ব্যবসায়ী ও কারিগরদের সুদ-দাসত্বের অবস্থায় রেখেছে, কারণ বর্তমান অবস্থায় তাদের অসহায় প্রচেষ্টা আরও বেশি ঘনীভূত হয় সুদ পরিষোধের বাধ্যবাধকতায়”। ছদ্ম-সমাজতন্ত্রের এই দুর্বল কণ্ঠস্বরেই ড. শাখটের ব্যাপক প্রতিআক্রমণ শানিয়ে উঠেছিল। উচ্চ অর্থলগ্নিকারীদের অনুগ্রহে ক্ষমতায় বসা হিটলারকে আর মধ্যশ্রেণীর ব্যবসায়ী ও কারিগরদের দুঃখ-দুর্দশাযর কথা শুনিয়ে উদ্বিগ্ন করা সম্ভব ছিল না।
জাতীয় সমাজতন্ত্রী অর্থনীতির মৌলিক মতবাদ এটাই ছিল যে, “সুদ-দাসত্ব” হলো সমস্ত অকল্যাণের মূল, জার্মান জনগণ এই রোগে ভুগছে। নাৎসি সামাজিক কর্মসূচির কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল সুদ পরিশোধের বাধ্যবাধকতা বিলোপ ও ঋণের উপর রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ। এই তত্ত্বের জনক ছিলেন গটফ্রিড ফেডার, যিনি হিটলারকে “জাতীয় বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যা কিছু শিখেছি” (“হিটলারের আত্মজীবনী”) তা শিখিয়েছিলেন। কিন্তু ক্ষমতায় আসার অল্প সময়ের মধ্যেই হিটলার তার অর্থনৈতিক গুরুকে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সব পদ থেকে সরিয়ে দেন। উচ্চ অর্থলগ্নিকারীদের মুখপাত্র ড. শাখট অর্থনৈতিক একনায়ক হয়ে ওঠেন। ১৯৩৪ সালের শেষ নাগাদ, সুদ-দাসত্বের এক বেদনাহীন উপশম আবিষ্কৃত হয়েছিল। প্রেস্ক্রিপশনটি দিয়েছিলেন এক নতুন ওঝা কোলার, যিনি দলের অর্থনৈতিক কমিশনের প্রধান হয়েছিলেন। সহজ প্রেস্ক্রিপশন: “তোমাদের ঋণ শোধ করো, নতুন ঋণ নিও না। ঋণ না থাকলে সুদ-দাসত্বও থাকবে না”। রিচার্ড ডারে ছিলেন জাতীয় সমাজতন্ত্রের শেষ মোহিকানদের একজন। হিটলারের ক্ষমতায় আসার দুই বছর পরও ডারে দলের কৃষকদের দেওয়া প্রতিশ্রুতির কথা, অর্থাৎ জমি বণ্টন, মনে রেখেছিলেন। এ ছিল ন্যাশনাল-সোশ্যালিস্ট রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এক গুরুতর অপরাধ। কিন্তু ড্যারেকে কৃষিমন্ত্রীর পদ থেকে অপসারণ করা হয়েছিল একটি আরও হালকা অপরাধের জন্য। তিনি কৃষিজ পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির স্বার্থে মার্কের মূল্যমান হ্রাস করার পক্ষে ওকালতি করেছিলেন মাত্র। শিল্পপুঁজিপতিদের জন্য ক্ষতিকর এই আর্থিক বিধর্মাচরণের জন্য শাখট ড্যারের পদত্যাগ দাবি করেন, এবং হিটলার তৎক্ষণাৎ শাখটকে সন্তুষ্ট করেন।
১৯৩৪ সালের শেষের দিকে হিটলারের অবস্থান ছিল নিম্নরূপ: “ফ্যুয়েরার নিঃসন্দেহে পরম ক্ষমতাধর, কিন্তু তিনি সর্বশক্তিমান নন। তাকেও মহৎ স্বার্থগুলোর প্রতি নমনীয় হতে হয় এবং জনমতের ওপর দমন-পীড়ন চালানোর সময়ও তার মধ্যে যে স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতির ধারা টিকে আছে তা তাকে বিবেচনা করতে হয়। গণআবেগ এখনও তার জন্য উদ্বেগের বিষয় নয়; তিনি আত্মবিশ্বাসী যে প্রচার দ্বারা তিনি এখনও তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন, এবং আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের বিনোদন দিতে পারবেন। দমন ও সন্ত্রাস চালানো হবে শেষ অস্ত্র হিসেবে, তিনি ব্রাউন আর্মির কম নির্ভরযোগ্য অংশকে দমন করেছেন। তার প্রাক্তন অর্থদাতা, বৃহৎ শিল্পের কর্ণধারদের প্রতি তিনি বেশি শ্রদ্ধা পোষণ করেন। তারা তাকে ছদ্ম-বিপ্লবী বামপন্থীদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে বলেছিল; নিজের ব্যক্তিগত কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করছেন বলে বিশ্বাস করে তিনি তৎক্ষণাৎ তাদের সেই আদেশ পালন করেছিলেন। সম্ভবত তিনি তাদের আদেশই পালন করতে থাকবেন”। (“দ্য নিউ স্টেটসম্যান অ্যান্ড নেশন”, ১১ আগস্ট, ১৯৩৪)।
বারবার হিটলার এবং তার দলের নেতৃবৃন্দ দাবি করেছেন যে জার্মানিতে জাতীয় সমাজতন্ত্রের বিজয় ইউরোপকে বলশেভিজম থেকে রক্ষা করেছে। “যদি নাৎসিরা জয়ী না হতো, বলশেভিজম কেবল জার্মানিকেই নয়, সমগ্র ইউরোপকেই জয় করত। নাৎসি সাফল্য ছিল সম্পূর্ণ বলশেভিক বর্বরতা থেকে আমাদের মুক্তিদাতা”। বাস্তবে, শুরুতে জার্মান ফ্যাসিস্টরা সমাজতন্ত্রী হওয়ার ভানও করেনি। ১৯১৯ থেকে ১৯২০ সালের বৈপ্লবিক দিনগুলোতেই তারা তাদের উদ্দেশ্য ঘোষণা করেছিল “লাল বিপদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ”। হিটলার ১৯২৩ সাল থেকেই এমপ্লয়ার’স এসোসিয়েশনের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা চাইতে শুরু করেন এই যুক্তিতে যে তার দল শ্রমিক-বিরোধী নীতি গ্রহণ করতে দায়বদ্ধ। “তিনি ক্ষমতায় আসার পর শ্রমিকদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন এমন নয়; তিনি শুরু থেকেই শ্রমিকদের বিরোধী ছিলেন”। (কনরাড হেইডেন, “হিস্ট্রি অব ন্যাশনাল সোশ্যালিজম”)। কেবলমাত্র ১৯২৬ সালেই হিটলারপন্থীরা পুঁজিবাদ-বিরোধী আন্দোলন শুরু করে। দলের কর্মসূচিতে ছদ্ম-সমাজতান্ত্রিক ধারাগুলো হিটলারের উদ্যোগে নয়, বরং স্ট্রাসার ভাইদের বিরোধিতার মুখে পড়ে যোগ করা হয়েছিল। ক্ষমতায় আসার পরেই স্ট্রাসার ভ্রাতৃদ্বয়কে দলীয় নেতৃত্ব থেকে সরানো হয়, এবং শেষ পর্যন্ত একজন নিহত হন ও অন্যজন দেশত্যাগ করেন।
হিটলারী শাসনের দ্বিতীয় বছরে দলের বামপন্থীরা শাসক গোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়াশীল নীতির বিরুদ্ধে অসন্তোষের স্পষ্ট লক্ষণ দেখাতে শুরু করে। দলে একটি বড় প্রলেতারিয়ান অংশ ছিল। ব্রাউন আর্মির সাধারণ কর্মী ও সদস্যরা ছিল মূলত বেকার তরুণ শ্রমিক। তারা অর্থনৈতিক ত্রাণের অতিরঞ্জিত প্রতিশ্রুতিগুলি পূরণ হবে বলে আশা করেছিল। “দ্বিতীয় বিপ্লব”-এর দাবি ক্রমশ জোরালো হচ্ছিল। ফলত হিটলারের সিংহাসনের পেছনের শক্তিগুলো বিরক্ত ও শঙ্কিত হয়ে পড়ে। জমিদার ও সামরিক নেতাদের পক্ষে ফন পাপেন হুমকি বক্তৃতা দেন। পাপেনের মাধ্যমেই হিটলার জার্মানির চ্যান্সেলর হয়েছিলেন। তিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে সিংহাসনে বসানো পুতুলটি যদি তার পৃষ্ঠপোষকদের ইচ্ছা অনুযায়ী আচরণ না করে, তবে তাকে ঠিক তত সহজেই নামিয়ে দেওয়া যাবে যত সহজে তাকে তোলা হয়েছিল। ক্রুপ ফন বোলেন ইকোনমিক অ্যাডভাইজরি কাউন্সিলের চেয়ারম্যান পদ থেকে পদত্যাগের হুমকি দেন। এই হুমকির অর্থ ছিল হিটলারী শাসনের প্রতি ভারী শিল্প মহলের সমর্থন প্রত্যাহার করে নেওয়া। সুতরাং, আদেশ দেওয়া হলো এবং হিটলারকে তা মেনে নিতে হলো। তিনি ১৯৩৪ সালের ৩০ জুন তার দলের কুখ্যাত “রক্ত শুদ্ধি” কার্যকর করেন “দ্বিতীয় বিপ্লবের বিপদ” দমনের উদ্দেশ্যে (গোয়েরিং)।
এইভাবে জমিদার, সামরিক নেতা ও পুঁজিপতিদের আদেশে কাজ করার সময় হিটলার ঘোষণা করেন: “আমাদের কর্মসূচি যুগান্তকারী, তাৎক্ষণিক নয়। আমাদের ব্যবস্থা হাজার বছর টিকে থাকবে। আমরা সহস্রাব্দের জন্য কাজ করছি। ধৈর্য ধরো! অপেক্ষা করো!” ভুল পথে চালিত তার অনুসারীদের দাবি করা শিল্পের সামাজিকিকরণের ব্যাপারে তিনি বিপজ্জনক পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিরোধিতা করেন, “কারণ এগুলো শিল্প প্রক্রিয়া থেকে সৃজনশীল উপাদান, ব্যক্তিত্বের শক্তিকে বাদ দেয়”। বড় জমিদারিগুলির জবরদখলও তার দলের মূল কর্মসূচির অংশ ছিল। ক্ষমতায় এসে তিনি মত প্রকাশ করেন যে “কার্যকর উৎপাদনের জন্য বড় জমিদারিগুলো অক্ষত থাকা প্রয়োজন”।
“নতুন জার্মানিতে যাদের হাতে পুতুলনাচের সুতোগুলো আছে, তারা হলেন ভারী শিল্পের শিল্পপতি, বৃহৎ অর্থলগ্নিকারী ও জাঙ্কার শ্রেণি। তাদের নির্দেশে হিটলার জাতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি থেকে ছদ্ম-সমাজতান্ত্রিক সুরটাও সরিয়ে দেন। পুঁজিবাদ তার অনুগত ভৃত্যকে আদেশ দেয় মুনাফায় হস্তক্ষেপ বন্ধ করার; হিটলার তা মেনে নেন; বিপ্লব শেষ”।(আর্নস্ট হেনরি, “হিটলার ওভার ইউরোপ”)। হিটলারের শাসনে জার্মানির অবস্থার এ হল এক সঠিক বর্ণনা। ফ্যাসিস্টদের সমাজতন্ত্রের দাবিটি ছিল প্রতারণা। শাসক শ্রেণীর দ্বারা ক্ষমতায় আসা নাৎসিরা তাদের মনিবদের লোভ মেটাতে জার্মানিকে ধ্বংস করছে।
ফ্যাসিস্টদের জাতীয়তাবাদও তাদের সমাজতন্ত্রের দাবির মতোই প্রতারণামূলক। জার্মানির মতো শিল্পোন্নত দেশে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থার উন্নতি ছাড়া প্রকৃত জাতীয় কল্যাণ সাধন করা যায় না। কারণ সেখানে শ্রমিক শ্রেণীই জনসংখ্যার বেশিরভাগ, এবং জাতীয় স্বার্থ নির্ধারণ করতে হবে সংখ্যাগরিষ্ঠের কল্যাণ দিয়ে। শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ জাতীয় কল্যাণের বিরোধী হতে পারে না। তাই, শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি ফ্যাসিস্টদের তীব্র শত্রুতা তাদের জাতীয় কল্যাণের দাবির সাথে সাংঘর্ষিক।
হিটলারপন্থীরা ভার্সাই চুক্তির বিরুদ্ধে কাঁদুনি গেয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমর্থন লাভ করে। তারা জাতীয় সম্মান পুনরুদ্ধার করতে চেয়েছিল। জার্মান জনগণের উপর অপমানজনক এই চুক্তি চাপিয়ে দেওয়া শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়া ছিল ফ্যাসিস্টদের যুদ্ধস্লোগান। কিন্তু ক্ষমতায় আসার এক বছরের মধ্যেই হিটলার ঘোষণা করেন: “যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের জনগণের সম্মান পুনরুদ্ধারের প্রয়োজন নেই। সেখানে কেউ তা আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়নি। আমাদের উপর শুধুমাত্র একটি কলঙ্ক এসেছিল। তা পশ্চিমে নয়, পূর্বেও নয়, বরং আমাদের নিজেদের ঘরেই। এই কলঙ্ক আমরা মিটিয়ে ফেলেছি”।(নুরেমবার্গ উৎসবে ভাষণ, সেপ্টেম্বর ১৯৩৩)। এই কলঙ্ক বলতে তিনি বুঝিয়েছিলেন বিপ্লবকে, যার বিজয়ই কেবল জার্মান জাতির প্রকৃত কল্যাণ নিশ্চিত করতে পারত।
সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষেত্রটি বাদ দিলে বাকি সব ক্ষেত্রেই ফ্যাসিস্টদের যুদ্ধংদেহী মনোভাবটা ছিল নিছক জনপ্রিয়তাবাদী বাগাড়ম্বর ও হুমকি। মিত্রশক্তিগুলোর মৌন সম্মতি ছাড়া ভার্সাই চুক্তির সামরিক ধারাগুলোকে হিটলারের নাটকীয়ভাবে বাতিল করা কখনই সফল হতো না। আজ জার্মানি আবার একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী গড়ে তুলেছে। কিন্তু চার বছর আগে, যখন ফ্যাসিস্ট সরকার ভার্সাই চুক্তি ছিঁড়ে ফেলে জার্মানিকে পুনরায় সশস্ত্র করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে, তখন ইউরোপীয় জাতিগুলোর রাজনৈতিক জোট ও সামরিক শক্তির সমীকরণ এমন ছিল যে মিত্রশক্তিগুলো চাইলেই যেকোনো সময় এই ব্লাফ ধরে ফেলতে পারত। ফ্রান্সে অনেকে যে “প্রিভেন্টিভ ওয়ার”-এর কথা বলছিল তা হলে নাৎসিদের কাছা খুলে দৌড়তে হত। সেই যুদ্ধটা জার্মান ভূমিতে হতো এবং দুই সপ্তাহের মধ্যে ফ্রাঙ্কো-পোলিশ জোটের সেনারা বার্লিন দখল করে নিত। এমন যুদ্ধে পশ্চিম জার্মানির শিল্পকেন্দ্রগুলি দ্রুত ফরাসিদের দখলে চলে যেত, এবং কোনো প্রতিরোধ হলে তা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতো। স্বাভাবিকভাবেই, নাৎসিদের পৃষ্ঠপোষকরা তা চাননি। হিটলারপন্থীদের নাটকীয় তলওয়ার ঝনঝনানিকে উৎসাহিত করে তাদের উদ্দেশ্য ছিল মাহার্ঘ অস্ত্র ব্যবসা থেকে মুনাফা লোটা। তারা যুদ্ধবাজির এই ঝুঁকিপূর্ণ খেলায় নামতে পেরেছিল কারণ তারা জানত ফ্রান্স তখনই আরেকটি যুদ্ধে জড়াতে অনিচ্ছুক। তাই, জার্মানি তার পরাজয় থেকে আবারও সশস্ত্র জাতি হিসেবে আবির্ভূত হয়ে “সূর্যের নিচে তার জায়গা” দাবি করতে পারলেও, এই সাফল্যের কৃতিত্ব ফ্যাসিবাদের দর্শন দ্বারা উদ্দীপিত “জার্মান পুরুষত্বের অদম্য সাহস”-এর নয়। নব্য-জার্মান সাম্রাজ্যবাদ হল মিত্রশক্তিগুলোর বিপ্লবের ভয়ে জন্ম নেওয়া এক বিকৃত বেজন্মা। জার্মানিতে বিপ্লবী শক্তিগুলোকে দমন করে নাৎসিরা আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের প্রতি তাদের মূল্যবান সেবা প্রদান করেছিল। তাদের এই কাজে সাহায্য করাটা তাই উচিত ছিল। ভার্সাই চুক্তিকে টুকরো টুকরো করে ফেলে দেওয়ার গৌরব হিটলারকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্ধ অনুসরণ আদায়ে সক্ষম করে তুলেছিল, যাদের সাহায্যে সে অন্তত সাময়িকভাবে বিপ্লবের জোয়ার ঠেকিয়ে দিয়েছিল।
জার্মানির সামরিক শক্তি পুনরুদ্ধারের মিরাকলকে যারা প্রশংসা করেন, তারা জানেন না কীভাবে মিত্রশক্তিগুলোর সাহায্য ও সম্মতিতে এই প্রক্রিয়াটি ঘটেছে। জার্মানিতে বিপ্লবের ভয়ে তারা এমন কাজ করেছিল। হিটলারের আবির্ভাবের বহু বছর আগেই, ভার্সাই চুক্তির সামরিক ধারাগুলো লকার্নো চুক্তির মাধ্যমে বহুলাংশে রদ করা হয়েছিল। জার্মানির রিপাব্লিকান গভমেন্ট দ্বারা সম্পন্ন এই চুক্তিটি, যাকে নাৎসিরা “জার্মানিকে মিত্রশক্তির কাছে বিক্রি করা হল” বলে অভিযোগ করে, সেই লাকার্নো চুক্তিটি দখলকৃত অঞ্চলগুলিকে ভার্সাই চুক্তিতে নির্ধারিত সময়ের বহু আগেই খালি করে দেয়। লকার্নো চুক্তির আরেকটি ছাড় ছিল অ্যালাইড কন্ট্রোল কমিশন প্রত্যাহার, যা জার্মানির নিরস্ত্রীকরণ ও বিশেষত রাইনের বাম তীরের বে-সামরিকীকরণ তদারকি করত। চেম্বারলেনের সোভিয়েত-বিরোধী ব্লক গঠনের ধারণায় মগ্ন ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্মানিকে এই ছাড়গুলি দেয়, যা কার্যত তার পুনঃসশস্ত্রীকরণের অনুমতি দিয়েছিল। এটি ঘটেছিল হিটলারের জনমোহিনী বক্তৃতা জার্মান পুরুষত্বকে জাতীয় সম্মান পুনরুদ্ধারের জন্য সংঘবদ্ধ করার বহু বছর আগে। চেম্বারলেনের অধীনে ব্রিটিশ কূটনীতি “বলশেভিক হুমকি”-র বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী জার্মানি চেয়েছিল। আর জার্মানিতে বিপ্লবের ঝুঁকি, যা সহজেই রাইন পার হয়ে যেতে পারত, ফ্রান্সকে ভীতসন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। ব্রিয়ান্ডের ভুলপথে চলা উদারনীতিবাদ ভার্সাই চুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত তার নিরাপত্তা ধ্বংস করেছিল।
অ্যালাইড কন্ট্রোল কমিশনের সাথে যুক্ত একজন বিশিষ্ট ব্রিটিশ আইনজীবী জে. এইচ. মর্গান, কে.সি., লিখেছেন: “এই দুটি চুক্তিই (দখলকৃত অঞ্চল খালি করা ও কন্ট্রোল কমিশন প্রত্যাহার) ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের সরকারগুলি কার্যকর করেছিল। এই দেশে খুব কম লোকই জানেন ব্রিটিশ ও ফ্রেঞ্চ সরকারগুলি কতদূর পর্যন্ত গিয়ে এই চুক্তিগুলি পালন করেছিল, এবং আসলে চুক্তির চেয়েও বেশি করেছিল। শুধু যে কন্ট্রোল কমিশনকে জার্মান সরকারের দেওয়া প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে প্রত্যাহার করা হয়েছিল তাই নয়, এই কাজে জার্মানির চলতি ত্রুটিগুলিও সংশোধন করা হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। রাইনল্যান্ডের বি-সামরিকীকরণের কাজ, অর্থাৎ ভার্সাই চুক্তির ৪৩ ও ১৮০ ধারা বাস্তবায়নও পরিত্যক্ত হয়েছিল”। (“ডেইলি টেলিগ্রাফ”, লন্ডন, ১৯৩৬ সালের এপ্রিলের শুরু)।
এই তথ্যসমৃদ্ধ ও যোগ্য সাক্ষী আরও সাক্ষ্য দেন যে এর আগেও কমিশন জার্মানির পুনঃসশস্ত্রীকরণে মদত দিয়েছিল বেসামরিকীকৃত অঞ্চলে কৌশলগত কাঠামোগুলো অক্ষত রেখে, জার্মান পক্ষের যুদ্ধসরঞ্জামগুলোর বাণিজ্যিক উপযোগিতা বিষয়ক বক্তব্যের ভিত্তিতে। এমনকি রাইনের বাম তীরেও, দুর্গাঞ্চল, পরিবহন ব্যবস্থা ও অন্যান্য “স্থায়ী সংঘবদ্ধকরণ” অক্ষত রাখা হয়েছিল লকার্নোর দিশার প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে সরিয়ে নেওয়া মিত্র বাহিনী দ্বারা। বছরজুড়ে জানা ছিল যে দখলকৃত অঞ্চলে জার্মান সিকিউরিটি পুলিশ ছিল আসলে ছদ্মবেশী রাইখসভেয়ার। কিন্তু সেই ক্ষেত্রেও, “জার্মান অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে ব্রিটিশ ও ফ্রেঞ্চ সরকার ১৯২৭ সালে এই বাহিনীগুলোকে রাইনল্যান্ডে থাকার অনুমতি দেয় এই শর্তে যে তাদের চরিত্র হবে বেসামরিক”।(প্রাগুক্ত)।
আরেকটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় ছিল “শ্যাডো আর্মি” তৈরি, যা ব্রিটিশ ও ফ্রেঞ্চ সরকার লকার্নো চুক্তি স্বাক্ষরের পর নীরবে মেনে নেয়। কন্ট্রোল কমিশনের চোখের সামনেই, ১৯২০ থেকে ১৯২৬ সালের মধ্যে জেনারেল ফন সেক্ট পুরানো সেনাবাহিনীর কাঠামো অক্ষত রেখেছিলেন এবং সাধারণ সৈন্যবাহিনী পুনঃপ্রবর্তনের পথ প্রস্তুত করেছিলেন। লকার্নো চুক্তি, জার্মানির পুনঃসশস্ত্রীকরণ প্রক্রিয়াকে থামানোর বদলে, যা তখন পর্যন্ত গোপনে চলছিল তাকে যেন আইনি বৈধতা দিয়েছিল।
সুতরাং, জার্মানিকে পুনরায় সশস্ত্র হওয়ার অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার বিতর্কিত গৌরবটা হিটলারের নয়। তার আগেই মিত্রশক্তির কাছ থেকে উপহার হিসেবে এটা পাওয়া হয়েছিল, এবং এই উপহারটি জার্মান জাতিকে দেওয়া হয়নি, বরং দেওয়া হয়েছিল তাদেরকে যারা জার্মান জাতিকে মহাযুদ্ধের বিপর্যয়ে নিয়ে গিয়েছিল এবং সেই কলঙ্ক থেকে বিপুল মুনাফা করেছিল। এখন তারা এই সহজে অর্জিত গৌরব থেকে আরও মুনাফা করার চেষ্টা করছে। কন্ট্রোল কমিশন প্রত্যাহারের এক বছরের মধ্যে জার্মান সরকারের সামরিক বাজেট দশগুণ বেড়ে যায়। এর অর্থ ছিল ভারী শিল্পগুলোর জন্য বিপুল বরাত। নাৎসিদের উগ্র জাতীয়তাবাদ ছিল বড় ব্যবসার জন্য বিপুল মুনাফার পুনঃসশস্ত্রীকরণ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার একটি অজুহাত। হিটলারের ক্ষমতায় আসার পরপরই মাসিক পুনঃসশস্ত্রীকরণ ব্যয় দাঁড়ায় মাসে একশ মিলিয়ন ডলার। তারপর থেকে তা দ্রুত হারে বেড়ে চলেছে। ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র সংসদীয় বাজেট প্রকাশের প্রক্রিয়া ত্যাগ করেছে। তাই অস্ত্রের পেছনে কত টাকা খরচ হচ্ছে তার সঠিক হিসাব করা খুব কঠিন। কিন্তু যোগ্য সামরিক বিশেষজ্ঞদের মতে, ১৯৩৪ সালে এটি ছিল এক হাজার মিলিয়ন মার্কের বেশি। আগের বছরের তুলনায় চল্লিশ শতাংশ বৃদ্ধি নির্দেশ করে। পরের বছর সামরিক বাজেট আবার দ্বিগুণ করা হয়। অনুমান করা হয় যে, হিটলারের শাসনের প্রথম চার বছরে পুনঃসশস্ত্রীকরণে মোট ব্যয় ছিল ষোল হাজার মিলিয়ন মার্ক। একই সময়ে আরও চার হাজার মিলিয়ন মার্ক ব্যয় করা হয়েছিল “জনসাধারণের কাজে”, যা বেশিরভাগই ছদ্মবেশী কৌশলগত নির্মাণ। অন্য কথায়, এখন পর্যন্ত ফ্যাসিস্ট সরকার সমগ্র মহাযুদ্ধে জার্মানির মোট ব্যয়ের প্রায় এক চতুর্থাংশ খরচ করে ফেলেছে।
এই বিপুল অর্থের বেশিরভাগই, যা কার্যত ভারী শিল্পের জন্য ভর্তুকি, অভ্যন্তরীণ ঋণের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়। জনগণকে কেবলই এই ঋণে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করা হয়। ১৯৩৫ সালে জার্মানির অভ্যন্তরীণ ঋণের পরিমাণ ছিল জাতীয় সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ। যেহেতু পুনঃসশস্ত্রীকরণ কর্মসূচি বর্তমান আয় দিয়ে পরিশোধ করা যায় না, তাই এটি ভবিষ্যতের আয় দিয়ে পরিশোধ করতে হবে। জাতির ভবিষ্যত অস্ত্র নির্মাতাদের কাছে বন্ধক দেওয়া হয়েছে। করের সীমা ছুঁয়ে ফেলা হয়েছে। ফলাফল হলো জনসংখ্যার বেশিরভাগের জীবনযাত্রার মান দ্রুত নিম্নগামী হওয়া। যারা সহজে দিতে পারে, তারা দায়িত্ব এড়ানোর পথ খুঁজে নেয়। ১৯৩৪ সালে একটি ডিক্রি জারি করা হয় যাতে সকল বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে ছয় শতাংশের বেশি লভ্যাংশের পুরোটা সরকারের কাছে জমা দিতে বলা হয়। তৎক্ষণাৎ, পুনঃসশস্ত্রীকরণের জাতীয়তাবাদী উন্মাদনা থেকে বিপুল মুনাফা করা বড় ট্রাস্টগুলোর (ক্রুপ, থিসেন, আই.জি. ফারবেন, এ.ই.জি. ইত্যাদি) ব্যালেন্স শিটে ছয় শতাংশের কম লাভ দেখানো হয়। অন্যদিকে, সঞ্চয় ব্যাংক, ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায় ও অন্যান্য সামাজিক বীমা প্রতিষ্ঠানের সমস্ত তহবিল সরকার “পুনঃসশস্ত্রীকরণ নোট”-এর বিনিময়ে অধিগ্রহণ করে। এভাবে, সমস্ত বোঝা পড়ছে গরিব মধ্যবিত্ত ও প্রলেতারিয়াতের উপর, যারা “জাতীয় সম্মান পুনরুদ্ধারের যুদ্ধ” যখন আসবে তখন তাদের জীবন দিয়েও মূল্য চোকাবে। এদিকে, ধনীরা জাতির খরচে আরও ধনী হচ্ছে। গরিবদের শোষণের সর্বশেষ কৌশল হলো বিক্রয় কর। এটি এক ধরনের স্থূল আয়কর, যা প্রদানকারীর আয়ের বিপরীত অনুপাতে বোঝা চাপায়। ধরুন, একজনের আয় একশ, সে প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে প্রায় সমস্ত টাকাই ব্যয় করে; এভাবে তার সমস্ত আয়ই করের আওতায় পড়ে। অন্যদিকে, যার আয় এক হাজার, সে একই উদ্দেশ্যে তার আয়ের একটি ক্ষুদ্র অংশই ব্যয় করে। আয় যত বেশি, করের আওতায় পড়া অংশ তত ছোট। এটি হলো ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট অর্থনীতির বাস্তব চিত্র।
জার্মান সরকারের সাথে যুক্ত একজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ লিখেছেন: “হিটলারের শাসনের গত দুই বছর আমাদের দেখিয়েছে যে, একমাত্র লাভবান হল অস্ত্র নির্মাতারা। কাঁচামালের ঘাটতির কারণে তাদের ক্ষতি সহ্য করতে হবে না, কারণ সরকারের আমদানি নীতি সামরিক উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কাঁচামালের আমদানিকে অগ্রাধিকার দেয় ভোক্তা পণ্য উৎপাদনের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের জায়গা কমিয়ে”।(পল ক্রসার, “দ্য নিউ রিপাবলিক”, নিউ ইয়র্ক, ৬ মার্চ, ১৯৩৫)।
গণভোগ জোর করে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভোগের মান সরকার নির্ধারণ করে দেয়। প্রধান প্রধান খাদ্যপণ্যের মান ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। পোশাকের ক্ষেত্রে এই পরিমান অর্ধেকে নামিয়ে আনা হয়েছে। জোরপূর্বক কমানো ভোগের মান মজুরি সমন্বয়ের মাপকাঠি হিসেবে কাজ করে। ছোট ব্যবসায়ী, কারিগর ও কৃষকরা শ্রমিক শ্রেণীর ক্রমহ্রাসমান ক্রয়ক্ষমতার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নাৎসি নেতারা কোনো উন্নতির প্রতিশ্রুতি দেন না। বরং তারা জাতীয় সম্মানের জন্য ত্যাগ ও আরও ত্যাগের দাবি করেন। গোয়েবলস চূড়ান্তভাবে ঘোষণা করেছেন যে “মজুরি বাড়ানো যাবে না”। অবশ্যই না। এর কারণ দিয়েছেন নাৎসি অর্থনীতিবিদ উইন্ডশুহ, যিনি স্বীকার করেন যে বর্তমান মজুরিতে দাম আরও বাড়লে জীবনযাত্রার মান কমবে; কিন্তু তিনি অস্ত্রশিল্পের কাঁচামালের জন্য প্রয়োজনীয় রপ্তানি বাড়ানোর আহ্বান জানান এবং নির্মমভাবে বলেন যে “জীবনযাত্রার মান এই উদ্দেশ্যের অধীনস্থ হওয়া উচিত”। এটা কোনো একক মত নয়। কর্তৃত্বপূর্ণ নাৎসি নেতারা বারবার জাতীয় সমাজতন্ত্রের নিম্নলিখিত স্লোগানটি ঘোষণা করেছেন: “যদি জার্মানি মুক্ত ও দুঃসাহসী হয় এবং পর্যাপ্ত বন্দুক থাকে, তবে মাখন, ডিম ও কাপড়ের মতো তুচ্ছ জিনিসের জন্য অত চিন্তা কিসের?”
এইভাবে জাতিকে অর্থনৈতিকভাবে ধ্বংস করা হচ্ছে “জাতীয় সম্মান” পুনরুদ্ধারের জন্য। জার্মান জনগণকে রুটির বদলে সার্কাস দেখানো হচ্ছে। কিন্তু এই সার্কাসও একটি বিপজ্জনক খেলায় পরিণত হবে, যদি নাৎসিদের যুদ্ধবাজি সত্যিই জার্মানির পূর্বশত্রুদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়।
কেবলমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষেত্রেই নাৎসি যুদ্ধবাজরা যা বলে সেটাই বাস্তবায়ন করতে চায়। তাদের বৈদেশিক নীতি বিসমার্কের “ড্রাং নাচ ওস্টেন” (পূর্ব দিকে ধাবিত হওয়া) নীতিতে পরিচালিত হয়। বলশেভিজম ধ্বংস করে রাশিয়ার উর্বর ভূমি দখল করা নব্য-জার্মান সাম্রাজ্যবাদের স্বপ্ন। ক্ষমতায় আসার অব্যবহিত পরেই হিটলার সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর আক্রমণের জন্য একটি আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। বলশেভিজমের আবাসভূমির বিরুদ্ধে এই পরিকল্পিত পবিত্র ধর্মযুদ্ধে নাজিরা জার্মানির জাতীয় শত্রু, যথা ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের সাথে জোট বাঁধতে প্রস্তুত ছিল। ভার্সাই চুক্তির অপমান জার্মানির উপর চাপিয়ে দেওয়া শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিশোধের যুদ্ধের জন্য আন্দোলন ছিল সম্পূর্ণ ব্লাফ। ১৯৩৩ সালের মার্চে হিটলার বার্লিনে পোলিশ মন্ত্রীর সাথে একটি গোপন বৈঠক করেন। তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর যৌথ আক্রমণের প্রস্তাব দেন। পোল্যান্ডও জার্মানির জাতীয় শত্রুদের মধ্যে গণ্য ছিল। কিন্তু হিটলার সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পোলিশ সাহায্য পেতে পুরানো ক্ষোভ ভুলে যেতে প্রস্তুত ছিলেন। জানা যায়, তিনি পোল্যান্ডের সাথে রাশিয়ার অঞ্চল ভাগ করে নেওয়ার প্রস্তাবও দিয়েছিলেন। হিটলারের পরবর্তী কূটনৈতিক পদক্ষেপ ছিল রোজেনবার্গকে লন্ডনে তার বিশেষ দূত হিসেবে পাঠানো, যার মিশন ছিল ব্রিটেনকে একটি সোভিয়েত-বিরোধী জোটে টানা। এটি লক্ষণীয় যে জাতীয় সমাজতন্ত্রের এই উচ্চ পুরোহিত লন্ডন সফরে রয়্যাল ডাচ পেট্রোলিয়াম কম্বাইনের প্রধান ডিটারডিং-এর অতিথি ছিলেন, যিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে অবিরাম ষড়যন্ত্রের জন্য কুখ্যাত। রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সযত্ন লালিত প্রিয় স্বপ্ন স্থগিত রাখতে হয়েছিল হিটলারকে, কারণ তা লন্ডন বা প্যারিসে অনুকূল সাড়া পায়নি। এমন নয় যে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের শাসকরা এরকম একটা যুদ্ধের বিরোধী ছিলেন, কিন্তু তারা বিষয়টা হিটলারের চেয়ে ভালো জানতেন, এবং তাই এই দুঃসাহসিক কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে অনিচ্ছুক ছিলেন।
বাস্তবে, নাৎসিরা শুধু ইংল্যান্ডের সাথেই নয়, এমনকি ফ্রান্সের সাথেও সমঝোতায় আসার চেষ্টা করেছে, যাকে তারা প্রকাশ্যে ঘৃণা করে। ভার্সাই চুক্তি লঙ্ঘন করে জার্মান সেনা নাটকীয়ভাবে রাইনল্যান্ডে প্রবেশ করার মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে হিটলার একজন গুরুত্বপূর্ণ ফরাসি সাংবাদিককে বিশেষ সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন। সেই সময় তিনি ফ্রান্সের সাথে একটি চুক্তিতে আসার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। ফরাসি সাংবাদিক তার আত্মজীবনীতে প্রকাশিত ফ্রান্স-বিরোধী অনুভূতির দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করলে হিটলার ব্যাখ্যা করেন যে ওটা কেবল দেশের ভেতরের খোরাকের জন্য ছিল। যেহেতু রাইনল্যান্ডে প্রবেশ ফ্রান্সের প্রতি কোনও হুমকির উদ্দেশ্যে ছিল না, এবং আগে থেকেই এই বিষয়ে আশ্বস্ত করা হয়েছিল, তাই ভার্সাই চুক্তি বাতিলের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। যদি ফ্রান্স ব্যবস্থা নিত, তাহলে এই পদক্ষেপ সহজেই প্রতিহত করা যেত। জার্মানি তখনও একটি বড় যুদ্ধের ঝুঁকি নেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল না। জানা যায়, জেনারেল স্টাফ এই উত্তেজক পদক্ষেপের বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু ফ্রান্স বা ইংল্যান্ড এমন কিছুই করতে চায়নি যা দেশের ভেতরে হিটলারের প্রেস্টিজ অবশ্যম্ভাবি ক্ষুণ্ণ করবে। কারণ তা করলে নাৎসি শাসনের পতন ও রাইনের ওপারে বিপ্লবের ঝুঁকি ফিরে আসাকে ত্বরান্বিত করবে। তাছাড়া, ফ্রান্সকে আগে থেকেই আশ্বস্ত করা হয়েছিল যে জার্মানি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চায় না।
নাজি পার্টির ভেতরে “রক্ত শুদ্ধি”-র অল্প সময় পরেই হিটলারের সবচেয়ে বিশ্বস্ত সহযোগী রুডলফ হেস একটি “শান্তি ও শুভেচ্ছা” বার্তা পাঠান চরম জাতীয়তাবাদী ফরাসি যুদ্ধ-বিরোধী সমিতিকে। তিনি ফরাসি সৈন্যদের বীরত্বের প্রশংসা করেন। তিনি এমনকি ঘৃণ্য ক্লেমেন্সোর শিষ্য, ফরাসি পররাষ্ট্রমন্ত্রী বারথোকেও প্রশংসা করেন, যিনি ভার্সাই চুক্তি নির্ধারণ করেছিলেন, যা ছিঁড়ে ফেলা ছিল নাৎসিদের ঘোষিত মিশন। হেস স্নেহশীলভাবে শান্তির কথা বললেন। তিনি তাদের ঘৃণিত শত্রুকে এই কথাগুলো বললেন: “একজন গর্বিত সৈনিক হিসেবে আরেকজন গর্বিত সৈনিকের কাছে আমি জিজ্ঞাসা করছি, যুদ্ধ হওয়া কি আবশ্যক? আমরা কি একত্র হতে পারি না? আমরা কি, একসাথে, সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার করে মানবজাতিকে যুদ্ধের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করতে পারি না?”
নাৎসি যুদ্ধবাজির ব্লাফ ও বড়াই তখনই প্রকাশ পায় যখন জানা যায় যে ১৯২৪ সাল থেকেই হেস ছিলেন ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সবচেয়ে সোচ্চারে ঘৃণার গান গাওয়া মানুষ। তার অশ্লীল ঘৃণা নিম্নলিখিত কবিতায় প্রকাশ পেয়েছিল: “হেই, ফ্রান্স, তুমি মরবে সেখানে, যাতে আমরা বাঁচতে পারি”। এগুলো সবই ছিল উগ্র জাতীয়তাবাদকে উসকে দেওয়ার বাগাড়াম্বর, যা কেবল বড় শিল্পপতিদের অস্ত্র ব্যবসায় অর্থ উপার্জনে সাহায্য করেছে মাত্র। এটাই ফ্যাসিস্ট জাতীয়তাবাদের একমাত্র অর্জন।